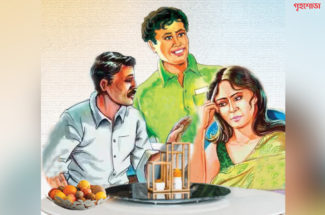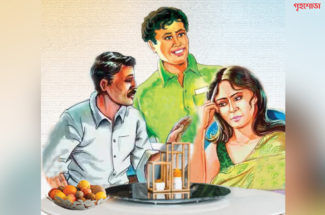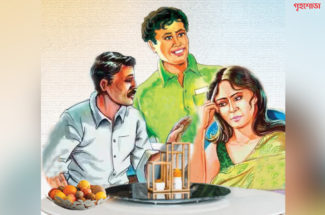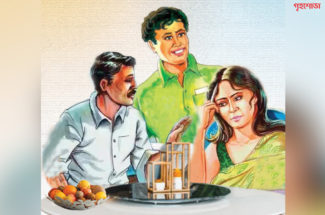ঘরের দেয়ালময় দাদার পছন্দের ক্রিকেটারদের পাশাপাশি ইন্দ্রজিতের নায়করা– ব্রুস লি, জ্যাকি চ্যান, অক্ষয় কুমার। এই তিনজন তারকার চটকদার অনাচ্ছাদিত সিক্সপ্যাক সমৃদ্ধ পোস্টারের পাশে, এখন জুড়েছে আরও কয়েক জনের মলিন ছবি– মাসুতাৎসু ওয়্যামা, হিদেয়েৎসু আশিয়ারা। পত্রিকার পাতা কাটা কাগজের ঝাপসা ছবিতে মুখ চেনার উপায় নেই, শুধু পোশাক জানান দিচ্ছে তারা মার্শাল আর্টিস্ট। জ্যাকি চ্যান-এর মতো কমেডি বা ব্রুসলির মতো তাক লাগানো হলিউডি অ্যাকশন হিরো নয়, অক্ষয় কুমারের মতো নাচিয়ে ঝাড়পিট করা বলিউড তারকাও নয়। এরা ক্যারাটের এক একটি ঘরানার নির্মাতা। অবশ্য জিৎকোন্ডোর মতো ক্যারাটে আর তাইকোন্ডোর মিশেল দেওয়া লড়াকু শিল্পের জনক হিসাবে ব্রুস লিরও একটা বাড়তি সমীহ প্রাপ্য। ইন্দ্রজিৎ অতশত না বুঝে অক্ষয়, ব্রুসলিদের দেখেই ক্যারাটেতে ঝুঁকেছিল। মার্শাল আর্ট কথাটার সঙ্গেও তখন পরিচয় ঘটেনি। দত্তপুকুরে তাদের বাড়ির কাছে যে – সম্মিলনি ক্লাব, সেখানে সাদা ঢোলা পোশাক আর কোমরে বাঁধা বেল্ট নিয়ে ছেলেদের ‘ইয়া ইয়া’ করে হাত পা ছুড়তে দেখে তারও শখ তীব্র হয়। মা-বাবার কাছে আবদার করে ঢুকেও পড়ে।
একদিন এক বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা মাঝ বয়সি এক পুরুষকে তাদের অনুশীলন দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসতে দেখে। মন্তব্য কানে আসে, ‘বেসিক স্টান্সগুলো না শিখেই কিক, আপার ব্লক, লোয়ার ব্লক? বেশ বেশ। এসবই তো চলছে এখন। কারই বা জ্ঞান আছে আসল জিনিস শেখাবার আর কজনেরই বা ধৈর্য আছে শেখবার? কয়েক বছরের মধ্যেই তো সব ব্রাউন বেল্ট, ব্ল্যাক বেল্ট পেয়ে যাবে সিলেবাস কমপ্লিট করে।’
ইন্দ্রজিৎ সেদিন থেকে পিছু নিয়েছিল ব্রহ্মদেশ থেকে আসা এই একটেরে লোকটার। আসল জিনিস শিখবে। ভদ্রলোকের ছাত্র পেটানোর মোহ নেই। খেদিয়েই দিয়েছিলেন ইন্দ্রজিৎকে আজকালকার নিষ্ঠাহীন ফাঁকিবাজ ওপর চালাক ছোকরার দলে ফেলে। ইন্দ্রজিৎও একদিন বলেই ফেলল, ‘শেখানোর মুরোদ নেই যখন, অন্যের তালিমকে হ্যাটা দেওয়া কেন? শুভ্রাংশু স্যাররা তো কিছু দিচ্ছে আমাদের মতো ফালতু ছেলে ছোকরাদের। আপনি ক’জনকে তৈরি করেছেন?’
ভদ্রলোক খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ইন্দ্রজিতের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, ‘বেশ কাল ভোর পাঁচটায় এসো। স্কুল কটা থেকে? দেখি তোমার কত এলেম, কত নিষ্ঠা।’ ওঁর কাছ থেকেই শোনা মাসুতাৎসু হলেন কায়োকুশিন ধারার প্রবর্তক। অত্যন্ত আক্রমণাত্মক এই শৈলীটি ক্রীড়ামঞ্চে গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্বজুড়ে শোটোকান ও গোজুকান-এরই রমরমা। হিদেয়ুকো আশিয়ারা কায়োকুশিনকে একটু নরম ধাঁচে ফেলে নিজস্ব ঘরানা তৈরি করেন, কায়োকুশিন আশিয়ারা। বিনোদ শেঠ ব্রহ্মদেশে থাকা কালে এই শৈলীটিই ‘সামান্য একটু’ শিখেছিলেন।
পরের দিন ইন্দ্রজিতের নবলব্ধ জেনারেল নলেজের ভাণ্ডার দেখে আকৃষ্ট হয়ে সম্মিলনি ক্লাবের আরও কিছু ছেলে বিনোদদার বাড়িতে হানা দেয়। বিনোদদার উঠোনে অতজনের জায়গা হবে না। তিনি বাধ্য হয়ে বাড়ির পাশের মাঠে প্রশিক্ষণ শুরু করলেন। দক্ষিণার কথা জানতে চাইলে হাসতেন, ‘আগে মাসখানেক দেখি।’
বস্তুত এক মাসের আগেই ইন্দ্রজিৎ আর সুজয় ছাড়া বাকিরা কেটে পড়েছিল। তারা আবার নাকে খত দিয়ে সম্মিলনিতে। অনেক ত্যারছা মন্তব্য হজম করতে হয়েছিল তাদের, ‘দেখি আসল জিনিস কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস তোরা? শার্টের পকেটে না প্যান্টের পকেটে, নাকি জাঙিয়ার বুক পকেটে?’
বিনোদদা শুরু করেছিলেন দাচি বা স্টান্স দিয়ে। কিবাদাচি বা ঘোড়সওয়ারের ভঙ্গি, জাঙ্গুৎসুদাচি বা সামনে ঝোঁকার কায়দা, কোকুৎসুদাচি বা পেছনে ঝুঁকে দাঁড়ানোর কৗশল, সানচিংদাচি বা থ্রি পয়েন্ট স্টান্স, কুমিতেদাচি বা রণপ্রস্তুতি– এইসব। দুই পায়ের নানারকম অস্বাচ্ছন্দ্যকর ভঙ্গি ও হাতকে বিশেষ অবস্থানে রেখে দাঁড়িয়ে থাকা। শুরুর কিবাদাচি অনেকটা ভরতনাট্যমের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। প্রথমটায় উৎকটাসনের মতো সহজ মনে হলেও যখন ওই স্টান্সে পনেরো মিনিট দাঁড়াতে বলা হতো, বেশিরভাগই ‘উঃ আঃ’ করে সাত আট মিনিটের মাথায় উঠে দাঁড়াত।
সময়টা বাড়তে থাকলে ছাত্র সংখ্যা কমতে থাকল। কেউই জাঙ্গুৎসুদাচির পর টিকে থাকেনি। ইন্দ্রজিৎ আর সুজয়কে যখন কোনও স্টান্সে এক ঘণ্টা পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রেখে দিতেন বিনোদদা, প্রবল যন্ত্রণাবোধটা যখন ক্রমশ অস্তিত্ব অসাড় করে দিত, তখন ইন্দ্রজিতের সংশয় হতো, লোকটা সত্যিই কিছু শেখাতে চায় তো। কিন্তু কষ্ট সহ্য করার অলৗকিক ক্ষমতা অর্জনের সাথে সাথে মাসখানেক পর স্নানের সময় নিজের উরু আর গুলির পেশির দিকে তাকিয়ে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। নার্সিসাসের মতো নিজেকে আয়নায় দেখে যেত। মুখখানা তো তার মারকাটারি ছিলই। কিন্তু শরীর ডিগডিগে, হাত-পা টিংটিঙে। ওই সুগঠিত পা’দুটো ইন্দ্রজিৎ পুরকায়স্থেরই তো? শুধু দাঁড়াতে শিখেই এই? তাহলে হাত পা ছুড়ে অক্ষয় মার্কা চেহারা পেতে কত দিন?
সুজয়ের চেহারা বরাবরই দোহারা। তার গায়ের জোর, ঘুসির পরিধি অনেক বেশি। তবু ইন্দ্রজিৎ ওর সঙ্গে সমানে টক্বর দিয়ে যেত। ওর সম্পদ ছিল নমনীয়তা, গতি আর অ্যাকিউরেসি যাকে বাংলা করে ত্রুটিহীনতা বললে বাড়াবাড়ি শোনাতে পারে। সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন কেই বা হতে পারে? বছর তিনেক পর সুজয় গেল অন্য গুরুর কাছে। বিনোদদার শিক্ষানবিশি যত উচ্চাঙ্গেরই হোক, তিন বছরেও একটা ন্যূনতম ‘ইয়েলো বেল্ট’-ও দিতে পারল না। কোনও স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় যে। ওদিকে, গৗরাঙ্গরা লম্ফঝম্প করে ব্রাউন বেল্ট থেকে এখন ব্ল্যাক বেল্টের দাবিদার। সম্মিলনি নয়, সুজয় গেল কলকাতার এক নাম করা প্রতিষ্ঠানে। তারা সোটোকান শৈলী শেখায়। তা হোক। সুজয়ের অসুবিধা হল না। বছর দুয়েকের মধ্যে সে-ই নতুন বাচ্চাদের তালিম দেওয়ার কাজ পেয়ে গেল। ক্যারাটেকেই ধ্যান জ্ঞান করেছে সে। মাধ্যমিকে ভালো ফলের অভিলাষ নেই, উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চায় না, তার পরে না পড়লেও চলে।
সুজয় বন্ধুকে লুকিয়ে চলে যায়নি। সঙ্গে নিতেই চেয়েছিল। কিন্তু ইন্দ্রজিতের পড়াশুনোয় ভালো হিসাবে মাধ্যমিকে স্টার পাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল, উচ্চমাধ্যমিকের পর জয়েন্ট ইত্যাদির পরিকল্পনা ছিল। স্কুল টিউটোরিয়াল করে বাড়ির কাছে বিনোদদার আখড়াটা চালানো যায়, কলকাতায় দৗড়ে সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়। তাছাড়া বিনোদদাকে ভালোও বেসে ফেলেছিল। ইন্দ্রজিতের বাবা এসে মাস তিনেক বিনে পয়সায় শিক্ষার পর খামে ভরে টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই থেকে ছেলের হাতেও মাসের শুরুতে খাম পাঠিয়ে দিতেন। সুজয়কেও লজ্জায় পড়ে গুরুদক্ষিণা চালু করতে হয়েছিল। কিন্তু এমন নির্লোভ আপনভোলা গুরু আজকের যুগে কেন, ত্রেতা যুগেও কেউ ছিল কিনা কে জানে? অন্তত দাপরে যে ছিল না, তার প্রমাণ দ্রোণাচার্য, পরশুরামরা রেখে গেছেন। গুরুগৃহে শ্লোক মুখস্থ ও পেট ভাতার বিনিময়ে বৈদিক যুগের ছাত্রদের গুরুর গরু চরানো, ক্ষেত চষা, বাড়ির কাজ সবই করতে হতো। সে অন্যত্র গেল না।
কিন্তু বিনোদদা বিনা নোটিসে বেমক্বা হার্টফেল করে চলে গেলেন। অমন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, কোনও মন্দ দোষ বা নেশা অন্তত ছিল না। হিসাব মিলছিল না। অনাত্মীয় মানুষটা কেন বার্মা ছেড়ে এই দত্তপুকুরে জমি কিনে বসবাস শুরু করেছিলেন, সেটাও অজানা থেকে গেল। উনি মারা যাওয়ার পর কোনও এক দূর সম্পর্কের ভাইপো নিজেকে একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী প্রমাণ করে ওই বাড়িতে সপরিবারে প্রতিষ্ঠিত। বাড়ির উঠোনে এখন দড়িতে শাড়ি, জামা, কাঁথা ঝোলে এক গাদা। সম্মিলনিতে ফিরে যাওয়ার মুখ নেই। ক্যারাটে তার এই পর্যন্তই ভাগ্যে ছিল।
আজকাল জয়েন্টের সিট অনেক বাড়ানো হয়েছে। নব্বই দশকের গোড়াতেও মেডিকেলের আসন ছিল হাজারের কম, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বারোশোর মতো। এখন নাকি বসলেই পাওয়া যায় প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর রমরমায়। বাবার ইচ্ছে কারিগরি, নিজের আয়ত্বে জীবনবিজ্ঞান। দুটোতেই বসেছিল। মেদিনীপুরের একটা কলেজে অ্যাডমিশন হয়েও যেত। কিন্তু বাবা শিবপুর, যাদবপুর বা বড়ো জোর উত্তরবঙ্গের সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাড়া প্রাইভেট কলেজগুলোতে পড়ে কিছু শেখা যায় বলে মানতেই নারাজ। হয়তো খরচায় কুলোলে মত বদলাতেন। মা বলেছিলেন, ‘পলিটেকনিক দে’। বাবা নাক সিঁটকে বলেন, ‘কোথায় বিই, আর কোথায় পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়ার? যে ডাক্তার হওয়ার যোগ্য, তাকে বলছ আয়া হয়ে থাক। অশিক্ষিত মেয়েমানুষের বুদ্ধি আর কাকে বলে? দরকার হলে ফিজিক্স নিয়ে জেনারেল পড়বে।’
‘কেন তোমার বন্ধু তিমিরবাবু পলিটেকনিক পাস করেই তো কোম্পানির অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে রিটায়ার করবে। আমি যেটা সহজে হবে আর ও পারবে সেটা বলেছি। মুখ্যু মানুষের খোঁটা তো নতুন নয়। তুমি ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে টেকনিক্যাল অফিসার…’
‘যা বোঝো না, তাই নিয়ে কথা বোলো না। অফিসে আমার কাছে এখনও সবাই আসে যে-কোনও টেকনিক্যাল সমস্যা নিয়ে, এমনকী যে-কোনও ক্রিটিক্যাল চিঠি ড্রাফট্ করাতে হলেও অবিনাশ পুরকায়েত। এত বছর কাজ দেখিয়ে…। আমার দুর্বল জায়গায় একদম ঘা দেবে না। আদর্শ স্ত্রী হওয়ার শিক্ষাই পাওনি, আর ছেলের পড়াশুনো নিয়ে ফোড়ন কাটতে এসেছে…’
দাদা বাবাকে কিছু বলতে সাহস পায় না। মায়ের ওপরই বিরক্তি প্রকাশ করে। সে নিজের জেদে এমকম করে আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভালো চাকরি করে। ইন্দ্রজিতের এখনও পড়াশুনোই শেষ হয়নি। তবু দাদা অরবিন্দের ভাষায় সে বেকার। ছোটো ভাইয়ের কেরিয়ার নিয়ে আলোচনা হতে একদিন মন্তব্য করল, ‘মা, বাবার কিন্তু বেশিদিন চাকরি নেই। ভস্মে ঘি ঢালার পর নিজেদের খাওয়া পরার ব্যবস্থাটা যাতে থাকে সেটা দেখো।’
সারা জীবন সবার জন্য এত করে নিজের ছেলেকে কি কোনও নৈতিকতা শেখাতে পারেননি অবিনাশ? বুড়ো মানে অরবিন্দ নিজের বাবাকে দেখেনি কীভাবে ঠাকুমা দাদু তিন কাকা, তিন পিসির অত বড়ো সংসার টেনেছেন? বাড়িতে এসোজন বোসোজন লেগেই থাকত। মা অভূক্ত থাকলেও কোনওদিন অভিযোগ করেননি। এখনও দুপুরে এলে কেউ না খেয়ে যেতে পারে না। সেই বাপ মার ছেলে হয়ে নিজের মায়ের পেটের ভাইয়ের দায়িত্ব এড়িয়ে হিংসা? ছোটনের তো এখনও দায়িত্ব নেওয়ার সময় শুরুই হয়নি। এখনও এই সংসার বাপের টাকায় চলে। রোজগেরে ছেলে খেয়াল খুশি মতো এটা সেটা শখের জিনিস কিনে নিজের ঘর সাজায়। সংসারে দেওয়ার মধ্যে পুরোনো ফ্রিজ বদলে একটা দুই দরজার ফ্রিজ কিনেছে। সেটাতেও সদা সতর্ক। যেন সে ছাড়া আর কেউ রেফ্রিজারেটর ব্যবহার করতে জানে না, নষ্ট করে ফেলবে। ছোটনের মতো শান্ত ও বাধ্য ভাই, যে বাবা দাদার ফরমাসে দিনে শতবার দোকান হাট ইলেকট্রিক অফিস, গ্যাসের দোকান দৌড়োচ্ছে, এমনকী পরীক্ষার আগেও মুখে কোনও ভাবান্তর ঘটায় না, তার প্রতি কেন এত বিদ্বেষ? ছোটো ছেলেটার মুখচোখ মায়ের আদলে বেশ চোখা চোখা, বাবার মতো মাঠো মাঠো গায়ের রং। বড়োর মাথা আর গায়ের রং দুটোই টকটকে পরিষ্কার, শুধু মনটাই সাফ হয়নি। …কাঁধে ব্যথা নিয়ে ইন্দ্রজিৎ দাদার ঝাঁজের কারণ খানিকটা অনুমান করতে পারে।
কস্তুরী সল্টলেকের একটা কল সেন্টারে চাকরি করে। শিফ্ট ডিউটি। কখনও ভোরে উঠে দৗড়োতে হয়, কখনও দুপুরে আবার কখনও সময় রাত্রি আটটায় অফিসের বাস ধরার জন্য এই মোড়ের মাথায় এসে দাঁড়ায়। অফিস ফেরতা তাকে প্রায় রোজই দেখত অরবিন্দ। একবার রবিবারে বাজারে দেখা হওয়াতে দুজনেই দুজনকে দেখে হেসেছিল, ‘বাজার করতে?’
কস্তুরীর নাইট শিফ্ট না থাকলে নিয়মিত দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই ছোটো ভাই নিয়ম করে বাজার করলেও রবিবার অরবিন্দ একবার বাজারে চক্বর দিয়ে যায়। রবিবার সকাল আটটা নাগাদ যেতে পারলে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সবজিপাতি, মাছ মাংস কী লাগবে জানা না থাকায় খান দশেক মিষ্টি কিনে বাড়ি ফেরে। কস্তুরীকে দেখতে পেলে খানিক গল্পগুজব আর প্রশ্ন, ‘নাইট শিফট কবে থেকে?’
আমেরিকান শিফট থাকলে কস্তুরী আজকাল একটু আগে আগেই অফিসের বাসের জন্য মোড়ের মাথায় অপেক্ষা করতে থাকে। আর অরবিন্দ স্টেশনে নেমে একটু দেরিতে বাড়ি ঢোকে।
‘রবিবার দিন বাজার ছাড়া আর কোথাও দেখা করা যায় না?’
‘এই তো দেখা হচ্ছে।’ হেসেছিল কস্তুরী।
অতঃপর দুজনেরই বাজারের ঘটা বেড়ে যায়। রোজগেরে ছেলে শুধু মিষ্টি কিনে বাড়ি ফিরলে ভালো দেখায় না বলে মাছ, মাংস, পনির, গোলদারি যেসব দোকানে কস্তুরী লাইন দেয়, অরবিন্দকেও সেখানে সেখানে হাজিরা দিতে গিয়ে এটা সেটা কিনতেও হয় মাঝেমধ্যে। যদিও জানিয়ে দেয়, সংসার খরচ বাবদ মা আর বাজার বাবদ ছোটো ভাইকে টাকা দেওয়াই আছে। কস্তুরীর একটাই উত্তর, মৃদু হাসি।
ফেরার পথে একটা চায়ের দোকানে খানিকক্ষণ বসা। দুজনেই বাড়ি গিয়ে মায়ের হাতে বানানো চা খেতেই পছন্দ করে। তবু। চায়ের দোকানে বসার প্রস্তাব অরবিন্দের হলেও তার খুচরোর অভাবে দাম বেশির ভাগ কস্তুরীই মেটায়। সঙ্গের হাসিটা ফাউ।
সেদিনও চা খেতেই ঢুকেছিল। দোকানটায় বড্ড বেশি ভিড় ছিল ওইদিন। একদল টি-শার্ট পরা ছোকরা উচ্চকণ্ঠে গুলতানি করছিল। কস্তুরী বলল, ‘আজ থাক। এত ভিড়ের মধ্যে…। চেয়ারও তো ফাঁকা দেখছি না’।
‘কেন, এই তো জায়গা ফাঁকা ওদিকে। সব সময় কি অধৈর্য হলে চলে? ফাইভস্টার হোটেলেও অনেক সময় ক্যাফেটেরিয়ায় টেবিল পেতে লাইন দিতে হয়। হাবু দা চারটে বেগুনি আর দুটো চা দাও।’
‘না না। আজ এই ক্যালর-ব্যালোরের মধ্যে বসতে ইচ্ছা করছে না। আমার বাড়িতে এসো বরং, চা খেয়ে যাও।’
একটা তালঢ্যাঙা লোক কস্তুরীর দিকে মন্তব্য ছুড়ে দিল, ‘ভিড়ে পোষাচ্ছে না? নিরিবিলি চাও? সকালবেলাতেই ফুর্তির ফোয়ারা বসাবে নাকি মান্তু? সন্ধেটা ফ্রি থাকলে আমাদের কাছে এসো না, সব পুষিয়ে দেব।’
‘একদম বাজে কথা বলবেন না। মিনিমাম ভদ্রতাটুকু নেই। এদের জন্যই আমি এখানে বসতে চাইছিলাম না। এখন বুঝেছ তো? শুধু শুধু এইসব নোংরা কথা শুনতে হল।’ কস্তুরী বেশ শান্ত মিষ্টি মেয়ে। এভাবে রেগে গলা চড়িয়ে কথা বলতে দেখেনি অরবিন্দ।
‘ঠিক আছে, ঠিক আছে। আজ থাক। চলো যাই।’ অরবিন্দ কস্তুরীর বাহু ধরে টান দিল।
ওই দলের আর একজন উঠে এসে বলল, ‘মেয়েছেলের হাত ধরে টানাটানি করছিস। তার বেলা কিছু নয়। আর আমার ফ্রেন্ড দুটো রসিকতা করল তো ইজ্জত খসে গেল?’ ছেলেটা সোজা কস্তুরীর অন্য হাত ধরে টান লাগাল।
‘একী? একী অসভ্যতা! ছাড়ুন বলছি হাত। আমি কোথায় বসব, কার সাথে চা খাব আমার ব্যাপার। আপনারা মাথা গলানোর কে? হাবুদা কিছু বলুন। দেখছেন তো কী করছে।’
হাবুদা মন্তব্য করল, ‘শালা, মেয়েছেলে থাকা মানেই ঝঞ্ঝাট!’
বাকিরা কেউ কিছুই বলছে না। গুনগুন করে যে আওয়াজটা হল তাতে মনে হল হাবুর কথাটা একাধিক সমর্থন পেল। অরবিন্দও চুপ। সে কস্তুরীর হাত ছেড়ে দিয়েছে।
কস্তুরী স্তম্ভিত হয়ে অরবিন্দের দিকে তাকাল, ‘তুমিও কিছু বলবে না? আমাকে এখানে নিয়ে এসে এখন বিপদে ফেলে ল্যাজ গুটিয়ে পালাবে?’
‘তুমি চুপচাপ ওই কোণার টেবিলে ওয়েট করলে এত কথা হতো না। তা নয়, ঘটা করে নিজের চলে যাওয়া অ্যানাউন্স করে ওদের প্রভোক করলে।’
‘আমি প্রভোক করেছি? তোমাকে দোকানে ঢোকার আগেই বললাম এখান থেকে চলো যাই। ছেলেগুলোর হাবভাব দেখেই সুবিধের নয় মনে হয়েছিল। আমরা ভেতরে ঢুকলে কি ওরা টিজ করত না? এত স্পর্ধা আমার গায়ে হাত দিচ্ছে!’ কস্তুরী উত্তেজনায় কাঁপছিল।
‘গায়ে তো হাতই দিয়েছি সোনা। অন্য কিছু তো নয়। খিক্খিক্।’ ঢ্যাঙার মন্তব্যে দলের সবকটা মিলে বিকট হাসতে শুরু করল। দোকানের ভেতরে খদ্দেরের ভিড় কমে গেল, বাইরে দর্শকের ভিড় বাড়তে লাগল।
হাবুদা গজগজ করল, ‘মেয়েছেলে রোজগার করলে ধরাকে সরা জ্ঞান করে।’ কী আশ্চর্য! লোকটা সব দেখেও ছেলেগুলোকে কিছু বলছে না। কস্তুরীর ওপর ঝাল ঝাড়ছে, যে নিয়মিত আসে। আরও আশ্চর্য– অরবিন্দের প্রতিবাদের সাহস না থাকুক, কস্তুরীকে দোষ দিয়ে পালানোর পথ খুঁজছে?
‘এবারের মতো ছেড়ে দিন। ওকে বাড়ি পৌঁছে দিই।’ বাপরে, অরবিন্দ অনেক সাহস দেখিয়ে ফেলল তো।
‘আমরা কি খুকিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি না?’
অকস্মাৎ জনতার জটলা ভেদ করে এক সুদেহী যুবক বেরিয়ে এল। আততায়ীর কবজি চেপে ধরে কস্তুরীর হাত ছাড়িয়ে নিল ওদের হাত থেকে। ‘দাদা তুই কস্তুরীদিকে নিয়ে চলে যা, আমি এদের দেখছি– কত বড়ো মস্তান। চিন্টু সুজয়কে খবর দে তো।’
সুজয় আসার আগেই তিনটে ছেলেকে দোকান থেকে টেনে বের করে মেরে পাট করে দিল ইন্দ্রজিৎ। বাকিরা আক্রোশে কাপ-প্লেট ভেঙে, চেয়ার হাতে নিয়ে আক্রমণ করতে এল ইন্দ্রজিৎকে। অরবিন্দ সেদিন কার মুখ দেখে উঠেছিল কে জানে? কিন্তু ভাইকে সাবধান করার মতো গলার জোরটাও নেই। কস্তুরীর উদ্দেশ্যে দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলল, ‘তোমার জন্য এই ঝামেলার উৎপত্তি। ছেলেগুলোকে গালাগাল না দিয়ে ভদ্র ভাষায় বলা যেত না? বোলতার চাকে ঢিল ছুড়েছ। এবার দেখো, কদ্দুর গড়ায়। চলে এসো।’ হাত ধরে টানল অরবিন্দ।
কস্তুরী এক ঝট্কায় হাত ছাড়িয়ে নিল। ‘আর যার সাথে যাই, তোমার সঙ্গে তো নয়ই। আর কাউকে আমার জন্য বিপদে পড়তে দেখে তোমার মতো পালিয়ে যেতে আমি পারব না। ছোটন, তোমায় চেয়ার তুলে মারতে আসছে!’ কস্তুরী চেয়ার মাথায় ছেলেটাকে ঠেলার চেষ্টা করল। বাকিরা ওকে যাচ্ছেতাই ভাবে জড়িয়ে ধরল।
সুজয় আর সম্মিলনি কতগুলো ছেলে চলে এসেছে। অত বড়ো হাট্টাকাট্টা চেহারা নিয়ে সুজয় এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। অতনু তার প্যানপ্যাঁকাটি চেহারা নিয়ে চিতার মতো অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার দেখাদেখি তনয়। সুজয় সামান্য খাঁকারি দিল দল ভারি হতে, কিন্তু ষোলো ইঞ্চির বাইসেপস্ওয়ালা হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে। মাথা বাঁচলেও চেয়ার কাঁধে লেগে ইন্দ্রজিতের মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল।
‘তোমার পরিচয় পেয়ে গেছি। আমার সঙ্গ পাবে বলে এখানে নিয়ে এসে কতগুলো ইতর হুলিগানের হাতে তুলে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ? নিজের ভাইকে দ্যাখো’।
‘ওর মাস্তানি দেখানো বেরিয়ে যাবে। গুন্ডা বদমাশদের সঙ্গে যেচে কেউ লাগে? ওদের কাছে ছুরি-ছোরা, আর্মস থাকে। ক্যারাটে শিখে হিরোগিরি দেখাচ্ছে।’
‘ছিঃ! প্রতিবাদ করার সাহস সবার থাকে না। যা ঘটছে চারদিকে, সেটা করা নিরাপদও নয়। কিন্তু নিজের অক্ষমতা ঢাকতে কখনও আমাকে দোষারোপ করছ, কখনও নিজের ভাইকে। আমি কিন্তু ছোটনের সঙ্গে নয়, তোমার সঙ্গে এখানে এসেছিলাম। ও মাগো! ছোটন সাবধান!’
সুজয় এসে আক্রমণকারীকে অনুনয়ের ভঙ্গিতে পেছন থেকে জাপটে ধরল। ‘ভাই কী হচ্ছে কী? শান্ত হও। শুধু শুধু…।’
সুজয়ের দুই বাহুর আলিঙ্গনে একসাথে দুজন চ্যাঙড়া চলৎশক্তিহীন হয়ে গেল। অথচ ওই বিশাল দেহ আর বল নিয়ে সে এতক্ষণ চুপচাপ দেখছিল। ও আগে এগিয়ে এলে ইন্দ্রজিতের আঘাত লাগত না, অতনুর মুখ মাথা ফেটে কনুই কেটে রক্তারক্তি হতো না। সুজয় ছাড়া অল্প-বিস্তর চোট লেগেছে, এ পাড়ার যে ছেলেগুলো এগিয়ে এসেছিল তাদের সবারই।
অরবিন্দের সঙ্গে এক মুহূর্ত থাকতে রাজি নয় দেখে, কস্তুরীকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য সুজয় রিকশা ডেকে চড়ে বসল। কস্তুরী ঠান্ডা গলায় বলল, ‘আমি একাই যেতে পারব। তার আগে আমার জন্য যারা ইনজিওরড্ হল তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।’
কস্তুরীর সঙ্গে বাড়ি ফিরতে অরবিন্দর কী ঝাঁজ! ‘ক্যারাটে ব্ল্যাক বেল্ট, বীরত্ব দেখানোর হাতে গরম পুরস্কার পাওয়া হয়ে গেল তো? ইস্! এমন দয়াময়ী সাহসিনী আর দুচার পিস থাকলে ওই ইভটিজিং-এর প্রোটেস্ট করা ছোকরাগুলোকে বেঘোরে মরতে হতো না।’
কস্তুরী মুখ খুলল, ‘নিজের ভাইয়ের ওই ছেলেগুলোর মতো পরিণতি হোক চাইছিলে মনে হচ্ছে!’
‘আমাকে ভদ্রলোকের মতো খেটে খেতে হয়। বাপের হোটেলে থেকে আর ভাইয়ের অন্ন ধবংস করে মারামারি শেখার সৌভাগ্য তো সবার হয় না। আর লম্বা চওড়া মাসল্ বাগানো বডি নিয়ে হিরোইজম দেখাতে কার না সাধ যায়?’
‘দাদা, অন্যায়ের প্রোটেস্ট করতে সবার আগে যেটা দরকার হয় সেটা হল মেরুদণ্ড। স্ট্রিট-ফাইটিং-এর জন্য মাসলস-এর চেয়ে আগে দরকার কলজে। অতনুকে দেখলি না? ওই নিঙলে চেহারা নিয়ে কীভাবে ফুঁসে উঠল? তনয়, বাপি এরাও কেউ ব্রুস লি বা হলিফিল্ড নয়। ওদিকে সুজয় আমার দেড়া চেহারা নিয়ে চুপচাপ আমাদের মার খেতে দেখে গেল। ওরা কোণঠাসা হওয়ার পর শালা মিটমাট করতে ময়দানে নামল। না হলে সবকটাকে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখাতাম আমরা। কস্তুরীদি তো আগে অতনুকে হাসপাতালে অ্যাডমিট করার ব্যবস্থা করল। বাকিদেরও হসপিটালে ফার্স্টএইড দেওয়া হয়েছে।’
অরবিন্দ ভেতর ঘরে যাওয়ার আগে হিসহিসিয়ে স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে কথা ছুড়ে দিয়ে গেল, ‘সবচেয়ে উপাদেয় পদটা শেষপাতের জন্য তোলা থাকে।’
কস্তুরী চোয়াল শক্ত করে তারপর চোখ বুজিয়ে রাগের সঙ্গে বোধহয় খানিকটা কান্নার দলাও গিলে ফেলল। তারপর ধরা গলায় বলল, ‘মাসিমা, এলাম। ডাক্তার কিন্তু গরম জল নয়, আইস কম্প্রেস করতে বলেছেন। হট ওয়াটার ব্যাগ থাকলে তার মধ্যেও বরফ ভরে নিতে পারেন। ডাক্তারবাবু এক্স-রে প্লেট দেখে নিয়েছেন, কিন্তু ক্লিনিক থেকে রিপোর্টটা আজ সন্ধেবেলায় কালেক্ট করতে হবে। ওষুধগুলো মনে করে খেও ছোটন। আর পরের কথা– ভগবান দুটো কান দিয়েছেন কেন জানো তো?’ তারপর নিজেকেই বলল, ‘আমি ভেবে পাই না, মেয়েরাই যেখানে টার্গেট হয় সেখানে তাদের নিদেন পক্ষে সেলফ্ ডিফেন্সটুকু শেখারও ব্যবস্থা থাকে না বেশিরভাগ জায়গায়। অ্যাটাক করে ভয় না দেখালে রেসকিউ করে ছেলেরা কথা শোনাবে কী করে?’
বাকিদের কাটা ছড়া, হাড়ে ফাটল ধীরে ধীরে সেরে গেলেও ইন্দ্রজিতের কাঁধের ব্যথাটা ছ মাস পরেও পুরোপুরি গেল না। এখনও বাজার দোকান করে, মানে করতে হয়। কিন্তু ডান হাতে বা কাঁধে ভারি ব্যাগ নিলেই পুরো হাতটাই খচকা লেগে অবশ হয়ে আসে। কস্তুরী জোর করে কিছুদিন ওর চিকিৎসার খরচ চালিয়েছিল। বাড়ি এসে খোঁজ করে যেত মাঝে মাঝে। অরবিন্দের উপস্থিতি বা প্রতিক্রিয়া যেন দেখতেই পেত না। রিকশায় বসিয়ে সঙ্গে করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেত।
অতনুরা ওদের একসাথে দেখে একবার দুই আঙুলে ‘দারুণ’ মুদ্রা ফুটিয়ে মন্তব্য ছোড়ে, ‘বস, সচীনের চেয়ে অঞ্জলি সাত বছরের বড়ো, অভিষেকের চেয়ে ঐশ্বর্যও দু-তিন বছরের বড়ো।’ বুকের ভেতরটা যে একটু শিরশির করেনি তা নয়। দাদার বান্ধবী বলে কস্তুরীকে দিদি ডাকে, না হলে বয়সের ফারাক তেমন কিছু নয়। কিন্তু বন্ধুদের রসিকতায় কস্তুরীর সাহস ও সহানুভূতি দুটোর প্রবাহই বন্ধ হয়ে গেল। এখন রাস্তাঘাটে চোখাচোখি হলে, ‘ভালো?’– এর বেশি কথা হয় না।
কাঁধের ব্যথাটা এমনিতে নিয়ন্ত্রণেই থাকে। কিন্তু ডাক্তার ও ফিজিওথেরাপিস্টের দেখানো ব্যায়াম ছাড়া আর কোনও কসরত করতে গেলেই হাত নড়ানো, ঘাড় ঘোরানোর উপায় থাকে না বেশ কিছু দিন। ওয়েট ট্রেনিং তো নৈব নৈব।
বিনোদদা চলে গেছেন চার বছরের ওপর। সুজয় এখন সম্মিলনি ক্লাবের সুজয় স্যর। কস্তুরী কর্মসূত্রে ব্যাঙ্গালোরে। কথা তো দূর, দেখাই হয় না আর। নতুন নম্বরও নেওয়া হয়নি। চাকরির পরীক্ষা সাক্ষাৎকারের ছোটাছুটির মধ্যে দেহটাকে যোগাসন করে সচল রেখে চলেছে। কাঁধে মাঝেমধ্যে চিড়িক মারা চিনচিনে ব্যথার মতো দাদার এখনও অবদি চালিয়ে যাওয়া তির্যক মন্তব্যগুলোও যেন জিইয়ে রেখেছে কিছু গোপন পর্বের স্মৃতি– চার বছরের তদগত মার্শাল আর্ট সাধনা অথবা কাঁধে কস্তুরী…দির হাতের স্পর্শ, ‘ছোটন পেইনকিলার বেশি খেয়ো না, সেঁক নিও। তুমি আবার প্রাকটিস শুরু করতে না পারলে নিজেকে বড়ো অপরাধী মনে হবে।’