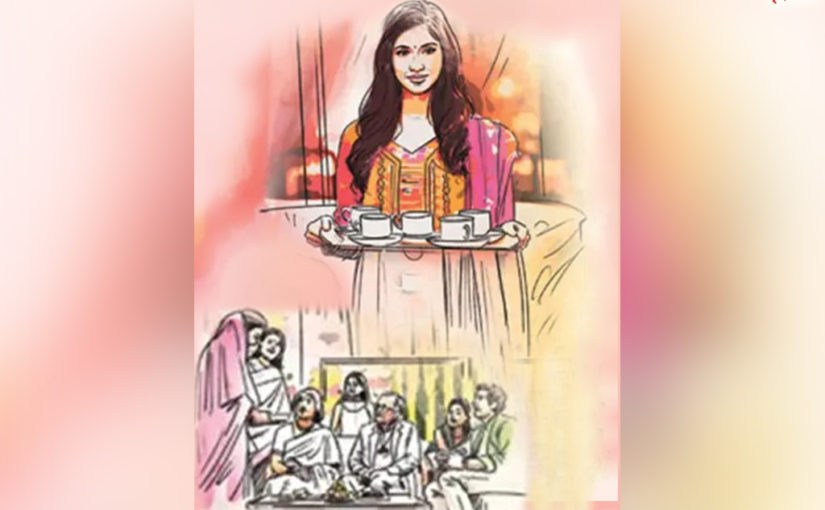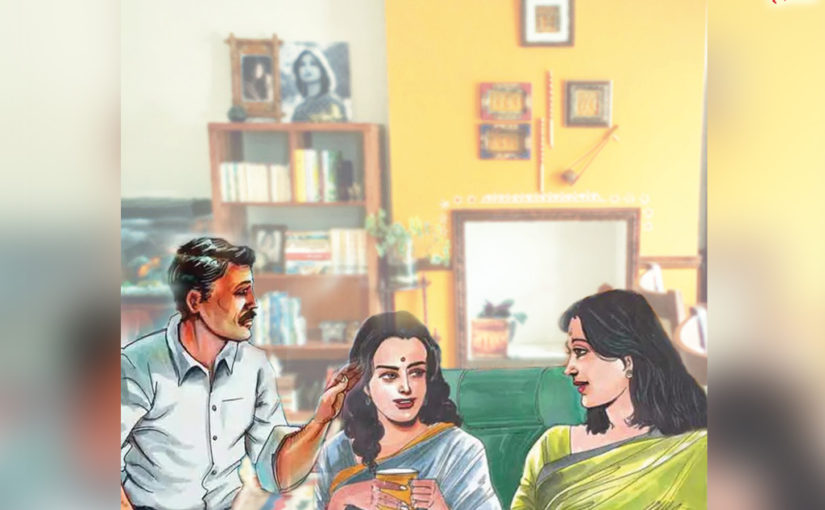আজ অনেকদিন পর আবার এক নতুন সাজে সেজেছে ইমন-কল্যাণ। আজ এই অনুষ্ঠান শুধুমাত্র এই বাড়ির মালিক ও মালকিনের পঞ্চম পুণ্যতিথি বলে যে তা কখনওই নয়, কারণ সেই ভয়ঙ্কর দিন কখনওই তিথি ভুলতে পারে না। আজকের দিনে সে তার একান্ত নিজের বলেই যাদের জানত, তার মা ও বাবাকে হারিয়েছে। আর তাদেরকে হারাতেই এই সমাজের কদর্য, স্বার্থপর রূপ ওর সামনে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়েছে। আজ সেই সকল স্মৃতি ওর মনের আনাচে কানাচে উঁকি মারছে। কিন্তু কিছু বিশেষ কারণে আজ তার মন কিছুটা তৃপ্ত আবার শান্ত।
আজ বহুদিন ধরে চলে আসা নানান পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। তার মায়ের মনের ইচ্ছে সে আজ পূরণ করতে চলেছে। আর তারই সঙ্গে অনেক মানুষের অনেক প্রশ্নের জবাব আজ বিনা বাক্যব্যয়ে করেই দিতে পারবে, এটা ভেবেই সে আজ অনেক তৃপ্ত। আজ সকল অপেক্ষার অবসান হবে কিছু সময় পর। আজ দীনু কাকা, মঙ্গলা পিসি আর যারা বাইরের কাজ করেন, প্রত্যেকে নতুন উদ্যমে কাজ করছেন।
আবার বহুদিন পর এই বাড়ি অনেক মানুষের কথায় ভরে উঠবে। সত্যিই তিথি দিদির হাত ধরেই এইসব মানুষগুলো যেন আরও কয়েক বছর বাঁচার রসদ পেল। কিন্তু তিথি সে এরপর কী করবে, তার তো পথচলা এই পর্যন্তই ছিল। তাকে তো এবার তার নতুন ঠিকানা খুঁজতে হবে। কখনও কখনও গভীর চিন্তায় আমরা আমাদের বাহ্যিক পরিবেশ থেকে এতটাই সরে যাই যে, আমাদের আশেপাশে কোনও মানুষের উপস্থিতিও আমরা টের পাই না।
তিথি নিজের ভাবনার মধ্যে এমন ভাবে ডুবেছিল যে, বাবা ও মায়ের ছবির ভিতর যে কারোর প্রতিচ্ছবি এসে পড়েছে সে সেটা এতক্ষণ খেয়ালই করেনি। এবার সে পিছন ফিরতেই বাগানের মালি দামু দাদাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, “কিছু বলবে?” তার প্রশ্নে দামু কিছু একটা ভেবে বলল, ‘এজ্ঞে ওই ভালোমানুষ দাদা, দিদিরা এয়েছেন গো দিদিমণি, তোমার খোঁজ করতাছেন। আমি উনাদের বৈঠকখানাতে বসায়ে এলুম।’
তিথি সব শুনে বুঝতে পারল, কাদের কথা দামু বলছে। দামুকে বিদায় করে নিজের মনে হাসল, আহা এই সহজ সরল মানুষগুলো কত সুন্দর ভাবে মানুষের কাজের উপর বিশ্বাস রেখে তাদের পরিচয়ের সামনে একটা বিশেষণ ব্যবহার করে তাদের উপস্থিতি বুঝিয়ে দেয়। সত্যিই তো মেঘা, রুমেলা, কৌশিক, নীল— এরা সততার সঙ্গে সমাজের উদ্ধারে নিজেদের ব্রতী করেছে। আর তাদের সাহায্যেই আজ তিথিও এত বড়ো কাজটা করতে পারবে।
নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গেই ওর নজর চলে গেল সোজা লনের দিকে, যেখানে তার কিছু পরিচিত প্রতিবেশী, সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত কিছু অতিথি আর এই বাড়ির মালিকের কিছু আত্মীয় নিজেদের আসনে বিরাজ করছেন। এত জনসমাবেশের কারণ বুঝতে না পারায় কিছু কৌতূহলী চোখ তিথিকে খুঁজছে, আর কেউ কেউ নিজেদের মধ্যেই সম্ভাব্য কী ঘটতে পারে তা নিয়ে নিজেদের মত পোষণ করছেন, ফলে একটা মৃদু গুঞ্জনের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।
যথাসময়ে তিথি তার ভালোমানুষ বন্ধুদের (দামু দাদার মতে) নিয়ে সকলের সামনে উপস্থিত হল। সকলের সামনে দুই হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাল। এরপর সে আজকের এই অনুষ্ঠানের মূল কারণে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাল— সে আগে সকলকে কিছু পুরোনো কথা জানাতে চায়, যা এই বাড়ির সঙ্গে যুক্ত, তার জীবনের সঙ্গে জড়িত। এই বলে সে সকলকে আজ থেকে পাঁচশ বছর পিছনে নিয়ে গেল।
ইমন-কল্যাণ-এর প্রধান আকর্ষণ ছিল তার মালিক কল্যাণ রায় আর মালকিন ইমন রায়। দুইজন ছিলেন যেমন প্রাণবন্ত, তেমনই তাদের ছিল পরোপকারী মন। সকলের খুব প্রিয়, কোনও শত্রু তাদের ছিল না। পৈতৃক ব্যাবসা সামলানোর পরও সকলের বিপদ-আপদে ঠিক পৌঁছে গেছেন ওনারা। শুধুমাত্র একটি কষ্ট ভগবান তাদেরকে দিয়েছেন, সেটা হল সন্তান-সুখ থেকে বঞ্চিত থাকার দুঃখ। এই দুঃখের একদিন অবসান হল এই ছোট্ট তিথিকে দত্তক নিয়ে।
কিন্তু এই মেয়ে যত বড়ো হতে লাগল ততই ইমনের মনে নানান ধরনের দ্বন্দ্ব শুরু হল। কারণ সে বেশ বুঝতে পারছিল তাদের অবর্তমানে আশেপাশের লোকজন তাকে নানাভাবে বিরক্ত করবে। যে সত্য ওনারা তিথিকে কোনওদিন জানতে দিতে চাননি, সকলে মিলে সেটাই আগে তার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবে। এইসব ভেবেই ইমন ঠিক করলেন যে, তিনি তিথিকে এমন ভাবেই মানুষ করবেন যেন সকল পরিস্থিতির জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত রাখে।
যখন তিথির ষোলো বছর পূর্ণ হল, তখন থেকেই তিনি তার সকল প্রয়োজন মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতেন, ‘সব বাবা-মা সন্তানকে সেরা জিনিসটা তুলে দেন, আমরাও তাই করবার চেষ্টা করি। কিন্তু সন্তান যদি এটাতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তবেই হবে মুশকিল। কারণ সকলের সবদিন এক নাও যেতে পারে। তাই এই উপযুক্ত সময় নিজেকে তৈরি করার, একে কাজে লাগাও। নিজেকে সকল পরিস্থিতির জন্য তৈরি করো। আমরা তোমার এই নিজেকে গড়ার কাজে সাহায্যের জন্য আছি, কিন্তু তারপর তোমাকে নিজেকে সফল ভাবে সমাজের একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তোমার সেই উন্নতি, প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র তোমার— যা কেউ কখনও কেড়ে নিতে পারবে না।’
এতসব কথা ঠিক মতোন করে সবটা তিথির বোধগম্য হতো না। কিন্তু যখন মা এইসব কথা বলতেন তখন মাকে যেন ভীষণ অচেনা মনে হতো। এই ভাবেই বেশ ক’টা বছর আনন্দের সঙ্গে কাটছিল। তিথির স্কুল-জীবন শেষ হতেই কল্যাণবাবু তার উচ্চশিক্ষার জন্য তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সময় সব সময় একরকম যায় না। হঠাৎই একটা দুর্ঘটনার ফলে এই রায় দম্পতির জীবনের প্রদীপ নিভে গেল। তিথি খবর পেয়ে এসে দেখল সব শেষ।
এই ভাবে তার জীবনে যে এরকম বিপর্যয় নেমে আসবে তা তার কল্পনার অতীত। যখন সে সকল ক্রিয়াকর্ম মিটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে তখন অতিপরিচিত মানুষদের ব্যবহার তার কাছে খুব অদ্ভূত লাগতে লাগল। যারা এতদিন তাকে খুব ভালোবাসত এখন কেমন ঈর্ষার চোখে দেখছে, বলছেও যে তার নাকি কপাল খুলে গেল। সে ভাবত, তার যা হারিয়ে গেল তাতে কীভাবে সে লাভবান হয়। নিজের মা-বাবাকে হারিয়ে কেউ কি খুশি হয়।
এইসব ভাবনা নিয়ে সে বিদেশ ফেরার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। কারণ তার পড়া শেষ হতে এখনও কয়েক বছর বাকি। সেইসময় জিনিসপত্র গোছানোর সময় তার হাতে আসে মায়ের ডায়েরি। যার প্রথম পাতার উপর তিথির উদ্দেশ্যে লেখা, তিথির জন্য মায়ের আশীষ। সেই ডায়েরি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে নতুন করে জানতে শুরু করল। সে এইদিন প্রথম জানল যে, সে দত্তক কন্যা। তাই আশপাশের লোকজনের থেকে তার মা তাকে কীভাবে আগলে রেখেছেন। তার মা ও বাবা তাকে তাদের যথা সর্বস্ব দিয়ে মানুষ করতে চেয়েছেন। এইসবের বদলে তার মা তার কাছে একটাই দাবি রেখেছেন, ‘জীবনে তুই অনেক বড়ো মাপের মানুষ হয়ে আশপাশের সকলকে দেখিয়ে দে যে, তুই শুধুমাত্র মা ও বাবার আশীর্বাদ নিয়ে, নিজের যোগ্যতায় নিজের একটা আলাদা জগৎ ও পরিচয় তৈরি করেছিস। তোর বাবার সমস্ত কিছুই তোর হওয়া সত্ত্বেও তুই সকল বৈভব দূরে রেখে নিজের কর্মের দ্বারা এইসব কিছু অর্জন করে দেখা। তখন আমরা যেখানেই থাকি আমাদের তোকে নিজের সন্তান বলে ভাবতে গর্ববোধ হবে। মনে হবে কাউকে আমরা আমাদের সত্যিকারের উত্তরাধিকারী হিসেবে এই পৃথিবীতে রেখে যেতে পারলাম। আর আমাদের অবর্তমানে তুই এই বাড়ি কোনও এক সংস্থাকে দিয়ে দিবি, যারা এখানে অনাথ শিশুদেরকে যথার্থ শিক্ষা দিয়ে বড়ো করতে পারে। এটা আমার একটা স্বপ্ন।’
এইসব কথা বলতে গিয়ে কখন যে তার দুই গাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এসেছিল, তা তিথি খেয়াল করেনি। চোখ মুছে সে সকলকে জানাল যে, আজ সে তার মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে চলেছে। এই বাড়ি সে ‘নবজন্ম’ নামে এক সংস্থার হাতে তুলে দিচ্ছে। এই বলে সে রুমেলা, নীল, কৌশিক আর মেঘার হাতে বাড়ির কাগজ আর কিছু চেক তুলে দেয়। আর সকলকে বলে সে আজ থেকে এইসব কিছু থেকে মুক্ত। তার নতুন ঠিকানায় সে কেবল তার মা ও বাবার স্মৃতি হিসেবে তাদের ফোটোটাই নিয়ে যাবে। কিন্তু এখানকার পুরোনো কাজের লোক আগের মতোই এখানে থাকবে।
তার এই মহৎ উদ্দেশ্য জানার পর ওখানে উপস্থিত সকলে এতটাই অবাক হলেন যে, বলার মতো কিছু ভাষা খুঁজে পেলেন না তাঁরা। শুধু এই মেয়েটিকে আজ মন থেকে আশীর্বাদ জানালেন। কারণ সে আজ প্রতিষ্ঠিত শুধুমাত্র কারওর দয়ার জন্য নয়। তার মধ্যে যে মেধা ছিল, সহনশীলতা আর শালীনতাবোধ ছিল, তার জন্যই আজ সে সকলের থেকে আলাদা। আজ সকলের সামনে তার ‘নবজন্ম’ হল।