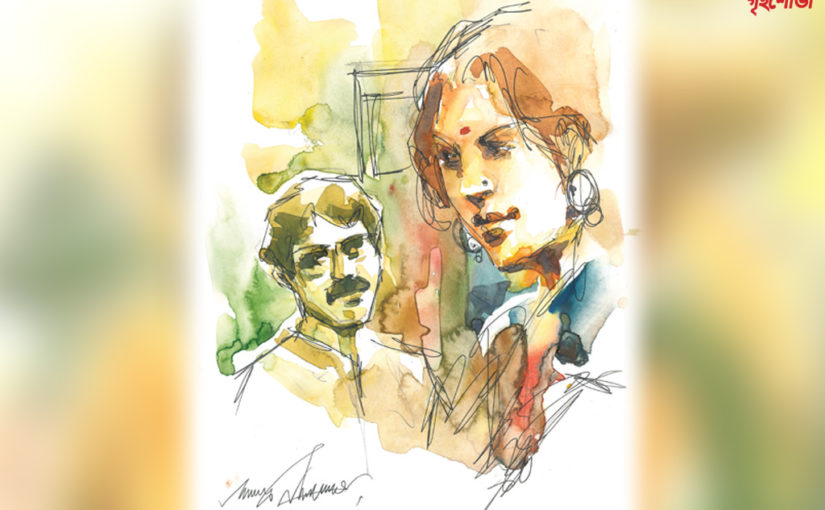উত্তরপ্রদেশের রাজনীতির ধরনটাই একটু ভিন্ন। নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ারা এখানে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় গোড়া থেকেই। এখানে অঙ্কুরিত হয় বৃহত্তর রাজনীতির ক্ষেত্রে পদার্পণ করার স্বপ্ন। ক্ষমতা দখলের খেলায় খুব সহজেই মেতে ওঠে ইয়ং জেনারেশন। বদলে যায় তাদের জীবনদর্শন। জীবনযাপন আর সাদামাটা থাকে না তখন।
মণীশ যখন প্রথম এরকমই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েশন করতে এসেছিল, সে ভাবেনি জীবন তার জন্য ঠিক কী কী নির্দিষ্ট করে রেখেছে। ফার্স্ট ইয়ার-এ র্যাগিং-এর সময়টাতেই প্রথম সিনিয়রদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল মণীশকে। সেখানেই প্রথম সে দেখেছিল দেবেন্দ্র ওরফে দেব-কে। ইউনিয়নের জিএস হওয়ার দরুন সবাই চিনত দেব-কে। তার ব্যক্তিত্বকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই কারও। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকবে বলেই সে এমএ-টাও এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই করবে ঠিক করেছিল। দেব-এর পড়াশোনার ব্যাপারে যত না আগ্রহ, তার চেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল পাকাপাকি রাজনীতিতে চলে আসার। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু থেকেই সে নিজেকে চোখে পড়ার মতো জনপ্রিয়তার স্তরে তুলে এনেছিল।
র্যাগিং-এ খুব বেশি নাজেহাল হতে হয়নি মণীশ-কে। কারণ দেব-এর চোখে পড়ে গিয়েিল সে, ভালো টেবিল টেনিস খেলার জন্য। দেব বড়ো ভাইয়ে মতোই মণীশকে আগলাতে শুরু করেছিল, সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকেই। তারপর থেকে নানা প্রযোজনে মণীশ, দেব ভাইয়া-কে পাশে পেয়েছে। কখনও তাকে সাহায্য না করে ফেরায়নি দেব। মণীশ যে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, সেখান থেকে তার বাড়ি বেশ খানিকটা দূরে। একটু মফস্সল বললেও ভুল হয় না। দেব-ই ব্যবস্থা করে দিয়েিল, যাতে কোনও কোনও দিন বাড়ি ফিরতে না পারলেও, সে হোস্টেলে দেব-এর ঘরে থেকে যেতে পারে।
গ্রাজুয়েশন শেষ করার পর মণীশ বেশ কিছুটা মানসিক অবসাদে ভুগছিল। তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। একটা ট্রেন দুর্ঘটনায় বাবার পা কাটা গিয়েছিল। বোন-কে খুব কষ্ট করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াচ্ছে বাবা, তাঁর শেষ সম্বল ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে। এই অবস্থায় মণীশ
এমএ-তে ভর্তি হবে, নাকি একটা চাকরি খুঁজবে সেটা নিয়ে সে কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। টাকার খুব প্রযোজন তার। দু-একটা টিউশনি করে কিছু টাকা সে আয় করে ঠিকই কিন্তু পরিবারের প্রযোজন মেটাতে সেটা যথেষ্ট নয়। বোন রিঙ্কুর জন্য এখনই একটা ল্যাপটপ-এর প্রযোজন। কিন্তু সেই টাকাটাও জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে মণীশকে। চাকরির চেষ্টা যে সে করছে না তা নয়, কিন্তু ভালো চাকরি পাওয়াও তো মুখের কথা নয়।
এসব ক্ষেত্রে তার একমাত্র ভরসা দেব ভাইয়া। দোনামোনা করে দেব-এর
হোস্টেল-এর দিকেই পা বাড়ায় মণীশ। হোস্টেলের ঘরে বসে দেব তখন তার চ্যালাচামুণ্ডাদের নিয়ে কলেজের ইলেকশনের ব্যাপারে আলোচনা করছে। ইশারায় মণীশকে বসতে বলে কাজের কথাগুলো সেরে নেয় ছেলেগুলোর সঙ্গে। তারপর ওরা চলে গেলে, মণীশকে বলে
বল ভাই, সকাল সকাল আজ কী মনে করে?
দেব ভাইয়া আর কী বলব তোমায়, তুমি তো সবই জানো।
আরে নির্দ্বিধায় বল। তুই আমার নিজের ভাইয়ে মতো। দাদাকে বলবি না তো কাকে বলবি?
আসলে তুমি তো জানোই, বোনের এটা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সেকেন্ড ইয়ার। ওকে এবার একটা ল্যাপটপ না কিনে দিলেই নয়। খুব মেধাবী আমার বোনটা। আমার মতো নয়।
হ্যাঁ জানি রে। তা রিঙ্কু তো আমারও বোন। তার জন্য কিছু করতে পারলে আমারও ভালো লাগবে।
আমি অল্প কিছু টাকা জমিয়েছি, কিন্তু…
ওই টাকাটা তুই রেখে দে। রাখিতে একটা মোবাইল কিনে দিস। আপাতত তোর দেব ভাইয়া ওর জন্য ল্যাপটপ-এর ব্যবস্থা করছে।
কথাটা বলে দেব সত্যি সত্যি পকেট থেকে ফোন বের করে মণীশের অ্যাকাউন্ট-এ পঁচিশ হাজার টাকা ট্রান্সফার করে দিল। কৃতজ্ঞতায় প্রায় নুয়ে পড়েছে মণীশ। পায়ে হাত দিতে যায় দেব-এর। দেব তাড়াতাড়ি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।
পাগল, তুই আমার ভাই।
সে জানি দেব ভাইয়া, কিন্তু এটা ধার হিসেবে নিচ্ছি আমি। টাকাটা আমি শোধ দিয়ে দেব যত তাড়াতাড়ি পারি।
ধুর বোকা। বললাম না রিঙ্কু আমারও বোন। এটা আমি আমার বোনকে উপহার দিলাম।
এরকম ভালোবাসা পেয়ে মণীশ সত্যিই অভিভত। প্রায়ই এমন হয়, দেব তাকে ভালো ভালো হোটেলে খাওয়ায়, মাঝে মাঝে পাঁচশো-হাজার এমনিই পকেটে গুঁজে দেয়। মণীশ বুঝতে পারে না, কী এমন দেখল দেব ভাইয়া তার মধ্যে, যে এত ভালোবাসে!
বোন ল্যাপটপ পেয়ে তো দারুণ খুশি। দাদাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেঁদেই ফেলল। মা শুধু একবার অবাক হয়ে আড়ালে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হ্যাঁ রে মণীশ, এত টাকা কীভাবে জোগাড় করলি?
সত্যি-মিথ্যের মাঝামাঝি একটা উত্তর দিয়ে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল মণীশ।
এর কিছুদিন পর দেব ভাইয়া কলেজে ডেকে পাঠাল মণীশকে।
বুঝলি মণীশ জোর ক্যাম্পেন করতে হবে তোকে আমার হয়ে এবারও ইলেকশনটা জিততেই হবে। দেখিস সব জায়গায় যেন ঠিকঠাক পোস্টার লাগানো হয়।
ইলেকশনে এবারও দেবের জয় নিশ্চিত ছিল। মণীশও দারুণ খুশি এই জয়ে দেবকে কাঁধে তুলে তারা গোটা ক্যাম্পাস ঘুরল, বিজয় মিছিলে।
এর কিছুদিন পর রাখি। মণীশ ঠিক করল রিঙ্কুকে রাখিতে একটা ভালো মোবাইল ফোন কিনে উপহার দেবে। সেইমতো একটা ফোন কিনে বোনের কাছে রাখি পরতে বসল মণীশ। রিঙ্কু খুশিতে দিশেহারা হয়ে উঠল। বলল,
তোমার মতো দাদা যেন জন্ম জন্ম ধরে পাই।
এই আনন্দঘন ঘটনার দিনদুয়েক পরে, হঠাত্-ই দেবের ফোন।
মণীশ, ভাই একবার ক্যাম্পাসে আয় তো, একটু জরুরি কথা আছে।
হ্যাঁ ভাইয়া, এখুনি যাচ্ছি আমি।
ক্যাম্পাসে পৌঁছে দেখে সকলে প্রস্তুতি নিচ্ছে বিধানসভা অভিযানের। দলের একটি ছেলেকে অপোনেন্ট পার্টির ছেলেরা মারধর করেছে। তাদের শাস্তি আর অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে এই অবস্থানের পরিকল্পনা। দেব, মণীশকে আলাদা করে একটু সাইডে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল এসব সিরিয়াস কিছু না, চল একটু স্লোগান দিবি, দুটো মিডিয়ার সামনে বাইট দেব, তারপর খাওয়া দাওয়া করে ফিরে আসব।
মণীশ এসব ব্যাপারে আগে কখনও থাকেনি। কিন্তু বিষয়টা যে এতটাই অন্যরকম, সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করার লোভ সে সামলাতে পারল না। এভাবেই দেবের সংস্পর্শে আস্তে আস্তে সেও পরোক্ষ ভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে লাগল।
মাস খানেক পরে ঘটল আরও এক অভাবনীয় ঘটনা। বাজারে সবজি কিনতে এসেছিল মণীশ। সেই সময় মোবাইলটা বেজে উঠতেই দেখে দেবের ফোন। ডান হাতে সবজির বোঝাটা নিয়ে বাঁ হাতে ফোনটা ধরতেই ওপাশে দেবের অস্থির কণ্ঠ ভেসে এল।
কোথায় আছিস? জরুরি দরকার। না, না ফোনে বলা যাবে না। হোস্টেলে চলে আয়।
হোস্টেলে পৌঁছে আজ একটু যেন অন্যরকম লাগল দেবকে। গোটা ঘরে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে। আর তার খুব ক্লোজ, জনাদুয়েক ছেলে রয়েছে ঘরে। মণীশকে দেখে বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে দেব।
ভাই এসেছিস! বোস। খুব মন দিয়ে শোন যা বলছি।
হ্যাঁ বলো ভাইয়া
তুই আমার জন্য কী করতে পারিস?
আরে, এ কেমন প্রশ্ন ভাইয়া। তোমার জন্য জান হাজির।
একটা ছেলেকে তুলতে হবে। পারবি?
তুলতে মানে?
কথাটা বলার সময় একটু যেন ঘাবড়ে গেল মণীশ। কী বলছে দেব ভাইয়া, কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না! দেব ভাইয়া তার অবাক হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে একটু যেন শ্লেষের সঙ্গে বলে,
বড্ড সরল তুই মণীশ। আমি যে এই ছাত্র সংগঠনটা করছি, এটাই তো শেষ নয়। আমার একটা বড়ো ফোকাস আছে, তুই জানিস। এবার আমি যুব সংগঠনের সেক্রেটারি হতে চাই। কিন্তু এই পথে একটা বাধা আছে। আমার পথের কাঁটা। অপোনেন্ট পার্টির এই ছেলেটাকে তুই-ও এক-আধবার দেখেছিস। সুরজিত্। এই ছেলেটা ক্রমশ পপুলার হওয়ার চেষ্টা করছে। শালাকে এমন শিক্ষা দেব, যাতে ও আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। তোর হেল্প চাই, ভাই।
কাঁপা গলায় মণীশ বলে কী ভাবে সাহায্য করতে বলছ আমায়?
কিছু না। তুই যখন টেবল টেনিস খেলতিস কমন রুমে, আমি তোকে খুব ভালো ভাবে লক্ষ্য করতাম, দারুণ রিফ্লেক্স তোর। পারলে তুই-ই পারবি। সুরজিত্ হালওয়াই সরাই-এ থাকে। রোজ ভোরবেলা জগিং করতে আসে দিলবাগ-এ। ঠিক পাঁচটায় রোজ ও দিলবাগ-এর গেট-এ পেঁছোয়। ওখানেই একটা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবি তুই আর এই দুজন।
ঘরে যেন পিনপতন নিস্তব্ধতা। দেব যে দুজনের কথা বলছে, তাদের দিকে এক বার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয় মণীশ। তার বুকের ভিতর ঢিপঢিপ আওয়াজটা যে দ্রুততর হচ্ছে, সে টের পায়। দেব পকেট থেকে একটা রামের নিপ বের করে ছোট্ট চুমুক দেয়। তারপর আবার মণীশকে বলে,
সুরজিত্ জগিং করতে করতে গাড়ির পাশে এলেই, তুই ঝট করে বেরিয়ে ওর মুখে কাপড় বেঁধে তুলে নিবি গাড়িতে। তোর মুখে মাস্ক থাকবে। তোর ভয় নেই।
আমতা আমতা করে মণীশ বলার চেষ্টা করল,
কিন্তু দেব ভাইয়া, এটা তো অপহরণ।
তো?
না আমি এসব কখনও করিনি।
সব কিছুরই একটা প্রথমবার হয় মণীশ। তুই পারবি।
দরদর করে ঘামছে মণীশ। ঠিক তখনই একটা মোক্ষম কথা বলল দেব।
কাজটা করার পরই তোর
অ্যাকাউন্ট-এ পাঁচ হাজার টাকা ঢুকে যাবে। আর এখন পাঁচ। ভেবে দ্যাখ, কড়কড়ে দশ হাজার টাকা। ছেড়ে দিবি?
মণীশের অভাবের সংসারে দশ হাজার টাকার ভ্যালু সে জানে। মায়ে চোখের ছানিটা অপারেশন না করালেই নয়। সে আর কিছু ভাবতে পারে না। খপ করে দেবের হাতটা ধরে নিয়ে বলে,
কবে করতে হবে কাজটা ভাইয়া?
মুখে একটা নিষ্ঠুর হাসি খেলে যায় দেবের। বলে,
কালই। বাকিটা তোকে আমার এই দুই শিষ্য বুঝিয়ে দেবে।
২
ঠিক পাঁচটার সময় একটা কালো রঙের অলটো পিক আপ করল দেব-কে। ভেতরে আগের দিনের দুজন, আছে। আর অপরিচিত একজন ড্রাইভার। ঠিক হয়ে আছে সুরজিত্-কে গাড়িতে তোলার পরই একজন ভালো ভাবে বেঁধে ফেলবে তার মুখ আর হাত দুটো। কিছুটা দূর গিয়ে একটা সিনেমা হলের সামনে গাড়ি থেকে নেমে পড়বে মণীশ। তার পরিবর্তে অন্য একজন গাড়িত উঠবে। ব্যস তার দাযিত্ব শেষ।
ভেতরে ভেতরে উত্কণ্ঠা টের পাচ্ছে মণীশ। এরকম কাজ আগে কোনওদিন করা তো দূরে থাক, ভাবেওনি যে সে করতে পারে। তাকে চিরকাল তার বাবা-মা একটু খাটো নজরেই দেখে এসেছে। পড়াশোনায় খুবই সাধারণ সে। নিজে হাতে এই প্রথম অনেকগুলো টাকা রোজগার করেছে একদিনের কাজে।
পাশের ছেলেটা সিগারেট খেতে খেতে গাড়ির সাইড মিরর দিয়ে খেয়াল রাখছিল জগিং করতে করতে সুরজিত্ আসছে কিনা। এবার সে মুখ দিয়ে একটা ইঙ্গিতপূর্ণ আওয়াজ করতেই, সচকিত হয়ে উঠল মণীশ। একটা নেভি ব্লু ট্র্যাক সুট পরে ধীর পায়ে জগিং করতে করতে গাড়ির পাশে আসতেই, তার মুখ চেপে ধরে সবলে তাকে গাড়িতে ঢুকিয়ে নিল মণীশ। সুরজিত্ ঘটনার আকস্মিকতায় এবং মুখ বাঁধা অবস্থায় গোঙাতে লাগল। মাস্ক পরা আগন্তুকদের সে ভালো চিনতে পারছে না। শুধু মণীশের চোখের নীচে বড়ো আঁচিলটা খুব চেনা মনে হতে লাগল তার।
মণীশের বুকের ভেতর কে যেন হাতুড়ি পিটছে। সে অধীর হয়ে রইল সিনেমা হলটার সামনে গাড়িটা না পেঁছোনো অবধি। তারপর দরজা খুলে নেমে যেতেই অন্য একজন তার জায়গায় উঠে পড়ল। গাড়িটা একরাশ ধুলো উড়িয়ে গোমতী নদীর দিকে চলে গেল।
সবে সকাল হচ্ছে। একটা ফাঁকা চায়ে দোকানে বেঞ্চ-এ বসে চা-এর অর্ডার দিল মণীশ। তারপর খুব মৃদু গলায় ফোন করে দেবকে জানাল কাজটা হয়ে গেছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ব্যাংক অ্যালার্ট এল। তার অ্যাকাউন্ট-এ এখন সদ্য উপার্জিত দশ হাজার টাকা।
আর অতটা খারাপ লাগছে না মণীশের। এটা জাস্ট একটা কাজ। ক্রাইম তো নয়। তাছাড়া ছেলেটাকে হয়তো ওরা একটু শাসানি দেবে, হুমকি দেবে, চড়চাপড় মেরে ছেড়ে দেবে। যাতে সে আর দেবের বিরুদ্ধে ফণা না তুলতে পারে। দেবের এখন অনেক ওপর লেভেল-এ চেনাজানা। যেভাবে রাজনীতির সোপানে সে তরতর করে উপরে উঠছে, ভবিষ্যতে তার বড়োসড়ো নেতা হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না।
কিন্তু যতটা নিশ্চিন্তে থাকবে ভেবেছিল মণীশ, তা আর পারা গেল না। দিন দুয়ে পরে গোমতী নদীতে লাশ ভেসে উঠল সুরজিতের। মিডিয়া, পুলিশ, তোলপাড়। খবরটা পাওয়া মাত্র ছুটতে ছুটতে দেবের কাছে গিয়ে পৌঁছোল মণীশ।
দেব ভাইয়া, এরকম তো হবার কথা ছিল না! দেব তখন তার ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে হোস্টেল-এর পেছনের মাঠের ঝুপসি অন্ধকারে মদের আসর বসিয়েে। লাইটার জ্বেলে সে মণীশের মুখের খুব কাছে ধরে বলল,
ন্যাকা আমার। জলে নামব আর চুল ভিজবে না। রাজনীতিতে এসব হয়?
কিন্তু ওকে মারার কথা তো বলোনি ভাইয়া! আমি… আমি কিছুতেই করতাম না এই কাজ, তুমি ওকে জানে মারবে জানলে।
চুব বে! শত্রুর শেষ রাখতে নেই। যা করেছিস বেশ করেছিস মেরা শের। আয় বুকে আয়। তোকে কত ভালোবাসি জানিস ভাই আমার। নে মদ খা। অ্যায়ে কর।
দেব নেশাগ্রস্ত। মণীশকেও বাকিরা প্রচুর মদ খাওয়াল সে রাতে। মদ খাওয়ার পর মণীশের খারাপ লাগাটা কমে গেল। দেবের হোস্টেলের ঘরে শুয়ে শুয়ে সে জড়ানো গলায় বলল
মিডিয়া, পুলিশ, এসব কুত্তাদের চিত্কার কী করে সামলাবে ভাইয়া?
তুই কিছু ভাবিস না ভাই। ওসব আমার বাঁ হাতের খেল। তুই শুধু কটা দিন আন্ডারগ্রাউন্ড-এ চলে যা।
মাসখানেক কেটে গেছে। একটা কন্ট্রাক্টে কিছু কাজের অফার পেয়েছে, এই বলে কিছুদিন বাড়ির বাইরে রইল মণীশ। ঘরে নিয়মিত টাকা পৌঁছোনোর ব্যবস্থা করেছে দেব। পরিবারের সবাই খুব খুশি মণীশ উপার্জন করছে শুনে। সুরজিত্-এর খবরটা ধামাচাপা পড়ার পর আবার যখন সব স্বাভাবিক, আবার প্রকাশ্যেই দেবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত্ শুরু হল মণীশের।
একদিন কমনরুমে দেবের সঙ্গে টেবিল টেনিস খেলছিল মণীশ। ক্যাম্পাস এখন ফাঁকা। দেওয়ালির ছুটিতে বেশির ভাগ ছাত্ররাই যে-যার বাড়িতে গেছে। খেলতে খেলতে হালকা ভাবেই দেব বলল, এবার আর-একটা দাযিত্ব দেব তোকে ভাই। তুই ছাড়া আমার ভরসাযোগ্য কে আছে বল? খেলা থামিয়ে সরাসরি দেবের মুখের দিকে তাকায় মণীশ।
কী হয়েছে, আমায় বলো ভাইয়া। কী দায়িত্ব?
কিছু না, খুব সাধারণ একটা কাজ। একজনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে ভাই। শুট করতে হবে।
এত সহজ স্বাভাবিক ভাবে কথাগুলো বলছিল দেব, যে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাচ্ছিল মণীশ। সে নার্ভাস হয়ে বলল, কী বলছ ভাইয়া, আমি কী করে… মানে মার্ডার!
হ্যাঁ ভাই। মার্ডার। শুট করতে হবে।
কঠিন হয়ে উঠেছে দেবের চোয়াল, তবু তার মুখে ঝুলে আছে একটা নিষ্ঠুর হাসি। সরাসরি মণীশের চোখের দিকে চোখ রেখে তাকে জরিপ করছে দেব।
মণীশ কোনও রকমে তোতলাতে তোতলাতে বলে,
আমি তো বন্দুক চালাতেই পারি না ভাইয়া। আমি পারব না।
দেবের পা দুটো ধরে বসে পড়ে মাটিতে মণীশ।
দেব তাকে তুলে দাঁড় করায় কাঁধ দুটো ধরে।
তোকে আমার লোক ট্রেনিং দিয়ে দেবে। তুই কাল থেকে দশ দিনের জন্য আমার ফার্ম হাউসে থাকবি। ওখানেই হবে তোর ট্রেনিং। টার্গেট যেন মিস না হয়।
আমি পারব না ভাইয়া। হাত জোড় করে মণীশ।
পারতে তো তোকে হবেই। আর পারলেই ৫০ হাজার টাকা সোজা ঢুকে যাবে তোর অ্যাকাউন্ট-এ।
না ভাইয়া। এ কোন অন্ধকারে তুমি আমায় টেনে নামাচ্ছ। ছেড়ে দাও আমায়।
একটা পৈশাচিক হাসি হেসে ওঠে দেব। তারপর বলে,
ভাই এটা এমনই একটা অন্ধকার, যেখানে ঢোকা সহজ, বেরোনোটাই কঠিন। এই দ্যাখ এটা।
বলার সঙ্গে সঙ্গে দেব তার মোবাইলটা অন করে একটা ভিডিয়ো প্লে করল মণীশের সামনে। সেদিনের গাড়ির অপহরণের ভিডিয়ো। মণীশের মুখে মাস্ক থাকলেও তাতে মুখের নীচের দিকটা ঢাকা পড়েছে। কিন্তু প্রমাণ হিসেবে জ্বলজ্বল করছে তার চোখের নীচের বড়ো আঁচিলটা। মানুষের চোখও তার একটা আইডেন্টিফিকেশন। মণীশ পালাতে পারবে না। সে ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে পাঁকে। যে-পাঁক থেকে তার নিস্তার নেই।
৩
টার্গেট মিস যেন না হয়। এটাই মন্ত্রের মতো এই কদিনে মাথায় ঢুকিয়ে নিয়েে মণীশ। আজ সেই দিন। সেই গাড়ি। সেই একই সওয়ারি। স্থান কাল পাত্র শুধু আলাদা। পাত্র বলা ভুল হল। পাত্রী। দেবের গার্ল ফ্রেন্ড। গদ্দারি দেব সহ্য করতে পারে না। তাকে আর একটা অন্য লোকের সঙ্গে বিছানায় দেখে খুন চেপে গেছে দেবের মাথায়। মেয়েটি দেবের অনেক কুকীর্তি এবং প্ল্যান জেনে ফেলেছে। তাই, চিরতরে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চায় সে তার প্রেমিকাকে। আর আজ তাকে মারার বরাতটাই পেয়েছে মণীশ।
প্ল্যান মাফিক নিখুঁত কাজ করল মণীশ॥ গাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যওয়ার সময় পেছন থেকে শুট করল মেযোকে। গুলিটা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল মেযোর শরীর। কিন্তু সাইলেন্সার লাগানো বন্দুকের আওয়াজ কারও কানে গেল না। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রক্তাক্ত কবুতরির মতো ছটফট করছিল যখন মেযো, গাড়িটা তখন স্পিডে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যার মুখে স্ট্রিট লাইটগুলো তখন সবে একটা একটা করে জ্বলতে শুরু করেছে।
আর কোনও অপরাধ বোধ হচ্ছে না মণীশের। দেবের হোস্টেলের ঘরে ঢুকে চিল্ড বিয়ার খেতে খেতে, সে গা এলিয়ে ভাবছিল ৫০ হাজার টাকা দিয়ে কী কী করবে। বোনের মাস দুয়ে পর ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ফাইনাল। খুব পরিশ্রম করছে রিঙ্কু। তাকে খুশি দেখলে বড্ড ভালো লাগে মণীশের।
কিন্তু সব ভালো বোধহয় চিরস্থায়ী হয় না। কিছুদিন পরই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উত্তপ্ত হয়ে উঠল সিএএ অর্থাত্ নাগরিকত্ব প্রমাণের বিষয়টি নিয়ে পরিষ্কার দুদলে ভাগ হয়ে গেল মানুষ মতাদর্শের নিরীখে। যুব ও ছাত্ররাজনীতির ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ল। সরকারের পক্ষে ও বিপক্ষে ভাগ হয়ে মারামারি শুরু হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। এরকমই একদিন, গেট ক্র্যাশ করে নানা কলেজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্ল্যান করে ফেলল দেব। যড়যন্ত্রে সামিল করল মণীশকেও। টুকরো টুকরো দলে ভাগ হয়ে তারা ছড়িয়ে পড়ল নানা কলেজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে বলে। বিকেলের দিকে গেটের মুখে দেশনায়কের মতো পুলিশের জিপে ওঠার আগে, মিডিয়াকে বাইট দিল দেব, আমাদের লড়াই চলছে চলবে… ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে দিল পুলিশ। মণীশ বিপদ বুঝে বাড়িতে চলে এল।
এর কিছুক্ষণ পরই বাড়ির সামনে একটা শোরগোল শুরু হল। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মারতেই দেখে, একটা পুলিশের জিপ ও একটা অ্যাম্বুল্যান্স এসে হাজির। দরজা খুলে বেরোতেই মণীশের বাকরুদ্ধ অবস্থা। অ্যাম্বুল্যান্স-এর দরজা খুলে যাকে নামানো হল মাটিতে সে রিঙ্কু। তার চোখ দুটো বন্ধ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গোটা দেহ। টুপি খুলে এসআই এগিয়ে এলেন।
হাসপাতালে যাওয়ার পথেই মৃতু্য হয়েে ওনার। কলেজের বইখাতা ঘেঁটে ঠিকানা পেলাম। আজ একদল ছেলে চড়াও হয়েিল এদের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। দুদলের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ইটের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ইনি। তারপর আমরা রেসকিউ করে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার পথেই…
মণীশ হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়ে। হাউ হাউ করে কাঁদছে সে। মা-ও বেরিয়ে এসেছেন ঘরের ভিতর থেকে। বাবা ক্রাচটা ধরে থরথর করে কাঁপছেন। কাকে সামলাবে মণীশ। এ তো তারই পাপের শাস্তি পেল তার ফুলের মতো বোনটা! রিঙ্কুর নিথর রক্তাক্ত দেহটাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে সে। হাতে রক্ত লেগে যায় তার। এ রক্ত কি সারাজীবনেও ধুতে পারবে মণীশ!