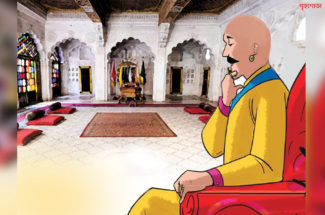বেঙ্গালুরু থেকে সুলগ্না বিএসসি নার্সিং পড়া শেষ করে বাড়ি ফিরছে। বহুকষ্ট স্বীকার করে, প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে সে কোনওরকমে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বছর দশের আগে পরিস্থিতি এতখানি খারাপ ছিল না। সুলগ্নার বাবা প্রভাসবাবু আমেদাবাদে একটা টেক্সাইল মিলে কাজ করতেন। তাঁর ভালো উপার্জন ছিল। সুলগ্নার মা সুনীতা সুনিপুণ হাতে সংসার চালাতেন।
সুলগ্নার বাড়িতে একটা জায়গা কমজোরি ছিল তার বড়ো দিদিকে নিয়ে। বড়ো দিদি জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী। হুইল চেয়ারে বসেই সে সাতাশ বছর কাটিয়ে দিল। তবু সেই ব্যাপারে সুলগ্নার বাবা-মা-র কোনও আক্ষেপ অথবা কোনও অনুতাপ ছিল না। তাঁদের একটা মানসিক কষ্ট ছিল। বাবা-মা ভাবতেন যে, তাঁরা মারা গেলে তাঁদের মেয়েকে কে দেখবে। বড়ো মেয়ে আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতো হলে তাঁদের আর ভাবতে হতো না। আর্থিক সচ্ছলতা অনেক কমজোরিকে অতিক্রম করার সাহস জোগায়। কিন্তু এক্ষেত্রে তা ঘটেনি।
প্রভাসবাবুর উপার্জনের টাকায় সংসারের চাকা সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছিল। সুলগ্নার এগারো ক্লাসে পড়ার সময় হঠাৎই তার পরিবারের উপর বিপর্যয় নেমে আসে। প্রভাসবাবু দুর্গাপুজোয় ছুটি নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁর এক পা কাটা যায় ও মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পান। বহু ডাক্তার দেখিয়ে, বহু অর্থ ব্যয় করে প্রাণে বেঁচে গেলেও তিনি আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারলেন না। সংসারের মোড় ঘুরতে লাগল।
প্রভাসবাবুর শারীরিক অবনতি ও আর্থিক দুরবস্থা সদাহাস্যমুখী সুনীতার চরিত্রের পরিবর্তন করে দিল। ভাগ্যের উপর দোষারোপ করতে করতে তাঁর মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেল। তিনি দুই মেয়ের সঙ্গে কোনও সময় ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতেন না। কারণে-অকারণে মায়ের মুখঝামটা খেতে খেতে দিন কাটত সুলগ্নার ও তার দিদির। সময়ের স্রোতে ভেসে কোনওরকমে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হল সুলগ্নার। তাকে খুঁজতে হল স্বল্প সময়ের মধ্যে ভালো রোজগারের পথ।
রোজগারের পথ দেখালেন সুনীতার এক বন্ধু। তিনি সুনীতাকে পরামর্শ দিলেন মেয়েকে বিএসসি নার্সিং পড়ানোর। তিনি সুনীতাকে এই ভরসাও দিলেন যে, পাশ করার পর সুলগ্না যে-কোনও সরকারি অথবা বেসরকারি হাসপাতালে অনায়াসে চাকরি পাবে। সুনীতা তাঁর বিয়ের গহনা বন্ধক দিয়ে সুলগ্নাকে বেঙ্গালুরু পাঠিয়ে দিলেন বিএসসি নার্সিং পড়তে।