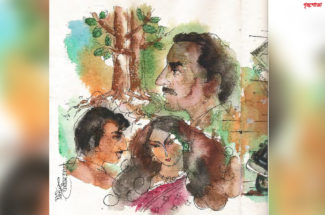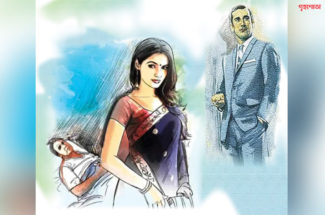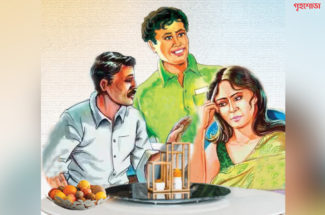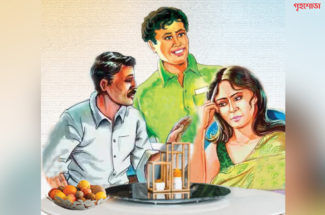অসীম টুরে গেছে পাঁচ দিনের জন্য, তিতির কলেজে। কারেন্টও নেই। একা বাড়িতে লম্বা দুপুরটা কাটতে চাইছিল না। আজকের কাগজটা নিয়ে বিছানায় গড়াচ্ছিল নন্দিনী। এ পাতা থেকে ও পাতায় এলোমেলো উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে ঘুরতে আচমকাই চোখটা পার্সোনাল কলামে আটকে গেল। ডান দিকের কোণে একদম তলার দিকে ছোটো ছোটো কয়েকটা অক্ষর। আলাদা করে সেইভাবে চোখে পড়ার কথাই নয়। তবু পড়ল। হয়তো পড়ার ছিল বলেই। ‘জেনিফার ক্যাথারিন ম্যাকলেন অফ হ্যাপি নুক, জোরহাট– পাসড অ্যাওয়ে পিসফুলি, অ্যাট হার রেসিডেন্স। ফিউনারেল মাস অন’…
জেনিফার ম্যাকলেন? জোরহাটের জেনিফার ম্যাকলেন? এই নামে অনেকদিন আগে একজনকে চিনত না নন্দিনী? হ্যাপি নুকের জেনিফার ম্যাকলেন বলতে তো একজনের কথাই মনে পড়ে। মিস ম্যাকলেন তাহলে এতদিনে মারা গেলেন। কে দিল নোটিসটি? চার্চ থেকেই হবে নিশ্চয়ই। নন্দিনী অন্যমনস্কভাবে হাতের কাগজটা ভাঁজ করে। আশ্চর্য, একেবারে ভুলেই গিয়েছিল মহিলার কথা।
অসীমের পোস্টিং তখন ছিল অসমের জোরহাটে। জোরহাট টাউন থেকে একটু দূরে কিছুটা ভেতরের দিকে ছিল ওদের বাড়িটা। বেশ নির্জনই ছিল পাড়াটা সেই সময়। প্রচুর জায়গা, বাগান, ফলের গাছ-টাছ নিয়ে এক একটা বাড়ি। এরকমই একটা বাড়ির একতলাটা অসীমের অফিস থেকে তাদের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।
কলকাতায় ও রকম বাড়ি স্বপ্নের অতীত। বিরাট বড়ো বড়ো চারখানা ঘর, আলো ভরা বাথরুম, বাদশাহি রান্নাঘর, সঙ্গে আলাদা প্যান্ট্রি, চারদিক ঘুরিয়ে কাঠের জাফরি ঝোলানো টানা বারান্দা, মানে এককথায় এলাহি ব্যাপার। কিন্তু এত বড়ো বাড়িতে সারাদিন একা একা কাটাতে নন্দিনীর দম বন্ধ হয়ে আসত। তাদের মানিকতলার বাড়িও যথেষ্ট বড়ো। কিন্তু সেখানে ছিল কাকা-কাকি, জ্যেঠা-জেঠি তুতো ভাইবোন সবাইকে নিয়ে বিশাল যৌথ পরিবার। চেষ্টা করলেও ওবাড়িতে একা থাকা যেত না।
সেই হট্টমালার দেশ থেকে বিয়ে হয়ে এসে পড়ল এই ভূতবাংলোয়। ঘর মোছা, বাসন মাজার জন্য একজন আর কাপড়চোপড় কাচার জন্য একজন, এই দু’জন স্থানীয় আদিবাসী কাজের মেয়ে ছিল, কিন্তু সারাদিনের জন্য নয়। সকাল সকাল এসে দশটার মধ্যে সব কাজ সেরে তারা চলে যেত। কতটুকুই বা কাজ থাকত দুজনের সংসারে। তাদের ওদিককার ভাষাও নন্দিনী সবটা ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারত না। ফলে সঙ্গী হিসেবে তারা খুব একটা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি।
তিতির হয়নি তখনও। অসীম অফিসে বেরিয়ে গেলে এত বড়ো বাড়িতে একলা নন্দিনী। শূন্যতা যেন বিশাল হাঁ করে তাকে গিলে খেতে এগিয়ে আসত। উপরতলায় কোনও ভাড়াটেও ছিল না যে গল্প করে সময় কাটাবে। পাড়াটাও এত চুপচাপ। লোকজন বাস করে বলে বোঝাই মুশকিল। কলকাতার শোরগোলের একেবারে বিপরীত। কী করে যে দিনগুলো কাটত এখন ভাবলেও অবাক লাগে। তখনই কোনও এক সময় মিস ম্যাকলেনের সঙ্গে নন্দিনীর পরিচয়।
নন্দিনীদের বাড়িটার ঠিক পাশেই একটা একতলা বাংলো প্যাটার্নের ছোটো বাড়ি ছিল। রংচটা, ধুলোটে। চওড়া কাঠের গেটের রং এককালে হয়তো সাদাই ছিল, বা অন্য কিছুও হতে পারে, বলা মুশকিল, কারণ বহুদিনের অযত্নে অবহেলায় সেটা একটা অবর্ণনীয় শেড ধরে নিয়েছিল। কার্নিশে যেখানে সেখানে বেয়াড়া বট অশ্বত্থের চারার যথেচ্ছ জবরদখল অভিযান। দেয়ালে জায়গায় জায়গায় বৃষ্টি গড়ানো শ্যাওলাটে সবুজ দাগ। গেটের পাশে বহু বছরের ময়লায় কালচে হয়ে যাওয়া ফলকে কষ্ট করে পড়া যায় ‘হ্যাপি নুক’। বাগান হয়তো কোনওকালে একটা ছিল, নন্দিনীর চোখে যেটা পড়েছিল তাকে বাগানের অপভ্রংশও বলা চলে না।
এই বাড়িতেই থাকতেন জেনিফার ম্যাকলেন। একাই। কাজের লোকটোকও কেউ ছিল না। অন্তত নন্দিনী তো কোনওদিন কাউকে থাকতেও দেখেনি, আসতে যেতেও দেখেনি। সঙ্গী বলতে একটি বৃদ্ধ পমেরিয়ান কুকুর। এত দিন পরে হঠাৎ তার নামটাও আজ নন্দিনীর মনে পড়ে গেল। পিক্সি। তাকে নিয়ে রোজ সকাল-বিকেল হাঁটতে বেরোতেন। চুপচাপ মাথা নীচু করে কোনও দিকে না তাকিয়ে একটু ঝুঁকে হেঁটে যেতেন, আবার ওই ভাবেই বাড়ি ফিরে আসতেন। যতদিন নন্দিনী ছিল ওখানে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ওই রুটিনে কোনওদিন ছেদ পড়তে দেখেনি।
মিস ম্যাকলেনের মতো নিরুত্তাপ মানুষ নন্দিনী আজ পর্যন্ত আর দ্বিতীয় একজন দেখল না। কোনও মানুষ যে তার চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে এতটাই নিরাসক্ত হতে পারে ভাবা যায় না। কারমেল কনভেন্টে ইংরেজি পড়াতেন। শোনা কথা, ছাত্রীরা নাকি আড়ালে বলত ‘আইসবার্গ’। স্বভাবের জন্য না চেহারার জন্য সেটা জানা যায়নি। তবে দুদিক থেকেই নামটা মানানসই।
রোগাপাতলা ছোটোখাটো চেহারা। গায়ের রং পুরোনো খবরের কাগজের মতো। সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন মুখ। পাতলা ফ্যাকাশে ঠোঁট। ফ্যাকাশে সবজেটে চোখের মণি। ফ্যাকাশে বাদামি চুল। চিরটাকাল পরনে হালকা রঙের ছাঁটকাটহীন ঢোল্লা হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঝুলের ফ্রক। সব মিলিয়ে একজন ফ্যাকাশে মানুষ। কেউ ডেকে কথা বললে উত্তরে বাধ্য হয়ে ভদ্রতাসূচক দু-চারটে কথা যা বলার বলতেন, নইলে চুপচাপ। গলার আওয়াজও চেহারার মতোই নিষ্প্রভ, নিরুত্তেজ। কোনও ওঠাপড়া নেই। স্কুল, বাড়ি আর পিক্সির মধ্যেই ওঁর জগৎ সীমাবদ্ধ ছিল। প্রতি রবিবার অবশ্য নিয়ম করে চার্চে যেতেন। আর প্রতি মাসে দিন দুয়েক বাড়ি তালা বন্ধ রেখে সম্ভবত গৃহস্থালির টুকটাক কেনাকাটার জন্য টাউনেও যেতেন। কারণ এবং গন্তব্যস্থলটা লোকের ধরে নেওয়া। কোনওটাই কারও সঠিক জানা ছিল না, কারণ উনিও কোনওদিন কাউকে ডেকে বলেননি, আর ওঁর কাছে কোনওদিন কেউ জানতেও চায়নি। কাকেই বা বলবেন, কেই বা জানতে চাইবে। কুকুরটি ছাড়া তো তিন কুলে কোথাও কেউ ছিলও না। অন্তত আছে বলে কেউ জানত না। উনি যে দিনগুলো বাড়ির বাইরে থাকতেন সেই কটা দিনের জন্য পিক্সি চার্চের ফাদার অ্যান্টনির কাছে থাকতে যেত।
নন্দিনী বলতে গেলে সেধেই আলাপ করেছিল। ওঁর বাড়িতেও গিয়েছিল কয়েকবার। উনি অবশ্য বিশেষ আসতেন না। দেখা হলে বেড়ার পাশে বা গেটের ওধারে দাঁড়িয়েই সামান্য দুচারটে সৌজন্যমূলক কথা বলে চলে যেতেন। বাড়ির ভেতরে ঢুকতে স্পষ্টই অনীহা ছিল। তবে পরের দিকে মাঝেমধ্যে কেক বা বিস্কিট গোছের কিছু ভালোমন্দ বানালে ডাক দিতেন। নন্দিনী খেয়েও আসত, নিয়েও আসত। জিজ্ঞাসা করে করে শিখেও নিয়েছিল ওঁর কাছ থেকে নানারকম।
একদিন, শুধু একদিনই মিস জেনিফার ক্যাথারিন ম্যাকলেনকে অন্যরকম দেখেছিল নন্দিনী। একটা পুরো দিন।
সেদিন সকালে একটু বেলার দিকে মিস ম্যাকলেনের গেটের লেটারবক্সে পিওন চিঠি ফেলে গিয়েছিল একটা। নন্দিনী নিজের শোবার ঘরে কী যেন করছিল। জানালা দিয়ে ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে মনে মনে একটু অবাকই হয়েছিল। এতদিনের মধ্যে কোনও দিনও ওবাড়িতে কোনও চিঠিপত্র আসতে দেখেনি সে। পিক্সির ডাকাডাকির আওয়াজ পেয়েই আসলে তার চোখ বাইরের দিকে গিয়েছিল। সে বেচারাও পিওন নামক খাকি পোশাকধারী অপরিচিত জীবটিকে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে পাহারাদারির সহজাত সারমেয় প্রবৃত্তি পালনের তাগিদে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে যাচ্ছিল। একটু পরে মিস ম্যাকলেনের ভাবভঙ্গি দেখে নন্দিনীর অবাক হওয়ার মাত্রাটা আরও বেড়ে গিয়েছিল যেন। পিক্সির চিৎকারে উনিও বেরিয়ে এসেছিলেন। পিওন চলে যেতে যেতে হাতের ইশারা করে বুঝিয়ে দিল চিঠি দিয়ে গেছে। উনি খানিকক্ষণ যেন কিছু না বুঝে পিওনের চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে ছিলেন। তারপরে পায়ে পায়ে গেটের দিকে এগোলেন।
নন্দিনী ঘটনাটা কী ঘটছে দেখার জন্য জানালার পাশ থেকে সরেনি, ওখান থেকেই তাকিয়ে ছিল। মিস ম্যাকলেন লেটারবক্স থেকে চিঠিটা বার করে একটু হতবুদ্ধি ভাবে প্রথমটা ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাদামি কাগজের খামটা হাতে নিয়ে ভুরু কুঁচকে উলটেপালটে দেখছিলেন, বোঝার চেষ্টাই করছিলেন হয়তো তাঁকে কে চিঠি লিখতে পারে। তারপরে ওখানে দাঁড়িয়েই খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বার করলেন। নন্দিনী আশ্চর্য হয়ে দেখল চিঠিটা পড়তে পড়তেই ওঁর হাবভাব কেমন যেন পালটে গেল। দূর থেকেও সে বুঝতে পারছিল মহিলা থরথর করে কাঁপছেন। হাত বাড়িয়ে একবার গেটটা ধরারও চেষ্টা করলেন। নন্দিনীর ভয় হচ্ছিল উনি পড়ে-টড়ে না যান। হয়তো কোনও খারাপ খবর আছে চিঠিতে। তারপরে আরও অবাক হয়ে গেল যখন দেখল উনি ওদের বাড়ির দিকেই আসছেন।
মিস ম্যাকলেন বেল বাজানোর আগেই নন্দিনী বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন উনি। মুখচোখ যেন কেমন কেমন। নাকের তলায় ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে। কিছু না বলে অকস্মাৎ নন্দিনীর দিকে চিঠিটা বাড়িয়ে ধরলেন। নন্দিনীও কিছু না বুঝেই ওঁর হাত থেকে ওটা নিয়ে নিল। পড়তে ইশারা করছিলেন মিস ম্যাকলেন। তখনও কথা বলতে পারছিলেন না। নন্দিনী আগে ওঁকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে ঘরে বসাল। তাড়াতাড়ি এক গ্লাস খাবার জল এনে দিল। উনি এক নিঃশ্বাসে জলটা শেষ করে গ্লাসটা ফিরিয়ে দিলেন। তারপরে কেমন যেন গা ছেড়ে দিয়ে সোফার পিছনে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। নন্দিনী নজর ফেরাল হাতে ধরা চিঠিটার দিকে।
চিঠিটা লিখেছেন কোনও এক ডাক্তার এসপি বড়ুয়া। ইংরেজিতে লেখা চিঠির বাংলা করলে এরকম দাঁড়ায়–
‘ডিয়ার জেনিফার,
আশা করি ভালোই আছ। তোমার জন্য সুখবর আছে একটা। তুমি হয়তো জেনে খুশি হবে যে ফ্র্যাংকলিনের মধ্যে আজকাল আগের থেকে অনেক বেশি উন্নতি দেখা যাচ্ছে। গত সপ্তাহে ওর ঘরে রাখা তোমার ছবিটা দেখে তোমাকে চিনতে পেরেছিল। কাল নিজে থেকেই বলল, জেনি খুব ভালো চকোলেট কেক বানায়। আমার মনে হচ্ছে নতুন ওষুধটায় বোধহয় কাজ হচ্ছে।
যে জন্য তোমাকে চিঠিটা লেখা। আমি ভাবছিলাম এ মাসে তুমি না এসে যদি আমিই ফ্র্যাংকলিনকে নিয়ে তোমার কাছে যাই তাহলে কেমন হয়? একটা চেঞ্জও হবে ওর। তাই এই বৃহস্পতিবার বিকেলে তোমার বাড়ি আসছি আমরা। তৈরি থেকো।’ তারপরে আবার পুনশ্চ দিয়ে লিখেছেন– ‘খুব বেশি কিছু আশা কোরো না। এই রিঅ্যাকশনগুলো প্রায়ই খুব একটা পার্মানেন্ট হয় না। তবুও লেট আস হোপ ফর দ্য বেস্ট।’
বৃহস্পতিবার? বৃহস্পতিবার তো আজকেই। কিন্তু কে এই ডাক্তার বড়ুয়া? যে ফ্র্যাংকলিনের কথা চিঠিতে আছে সে-ই বা কে? আর এই চিঠি পেয়ে মিস ম্যাকলেনেরই বা অমন অবস্থা কেন হল? নন্দিনী সত্যি কিছুই বুঝতে পারে না। এ প্রহেলিকার উত্তর একমাত্র মিস ম্যাকলেনই জানেন। ধাঁধায় পড়ে সে মিস ম্যাকলেনের দিকে তাকায়। আর অবাক হয়ে দেখে মিস ম্যাকলেন কেমন অদ্ভুত চোখে ওর দিকেই চেয়ে আছেন। চেয়ে আছেনও, আবার নেইও। ওঁর ওই ফ্যাকাশে সবুজ চোখের দৃষ্টি যেন নন্দিনীকে ভেদ করে, এ ঘর ছাড়িয়ে কোথায় কতদূরে উধাও হয়ে গেছে।
আস্তে আস্তে একটি দুটি করে কথা বলতে আরম্ভ করেন জেনিফার ম্যাকলেন। তারপরে বাঁধভাঙা বন্যার মতো বেরিয়ে আসতে থাকে অনেক দিনের অনেক জমে থাকা কথা। গলার আওয়াজ থরথর করে কাঁপে। আর নন্দিনী স্তব্ধ হয়ে শুনতে থাকে এক আশ্চর্য কাহিনি। যাকে কাহিনি না বলে রূপকথা বলাই বোধহয় উচিত।
আসাম চা বাগিচার দেশ। আর চা বাগিচা মানেই প্ল্যান্টার। প্রথম দিকে খাঁটি সাহেবরাই বাগান চালাত। পরে আস্তে আস্তে তাদের সংখ্যা কমতে থাকে। সে জায়গায় আসতে শুরু করে দেশি সাহেবরা। এ কাহিনির যখন শুরু তখন সবে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। কিছু কিছু বাগানে দু-একজন সাদাচামড়া সাহেব তখনও ছিল। তাদেরই একজন রঙালি টি এস্টেটের ছোটো সাহেব প্যাট্রিক ম্যাকলেন। প্যাডি সাহেব। প্যাডি সাহেবকে সবাই চিনত দুটো কারণে। এক নম্বর কারণ তার দিলদরিয়া স্বভাব। গায়ের রংটা তাকে আলাদা করে চিনিয়ে দিত ঠিকই, তা নইলে এদেশের লোকেদের সঙ্গে মেলামেশায় সে, সাহেব আর নেটিভের কোনও ফারাকই রাখত না। কত প্ল্যান্টারদের কত অত্যাচারের কাহিনি সে সময় বাগানের কুলি কামিনদের মুখে মুখে ফিরত, কিন্তু প্যাডি সাহেব সম্বন্ধে কেউ কোনওদিনও অমন কথা ভাবতেও পারত না।
আর দু-নম্বর কারণ তার মা-মরা একমাত্র মেয়ে জেনি মেমসাহেব। জেনিফার ক্যাথারিন ম্যাকলেন। বলতে গেলে সেটাই তখন সাহেবকে চেনার প্রধান কারণ। বিশেষ করে উঠতি যুবকদের মধ্যে। পাহাড়ি ঝরনার মতো চঞ্চল, পরিদের মতো সুন্দর উনিশ বছরের জেনি মেমসাহেবকে দেখলে অতি বড়ো গোমড়ামুখোদেরও মন ভালো হয়ে যায়। সেই সময় আশপাশের ছোটোবড়ো যত গার্ডেনের সব ইয়ং ম্যানদের জীবনের একটাই লক্ষ্য, কে জেনিকে একটু খুশি করতে পারে। পিকনিক, টি-পার্টি, ক্রিসমাস ড্যান্স– সবের মধ্যমণি জেনি ম্যাকলেন। মিস স্টুয়ার্ট, মিস ব্রাউনদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। জেনির সঙ্গে একটা ড্যান্স মানে জীবন সার্থক। জেনি কারও দিকে চেয়ে একটু হাসলে সে নিজেকে পৃথিবীর সবথেকে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ভাবতে একটুও দ্বিধা করে না।
জেনি কাউকে নিরাশ করে না। কিন্তু কাউকে আশাও দেয় না। আজ ব্রিজ পার্টিতে ডিকি রবার্টসনকে পার্টনার করলে পরের দিন নাচের ফ্লোরে তার সঙ্গী হয় জেরি উইলিয়ামস। কেউ তার কাছে বিশেষ নয়। সবাই তার ভালো বন্ধু, ব্যাস।
বিশেষ তার একজনই। সেই ছেলেবেলা থেকেই। ফ্র্যাংকি। তখন ছিল শুধুই ফ্র্যাংকি। বড়ো হয়ে হল টগবগে তরুণ আর্মি অফিসার ক্যাপ্টেন ফ্র্যাংকলিন। প্যাডি সাহেবের বন্ধু ফ্রেডি ক্লিফটনের একমাত্র ছেলে। খাঁটি সাহেব ছিল না অবশ্য সে।
ফ্রেডি ক্লিফটন এদেশে আসার আগে ছিল বার্মায়। আজকাল যে দেশের নাম হয়েছে মায়ানমার। ইঞ্জিনিয়ার ফ্রেডি ক্লিফটন ভালোবেসে বিয়ে করেছিল সেই বার্মারই এক সুন্দরী মেয়েকে। ফ্র্যাংকি ছিল তাদের ভালোবাসার ফসল। মিশ্র রক্তের সন্তান।
তাতে অবশ্য বাগানের কারও কিছু আসত যেত না। ওখানে অনেকেরই জন্মের ইতিহাস ফ্র্যাংকির মতোই। তাও তো তার মা, পাতা তোলা কামিন ছিল না। যথেষ্ট শিক্ষিত, ধনী ঘরের মেয়ে ছিল তার মা। কেবল বিজাতীয়, বিধর্মীকে বিয়ে করার অপরাধে সে মেয়ের পরিবার তাকে ত্যাগ করে।
ফ্র্যাংকির যখন বারো বছর বয়স তখন তার মা বাবা দুজনেই এক সাংঘাতিক কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। এ-দেশে তার আর কেউ ছিল না। বহু দূর আয়ারল্যান্ডে, কখনও-না-দেখা তার এক কাকা ছিল বটে, সে ভাইপোকে নিয়ে যেতে চাইছিল না। ঝুটঝামেলায় না গিয়ে প্যাডি সাহেব ফিউনারেল হয়ে যাবার পর সটান ফ্র্যাংকিকে নিজের কাছে রঙালিতে নিয়ে চলে এসেছিল। জেনির বয়স তখন আট। সেই থেকে জেনি আর ফ্র্যাংকি একসঙ্গেই বড়ো হয়েছে।
দশ বছর বয়স থেকেই জেনি জানত সে ফ্র্যাংকির। কী করে জানত জানে না। কিন্তু জানত। ফ্র্যাংকিও যেমন জানত জেনি তার। একমাত্র তার। তারা দুজন একে-অপরের জন্যই তৈরি। আর কেউ কখনও তাদের মধ্যে আসবে না, আসতে পারে না। এই ধ্রুব সত্যিটা মনের মধ্যে গেঁথে রেখেই জেনি দশ থেকে উনিশ হয়েছে, ফ্র্যাংকি হয়েছে তেইশ।
‘হি ওয়াজ সাচ আ হ্যান্ডসাম ডেভিল য়ু নো। অ্যান্ড ডেয়ারিং। আর্মি জয়েন করল। ইউনিফর্ম পরে আমার সামনে দাঁড়াত। নানডিনি, বিলিভ মি, আমি মেল্ট করে যেতাম। আমাকে পেছনে বসিয়ে স্পিডে মোটরবাইক চালাত, ভাবতে পারবে না। আই থট মাইসেল্ফ দ্য লাকিয়েস্ট গার্ল অ্যালাইভ।’
নন্দিনী রূপকথা শুনছে। এই মিস ম্যাকলেনকে সে দেখেনি কোনওদিন। মিস ম্যাকলেনের গলায় উনিশের জেনি কথা বলে চলে। গলার আওয়াজ আর কাঁপছে না এখন। সেই কণ্ঠস্বরের সম্মোহনী ওঠাপড়া নন্দিনীকে আবিষ্ট করে ফেলে। রূপকথার নায়িকা স্মৃতিমগ্ন হয়ে নিজের কাহিনি শোনাতে থাকে।
‘সেদিন সানডে ছিল, জানো। আমাদের ফর্মাল এনগেজমেন্ট হয়ে গেল। ফ্র্যাংকি আমাকে আংটি পরাল। আমি পরালাম ফ্র্যাংকিকে। চার্চে বিয়ের নোটিস পড়ল। তিন মাস পরে আমাদের বিয়ে। উই ওয়্যার সো হ্যাপি দ্যাট ডে।’ হালকা হাসির রেখা জেনিফার ম্যাকলেনের ঠোঁট ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।
নন্দিনী অবাক বিস্ময়ে মিস ম্যাকলেনের দিকে চেয়ে দেখতে থাকে। তার চোখের সামনে মধ্য চল্লিশের বর্ণহীন মিস ম্যাকলেন আস্তে আস্তে খোলস ঝরিয়ে আদ্যন্ত জেনি হয়ে ওঠে। পুরোনো কাগজের মতো গালে গোলাপি রক্তোচ্ছ্বাস, চোখে পান্নার দ্যুতি।
গুনগুন করে কত দিনের কথা বলে যান মিস ম্যাকলেন। আর নন্দিনীর চোখের সামনে আস্তে আস্তে জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে রঙালি টি এস্টেট, জেনি মেমসাহেব আর সুদর্শন, ডাকাবুকো
ফ্র্যাংকলিন ক্লিফটন।
আর তার পরে সেই রাতের কথা। জেনি আর প্যাডি সাহেবের সঙ্গে ডিনার সেরে ইউনিটে ফিরছিল ক্যাপ্টেন ক্লিফটন। ঠিক কী যে সে রাতে হয়েছিল কেউই জানে না, কিন্তু পরের দিন সকালে রাস্তার পাশে দোমড়ানো মোচড়ানো মোটরবাইকটা ও তার থেকে অনেকটা দূরে ন্যাকড়ার পুতুলের মতো তালগোল পাকিয়ে পড়ে থাকা ফ্র্যাংকলিন ক্লিফটনের রক্তাক্ত অচৈতন্য শরীরটা দেখেছিল ভোরের পথচলতি বাগানশ্রমিকরা। খুব সম্ভবত কোনও মাতাল লরির ধাক্বায় বাইক শুদ্ধু রাস্তা থেকে ছিটকে গিয়েছিল ফ্র্যাংকলিন ক্লিফটন।
‘ওরাই ওকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। পকেটে ডায়ারি ছিল, তাতে আমার ছবি, ঠিকানা ছিল। হাসপাতাল থেকে আমাদের খবর দেয়।’
মাথায় সাংঘাতিক আঘাত লেগেছিল ফ্র্যাংকির। বাঁচার আশাই ছিল না। দীর্ঘ সাঁইত্রিশ দিন কোমায় অচেতন ছিল সে। তারপরে জ্ঞান যখন ফিরল তখন ক্যাপ্টেন ফ্র্যাংকলিন ক্লিফটন নিজের নামটুকুও মনে করতে পারে না আর। হাসপাতালের বিছানায় ফ্র্যাংকি তখন শুধুই স্মৃতিহীন, ভাষাহীন এক মানবশরীর মাত্র।
প্যাডি সাহেব অনেক করেছে তখন। মিলিটারির ডাক্তার ছাড়াও আরও বড়ো বড়ো ডাক্তার দেখিয়েছে। সবারই এক কথা। আশা ছাড়লে চলবে না। সময়, সময়ই করতে পারে যা করবার। ফ্র্যাংকির খুব ভালো বন্ধু ছিল ডাক্তার বড়ুয়া। সে-ও তাই বলে গেছে অহর্নিশ। ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো।
ধৈর্য ধরেছে জেনি। প্যাডি সাহেবের ধৈর্যের বাঁধও ভেঙে গেছে একদিন, কিন্তু জেনির ভরসা ভাঙেনি। প্যাডি সাহেব অনেক বুঝিয়েছে মেয়েকে, মন পালটাবার অনেক চেষ্টা করেছে, তারপরে একদিন বোধহয় মনের দুঃখেই ফট করে মাথার শিরা ছিঁড়ে ওপরে চলে গেছে।
এই হ্যাপি নুক বাড়িটা অনেকদিন আগে কিনেছিল প্যাডি সাহেব। কখনও কোনও দরকারে বাগান থেকে টাউনে এসে রাত হয়ে গেলে এখানেই থেকে যেত। সাহেব মারা যাবার পর জেনিরও বাগানের পাট চুকে গিয়েছিল। সেই তখন থেকেই জেনি এখানে। সেও আজ প্রায় ছাব্বিশ বছর হয়ে গেল। এখান থেকে মাসে মাসে হাসপাতাল যেতেও সুবিধে। ধৈর্য ধরে থাকতে থাকতে ফ্র্যাংকির মুখে ধীরে ধীরে একটা দুটো কথা ফুটল। আর দিনে দিনে কখন যেন রঙালির চুলবুলি জেনি মেমসাহেব আস্তে আস্তে সব রং ঝরিয়ে ফ্যাকাশে মিস ম্যাকলেন হয়ে গেল।
সেই ফ্র্যাংকি আজ ডাক্তার বড়ুয়ার সঙ্গে আসছে, জেনির বাড়িতে।
‘তুমি বিকেলে একটু থাকবে আমার সঙ্গে, নানডিনি, প্লিজ? আয়্যাম ফিলিং সো নার্ভাস। ফ্র্যাংকি এতদিন পরে আসছে আমায় মিট করতে।’ নন্দিনী খুব অবাক হয়ে দেখে মিস ম্যাকলেন সদ্য প্রেমে পড়া কিশোরীর মতো টুকটুকে গোলাপি হয়ে যাচ্ছেন।
বিকেলে মিস ম্যাকলেনকে চেনা যাচ্ছিল না। ঘন সবুজ সিল্কের একটা অপূর্ব ফ্রক পরেছেন। পুরোনো কাটের জামা, কিন্তু কী যে সুন্দর মানিয়েছে ওঁকে। ঝলমল করছেন যেন। নন্দিনী কখনও লক্ষ্যই করেনি, মিস ম্যাকলেনের হাত পায়ের পাতা কী অদ্ভুত সুন্দর। ঝিনুকের মতো পাতলা, শাঁখের মতো মসৃণ। লম্বা আঙুলের ডগায় বাদাম শেপের হালকা গোলাপি নখ। চোখ মুখ চেপে রাখা উত্তেজনার আঁচে গনগন করছে। এই অপরূপা মিস ম্যাকলেন কোথায় ছিলেন এতদিন? নন্দিনী নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।
অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে ছটফট করে বেড়াচ্ছিলেন জেনিফার। বারবার দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন। লজ্জাও পাচ্ছিলেন, নন্দিনী তাঁর অস্থিরতা বুঝতে পারছে বলে। টেবিলে একটা ট্রে আগে থেকেই সাজিয়ে রেখেছেন। চায়ের যাবতীয় সরঞ্জাম, আর একটা বড়ো প্লেটে নিজের হাতে তৈরি চকোলেট কেক। এত উত্তেজনার মধ্যেও কখন যেন ঠিক সময় করে বানিয়ে ফেলেছেন।
গাড়ির শব্দটা একই সঙ্গে দুজনের কানেই আসে। নন্দিনী মিস ম্যাকলেনের দিকে তাকায় একঝলক। যেখানে ছিলেন সেখানেই একদম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন উনি। মুখ থেকে সব রক্ত নেমে গিয়ে বরফের মতো সাদা দেখাচ্ছে। এক হাত দিয়ে অন্য হাতটা এত জোরে আঁকড়ে ধরেছেন যে আঙুলের গাঁটগুলো চামড়ার নীচে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বন্ধ দরজাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন জেনিফার। নন্দিনীই এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খোলে।
দুজন মানুষ। একজনকে স্পষ্টই বোঝা যায় এদিককার অধিবাসী বলে। খুব সম্ভব ইনিই ডাক্তার এসপি বড়ুয়া। এক হাত দিয়ে আরেকটি মানুষের কাঁধ জড়িয়ে রেখেছেন। সে মানুষটি এক বিশাল বৃক্ষের বাজ পড়া শুকনো কাণ্ড। ঝুঁকে পড়া লম্বা শরীর, পোড়া তামাটে গায়ের রং। নীল হাওয়াই শার্ট তার গায়ে ঢলঢল করছে। গাল ভাঙা, চোখের কোলে গভীর ক্লান্তি। কানের দু-পাশে কিছু পিঙ্গলে সাদায় মেশানো চুল। বাকি মাথা ফাঁকা। বয়স আন্দাজ করা অসম্ভব। পঞ্চাশও হতে পারে, পঁচাত্তরও হতে পারে। পিঠে ডাক্তার বড়ুয়ার হাতের চাপ অনুসরণ করে পা ঘষে ঘষে সে এগিয়ে আসতে থাকে নন্দিনীর দিকে।
‘হ্যালো জেনি।’ নন্দিনী ডাক্তার বড়ুয়ার কথায় সচেতন হয়ে পিছনে তাকায়। কখন যেন মিস ম্যাকলেন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ‘আমরা এসে গেছি।’
কথার জবাব দেন না জেনিফার। তাঁর দৃষ্টি শুধু দ্বিতীয় মানুষটির দিকে। ডাক্তার বড়ুয়া তার পিঠে চাপ দেন। ‘চিনতে পারছ ফ্র্যাংক? তোমার জেনিকে?’
ফ্র্যাংক নীরব থাকে। চোখে কোনও ভাষাই ফোটে না। মিস ম্যাকলেন নিজের হাতদুটো শক্ত করে মুঠি করেন। মুখ একবার লাল একবার সাদা হয়। নন্দিনীর ভেতরে কী একটা ভাঙতে থাকে, ভেঙে ভেঙে যায়।
ডাক্তার বড়ুয়া আস্তে আস্তে ফ্র্যাংককে ভেতরে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসান। সামনে টেবিলে মিস ম্যাকলেনের সাজানো ট্রে।
‘দেখছ ফ্র্যাংক, চকোলেট কেক। তুমি তো ভালোবাসো। দ্যাখো, জেনি নিজে বানিয়েছে, তোমার জন্য।’
ফ্র্যাংকি দুহাতে দুটো কেকের টুকরো তুলে নেয়। বাচ্চাদের মতো একবার এ-হাত একবার ও-হাত থেকে কামড়ায়। থুতনিতে গুঁড়ো গুঁড়ো ঝরে পড়া কেক মাখামাখি হয়ে যায়। শব্দ করে চিবোয় ফ্র্যাংকি। অথচ কী আশ্চর্য, মুখে কোনও অভিব্যক্তি ফোটে না।
‘আর এক পিস কেক নেবে ফ্র্যাংকি?’ জেনিফার খুব নরম গলায় বলে।
ফ্রাংকি কোনও উত্তর দেয় না। শুনতে পেল কী না তাও বোঝা যায় না। তাকিয়ে থাকে সোজা নির্বিকার। ফাঁকা দৃষ্টি জেনিফারকে ভেদ করে চলে যায়। তার হাতে মুখে আইসিঙের ক্রিম আর কেকের গুঁড়ো লেগে থাকে। সে বুঝতেও পারে না, বসে থাকে স্থির। জেনিফার ফ্রাংকির সোফার সামনে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে। অসীম মমতায় পরিষ্কার নরম ন্যাপকিন দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দেয়, হাত মুছিয়ে দেয়।
গোধূলির রং আস্তে আস্তে সন্ধ্যায় পালটে যেতে থাকে। আগে থেকে সাজিয়ে রাখা ট্রে-র কাপ ভর্তি চায়ে সর পড়ে যায়। ঘরের কোণায় কোণায় অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে। টেবিলবাতিটা জ্বেলে দেয় নন্দিনী।
জেনিফার ফ্র্যাংকির দুটি হাত মুঠিতে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসেই থাকে। হাতদুটি অল্প অল্প কাঁপে, পাতলা দুটি ঠোঁট কত কিছু বলতে চেয়ে থিরথির করে। কিন্তু কোনও কথাই বেরোয় না। বোধহীন, ভাষাহীন ফ্রাংকির মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখের পলকও বুঝি পড়ে না তার।
ঘরের মধ্যে ক্রমশ ভারী হয়ে জমতে থাকা একরাশ নৈঃশব্দ্য নন্দিনীকে চেয়ারে গেঁথে রাখে। নড়াচড়া করলেই যেন কী একটা ঘটে যাবে। সে শুধু দুচোখ মেলে এই ট্র্যাজিক মূকাভিনয় দেখতেই থাকে। গলার কাছে কী যে ভীষণ কষ্ট শক্ত হয়ে ডেলা পাকায়, সে জোর করে করে গিলে গিলে সেই ডেলাকে নীচে পাঠায়। কতক্ষণ যেন কেটে যায় এমনি করেই।
ডাক্তার বড়ুয়াই শেষে উঠে দাঁড়ান। শব্দ করে গলা পরিষ্কার করেন। ‘সরি জেনিফার।’ নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ পরে ওঁর কথাটা যেন ভীষণই জোরে বেজে ওঠে মনে হয়। চোখ তুলে তাকাতে পারছিলেন না ভদ্রলোক। গলা নামিয়ে আবার বলেন, ‘এবার যেতে হবে আমাদের।’
ডাক্তারের গলার আওয়াজে ঘোর ভাঙে জেনিফারের। ‘ফ্র্যাংকি আমার কাছে থাকতে পারে না? প্লিজ ডাক্তার? ও তো অনেক ভালো আছে আগের থেকে। ওকে তো এখন তোমরা এখানেই রাখতে পারো।’ জেনিফারের কণ্ঠস্বরে একরাশ আকুল আর্তি। অসহায় আশা ভরা দুটি চোখ ডাক্তার বড়ুয়ার দিকে চেয়ে থাকে।
জ্বলন্ত টেবিলবাতিটার চারপাশে একটা মথ অবিশ্রাম পাক খাচ্ছিল। ডাক্তার বড়ুয়া সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন। অনেকক্ষণ এমন ভাবে চুপ করে থাকেন যেন কানেই যায়নি। তারপর চোখ না সরিয়েই খুব নরম গলায় বলেন, ‘এইরকম সোবার কোয়ায়েট মোমেন্টগুলো ফ্র্যাংকির লাইফে খুবই রেয়ার, জেনিফার। তুমি পারবে না। পারবে না ম্যানেজ করতে তুমি। মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হবে…’ জেনিফারের দিকে তাকিয়ে কথা শেষ না করেই থেমে যান ডাক্তার।
এতক্ষণে বাঁধ ভাঙে। কী অসহ্য এক আক্ষেপে জেনির মুখ দুমড়ে দুমড়ে যায়। শব্দহীন কান্নায় বিকৃত মুখ দু-হাতে ঢেকে ফেলে সে। কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে শরীরটা। ডাক্তার বড়ুয়া আর নন্দিনী দুজনেই অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে শুধু। গতে বাঁধা সান্ত্বনাবাক্য এখানে এত অর্থহীন।
অস্বস্তি কাটানোর জন্য নন্দিনী চায়ের সরঞ্জামগুলো সরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ডাক্তার বড়ুয়া ফ্র্যাংকির দিকে তাকান। এ ঘরের চারজন মানুষের মধ্যে একমাত্র ফ্র্যাংকিরই কোনও বিকার নেই।
গেটের বাইরে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়ানো গাড়িটা এই সময়ে একবার জোরে হর্ন বাজায়। চমকে তাকিয়ে নন্দিনী এতক্ষণে দেখতে পায় গাড়িটার গায়ে বড়ো বড়ো সাদা অক্ষরে লেখা ‘সেন্ট জর্জেস অ্যাসাইলাম’।
পরের দিন সকালেও মিস ম্যাকলেনকে দেখেছিল নন্দিনী। রোজকার মতোই হালকা রঙের হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঝুলের ঢোল্লা ফ্রক পরে পিক্সিকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। মাথা নীচু, চোখ রাস্তার দিকে। বর্ণহীন, নিষ্প্রাণ, ফ্যাকাশে এক প্রৌঢ়া।
টিউব লাইটটা হঠাৎ দপদপ করে জ্বলে উঠে নন্দিনীর চোখটা ধাঁধিয়ে দিল। যাক, এতক্ষণে কারেন্ট এল তাহলে। বাবা, পাঁচটা বাজে। তিতিরের কলেজ থেকে ফেরার সময় হয়ে এল। সবিতা বিকেলের কাজ করতে এসে যাবে আর একটু পরেই। নন্দিনী দ্রুত হাতে খোলা চুল গোছাতে গোছাতে বিছানা থেকে নামে। আলস্যমন্থর স্মৃতিমেদুর দুপুরের ভার তাকে ছেড়ে চলে গেছে, এবার আবার সংসারের অভ্যস্ত ছন্দ তার আপাদমস্তক অধিকার করে নিতে শুরু করে।
মিস ম্যাকলেনের মতো ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া কাগজটা দলামোচড়া হয়ে খাটের উপরেই পড়ে থাকে।