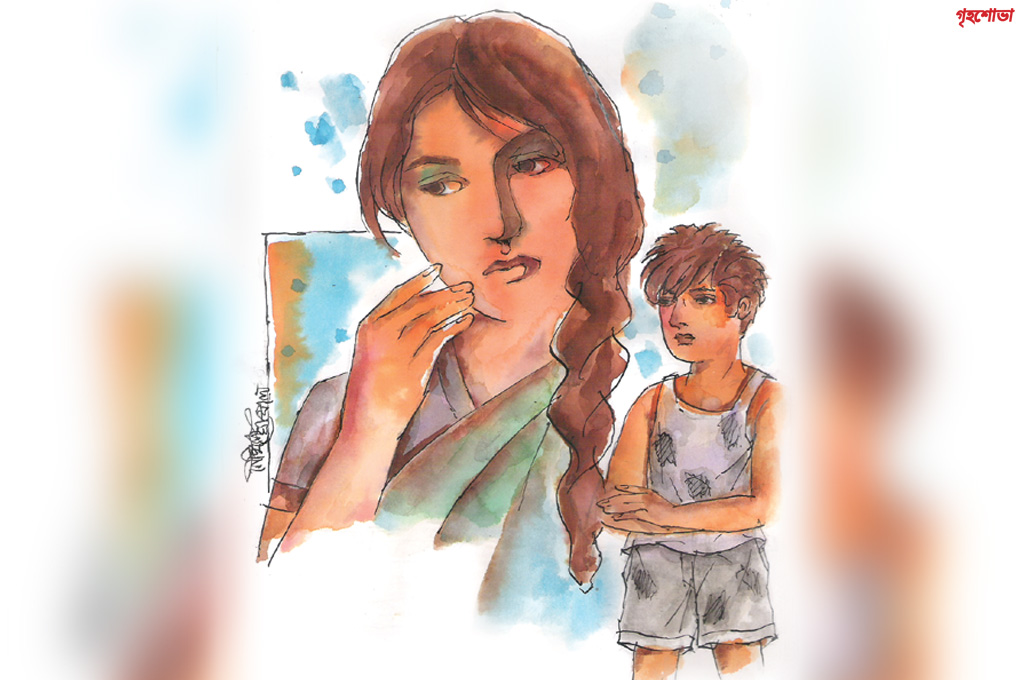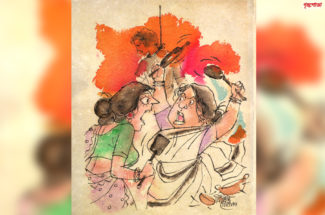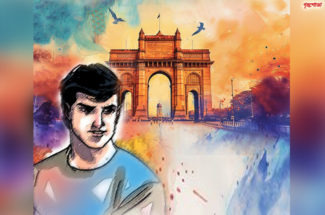পুঁটিকুমার আমার সামনে ভাতের থালাটা খটাস করে নামিয়ে লম্বা করে নাক টানল।
এগারো বছরের পুঁটিকুমার সবসময়েই নাক টানে। তার বারোমাসই সর্দি। এই কারণে তার আর-একটা নাম হল সর্দিকুমার। অবশ্য পুঁটিকুমার বা সর্দিকুমার কোনওটাই এই ছেলের ওরিজিনাল নাম নয়। ওরিজিনাল নাম কান্তি। রেস্টুরেন্টে বয় বেয়ারার এই কাজ পাওয়ার পর সে নতুন নাম পেয়েছে। এই রেস্টুরেন্টে এরকমই নিয়ম। যারা কাজ করতে আসে তারা একটা করে নতুন নাম পায়। কর্মচারীরা সবাই মিলে এই কাণ্ড করে। বলতে লজ্জা করছে, গত কয়েক বছর হল নামকরণের গুরুদায়িত্ব আমার ঘাড়ে পড়েছে। কী ঝামেলা! আমি কি এদের কর্মচারী? একেবারেই না। আমি এদের খদ্দের। কাস্টমার। তাও জেন্টলম্যান কাস্টমার নয়, ধারবাকির কাস্টমার। তবু কোনও এক রহস্যময় কারণে এখানকার কর্মচারীরা আমাকে অতিরিক্তরকম পছন্দ করে। সম্ভবত ওদের সঙ্গে প্রাণখুলে মেলামেশার কারণে। কে জানে। জেনে বিশেষ লাভ নেই।
অর্থনীতির নানান ধরনের মডেল আছে। কেইন্স মডেল, মার্কস মডেল, সেনস্ মডেল। কিন্তু ভালোবাসার ব্যাপারে কোনও মডেল নেই। কে কেন ভালোবাসে বোঝা দূরূহ। আমার বিশ্বাস একটা দিন আসবে যখন, নিশ্চয় এই বিষয়েও ফর্মুলা তৈরি হবে। সেই ফর্মুলাতে লাগিয়ে বুঝতে পারব রাঁধুনি, জোগানদার, বয়-বেয়ারা, বাজারসরকার, গ্যাস সাপ্লাইয়ের ছেলে, সাফাইকর্মী এমনকী গড়িয়াহাটা মোড়ের যে- ভিখিরি পরদিন গুছিয়ে বাসি এঁটোকাঁটা নিয়ে যায় তারা সকলে কেন আমাকে পছন্দ করে?
এরা একদিন আমাকে চেপে ধরল।
‘সাগরদা, নাম ঠিক করবার ভার এবার থেকে আপনার। না বললে হবে না। আমাদের দেওয়া নাম মোটেও জুতের হচ্ছে না। বক্বাস, ফক্বাস, খট্টাসে গিয়ে আটকে যাচ্ছি। এগুলো কোনও নাম হল? ভদ্রলোকদের সামনে বলা যায়? আমরা তাই ঠিক করেছি, এবার থেকে আপনি এই কাজ করবেন।’
আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। বললাম, ‘সে কী! আমি কী করে করব! আমি কি তোমাদের এখানে কাজ করি?’
‘কাজ করতে হবে না। কাজ না করলেও আপনি আমাদের লোক।’
আমি কাতর ভাবে বললাম, ‘নাম দিতে গেলে লেখাপড়া জানতে হয়। পণ্ডিত হতে হয়। নিদেনপক্ষে কবি সাহিত্যিক তো বটেই। তোমরা বরং স্কুল কলেজের মাস্টারমশাইদের ধরো। বাংলার মাস্টারমশাইরা নাম দেওয়ার ব্যাপারে ভারি দক্ষ হন। আমি একজন মাস্টারমশাইকে চিনি যিনি বছরে এক ডজন করে নাম সাপ্লাই দেন। হাসপাতাল,
নার্সিংহোমের সঙ্গে তার কনট্রাক্ট আছে। যদি বলো ঠিকানা জোগাড় করে দিতে পারি।’
এদের বাংলার মাস্টারমশাইয়ের কথা বললেও আমার নামের বেলায় ঘটনা অন্যরকম ঘটেছিল। সে এক কেলেঙ্কারি ঘটনা। বড়ো হয়ে আমি শুনেছি। আমার নাম দিয়েছিলেন পতিপাবন সমাজদার। তিনি বয়েজ স্কুলে বাংলা পড়িয়েছেন টানা সতেরো বছর। আমার জন্মের পর বাবা তার কাছে গিয়ে অনুরোধ করলেন, ‘মাস্টারমশাই, অনুগ্রহ করে আমার ছেলের একটা নাম ঠিক করে দিন। আপনার মতো বাংলা ভাষার পণ্ডিতের হাতে নামকরণ হলে আমার পুত্র ধন্য হবে।’
পতিতপাবনবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘এ তো তোমরা বিরাট ঝামেলা করো হে। দু-পাতা বেঙ্গলি লিটারেচার নিয়ে লেখাপড়া করেছি বলে আজীবন ছেলেমেয়েদের নাম দিয়ে বেড়াতে হবে? উফ্ বাংলায় বিএ, এমএ পাশ করাটাই দেখছি ঝকমারি হয়েছে। এমন হবে জানলে আমি ভূগোল পড়াতাম। যারা ভুগোল পড়ায় তাদের এসব ঝামেলা নেই।’
বাবা ধমক খেয়েও হাত কচলাতে লাগলেন। বাবা বিশ্বাস করতেন, মূর্খের ধমকে ক্ষতি আছে, পণ্ডিতের ধমকে ক্ষতি নেই। তার ওপর তিনি পুত্রের নাম সংগ্রহে বেরিয়েছেন। দু-একটা ধমকধামক তো শুনতেই হবে।
মাস্টারমশাই রাগ রাগ গলায় বললেন, ‘ঠিক আছে দেখব’খন। সাতদিন পরে এসো।’
সাতদিন পরে বাংলা ভাষার পণ্ডিত পতিতপাবন সমাজদার আমার নাম রাখলেন। সাগর। বাবা তো বিরাট খুশি। সাগর নামের জন্য খুশি নন, বাংলা ভাষার একজন পণ্ডিত তার ছেলের নাম রেখেছেন এই কারণে খুশি। সবাইকে ডেকে ডেকে তিনি বলতে লাগলেন। বাংলায় গভীর বুৎপত্তি এবং অধ্যয়ন না থাকলে এ জিনিস সম্ভব নয়। পরে কেলেঙ্কারি ফাঁস হল। জানা গেল, বুৎপত্তি, অধ্যয়ন তো দূরের কথা পতিতপাবনবাবু বাংলা নিয়ে পড়াশোনাই করেননি। তিনি বাংলার মাস্টারমশাইও নন। তিনি ভূগোলের মাস্টারমশাই। বয়েজ স্কুলে
বাংলার শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন শূন্য থাকার কারণে তিনি প্রক্সি দেন। গোলমালের আশঙ্কায় ঘটনা কেউ প্রকাশ করে না। পাছে চাকরি চলে যায়। শুনেছি, ঘটনা জানার পর বাবা খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। একজন ভূগোল শিক্ষককে দিয়ে পুত্রের নাম রাখা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। সবাই বলল, ‘তাতে কী হয়েছে? উনি তো লেখাপড়া জানাই মানুষ।’
বাবা বললেন, ‘প্রশ্নটা লেখাপড়ার নয়, প্রশ্নটা সাবজেক্টের। ভূগোলের পণ্ডিত জায়গার নাম দেবেন, মানুষের নাম দেবেন কেন? আমি কোনও কলম্বাস নই যে নতুন জায়গা আবিষ্কার করে তার কাছে গেছি।’
যুক্তি ঠিক নয়। নড়বড়ে। কিন্তু বিশ্বাস বলে একটা কথা আছে। তাকে কে টলায়? তবে আমি কিন্তু খুব খুশি। সাগর নাম পেয়ে গর্বিত। চমৎকার নাম। ভূগোলের টাচ আছে, আবার সাহিত্যের টাচও আছে। সাগর নিয়ে কত গান কবিতা লেখা হয়েছে। ভূগোল মাস্টারমশাই তো আমার নাম কর্কটক্রান্তি রেখা বা মৌসুমি বায়ু রাখেননি। যাই হোক, আমি এ গল্প রেস্টুরেন্টের কর্মীদের বলিনি। শুধু নিজে সরে পড়তে চেয়েছিলাম। ওরা কিছুতেই ছাড়ল না।
‘আমরা শুনব না। আমরা আপনাকেই চাই সাগরদা। এবার থেকে যে নতুন লোক এখানে কাজ করতে আসবে আপনি তার নাম ঠিক করে দেবেন। আপনিই আমাদের পণ্ডিত, আপনিই আমাদের কবি।’
হেসে ফেললাম। আমি পণ্ডিত! ফাঁকিবাজ এবং গাধা ছাত্রদের লেখাপড়ার বই দেখলে হাই ওঠে। আমি ছিলাম হাইয়ের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। বই দেখলে হাইয়ে সময় নষ্ট না করে আগে ভাগে ঘুমিয়েই পড়তাম। ছাত্রাবস্থায় আমার শ্লোগান ছিল, ‘আগে ঘুম পরে হাই’।
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে যেটুকু পড়বার পড়ে কলেজ পাশ করেছি। তারপর বেকার। নর্ম্যাল বেকার নয়, স্বেচ্ছাবেকার। স্বেচ্ছাবেকার হল স্বেচ্ছা অবসরের মতো। চাকরি পাইনি বলে চাকরি করি না এমন নয়। নিজের ইচ্ছে হয়েছে তাই চাকরি করি না। বেলা পর্যন্ত ঘুমোই। ঘুম ভেঙে গেলে আরও বেলা পর্যন্ত বিছানায় গড়াই। গড়ানো পর্ব শেষ হলে আরও আরও বেলা পর্যন্ত বিছানা ছাড়ব কিনা ভাবি। ভাবা কমপ্লিট হলে আরও আরও আরও বেলা পর্যন্ত ভাবি, এতক্ষণ যা ভাবলাম সবই তো ভুল ভাবলাম। নতুন করে ভাবতে হবে। জীবন হল ভাবার ভেলা। সেই ভেলায় শুয়ে উথালপাতাল সমুদ্রে ভেসে বেড়ানোই জীবনযাপন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই দার্শনিক চিন্তার তুলনা হয়? সামান্য রোজগার আর বেশিটাই ধারবাকিতে একার চমৎকার জীবন কাটিয়ে নেওয়া।
আমার কাছে চাকরি হল খাদের মতো। হাতির মতো বড়ো মানুষরা যখন ওই খাদে পড়ে, ব্যাঙের মতো অকিঞ্চিৎকররা লাথি কষায়। হাতিকে মরমে মরতে হয়। কিন্তু হায়রে! তখন আর করবারও কিছু থাকে না। ততক্ষণে বউ, ছেলেমেয়ে, সংসার, বাড়ির লোন, দুধের বিল, গ্যাসের দাম, অম্বলের ওষুধ নিয়ে ল্যাজে গোবরে সিচুয়েশন। তাই খাদ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের। বহু হাতছানি, বহু হুমকির পরও ওদিকে পা বাড়াইনি আমি। টিউশন, কলেজ স্ট্রিটের প্রুফ মাঝেমধ্যে হাবিজাবি দু-একটা উদ্ভট কাজ এবং ধারবাকি– এই আমার উপার্জন। এতেই সকাল-রাতে খাওয়া, এক কামরার বাসার ভাড়া জোগাড় হয়ে যায়। কখনও আবার হয়ও না। ব্যস্, আর কী চাই? আমি যেমন পণ্ডিত নই, তেমন কবি সাহিত্যিকও নই। আমার লেখালিখি বলতে চিঠি। চিঠিও না, চিরকুট। তার বেশিরভাগই বন্ধু তমালের কাছে ধার সংক্রান্ত।
‘ভাই তমাল, তুই শুনলে সবিশেষ দুঃখিত হবি। গত তিনদিন যাবৎ, ছোটো একটা সমস্যার মধ্যে আছি। সমস্যার নাম দারিদ্র্য। পকেটে একটিও পয়সা নেই। চিরকুটপাঠ আমাকে শ দুয়েক টাকা পাঠিয়ে নিজেকে দুশ্চিন্তামুক্ত কর।’
সাধারণত এই ধরনের চিরকুটের উত্তর আসে কড়া।
‘সাগর, তোর টাকাপয়সা নিয়ে আমার কোনও দুশ্চিন্তা, সুচিন্তা কিছুই নেই। অলস, ছন্নছাড়া, কোনও আহাম্মককে নিয়ে আমি কোনও ধরনের চিন্তা করতেই রাজি নই। গত এক বছরে আমার বলে দেওয়া তিনটে চাকরির একটাতেও তুই জয়েন করিসনি। গো টু হেল।’
এই উত্তর পাওয়ার পর আমি নিশ্চিত হই। এই গালির অর্থ পরদিনই টাকা চলে আসা। ‘বন্ধু’ এমনই হয়। তারা ভালোবাসার কথা গালি দিয়ে বলে।
যাইহোক, লেখালিখির এই বিদ্যে দিয়ে আমাকে কবি সাহিত্যিক বলা যায়? কখনওই না। এরপরেও পুঁটিকুমার, ওরা নাছোড়বান্দা। বাধ্য হয়ে নামকরণের দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিতে হয়েছে।
যেহেতু সকলেই রেস্টুরেন্টের কর্মী তাই আমার নামও আনাজপাতি, মাছ, ডাল, তরিতরকারির মধ্যে ঘোরাফেরা করে। তবে নামকরণে কাউকে ছোটো করার ব্যাপার নেই। কেউ যাতে দুঃখ না পায় তার জন্য শ্রী, শ্রীমান, কুমার, মহাশয়, মাননীয় যুক্ত করে দিই। কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথের ‘নাথ’, অতুলপ্রসাদের ‘প্রসাদ’, শরৎচন্দ্রের ‘চন্দ্র’ও লাগাই। যেমন এখানকার হেড রাঁধুনির নাম দিয়েছি লংকা মহাশয়। যোগানদার শ্রীমান উচ্ছে। একজন বেয়ারা পটলনাথ, আর-একজন, মুসুর প্রসাদ। একই ভাবে কান্তি নাম পেয়েছে পুঁটিমাছের। পুঁটিকুমার।
পুঁটিকুমার আবার নাক টানল। মাথা নামিয়ে খেলেও এবার আমার কানে লাগল। এতো ঠিক সর্দি ধরনের নাক টানা নয়।
গত তিন বছর ধরে আমি এই ‘ভাত ডাল’ রেস্টুরেন্টের কাস্টমার। বেশ কয়েকবার রেস্টুরেন্টের মালিক বদলেছে। আমি বদলাইনি। আমার হল বাই মান্থলি সিস্টেম। দু’মাস অন্তর বিল মেটাই। দু’মাস অন্তর খাওয়ার বিল মেটানোর ব্যবস্থা ভূ-ভারতে আর কোথাও আছে বলে জানা নেই। পুরোনো মালিককে এই সিস্টেমে রাজি করিয়েছিলাম। এখন এসেছে অভয়পদবাবু। বয়স্ক মানুষ। নাকের ওপর চশমা পরেন। চশমার ফ্রেম গোল এবং সোনালি। ডাঁটি তামার। একপাশে লাল রঙের সুতো ঝুলছে। সেটা টেবিল ফ্যানের বাতাসে ফর্ফর করে ওড়ে। এই সুতো চশমার, না বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা বলতে পারব না। অনেক সময় চাদর টাদর থেকে চশমার খোঁচায় সুতো আটকে থাকে। আর খোলা হয় না। নতুন মালিকের চরিত্র হল তিনি সারাক্ষণ একটা ‘মালিক, মালিক’ ভঙ্গির মধ্যে থাকবার চেষ্টা করেন। হাবেভাবে অহংবোধের মতো মালিকবোধ। সম্ভবত এটাই ওর প্রথম ব্যাবসা। মালিক হয়ে তিনি গর্বিত। মানুষটাকে আমি এড়িয়ে চলি। সেদিন ধরা পড়ে গেলাম।
আমি খাওয়া শেষ করে ক্যাশ কাউন্টার থেকে মৌরি তুলতে গিয়েছিলাম। অভয়পদবাবু এক গাল হেসে বললেন, ‘বসুন সাগরবাবু। আছেন কেমন?’
প্রমাদ গুনলাম। লক্ষ্য করে দেখেছি, যারা আমাকে খাতির যত্ন করে বসতে বলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আমাকে ধমক দেয়, বিপদে ফেলে। এটা প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতি এক একজনকে এক একটা বিষয়ের জন্য তৈরি করেছে। কাউকে লাথি ঝাঁটার জন্য তৈরি করেছে কাউকে বসিয়ে জল-বাতাসা খাইয়ে যত্নের জন্য তৈরি করেছে। লাথি ঝাঁটার মানুষকে জল-বাতাসা দিয়ে যত্ন করলে প্রকৃতির প্রেস্টিজে লাগে। সে প্রথমে চুপ করে থাকে। নিয়মের বাইরে খেলতে দেয়। কিন্তু কিছুটা পরেই প্রতিবাদ করে। আমার বেলাতেও তাই হয়। খাতিরের পরই গলাধাক্বা।
চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, ‘আমি ভালোই আছি। আপনি?’
অভয়পদবাবু চোখের চশমা নাকের ওপর আরও খানিকটা নামিয়ে অন্যমনস্ক গলায় বললেন, ‘ভালো তো ছিলাম ভাই, খানিক আগে থেকে বিগড়ে গেছি।’
আমি সহানুভূতির গলায় বললাম, ‘কেন? হলটা কী?’
ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘মালিক হিসেবে এখানকার নতুন দায়িত্ব পেয়েছি। বোঝেনই তো মালিকের দায়িত্ব কত কঠিন। মালিক না হলে সবদিকে নজর রাখার দরকার নেই, কিন্তু মালিক হয়ে গেলে আপনি খতম, তখন সবদিকে নজর দিতে হবে। এখন সব আমার। এই দোকান আমার, চেয়ার টেবিল আমার, কর্মচারীরা আমার, হিসেব খাতা আমার, লাভ লোকসান আমার। সবের ওপর শুধু আমার দখলদারি। ঠিক কিনা?’
আমি সবিনয় বললাম, ‘ঠিকই স্যার।’
অভয়পদবাবুকে ‘স্যার’ সম্বোধনের কারণ ধারবাকি। এ ব্যাপারে আমি কোনও ঝুঁকি নিই না।
অভয়পদবাবু আমার সম্মতি চাইলেন বটে, কিন্তু পেয়ে খুশি হলেন বলে মনে হল না। একই রকম বিরক্ত গলায় বললেন, ‘সেই নজর দিতে গিয়েই চমকে উঠেছি। হিসেবের খাতা ঘাঁটতে গিয়ে দেখি আপনার নামের মাসে লেখা দ্বিমাসিক। সাগরবাবু, দু’মাসের ধার বলে তো আমি কখনও কিছু শুনিনি। ধার খুব বেশি হলে একদিন, দুদিন। বড়োজোর হপ্তাখানেক। খাবার রেস্টুরেন্ট কোনও মুদিখানা নয় যে সেখানে মাসকাবারি খাতা থাকবে। ধারবাকি নিয়ে এসব কী চলছে! এতো ব্যাবসা লাটে উঠবে! মালিক হিসেবে আমি কি তা মেনে নিতে পারি?’
যা আঁচ করেছিলাম তাই ঘটল। বিপদ শুরু হয়ে গেল। নিজেকে সামলে হাসলাম। এই লোককে গুলিয়ে দিতে হবে। আমার ধারবাকির সিস্টেম বন্ধ হলে জলে পড়ব। না খেয়ে থাকতে হবে। বললাম, ‘কী যে বলেন স্যার ধারবাকিতে কখনও ব্যাবসা লাটে ওঠে! ধার বাকিই তো এখন ব্যাবসা। যত ধার তত লাভ। ধার শোধের কত নতুন নতুন প্যাটার্ন বেরিয়েছে। মান্থলি, বাই মান্থলি, হাফ ইয়ারলি, ইয়ারলি। ব্যাংক আর ক্রেডিট কার্ডগুলো মাথায় ঝুড়ি নিয়ে ধার নেবেন গো, ধার নেবেন গো বলে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের ধার শোধের ব্যবস্থাপনা শুনলে মাথা ঘুরে যাবে স্যার। কোনও, কোনও স্কিমে আবার ধার নিয়ে শোধ দিতেও হয় না। শুধু নিলেই হয়।’
নতুন মালিক আমার চোখের দিকে পলকহীন তাকিয়ে রইলেন। এই তাকানো যেমন ভালো তেমন আবার বিপজ্জনকও। পলকহীন চোখে মানুষ যেমন ভালোবাসার কথা বলে, তেমন আবার খুনও করতে পারে। রেস্টুরেন্টের মালিক নিশ্চই আমাকে ভালোবাসার কথা বলবে না।
‘সাগরবাবু, আমি ব্যাংক নই, ক্রেডিট কার্ডও নই। সামান্য ভাত-ডাল বেচে খাই। আমি এই ধারবাকির ব্যাবসা আর করব না বলে স্থির করেছি। এবার আপনার সিদ্ধান্ত। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দুদিন ভাববার সময় নিন। আচ্ছা, দুদিন নয়, তিনদিনই সময় দিলাম। আপনি পুরোনো লোক। এখানে যদি খেতে হয়, তিনদিন পরেই টাকাপয়সা যা বাকি আছে মিটিয়ে দেবেন। তারপর আমরা রোজকার রোজ হিসেবে যাব। ফ্যালো কড়ি খাও তেল সিস্টেম। খাও তেল কেন বুঝতে পারলেন? খাবার দোকান বলে। আমার এই অনুরোধ কি মনে থাকবে সাগরবাবু?’
আমি হাসলাম। চিন্তায় পড়ে গেছি বুঝতে দিলে চলবে না। তিনটে দিন তো চলবে। তারপর একটা কিছু ভাবা যাবে। আমি মাথা নেড়ে বললাম, ‘খুব মনে থাকবে।’
অভয়পদবাবু ঠোঁটের কোণায় মুচকি হাসলেন। গোল চশমা নিজেই খানিকটা ঝুলিয়ে নিয়ে বললেন, ‘না থাকবে না। ভুলে যাবেন। কঠিন কথা মানুষ সহজে মনে রাখতে চায় না। ধারবাকি শোধের কথা তো একেবারেই না। মালিক হলে জানতেন। সেই কারণে আমি একটা পথ ভেবেছি।’
আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘পথ! কী পথ? পুলিশে দেবেন?’
অভয়পদবাবু হাসলেন। গোল চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে বললেন, ‘ছি ছি ও কী বলছেন! পুলিশে ধরিয়ে দিলে আপনি তো ফুড়ুত করে গারদে ঢুকে যাবেন সাগরবাবু। তাতে আমার লাভ কী হবে? গারদ থেকে আপনি কি আমার ধার শোধ করতে পারবেন? পারবেন না। যদি চেষ্টাও করেন, মাঝপথে পুলিশ কমিশন খাবে।’
আমি হালকা ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, ‘তবে কি মারধোর ভাবছেন?’
‘না, আপনার মতো মানুষকে মেরে লাভ নেই। মার তো দূরের কথা। নিংড়োলেও টাকাপয়সা পড়বে না। আমার সব খোঁজ খবর নেওয়া হয়ে গেছে সাগরবাবু। আপনি হলেন ব্যাড ফর এভরিথিং ধরনের মানুষ। মারধোরের জন্যও ব্যাড। গালমন্দের জন্যও ব্যাড। আমি ছেলেদের বলে দিয়েছি, কাল থেকে আপনার ওপর ধাপে ধাপে অ্যাকশন শুরু হবে। কারণ আপনি আমাদের পুরোনো খদ্দের। ব্যাবসা যদি লক্ষ্মী হয়, পুরোনো খদ্দের তার বাহন। প্যাঁচা। তাই পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা। আপনার খাবার মেনু থেকে একটা একটা করে আইটেম স্টপ করতে বলেছি। বড়ো কোনও আইটেম দিয়ে শুরু করব না। শুরু হবে ছোটো খাটো কিছু দিয়ে। ধীরে ধীরে ‘বড়ো’তে যাব। কেমন হবে?’
আমার চোখ কপালে। এই মানুষ তো বিরাট খেলোয়াড়। খেলা চট করে বুঝতে দেয় না। আমি বললাম, ‘ঠিক ধরতে পারলাম না।’
‘পারবেন। ব্যবস্থা শুরু হলেই ধরতে পারবেন। ভালো চিকিৎসারই এই নিয়ম। চট করে ধরা যায় না। ধীরে ধীরে যায়। কাল থেকে ভাতের পাতে আপনার জন্য লেবু দেওয়া বন্ধ করতে বলেছি। লেবু বড়ো কিছু না। একটা ইঙ্গিত। তিনদিন পর বন্ধ হবে নুন। সল্ট। লেবু, নুনের পর আসবে মাছের ঝোল। দেন ডাল। তারপর সবজি। ধার না মেটালেও ভাত চলবে কয়েকদিন। ওনলি ভাত। আমরা কাউকে ভাতে মারতে চাই না। তবে এরপরেও যদি টাকা দেবার কথা ভুলে যান সাগরবাবু, আমাদের কিছু করার থাকবে না। বাধ্য হয়ে ভাতটুকুও বন্ধ করে দিতে হবে।’
আমি অভিভূত। আমি চমৎকৃত। ধার আদায়ের এই অভিনব পদ্ধতি আমাকে মুগ্ধ করল। বললাম, ‘আচ্ছা, ভাত বন্ধ হলে কি আমি খালি থালা নিয়ে বসতে পারব?’
‘আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?’
আমি মুচকি হেসে আড়মোড়া ভাঙলাম। চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললাম, ‘স্যার, আপনার চশমাটা কি ইংরেজ আমলের? মনে হচ্ছে, চার্লস টেগারের ফটোতে এরকম একটা চশমা দেখেছিলাম।’
আমার ওপর ধাপে ধাপে অ্যাকশন শুরু হয়েছে। আজ তৃতীয় দিন। ভাতের পাতে লেবু বন্ধ।
আমি থালা সামনে টানলাম। থালার ওপর ঢিবি করা ভাত। ভাতের গা ঘেঁষে দুটো বাটি। তাতে ডাল আর মাছের ঝোল। মাছের ঝোল নয়, মাছের জল। বাটির দিকে তাকালে মনে হবে, কিছুক্ষণের মধ্যে চকোলেট সাইজের পোনা মাছের টুকরো প্রাণ পাবে এবং বাটির জলে মহানন্দে সাঁতার কাটবে। আমায় যদি ছিপ দেওয়া হয়, আমি বাটিতে সেই ছিপ ফেলে পোনা মাছের টুকরো শিকার করব। থালার কোণায় নুন, ভাতের আড়াল থেকে উঁকি মারছে টসটসা লেবুর টুকরো। পাতিলেবু। মালিকের ব্যবস্থা অনুযায়ী লেবু আমার প্রাপ্য নয়। পুঁটিকুমার স্মাগল করে দিয়েছে। রান্নাঘর থেকে হাতসাফাই। গতকাল আমি আপত্তি করেছিলাম।
‘পুঁটিকুমার কাজটা ঠিক হচ্ছে না।’
পুঁটিকুমার নাক টেনে বলল, ‘কোন কাজটা?’
‘এই যে তুই আমাকে লেবু চুরি করে দিস এই কাজটা। ধার মেটাতে পারিনি বলে তো আমার লেবু বন্ধ থাকার কথা। আমি তো আর লেবুর জন্য এনটাইটেলড্ নই। এনটাইটেলড্ মানে জানিস? এনটাইটেলড্ মানে হল…।’
পুঁটিকুমার আমাকে থামিয়ে ধমক দেওয়ার ঢঙে বলল, ‘ইংরাজি শেখাবেন না। আমি লেবু চুরি করি না। চোরাপথে আপনার থালায় চালান করি।’
এই কথায় আমি থ’ মেরে যাই। বলি, ‘চোরাপথে চালান করিস মানে!’
‘তরিতরকারি কাটাকুটির পর পাতিলেবু আর পাঁচটা আনাজের খোসামোসার সঙ্গে দরজা দিয়ে রান্নাঘরের বাইরে চলে যায়। একটু পরেই আবার হাত ঘুরে জানলা দিয়ে ফিরে আসে।’
আমি চমকে উঠি। এতো রীতিমতো স্মাগলিং! আমার জন্য এরা এতটা ভাবে! আমার পুঁটিকুমার আবার নাক টানল। এই আওয়াজ আমার কেমন যেন ঠেকল! অন্যরকম। ঠিক সর্দির মতো তো নয়! আমি ডাল মাখা ভাতে লেবু কচলাতে গিয়ে থমকে গেলাম। মুখ তুললাম। হাফ প্যান্ট, ছেঁড়া স্যান্ডো গেঞ্জি পরে আমার টেবিলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সর্দিকুমার। সে কাঁদছে।
আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘কীরে কাঁদছিস নাকি?’
পুঁটিকুমার উত্তর না দিয়ে নাক টানল। আমি বললাম, ‘কীরে কেউ মেরেছে? মালিক? অন্য কেউ?’
পুঁটিকুমার দু’পাশে মাথা নাড়াল।
‘তাহলে!’
পুঁটিকুমার ছেঁড়া স্যান্ডো গেঞ্জির ভেতর থেকে একটা ঘামে ভেজা পোস্ট-কার্ড বের করল। এগিয়ে দিল আমার দিকে। পোস্ট-কার্ডে মেয়েলি হাতে মাত্র একটা লাইন লেখা–
‘ভাই, আমি ঠিক করেছি, বিষ খাব। আমার দিব্যি একথা তুই কাউকে জানাবি না। মা-বাবা কাউকে না। ইতি তোর প্রাণের দিদি।’
মেয়েলি হলেও হাতের লেখা সুন্দর এবং একটা বানানও ভুল নেই।
আমি আর পুঁটিকুমার বসে আছি ফুটপাথের ধারে। একটা চকচকে শহিদবেদির ওপর। পুঁটিকুমার পা দোলাচ্ছে। তার পা দোলানোর কায়দা অদ্ভুত। বসে বসে লেফ্ট রাইট। প্রথমে বাঁ, পরে ডান, শেষে ডান-বাঁ দুটো একসঙ্গে।
কলকাতা শহরে শহিদবেদির চেহারা বদলে গেছে। আগে হতো কালো, লম্বাটে। আখাম্বা দাঁড়িয়ে থাকত। গায়ে সাদা মার্বেল পাথরে খোদাই থাকত ‘শহিদ’-এর নাম। এখন কালো রং উঠে গেছে। বিভিন্ন রঙের মোজাইক দিয়ে মোড়া বেদিতে কারুকার্য এসেছে। বেদির আকারও বদলেছে। লম্বার জায়গায় হয়েছে চওড়া। চৌবাচ্চা ধরনের। চৌবাচ্চা মাটি দিয়ে ভর্তি। তাতে ফুলের গাছ। নেতারা যেদিন বেদি ‘উদ্বোধন’ করতে আসেন সেদিন ফুল শুদ্ধু গাছ এনে লাগিয়ে দেওয়া হয়। সেই গাছ কিছুদিনের মধ্যে ভ্যানিশ। হয় গরু ছাগল খায়, নয় তো জলের অভাবে শুকিয়ে মরে। সবথেকে বড়ো কথা, শহিদবেদিতে এখন আর শহিদের নাম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয় না। ছোটো করে কোথাও একটা লেখা হয়। চোখে পড়তে পারে, আবার নাও পারে। অসুবিধে নেই। যিনি শহিদ হয়েছেন তার থেকে বেদি যিনি ‘উদ্বোধন’ করেন সেই নেতার নাম থাকে বড়ো আকারে। ঠিকই হয়। মরে যাওয়া মানুষের দাম কী? কিছুই না।
এই বেদিরও অবস্থা তাই। শহিদের নাম বোঝা যাচ্ছে না। পাথরের লেখা ঘষে গেছে। শুধু পড়া যাচ্ছে–
‘তিনি ছিলেন নারী মুক্তির প্রজ্জ্বলিত শিখা…।’
আমি সহজ ভাবে বললাম, ‘তোর দিদির নাম কী?’
পুঁটিকুমার নাক টানছে, কিন্তু কান্নার নাক টানা নয়। তাকে নিয়ে আমি যে বেড়াতে বেরিয়েছি, এতে সে খুশি। কান্না বন্ধ হয়ে গেছে। ভাত ডালের দোকানে বিকেলের দিকে ঘণ্টা খানেকের ছুটি। নতুন মালিকের নিয়ম। আমার কর্মচারীকে আমি ছুটি দেব, কার কী?
‘দিদির নাম বিন্তি।’
‘বাঃ, ভাইয়ের নাম কান্তি, বোনের নাম বিন্তি। ভারি সুন্দর অন্তমিল আছে। আমি যদি ছড়া লিখতে পারতাম তাহলে লিখতাম কান্তি বিন্তি ভাই বোনযদুজনেরই একটা মন।’
পুঁটিকুমার বলল, ‘সাগরদা, তুমি আমার দিদির একটা নাম দাও।’
আমি অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, ‘তা কী করে হবে! আমি তো শুধু খাওয়ার দোকানের লোকদের নাম দিই। তোর দিদি তো আর সেখানে কাজ করে না।’
পুঁটিকুমার বলল, ‘না করলেও দাও। দিদি খুব মজা পাবে।’
আমি একটু ভেবে বললাম, ‘সে না হয় দেওয়া যাবে, কিন্তু পুঁটিকুমার, তোমার দিদি নাম নিয়ে করবেটা কী? সে তো বিষ খেতে চায়। বিষ খেলেই ফিনিশ।’
পুঁটিকুমার চুপ করে রইল। আমিও চুপ করে রইলাম। যদি বেশি উৎসাহ দেখাই এই ছেলে গুটিয়ে যেতে পারে। তারওপর চিঠিতে দিদি ‘দিব্যি’ কেটে রেখেছে। তার আত্মহত্যার পরিকল্পনা যেন ফাঁস না হয়। আমরা যতই হাইফাই জীবনে ঢুকি, আমেরিকা, লন্ডন করি, ভাইবোনের এইসব দিব্যি-টিব্যি খুব সিরিয়াস ব্যাপার। লেখাপড়া করলে দিব্যির কথা মুখে বলতে লজ্জা করে, মনে মনে বলে। মুখেও বলে। আমি এক বোনকে চিনি, বিয়ের পর মিশর চলে গেছে। কেমিষ্ট্রিতে তুখোড় ছাত্রী। মমির ওপর গবেষণা করছে। মৃতদেহ মমি করে রাখতে কোন ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়েছিল তাই নিয়ে গবেষণা। নিউইয়র্কের ‘পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার’ নামের অতি বিখ্যাত সায়েন্স জার্নালে এই মেয়ের লেখা ফটো দিয়ে বেরিয়েছে। আমি শুনেছি, কিছুদিন আগে এই মেয়ে তার হরিদেবপুরের ভাইকে ফোন করে বলেছে– ‘এবার ভাইফোঁটায় তোর কাছে যাবই যাব। কেউ ঠেকাতে পারবে না। ফ্যারাওয়ের দিব্যি কাটছি।’
পুঁটিকুমার বলল, ‘সাগরদা, আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করছে।’
আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম, ‘আমারও করছে। চল দুজনে মিলে আইসক্রিমওয়ালা খুঁজে বের করি। কতদিন কাঠি আইসক্রিম খাওয়া হয় না।’
পুঁটিকুমার বলল, ‘খুঁজতে যাব না। রাস্তা দিয়ে যখন যাবে ডেকে খাব।’
‘ঠিক বলেছিস। আইসক্রিম, ঝালমুড়ি, ঝুরিভাজা খুঁজে খেতে মজা নেই। টেস্ট কমে যায়। ডেকে খেতে মজা।’
পুঁটিকুমার একটু চুপ করে থেকে খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে বলল, ‘আমার দিদির কী হয়েছে তুমি কি শুনতে চাও?’
আমি উদাসীন ভাব দেখিয়ে বললাম, ‘বলতে পারিস, আবার না বলতেও পারিস। তোর ইচ্ছে।’
‘দিদি যে বারণ করেছে।’
‘আমার কী মনে হয় জানিস পুঁটিকুমার…।’ আমি চুপ করে গেলাম।
পুঁটিকুমার আমার দিকে ফিরে বলল, ‘কী মনে হয় সাগরদা?’
আমি ইচ্ছে করেই চুপ করেছিলাম। দেখছিলাম পুঁটিকুমার নিজে শোনার জন্য আগ্রহ দেখায় কিনা। বললাম, ‘সব বারণ শোনার জন্য নয়। এই যে তোদের অভয়পদবাবু, ধার শোধের জন্য আমার ওপর ধাপে ধাপে চাপ বাড়াচ্ছে, তোরা কি শুনছিস? তুই নিজেই তো লেবু পাচারের ব্যবস্থা করেছিস। বল, করিস নি?’ পুঁটিকুমার মাথা কাত করল। আমি বললাম, ‘আবার আর-একরকম বারণ আছে যার মানে উলটো ধরতে হয়। ধর, তুই রাগ করে বললি, আইসক্রিম খাব না। আমি তার মানে বুঝব, তুই আসলে আইসক্রিম খেতেই চাস। তেমন তোর দিদিও হয়তো তোকে বারণ করে উলটো কিছু বলতে চাইছে। নইলে এতক্ষণে চুপচাপ বিষ খেয়ে নিত। কষ্ট করে পোস্টকার্ড কিনে তোকে চিঠি লিখতে যাবে কেন?’
পুঁটিকুমার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি হাসলাম। ছেলেটাকে প্রভাবিত করতে পেরেছি। বিন্তি কেন বিষ খেতে চায় আমায় জানতে হবে। পুঁটিকুমারের কান্না আমি পছন্দ করিনি।
পুঁটিকুমার বিড়বিড় করে ঘটনা বলতে শুরু করল। আমি চুপ করে শুনতে থাকলাম। এর মাঝখানে আমরা আইসক্রিমওয়ালার দর্শন পেয়েছি। বাক্সগাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল ফুটপাথ ঘেঁষে। গাড়ির গায়ে রংচং দিয়ে লেখা ‘আইজ এণ্ড কোল্ট’ দুটো বানানই ভুল। এটাই ভালো। ভুল বানানের আইসক্রিম খেতে বেশি মজা। আমরা গোলাপি আর সবুজ রঙের দুটো কাঠি কিনেছি। পুঁটিকুমার সবুজ খাবে না। তার সবুজে নাকি অ্যালার্জি। গায়ে চিড়বিড় লাগে। সে নিয়েছে গোলাপি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল, গোলাপি নেওয়া সত্ত্বেও অল্পক্ষণের মধ্যেই পুঁটিকুমারের মুখের রং সবুজ হয়ে গেছে। আমার হয়েছে গোলাপি! অদ্ভুত না?
কান্তি-বিন্তিদের গ্রামের নাম মন্দিরতলা। পোস্ট অফিস বাণীপুর, জেলা উত্তর চব্বিশ পরগণা, থানা হাবড়া। কান্তির বয়স দশ, বিন্তির বয়েস পনেরো। হতদরিদ্র পরিবারে এই ছেলেমেয়েদুটি জন্মের পর থেকেই বাবা-মায়ের কাছে ‘শাকের আঁটি’। শাকের আঁটি শুনে ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই। বাবা-মায়ের নিজেদের জীবন চালানোই এতদিন ছিল বোঝার মতো। তারওপর ছেলমেয়েরা চাপলে তাকে শাকের আঁটি ছাড়া আর কী বলা হবে? সব মিলিয়ে বোঝার ওপর শাকের আঁটি।
এই সব পরিবারে শাকের আঁটি ঝেড়ে ফেলবার জন্য বাবা-মায়ের কসরতের শেষ থাকে না। নতুন কিছু নয়। আমাদের দেশে এমনটাই স্বাভাবিক। সবথেকে আদরের জনকে পেটের কারণে সবথেকে বড়ো দায় বলে মনে হয়। দায়মুক্ত হবার জন্য বাবা-মা অনায়াসে ছেলেমেয়ের গলা টিপে, বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে পারে। ফেলেও। পেট খুব কঠিন জিনিস। স্নেহ, মায়া, মমতা তার কাছে ধুলিকণাসম। ফুঃ দিয়ে উড়িয়ে দিতে মুহূর্তমাত্র।
মেয়েদেরবেলায় তো আরও সহজ। জন্মালেই আস্তাকুঁড়ে ফেলে দাও। খবরের কাগজে এইসব খবর আজকাল ছাপা হয় না। কত ছাপা হবে? মেয়ে মারা এখন জলভাত। গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে খবরের কাগজ কিনে পাবলিক জলভাত খেতে চায় না। কুড়মুড়ে জিনিস খেতে চায়। বিন্তিকে যে তার বাবা-মা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ে মুড়ে পুকুরের জলে ফেলে দেয়নি সেটাই অনেক। আমি ওই পরিবারের পয়সাকড়ির অবস্থা যা শুনলাম তাতে সেটাই উচিত ছিল। তবে কান্তি-বিন্তির বাবা-মা পুঁটিকুমারকে পাঠিয়ে দিয়েছে কলকাতায়। সেও একরকম জলে ফেলাই হল। হাবুডুবু খাও। পুঁটিকুমারও হাবুডুবু খাচ্ছে। সে হয়েছে বালক শ্রমিক। মেয়েকে কলকাতায় পাঠানো সম্ভব হয়নি। মেয়ে গ্রামে। ঘর সংসারে কাজ করে। বাবা-মা অপেক্ষা করে মেয়ে কবে বড়ো হবে। হলেই বিয়ে।
ঘটনা এই পর্যন্ত সাধারণেরও সাধারণ। বলার মতো নয়, শোনবার মতোও নয়। পাড়়াগাঁয়ে এমন মেয়ে আছে অজস্র। পিতা মাতার অনুপ্রেরণায় তারা আধপেটা খেয়ে না খেয়ে সেজেগুজে বিয়ের জন্য অপেক্ষা করছে। স্বপ্ন একটাই, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে আর চিন্তা থাকবে না। দু’বেলা পেট ভরবে। সন্ধের পর স্বামী কাজ সেরে বাড়ি ফিরলে গা ধুয়ে, কপালে বড়ো করে টিপ দিয়ে বসবে পাশে। গুজুরগুজুর করে গল্প হবে। সেই গল্পে যেমন সুখ থাকবে তেমন দুঃখও থাকবে। একসময় স্বামীর কাঁধে মেয়ে মাথা রাখবে আনমনে। কষ্টের সংসারও সুখের মনে হবে। নিজের মনে হবে।
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তেমনটা হয় না। শ্বশুরবাড়িতে আধপেটা খাবার জোটানোও কঠিন হয়ে পড়ে। তার থেকে অনেক সহজে গায়ে আগুন দেওয়ার জন্য কেরোসিন পাওয়া যায়। রান্নাঘর থেকে গোয়ালঘর, খাটের তলা থেকে সিঁড়িরতলা, শাশুড়ি-ননদ-বর যত্ন করে শিশি সাজিয়ে রাখে। নতুন বউয়ের যেন অসুবিধে না হয়। হাত বাড়ালেই বন্ধুর মতো, হাত বাড়ালেই কেরোসিন। যাক সে আলাদা গল্প। আমরা বিন্তিতে ফিরি।
আর-পাঁচটা গরিব ঘরের মেয়ের মতো আমাদের বিন্তিরও বিয়ের অপেক্ষা চলতে লাগল। একই ঘটনা। হেরফের নেই। ঘটনায় হেরফের হল হঠাৎই। ঘর সংসারের কাজের ফাঁকে বিন্তি গিয়ে একদিন নাম লিখিয়ে এলও গ্রামের স্কুলে। এই ভয়ংকর খবর জানার পর মা চুলের মুঠি চেপে ধরল। বিন্তি বলল, ‘ওরা দুপুরে খেতে দেয়। পয়সাকড়ি কিছু লাগে না।’ বিন্তির মা আর আপত্তি করেনি। সংসারের একটা পাত তো কমল। মিড ডে মিলে বিন্তি কোনওদিন খিচুড়ি খায়, কোনওদিন ভাত, কোনওদিন আবার রুটি, আলুর দম। খায় আর এলোমেলো ভাবে স্কুল থেকে পাওয়া বই খাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। খাবার পেতে হলে হাতে বই লাগে। একসময় বিন্তি খেয়াল করল, বই নাড়াচাড়া করতে তার মজা লাগছে! দুনিয়ায় এত কিছু জানার আছে! রাতে ঘরে আলো নেই। তাই দিনেরবেলা সঙ্গে বই নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বিন্তি। ফাঁক পেলে খুলে বসে। ধীরে ধীরে স্কুলের দিদিমণিদের নজরে পড়ে। তারা বুঝতে পারে, এই মেয়ে লেখাপড়ায় ভালো। গড়পড়তা ভালো নয়, বেশি ভালো। এই মেয়ের মাথায় বুদ্ধি আছে। গড়পড়তা বুদ্ধি নয়, বেশি বুদ্ধি।
পরীক্ষায় বিন্তি ক্লাসের সবাইটে টপকে যেতে লাগল। এইভাবে ক্লাস টেন পর্যন্ত চলেছে। এরপরই শুরু হয়েছে গোলমাল। বিন্তির জন্য পাত্র পেয়েছে তার বাবা। পাত্র অতি ভালো। একই গ্রামে বাড়ি। মন্দিরতলা। শক্তপোক্ত চেহারা। পাকা কাজকর্ম নেই বটে কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। গভর্নমেন্টের একশো দিনের স্কিম চালু হলে কাজ জুটে যায়। পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ আছে। পার্টি থেকে কাজ পায়, তবে বাকি সময় ছেলে যে বাড়িতে বসে ল্যাজ নেড়ে থাকে, এমন নয়। রোজের ভাড়ায় ডাকাতি খাটে। যেমন ডাক পায়। দু-তিনদিন বাইরে বাইরে থাকে। মাঝেমধ্যে পুলিশ এসে ধরেও নিয়ে যায়। তবে রাখে না বেশিদিন। জেলখানায় অত চোর ডাকাত রাখবার জায়গা নেই। সব মিলিয়ে ছেলে রোজগেরে। ছেলের মা এবার লক্ষ্মীমন্ত বউ চায়।
বিন্তির বাবা-মা হাতে পাত্র তো নয়, চাঁদ পেয়েছে। এমন পাত্রের হাতে মেয়েকে তুলে দেওয়া বিরাট ভাগ্যের ব্যাপার। জামাই সাহসী না হলে চলে? আতুপুতু জামাই হল পাড়াগাঁয়ের ভাঙা স্কুলের ভাঙা মাস্টার। চোপ্ বললে প্যান্টে ইয়ে। বিন্তি বোকাটা লেখাপড়া শিখলে হয়তো ওই দিকেই চলে যাবে। ল্যাগব্যাগে একটা মাস্টার জুটিয়ে ভাঙা সংসার করবে। ডাকাত পাত্র তার থেকে ঢের ভালো। সে যদি দু-পাঁচ মাস জেলে থাকে তাতেই বা ক্ষতি কীসের? বাড়ি তো আর ফাঁকা থাকবে না। শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, ভাসুর সবাই থাকবে। ভয় কীসের?
বিন্তির বাবা-মা ফুল ভল্যুমে বিয়ের গোছগাছ শুরু করেছে। একমাত্র মেয়ের বিয়ে বলে কথা। তারা ভালো করেই দিতে চায়। যতটা সাধ্য ততটাই করবে। এমনকী পুঁটিকুমারকে পর্যন্ত খবর পাঠিয়েছে, মালিককে সে যেন ছুটির কথা বলে রাখে। পারে যদি মাইনের টাকা কিছু অ্যাডভান্স চায় যেন। পুঁটিকুমারও তৈরি হচ্ছিল। অভয়পদবাবুকে ছুটি এবং মাইনের কথা বলব বলব করছিল। এমন সময়েই বিপদ হল। বেঁকে বসল বিন্তি। বিন্তি তার বাবা-মাকে জানিয়েছে, বিয়ে করবে না সে। লেখাপড়া শিখবে। আরও পড়বে। স্কুল পাশ হবে। কলেজেও নাকি যেতে চায়! বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চেয়েছে গাধাটা। সরি, গাধা নয়, গাধি। তিনদিন হল বাবা-মা কঠিন মার দিয়ে মেয়েকে ঘরে আটকে রেখেছে। একেবারে বিয়ের পর ডাকাত বর এসে মুক্ত করবে। এর ফাঁকে বিন্তি তার স্কুলের কোন এক বন্ধুকে দিয়ে ভাইয়ের কাছে পোস্টকার্ড পাঠিয়েছে একটা। বিয়ে দিলে সে বিষ খাবে।
ঘটনা বলা শেষ করে পুঁটিকুমার নাক টানল। আমি মুখ না ঘুরিয়ে বললাম, ‘পুঁটিকুমার, তুই কি কাঁদছিস?’
‘না।’
‘গুড। পুরুষমানুষের কথায় কথায় কান্নাকাটি ভালো নয়। কান্নার ঠাকুর রাগ করেন। কান্নার ঠাকুরের নাম জানিস?’
‘না।’
আমি বললাম, ‘আমি জানি, এখন মনে পড়ছে না। মনে হয়, আইসক্রিম খেয়েছি বলে ঠান্ডায় বুদ্ধি জমে গেছে।’
পুঁটিকুমার বলল, ‘সাগরদা, দিদি কি সত্যি বিষ খাবে?’
আমি একটু ভেবে নির্লিপ্ত গলায় বললাম, ‘মনে হচ্ছে না। গাধারা কখনও বিষ খেয়েছে বলে শুনিনি। তোর দিদি অবশ্য গাধা নয়, গাধি। পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া গাধি।’
পুঁটিকুমার আমার দিকে ঘুরে কটমট করে তাকিয়ে বলল, ‘তুমি আমার দিদিকে গাধি বললে!’
‘তাছাড়া আর কী বলব? অমন সু-পাত্রকে বিয়ে না করে যে লেখাপড়া চালাতে চায়, তার মাথায় কোনও বুদ্ধি আছে বলে মনে করিস? ক’জনের কপালে ডাকাত বর জোটে? তুই সবাইকে বুক ঠুকে বলতে পারবি, আমার জামাইবাবু কে জানো…হু হু…যদি চাস জামাইবাবুকে ধরে এনে তোর মালিককে দুটো ধমকও খাওয়াতে পারিস। বেটার মালিক মালিক করা বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁরে, ওই ছেলে কি মাথায় ফেট্টি, কপালে টিপ, কানে জবাফুল গুঁজে বিয়ের পিঁড়িতে বসবে?’
পুঁটিকুমার একটু গুম মেরে থেকে বলল, ‘দিদির এখনও বিয়ের বয়স হয়নি।’
আমি চমকে উঠলাম। পুঁটিকুমার এসব জানল কী করে!
‘তোকে কে বলল?’
সন্ধে নামছে। সন্ধে নামবে শান্ত ভঙ্গিতে। আকাশের আলো আবার আকাশে ফিরে যাবে চুপিচুপি। গাছ ডালপাতা নামিয়ে বিশ্রামে যাবে নীরবে। ঘর হারানো পাখি ক্লান্ত ভঙ্গিতে উড়ে যাবে আরও ভুল পথে। ধানখেত, মাঠ, পথঘাট ও শাপলা দিঘির পাড় মুড়ি দেবে জোনাকি আঁকা আঁধার অথবা কুয়াশার ফুলছাপ কাঁথায়। সারাদিন পর চাঁদের আলোয় লম্বা ছায়া ফেলে হেঁটে যাবে মানুষ। হেঁটে যাবে প্রিয়জনের কাছে। মনে মনে বলবে, এবার তুমি। এবার তুমি। এবার তুমি। এই শান্ত স্নিগ্ধভাব বড়়ো মায়াবী লাগবে। ভালো লাগবে খুব। অথচ কলকাতায় সন্ধে নামে হই হই করে। চারপাশ ঝলসে ওঠে ঝলমলে আলোয়। চকচকে রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটতে থাকে। পাল্লা দিয়ে ছুটতে থাকে মানুষ। সেই দৌড় দেখলে ভয় লাগে।
পুঁটিকুমার বলল, ‘আমি জানি। আমি অনেক কিছুই জানি।রেস্টুরেন্টে টেবিল মুছি বলে কি কিছুই জানি না মনে করো? আঠেরো বছর বয়স না হলে বিয়ে ঠিক নয়। আমাদের দোকানে একদিন দুটো লোক এসব বলাবলি করছিল। তার মধ্যে একটা ছিল হোৎকা, অন্যটা চিমসে। চিমসেটা বোধহয় পুলিশের লোক। তবে গোঁফ মোটা। ডালের বাটিতে চুমুক দিতে গিয়ে গোঁফে ডাল লাগিয়ে ফেলল। হোৎকাটাকে এসব বলছিল।’
আমি বললাম, ‘কী বলছিল।’
‘বলছিল, মেলা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ কোরো না। তোমার মেয়ের বয়স কত? হোৎকা বলল সতেরো বছর তিন মাস। না না তিন মাস নয়, পাঁচ মাস। চিমসেটা এক ধমক দিয়ে বলল, মেয়ের বয়স জানো না? যাই হোক আঠেরো বছর তো হয়নি। আঠেরো বছরের আগে বিয়ে করা যায় না, বিয়ে করলে হাজতে থাকতে হয়। ছোকরাকে থানায় আনার আগে আমাকে একটা ফোন করে দিও। এমন ডান্ডা মারব…। হি হি।’
পুঁটিকুমারের হাসি দেখে খুব ভালোলাগল। বেটা জোর পেয়েছে, মজাও। কম বয়সে দিদির বিয়ে হলে সে যেন নিজেই ডান্ডা মারবে। কাকে মারবে এইটা খালি বুঝতে পারছে না। আমি খানিকটা দমিয়ে দেবার জন্য বললাম, ‘ওসব আইনকানুন সবার জন্য নয়। আইন একেক জনের জন্য একেকরকম। তোদের মতো গরিবদের একরকম, আবার ওই যে দেখছিস গাড়ি নিয়ে সুঁই করে চলে গেল, তার জন্য আর-একরকম। এত জানিস এই আসল কথাটাও জেনে রাখ। তোর দিদির কম বয়েসে বিয়ে হলে কেউ ডান্ডা খাবে না। তাছাড়া বিয়ে না হলে তোর দিদি খাবে কী? তখনও তো বিষ খেতে হবে। বিষ আর বিয়ের মধ্যে বিয়েটাই তো ভালো অপশন। অপশন বুঝিস? অপশন হল পথ। তোর দিদির উচিত বিয়ের পথটাই বেছে নেওয়া।’
আমার কথায় পুঁটিকুমারের ভুরু কুঁচকে গেল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, ‘দিদি লেখাপড়া করতে চায়।’
আমি শহিদবেদি থেকে নেমে পড়লাম। এবার ফিরতে হবে। এই ছেলে মূল জায়গায় ঢুকে পড়েছে। তাহলে আর একটু বাজিয়ে দেখা যাক।
‘পুঁটিকুমারবাবু, ওটাও গরিব মানুষদের জন্য নয়। দেখিস না, গরিব মানুষ লেখাপড়া শিখলে কেমন ঢাক পেটানো হয়। টিভিতে দেখানো হয়, কাগজে ছাপা হয়। অভাবী অথচ মেধাবী। ভাবটা এমন যেন অভাবে থাকলে জ্ঞানগম্যি হওয়াটা বিরাট কোনও ব্যাপার।’
আমার এই লেকচার পুঁটিকুমার গা করল না। মনে হয় বুঝতে পারেনি। বললাম, ‘তোর দিদির লেখাপড়া শিখে হবেটা কী বল তো? বরং স্কুল-টুল পার হয়ে গেলে বিপদ হবে। তখন আর বিয়ের জন্য ছেলে পাওয়া যাবে না। তার থেকে এই ভালো। চল, এবার ফিরবি। অভয়পদবাবু তোকে না দেখলে খেঁচামেচি লাগাবে। মালিক বলে কথা।’
পুঁটিকুমার চুপ করে আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। সে নীল রঙের চেক একটা হাফ শার্ট পরেছে। তাকে বেশ দেখাচ্ছে। নাক টেনে বলল, ‘সাগরদা, তুমি আমাকে কী করতে বলো।’
‘দিদিকে, চিঠি লেখ। হয় বাবা-মায়ের কথা মতো বিয়ে করো, নয়তো বিষ খাও।’
পুঁটিকুমার থমকে দাঁড়াল। আমি বললাম, ‘কী হল?’
‘আমি দিদিকে বিষ খেতে বলব! সাগরদা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?’
আমি পুঁটিকুমারের কাঁধে হাত রেখে বললাম, ‘মাথা খারাপ হবে কেন! বিন্তি তো নিজেই বিষ খেতে চেয়েছে। আমার কী দোষ?’
পুঁটিকুমার মাথা নামিয়ে ব্যথিত গলায় বলল, ‘ছি ছি।’
আমি মনে মনে হাসলাম। মুখে চিন্তার ভাব নিয়ে বললাম, ‘তুই কী চাস?’
পুঁটিকুমার হনহন করে হাঁটতে শুরু করল। বলল, ‘আমি কিছু চাই না। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতেও চাই না।’
আমি এই রাগটাই চাইছিলাম। এই ছেলের বয়স যতই কম হোক, ভেতরে আগুন আছে। আমাকে লেবু পাচার করে দেবার ঘটনাতেই আঁচ পেয়েছিলাম। যত কথা বলছি, ছেলের ভেতরের আগুন সম্পর্কে নিশ্চিত হচ্ছি। আমার একটাই দায়িত্ব এই আগুন আরও বাড়িয়ে দেওয়া।
‘আচ্ছা, পুঁটিকুমার একটা কাজ করলে কেমন হয়?’
পুঁটিকুমার এতটাই রেগে আছে সে আমার দিকে তাকাল না।
‘তুই নিজে গিয়ে যদি বিন্তিকে খানিকটা বিষ পৌঁছে দিয়ে আসিস?’
পুঁটিকুমার আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। চারপাশের দোকানের আলো তার চোখে এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে, জ্বলছে। আমি খানিকটা থতমত খাওয়ার ভঙ্গিতে বললাম, ‘না মানে, তুই তো জানিস কলকাতায় তোদের গ্রামের থেকে অনেক ভালো বিষ পাওয়া যাবে। টক করে খেয়ে ফট করে মরে যাওয়া যায়। তাছাড়া রকমারিও পাবি। বেছেবুছে কিনতে পারবি। শুনেছি শিয়ালদার কোনও দোকানে যেন বিষের হোলসেল হয়। হোলসেল জানিস? পাইকারি। দুপুরের দিকে কাজ কম থাকলে চলে যাবি না হয়। একেকটা কারণে একেকরকম বিষ কাজ করে। খেতে না পাওয়ার কারণে মরতে চাইলে একরকম বিষ, শ্বশুরবাড়িতে মারধোর করলে একরকম বিষ, মা বকলে একরকম, পরীক্ষায় ফেল করলে অন্যরকম। আমার মনে হয় লেখাপড়া করতে না পেরে যেসব মেয়ে কষ্ট পায়, মরতে চায় তাদের জন্যও আলাদা জিনিস পাওয়া যাবে।’
আমি বলছি আর আড়চোখে পুঁটিকুমারের চোখের দিকে বারবার তাকাচ্ছি। চোখ জ্বলছে ধক্ধক্ করে। পুঁটিকুমার ঘন ঘন নাক টানছে। না সর্দি, না কান্না। এখন সে নাক টানছে রাগে। বাঃ রাগেও নাক টানা যায়! জানতাম না তো। পুঁটিকুমার তাহলে এখন রাগকুমার। আমি এই রাগ পাত্তা দিলাম না। মুচকি হেসে বললাম, ‘যদি বলিস, ওই দোকানে আমিও তোকে নিয়ে যেতে পারি। চল কালই নিয়ে যাব।’
পুঁটিকুমার আমার দিকে সরু চোখে তাকাল। তারপর হাফপ্যান্টের দুটো পকেট হাতড়িয়ে খানিকটা খুচরো পয়সা বের করল। এগিয়ে ধরে বলল, ‘এটা ধরেন।’
আমি নার্ভাস হেসে বললাম, ‘কী এটা!’
জবাব না দিয়ে পুঁটিকুমার গোঁ দেখিয়ে মুখ নামিয়ে থাকল। আমি আবার বললাম, ‘আরে বাপু, বলবি তো পয়সাগুলো কেন দিচ্ছিস! আচ্ছা ফ্যাচাং তো।’
পুঁটিকুমার নাক টেনে বলল, ‘আপনার আইসক্রিমের দাম। আপনার পয়সায় আইসক্রিম খাওয়াটাই আমার ভুল হয়েছে। গুনে দেখেন, কম পড়লে কাল যখন দোকানে খেতে আসবেন দিয়ে দেব।’
আমি খুশি হয়ে পয়সা গুনতে শুরু করলাম। আমি পেরেছি। বারো বছরের এই বালকের ভেতর যে-ধিকধিকি আগুন জ্বলছিল, তাকে দাউ দাউ করে দিতে পেরেছি। আমার শুধু ছোট্ট একটা কাজ বাকি রইল।
‘পুঁটিকুমার, আমি কি তোর সঙ্গে যেতে পারি।’
‘না।’
পুঁটিকুমার হন হন করে হেঁটে এগিয়ে গেল। পিছন থেকে আমার মনে হল, বেটা হাঁটছে না। ঘোড়ায় চেপে ছুটছে। আমি হলফ করে বলতে পারি, সে যাচ্ছে মন্দিরতলা। তার দিদির কাছে।
‘রেবা, কেমন আছ?’
‘তুমি আবার ফোন করেছ!’
‘রাগ করছ কেন?’
‘তোমার ওপর আমার যে রাগ বা খুশি কোনওটাই হয় না, তা তুমি ভালো করেই জানো।’
‘বাঃ তোমার অবস্থা তো দেখছি শঙ্খ ঘোষের কবিতার মতো রেবা। ওই যে কবিতাটা আছে না? কোনও গুপ্তঘর নেই। অজ্ঞাতবাসেও নিরাশ্রয়।য দেয়ালে দেয়ালে লেগে বারে বারে ফিরে আসে স্বর।’
রেবা চুপ করে রইল। সে এরকমই। মাঝে মাঝেই চুপ করে যায়। যখন কলকাতায় ছিল তখনও কথা বলতে বলতে থেমে যেত, অন্যমনস্ক হয়ে যেত। সম্ভবত যে বহু কারণে আমি তার প্রেমে পড়েছিলাম, তার একটা এই হঠাৎ থেমে যাওয়া স্বভাব। আজও তার এই স্বভাব। আর তাই আজও তাকে ভালোবাসি। আমার সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারেও সে হঠাৎ থেমে গেছে। আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ‘না’ শুনেছিল। শুনে ভেঙে পড়েনি। আমাকে দোষ দেয়নি মোটে। বরং খুশিই হয়েছিল।বলেছিল, ‘আমি জানতাম, তুমি না বলবে। সাগর তুমি বাঁধা পড়বার মানুষ নও। আর সেই কারণে তোমাকে আমি এত ভালোবাসি।’
রেবা তার রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার বাবার সঙ্গে লামডিং চলে গেছে। জঙ্গল আর কুয়াশা নিয়ে থাকে। বাবার তৈরি করা ফার্মে ম্যানেজারি করে। সেখানে দুঃস্থ, অসহায় মেয়েরা কাজ করে। ছোটো ছোটো পাহাড়ি ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলও খুলেছে। মাসে দু-মাসে আমায় ফোন করে, চিঠি লেখে। মাঝে মাঝে আবার স্বভাবমতো চুপ করে যায় দিনের পর দিন। আমি ফোন করলে কেটে দেয়। চিঠি পাঠালে ছিঁড়ে ফেলে দেয় কুচি কুচি করে।
কোনও কোনও ঝড়ের বিকেলে রেবার জন্য মন কেমন করে। গড়িয়াহাটার কংক্রিটে বোনা মোড়ে দাঁড়িয়ে শুনতে পাই কে যেন বলছে– আকাশতলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায় আয় আয় আয়য জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তাই– যাই যাই যাই।’ ইচ্ছে করে, ছুটে চলে যাই। আমি রেবাকে কয়েকবার বলেওছি।
‘আমি যদি তোমার কাছে যাই তুমি রাগ করবে? খুব মন কেমন করছে রেবা।’
রেবা গাঢ় গলায় বলে, ‘রাগ করব না। তবে তুমি এসো না। আমার জন্য তোমার মন কেমন, তোমার আসার থেকেও আমার কাছে অনেক বেশি দামি। প্লিজ, তুমি এসো না।’
রেবাকে ফোন করতে একবারেই ধরল। আসকারা দেওয়া গলায় বলল, ‘কবিতা না বলে, কেন ফোন করেছ বলো। শঙ্খ ঘোষ, জয় গোস্বামী শুনিয়ে আমাকে মুগ্ধ করতে পারবে না। ওই স্টেজ আমি পার করে এসেছি।’
‘তাহলে কি আমি অন্য কারও কবিতা শোনাব? আজকাল অনেকেই খুব সুন্দর কবিতা লিখছে। যদি বলো শোনাতে পারি। সেদিন কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে শুনলাম এদের নাকি শূন্য দশকের কবি বলা হয়।’
রেবা বলল, ‘তুমি আমাকে এইসব হাবিজাবি বলতে ফোন করেছ?’
আমি বললাম, ‘হ্যাঁ। তুমি ছাড়া আমার হাবিজাবি কে শুনবে?’
রেবা হেসে বলল, ‘আচ্ছা আমিই শুনব। দাঁড়াও এক কাপ কফি নিয়ে আসি। আজ এখানে খুব ঠান্ডা পড়েছে। কাল রাত থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।’
আমি হলফ করে বলতে পারি, কফি আনবার নাম করে আজকের মতো বিদায় নেবে রেবা। আমি সারাদিন মোবাইল কানে নিয়ে বসে থাকলেও তাকে পাব না। মোবাইল ছেড়ে যদি ল্যান্ড ফোনে ধরতে চেষ্টা করি তাতেও লাভ হবে না। ফোন বেজে যাবে সে ধরবে না। একাজ রেবা আগেও করেছে। পরে যখন জিজ্ঞেস করেছি বলেছে, ‘তোমার কথা খুব শুনতে ইচ্ছে করছিল। তাই ফোন রেখে পালিয়ে গেলাম। মনে হল, কথা শোনার থেকে কথা শোনবার ইচ্ছে অনেক বড়ো। কথা বারবার শোনা যায়, ইচ্ছে বারবার আসে না। ভালো করিনি?’
আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, ‘ভালো করেছ। ফিলজফি হিসেবে চমৎকার। রিয়েলিটির বদলে ইচ্ছে।’
তবে আজ ফিলজফি করলে চলবে না। আজ আমি সত্যি সত্যি কাজের জন্য ফোন করেছি। সুতরাং ওকে আটকাতে হবে।
‘দাঁড়াও রেবা, পরে কফি খাবে। জরুরি একটা দরকারে তোমাকে ফোন করেছি।’
রেবা একটু থমকাল। আমি প্রমাদ গুনলাম। এই রে, পুরো চুপ করে না যায়। হড়বড় করে বললাম, ‘একটা চোদ্দো পনেরো বছরের মেয়ে বিষ খেতে চলেছে…।’
রেবা এক মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে বলল, ‘কী হয়েছে? মেয়েটা কে?’
‘মেয়েটার নাম বিন্তি। চমৎকার মেয়ে। আমার ধারণা এই মেয়ে বিষ না খেয়ে যদি বেঁচে যায়, তাহলে একদিন তোমার বাবার মতো মস্ত বড়ো পুলিশ অফিসার হবে।’
রেবা অবাক গলায় বলল, ‘পুলিশ অফিসার! কেন পুলিশ অফিসার কেন?’
‘বুদ্ধি আর সাহস দুটোই এই মেয়ের আছে। সাময়িক ভাবে সেই সাহসে চিড় খেয়েছে। ঘাবড়ে গেছে বলতে পারো। ওর সাহস যদি ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে দেখতে হবে না, বিন্তি অনেক দূর যাবে।’
‘এবার ঘটনাটা বলো। আমি কী করতে পারি সেটা বলো।’
আমি সংক্ষেপে এবং দ্রুত কান্তি-বিন্তির ঘটনা বললাম। কীভাবে মেয়েটা লেখাপড়া শিখেছে, কীভাবে মেয়েটাকে বিয়ের জাঁতাকলে ফেলে পিষে মারবার প্ল্যান হয়েছে।
‘কদিনের জন্য তোমার ওখানে মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয় রেবা? লামডিং-এ থাকবে হপ্তাখানেক। কিছুদিন থাকার পর এদিকটা যখন শান্ত হবে, তখন না হয় ফিরিয়ে আনা গেল। হস্টেলে রেখে কোনও স্কুলটুলে যদি ভর্তি করে দেওয়া যায়। তমালের এক মামাতো না মাসতুতো বোন বারাসতে এরকম একটা স্কুল বানিয়েছে। গরিব মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর স্কুল।’
রেবা একটু ভেবে বলল, ‘আমার এখানে পাঠানো ঠিক হবে বলে মনে হয় না। মেয়ের বাবা-মা বা ভাবী বর কিডন্যাপিং আর পাচারের অভিযোগ করতে পারে। বলবে গ্রাম থেকে নাবালিকা অপহরণ করে পাচার করে দিয়েছে।’
এবার আমি হাসলাম। বললাম, ‘সেটা সম্ভব নয়। তাহলে ভাইয়ের বিরুদ্ধে দিদিকে অপহরণের মামলা করতে হবে। সেই কারণেই তো আমি নিজে গেলাম না। পুঁটিকুমারকে রাগিয়ে, তাতিয়ে পঠিয়ে দিচ্ছি। আমি জানি ও ঠিক দিদিকে নিয়ে চলে আসবে। আমি সঙ্গে গেলে এত সহজে হতো না। অনেক ঝামেলা করতে হতো।’
রেবা বিরক্ত হল। গলায় সামান্য ঝাঁঝ নিয়ে বলল, ‘কী ঝামেলা হতো? হলে হতো। ওই গ্রামে তোমার নিজের যাওয়া উচিত ছিল। তুমি যে এত ভীতু হয়ে গেছো আমি জানতাম না। এত বড়ো একটা অন্যায় হচ্ছে… একটা মেয়ে লেখাপড়া করতে চায়, অথচ বয়স হয়ে যাবার আগেই তাকে বাড়ি থেকে জোর করে বিয়ে দেবে? তোমার পুলিশে যাওয়া উচিত ছিল। বাবা-মায়ের নামে ডায়ারি করা উচিত ছিল।’
আমি একটু ভেবে, বানিয়ে হাই তোলার আওয়াজ করে বললাম, ‘ওসবে বড্ড পরিশ্রম রেবা।’
‘কী বলছ! পরিশ্রম? ছি ছি। এটা তুমি কী বলছ? একটা মেয়ে বিষ খেতে চলেছে, জেনেও তুমি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে।’
আমি মিথ্যে অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, ‘হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলাম কোথায়! পুঁটিকুমারকে যে উত্তেজিত করলাম।’
‘এসব তোমার ফাঁকিবাজির কথা। ওইটুকু ছেলেকে এরকম একটা সিরিয়াস বিষয়ে উত্তেজিত করে লাভ কী? আমি হলে নিজে চলে যেতাম।’
আমি মুখ দিয়ে তাচ্ছিল্যের আওয়াজ করে বললাম, ‘তারপর আমি গেলাম আর ওই মেয়ে বলল, আপনি কে? আপনি কি আমার বিয়ে দিচ্ছেন? নাকি আপনি আমায় বিয়ে করবেন? মেয়ে যদি পালটি খায়? আমার কী হতো একবার ভেবে দেখেছ?’
রেবা আর সহ্য করতে পারল না। এবার ধমকে উঠল।
‘স্টপ ইট। মেয়েদের সম্পর্কে এই ধরনের বিশ্রী কথা বলবে না। বিন্তি মত বদলাবে কেন? আজকাল প্রায়ই খবরের কাগজে বেরোয়, মেয়েরা রুখে দাঁড়িয়েছে। বিন্তিও তাই করত। সাপোর্ট পেলে রুখে দাঁড়াত।’
রেবার এই রাগ, এই তেজ আমার দারুণ লাগল। আরও খোঁচা মারলাম।
‘আমি সাপোর্ট দেবার কে? আমাকেই কেউ সাপোর্ট দেয় না।’
রেবা বলল, ‘চুপ কর তো, আমাকে ভাবতে দাও।’
আমার উদ্দেশ্য সফল। একজন দুঃখী মেয়ের ভাবনার দায়িত্ব একজন দুঃখী মেয়ে নিয়ে নিয়েছে। এর থেকে খুশির খবর আর কী আছে? এবার দুঃখে দুঃখে আনন্দ হবে।
আমি গলা নরম করে বললাম, ‘শান্ত হও রেবা। তুমি ঠিকই বলেছ, এই মেয়ের বাবা-মাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু তারপর? দুদিন খবরের কাগজে বিন্তির ছবিটবি না হয় বেরোবে। বাবা-মাকে জেলে পুরে সাহসিনী পুরস্কারও জুটে যেতে পারে। কিন্তু তারপর? সে কার কাছে থাকবে? কোথায় পড়বে? কীভাবে বড়ো হবে? একটা অলটারনেটিভ ব্যবস্থা করতে হবে না? আর একটা সত্যি কথা বলব, আমি বিন্তির বাবা-মায়ের কোনও দোষ দেখি না। হতদরিদ্র এই পরিবার মেয়ের বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে? দোষটা আমাদের সকলের। তাই দায়িত্ব আমাদের। তাৎক্ষণিক কোনও সমাধানে লাভ হবে না।’
রেবা মনে হয় আমার লেকচারে সামান্য শান্ত হল। বলল, ‘আজকাল এরকম তো হচ্ছে। মেয়েরাই প্রতিবাদ করছে।’
‘বললাম তো। এই মুহূর্তে বিন্তির প্রতিবাদ করার সাহস নেই। সে নিজে পুলিশের কাছে যেতে পারবে না। সেই কারণেই বিষ খাবার পরিকল্পনা করেছে। অন্তত ঘটনা শুনে আমার তো সেরকমই মনে হয়েছে। যদি বা এখন কিছু না করে, বিয়ের পর করবেই।’
রেবা একটু চুপ করে থেকে চিন্তিত গলায় বলল, ‘তুমি ওর ভাইকে পাঠালে কেন? ওইটুকু ছেলে কি পারবে?’
‘আমি তো পাঠাইনি। সে নিজেই যাবে। আমি পাঠালে না হয় একটা কথা ছিল। যে নিজের জোরে যুদ্ধে যায় তার পরাজিত হবার সম্ভবনা কম থাকে।’
কথা শেষ করে আমি হাসলাম। রেবা বলল, ‘আমার টেনশন হচ্ছে। মেয়েটা এর মধ্যে কিছু করে না বসে। এই বয়েসে ছেলেমেয়েরা খুব সেনসেটিভ হয়। মেয়েরা বিশেষ করে।’
আমি শেষ খোঁচাটা মারলাম। বললাম, ‘তুমি বিষ খাওয়ার কথা বলছ? অত চিন্তার কি আছে? খেলে খাবে। ধেড়ে মেয়ে। তাছাড়া বললাম তো, এখন না খেলে, পরে খাবে। আমাদের যতটুকু করবার করলাম। এর বাইরে যা ঘটবার তাই ঘটবে। আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই।’
রেবা ঝাঁঝিয়ে উঠল, ‘তুমি আবার কী করলে? কিছু তো করোনি। একটা এগারো-বারো বছরের ছেলেকে উসকে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছ। গ্রামের নাম কী, কোন থানা? দাঁড়াও কাগজ পেন নিয়ে এসে টুকি।’
আমি অবাক গলায় বললাম, ‘গ্রাম, থানার নাম জেনে কী করবে রেবা? তুমি যাবে?’
রেবা থমথমে গলায় বলল, ‘হ্যাঁ। যাব।’
রেবা কাগজ পেন আনতে গেল। আমি নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রেবা ফিরে আসবে। কাগজে গ্রামের নাম লিখে নেবে। সুদূর লামডিং-এ বসে সে মন্দিরতলার কান্তি- বিন্তিদের দুঃখের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। যে বহু কারণে রেবাকে এত ভালোবাসি তার একটা আগেই বলেছি। আর-একটা হল, অসহায়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া। এত ভালোবাসা কি শুধু মেয়েদেরই থাকে।
অভয়পদবাবু তার গোল চশমা নাকের ওপর আরও নামিয়ে বললেন, ‘আপনি সত্য বলছেন!’
আমি খনিকটা মউরি মুখে দিয়ে বললাম, ‘অবশ্যই সত্যি বলছি স্যার। আপনি খোঁজ নিন। আপনার পুঁটিকুমারকে ওরা ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখেছে।’
অভয়পদবাবুর সোজা হয়ে বসে বললেন, ‘এতবড়ো সাহস! আমার পুঁটিকুমারকে বেঁধে রেখেছে! ওরা কে বাঁধবার? যদি বাঁধবারই হয় আমি বাঁধব। কে ওরা বলুন তো সাগরবাবু। আমার কর্মচারীকে বাঁধছে! মারছে! হারামজাদাদের দাঁত ভেঙে দেব।’
আমি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বললাম, ‘যতদূর খবর পাচ্ছি, একটাঞ্জভাড়া খাটা ছেঁদো ডাকাত আর তার কিছু চেলাচামুণ্ডা এই ব্যাপারে জড়িয়ে আছে।’
অভয়পদবাবু গলায় হুংকার দিলেন, ‘ডাকাত! আমার কর্মচারীকে ডাকাত ঘরে বন্দি করে রাখে কোন সাহসে?’
আমি হাই তোলার ভান করে বললাম, ‘কোন সাহসে সে আপনি জানেন স্যার। আজকাল তো এমনই হয়। ভালো লোককে ডাকাত বন্দি করে রাখে, আর ডাকাতরা ট্যাং ট্যাং করে ঘুরে বেড়ায়। আপনার মতো ভদ্রলোকরা পাত্তাও পায় না। কালে কালে দেশটার পজিশন খুবই খারাপ দিকে যাচ্ছে। আপনার কি মনে হয় রসাতলে যেতে আর কত দেরি?’
আমার কথা শুনে অভয়পদবাবু মুখে ‘হুম্মম…’ শব্দে চাপা গর্জনের মতো করলেন।
খাওয়াদাওয়ার পর আমি একটা চান্স নিয়েছিলাম। ঢিল ছুড়েছিলাম বলা যায়। পুঁটিকুমারের মালিককে খেপিয়ে তুলতে পারলে কেমন হবে? খেপিয়ে যদি ঘটনায় জড়িয়ে নেওয়া যায়? ভেবেছিলাম, হবে না, তবু ভাবলাম, ট্রাই নিতে দোষ কী? কোনও দোষ নেই। মানুষের গোটা জীবনটাই তো ট্রাই, ট্রাই এবং ট্রাই। লেবু ছাড়া ডাল-ভাত খেতে খেতে প্ল্যান করছিলাম। এর আগেই অন্য কর্মচারীদের কাছ থেকে খবর নিয়ে নিয়েছি।ঞ্জপুঁটিকুমার দিদির বিয়ের নাম করে ছুটি নিয়ে গ্রামে চলে গেছে কাল রাতেই। যাবার আগে তার মুখ ছিল থমথমে। কে যেন আমার নাম করে তাকে কী একটা বলতে গিয়েছিল, পুঁটিকুমার তাকে বলেছে, খবরদার, ওই লোকের নাম তার সামনে যেন কেউ না করে। শুধু ভাত খেতে এলে পাচার করা লেবুর টুকরো যেন পাতে দেওয়া হয়। লেবুর টুকরো যেন বড়ো সাইজের হয়।
সেই লেবু মেখে ডাল-ভাত খেতে খেতে প্ল্যান ঠিক করে নিলাম। অভয়পদবাবুর মালিকানা বোধে টোকা মারতে হবে। মালিকানাবোধ একটা স্পর্শকাতর বিষয়। যারা মালিক তারাই কেবল বুঝতে পারে। খাওয়া শেষ করে হাসি মুখে নিয়ে অভয়পদবাবুর সামনে গিয়ে বসলাম। তারপর টকাস্…। ঢিলটা যে এত সহজে লেগে যাবে ভাবতে পারিনি। আসলে যাবতীয় লক্ষ্যভেদের এটাই নিয়ম। ফিফটি ফিফটি চান্স। অর্জুন যে মাছের চোখে তীর মেরেছিল তাও একই তত্ত্বে। আচ্ছা, লক্ষ্যভেদ ফিফটির বদলে যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট ফিফটি কাজ করত? তাহলে মহাভারত কি অন্যভাবে লেখা হতো?
চশমার লাল সুতো উড়িয়ে অভয়পদবাবু আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলেন। বললেন, ‘আচ্ছা, আমার কী করা উচিত বলে আপনার মনে হয় সাগরবাবু?’
আমি পায়ের উপর পা তুলে বসলাম। চেয়ারে হেলান দিলাম আয়েস করে।
‘সেটা নির্ভর করছে আপনি কতটা মালিক তার উপরে। যদি হাফ মালিক হন তাহলে একরকম কথা। তখন আপনি শুধু ধার বাকি নিয়ে ভাববেন। যেমন ধরুন আমার এক মামা ছিলেন, তিনি সারাক্ষণ বাড়ির সেপটিক ট্যাংক নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতেন। তার ভয় হতো, এই বুঝি ট্যাংক উপচে কেলেঙ্কারি ঘটবে। বাড়ির অন্য কোনও সমস্যায় তার মনই ছিল না। মামি রেগে গিয়ে বলতেন, তুমি কি শুধু বাড়ির গু’য়ের মালিক? বাড়ির অন্য কিছুর মালিক নও? আসল ব্যাপারটা হল তাই। মালিক যদি স্যার, আপনি শুধু গু’য়ের হন, তাহলে একরকম কথা, আর যদি গোটা বাড়ির হন তালে আর-একরকম কথা। যদি ওনলি গুয়ের হন তাহলে স্যার খুব একটা মাথা ঘামানোর কিছু নেই। আমার মতো কোনও ছ্যাঁচড়া ধারবাকিতে চাট্টি ভাত-ডাল খায়, তাই নিয়ে মাথা ঘামালেই চলবে, আর যদি গোটা বাড়ির হন, তাহলে স্যার আপনাকে নিজের কর্মচারী পুঁটিকুমারকে নিয়েও ভাবতে হবে। তাকে কেউ আটকে রাখলে গিয়ে উদ্ধার করতে হবে।’
কথা শেষ করে আমি দু’হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলাম।অভয়পদবাবুর অবস্থা ঢিলা। সুতো চশমা নিজে থেকেই ঝুলে গেছে। ইয়ের মতো অমন একটা শব্দ যে কেউ এমন অবলীলায় বারবার উচ্চারণ করতে পারে তাতেই তিনি বিহ্বল। অপমানিতও বটে। আমি দু’হাত মাথার ওপর তুলে আড়মোড়া ভাঙলাম। অভয়পদবাবু পিঠ সোজা করে বসলেন। চোখ দেখে মনে হচ্ছে, মানুষটার রাগ বাড়ছে। বাড়ারই কথা। মালিকানার প্রশ্ন খুব কঠিন প্রশ্ন। এড়ানো মুশকিল।
অভয়পদবাবু বিড়বিড় করে বললেন, ‘আমি যাব। আমি এখনই যাব। দেখব কোন হারামজাদা আমার কর্মচারীর গায়ে হাত দেয়।’
আমি উঠে পড়ে বললাম, ‘সাবধানে যাবেন স্যার। আজকাল চোর ডাকাতরা ভদ্রলোক দেখলেই পেটাচ্ছে।’
অভয়পদবাবু চোখ কটমট করে বললেন, ‘পেটালে পেটাবে। আমাকে ওসব ভয় দেখাবেন না। আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনিও আমার সঙ্গে যাবেন।’
আমি আঁতকে উঠে বললাম, ‘খেপেছেন? আমি এসবে নেই। বিয়ে ভাংচির কেসে ঢুকে মরব নাকি? তাছাড়া আমাকে আপনার ধারবাকির টাকা জোগাড় করতে হবে না?’
অভয়পদবাবু হুংকার দিয়ে উঠলেন, ‘আমাকে ধারবাকির ভয় দেখাবেন না সাগরবাবু। খবরদার ভয় দেখাবেন না। আপনার মতো ফুটো পার্টিকে আমি সারাজীবন বসিয়ে খাওয়াতে পারি।আমাকে বলে কিনা গুয়ের মালিক! এত বড়ো সাহস। অ্যাই কে আছিস, ট্যাক্সি ডাক…।’
অভয়পদবাবুর হম্বিতম্বির মধ্যেই আমি গুটিগুটি বেরিয়ে এলাম। আমার ডিউটি শেষ। বিন্তি উদ্ধারের কর্মকাণ্ডে বারো বছরের পুঁটিকুমার, লামডিংবাসী রহস্যময়ী রেবা, সুতো বাঁধা চশমা পরা অভয়পদবাবু (সঙ্গে হোটেলের কর্মীবৃন্দ) নেমে পড়েছে। আমার কাজ ছিল একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে খানিকটা ক্রোধ ছড়িয়ে দেওয়া। আশাকরি আমি তা পেরেছি। এর বেশি আমি কী করব? কী বা পারি আমি? অলস, বেকার, অকর্মণ্য এক যুবক। সাহসও নেই, ক্ষমতাও নেই। চেহারাও রোগা পটকা। শুধু অনেকটা ধারবাকি আর খানিকটা বিশ্বাস নিয়ে টিকে আছি। যেমন বিশ্বাস করি বিন্তির মতো মেয়েদের বাঁচাতে হলে জ্ঞানগর্ভ লেকচার, পত্রপত্রিকার মুখ টেপা প্রবন্ধ, টিভি চ্যানেলের পাউডারের থেকে আগে দরকার ‘রাগ’। গনগনে রাগ। সেই রাগ বিন্তিদের বাঁচবার পথ আগুনে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে দেবে। আমি পুঁটিকুমার, রেবা, অভয়পদবাবু সবাইকে রাগাতে পেরেছি। ওরা মাঠে নেমে পড়েছে। সমস্যা একটাই। ওরা সবাই আমার ওপর রেগে গেছে। তাতে কোনও ক্ষতি নেই। রাগে আমার অভ্যেস আছে। বরং রাগ না দেখলেই কেমন যেন অস্বস্তি হয়।
দপুরের খাওয়াটা একটু বেশির দিকে হয়ে গেছে। বেটারা ডবল ভাত খাইয়ে দিয়েছে। একটু গড়িয়ে নিলে ভালো হতো। গড়াব কোথায়? আমার জন্য খাট পালঙ্ক কে সাজিয়ে রেখেছে? আচ্ছা আজ যদি…।
শুয়ে আছি চৌবাচ্চা শহিদবেদির ওপর। বেদির গায়ে অস্পষ্ট ভাবে লেখা ‘তিনি ছিলেন নারী মুক্তির প্রজ্জ্বলিত শিখা…।’ কে তিনি? যে-ই হোন, আমার ঘুম পাচ্ছে। আহা! শহিদবেদিতে ঘুমোতে এত আরাম!
ঘুমের মধ্যে বড়ো সুন্দর স্বপ্ন দেখলাম। লামডিং-এর পাহাড়ের ধারে আমি আর রেবা দাঁড়িয়ে আছি মুখোমুখি। আমাদের পিছনে পাহাড় উঠে গেছে। সামনে গিরিখাদ। রেবা আমার ওপর রেগে আছে খুব। বলছে, ‘ছি ছি, বিন্তিকে উদ্ধার না করে তুমি আমার কাছে চলে এলে! ছি ছি।’
ফিসফিস করে বললাম, ‘আমি কি চলে যাব?’
‘হ্যাঁ, চলে যাবে। এখনই চলে যাবে। যাবার আগে আমার কাছ থেকে শাস্তি নিয়ে যাবে। পানিশমেন্ট।’
আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘শাস্তি! পানিশমেন্ট! কী শাস্তি রেবা?’
রেবা এগিয়ে এসে গাঢ় স্বরে বলে, ‘আমি তোমাকে চুমু খাব। অনেক লম্বা একটা চুমু। যতক্ষণ আমি চুমু খাব তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি দেখতে চাই মেঘ আর কুয়াশার মধ্যে একজন মানুষকে চুমু খেতে কেমন লাগে।’
পরিশিষ্ট
গল্পের পরিশিষ্ট হয় না। যেহেতু এটা কোনও গল্প নয়, এটা সত্যি কথা, তাই মনে হয়, পরিশিষ্ট লিখলে কোনও অন্যায় হবে না।
মন্দিরতলা গ্রামে পুঁটিকুমারকে কেউ বেঁধে রাখেনি ঠিকই, কিন্তু তাকে আটকে রেখেছিল। আটকে রেখেছিল তার বাবা-মা। আটকে রাখাটাই স্বাভাবিক। যে-বালক তার কিশোরী দিদিকে বিয়ের মুখ থেকে ছিনিয়ে রাতের অন্ধকারে কলকাতা পালিয়ে আসতে চেষ্টা করে, তাকে আটকে রাখা ছাড়া আর কী বা পথ থাকে। অভয়পদবাবু তার রেস্টুরেন্টের লংকা মহাশয়, শ্রীমান উচ্ছে, পটলনাথ, মুসুরপ্রসাদকে নিয়ে মন্দিরতলা পৌঁছোলে বড়ো গোলমাল শুরু হয়। বিন্তির ভাবী ডাকাত বর লাঠি সোঁটা নিয়ে আক্রমণ করে। লামডিং থেকে রেবা তার রিটায়ার্ড পুলিশ বাবাকে দিয়ে আগেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। হাবড়া থানার পুলিশ ঠিক সময় ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে যায়।
বিন্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই মুহূর্তে বিন্তি তার ভাই এবং বাবা-মায়ের সঙ্গে লামডিং, রেবার ওখানে বেড়াতে গেছে। বিন্তিকে রেবার খুব মনে ধরেছে। ঠিক হয়েছে আপাতত সে ওখানে থেকেই লেখাপড়া করবে। গোটা ফ্যামিলির যাতায়াতের খরচ দিয়ছে রেবা। শুধু পুঁটিকুমার বাদ। শুনলে বিশ্বাস হবে না, পুঁটিকুমারের খরচ ভাতডাল হোটেলের মালিক অভয়পদবাবু রেবার কাছ থেকে নিতে দেননি। বলেছেন, ‘আমার কর্মচারী, আমি যাতায়াতের ভাড়া দেব। আমার কর্মচারীর বেড়াতে যাবার পয়সা অন্য কেউ দেবার কে? মনে রাখবেন আমি মালিক। কী ভাবেন আমাকে, আমি কি শুধু ইয়ের মালিক?’
আমি বেরাকে ফোন করে খুব বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘আমি কি বিন্তিদের সঙ্গে লামডিং যেতে পারি? অনেকদিন কলকাতার বাইরে যাওয়া হয় না। পকেটে পয়সা নেই। তোমার খরচে বেড়িয়ে আসতাম।’
রেবা বলেছে, ‘না, আসবে না। তোমাকে দেখার থেকে, না দেখতে পাওয়ার মনকেমন আমার কাছে অনেক বেশি দামি। তুমি আসবে না।’