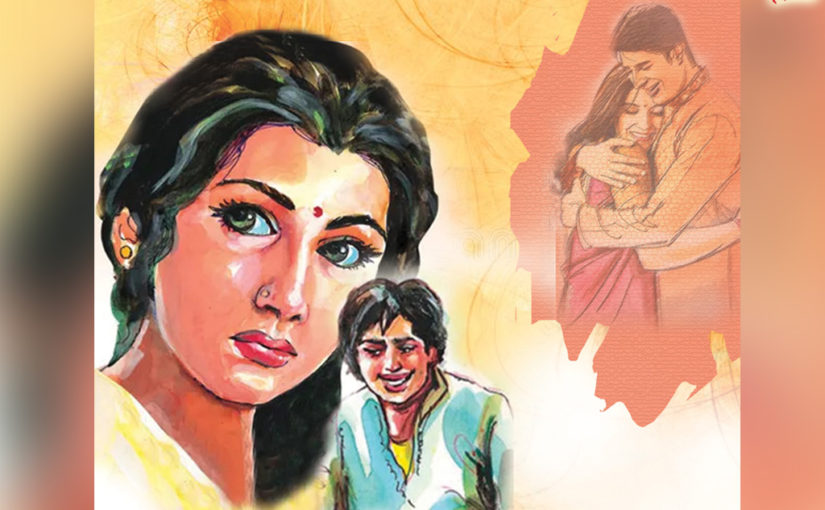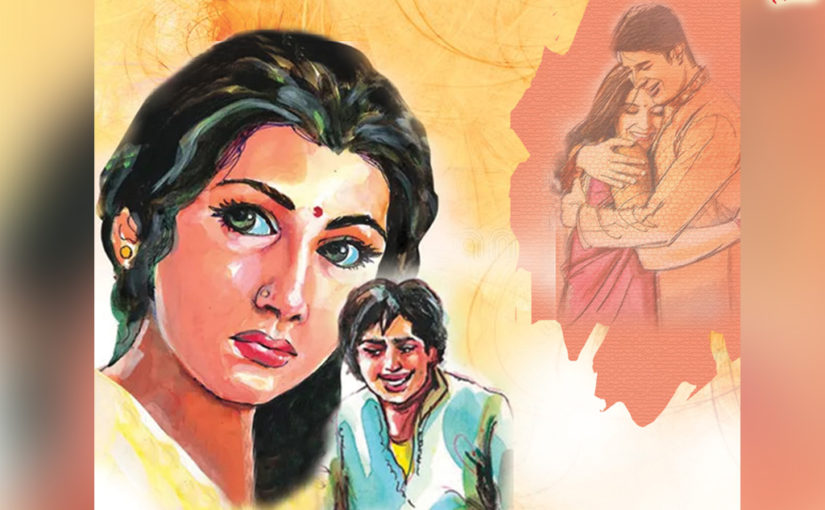ঠাকুমার শেষ কাজকর্মের ঝামেলায় এই ক’দিন আর পূজারিনি বাড়ির বাইরে বেরোতে পারেনি। শ্রাদ্ধশান্তির পর একদিন ইউনিভার্সিটি গিয়ে দেখা হল অরুনাংশুর সঙ্গে। ঘরের টুকটাক খবরাখবর নেওয়ার পর বলল, ‘পরের রবিবার বিকেলে একটু নন্দনে যেতে পারবি?’
পূজারিনি জানত অরুনাংশু লেখালেখি করে, মাঝেমাঝে নানা জায়গায় নানারকম সাহিত্যের অনুষ্ঠানে যায়৷ বলল, “ওসব অনুষ্ঠানে তুই-ই যা, আমার সময় নেই।”
—আরে চল না, সারপ্রাইজ আছে।
—কী সারপ্রাইজ?’ পূজারিনি অবাক চোখে চাইল।
—সেটা হলে গিয়েই দেখতে পাবি, এখন বলব না।
রোববার বিকেলে বাংলা আকাদেমিতে গিয়ে পূজারিনি দেখল— হলভর্তি মানুষের ভিড়। মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথিরা বসে আছেন। পিছনে টাঙানো একটি নামি প্রকাশনার ব্যানার। আর সামনের টেবিলে বইয়ের পাহাড়। কিছুক্ষণ পরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, উদ্বাধনী সংগীত ও বিশিষ্ট অতিথিদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের সঙ্গে শুরু হয়ে গেল অনুষ্ঠান।
দু’টি প্রবন্ধের বই প্রকাশের পর সঞ্চালিকা বললেন— এবার এমন একজন লেখিকার বই প্রকাশ হতে যাচ্ছে যিনি দুর্ভাগ্যবশত আর আমাদের মাঝে নেই। যাঁর সৃষ্টিশীল মন সংসারের বন্ধন ও প্রতিকূলতার মধ্যে বন্দি হয়েও হারিয়ে যায়নি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যার কলম ছিল সচল, অপ্রতিরোধ্য। জীবনের ছোটোছোটো উপলব্ধি, আবেগ, আর বাস্তব ও কল্পজগতের টানাপোড়েন তিনি সাবলীল ভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর ডায়ারির পাতায়। তাঁর লেখার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই প্রথিতযশা সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর ছায়া। তাঁর ডায়ারির পাতা থেকে তুলে আনা সেই মণিমুক্তাগুলি পুস্তক আকারে প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত। এ ব্যাপারে উদীয়মান কবি অরুণাংশু সামন্তর উদ্যোগ বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তার জন্যেই খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল নির্মলা দেবীর সৃষ্টিকে। বইটি প্রকাশের জন্য এবার মঞ্চে ডেকে নেব কবি অরুণাংশু সামন্ত এবং দর্শকাসনে আসীন নির্মলা দেবীর নাতনি পূজারিনি চৌধুরীকে। প্রকাশিত হচ্ছে নির্মলা দেবীর ‘উপলব্ধি”।
সঞ্চালিকার মুখে হঠাৎ ঠাকুমা আর নিজের নাম শুনে পূজারিনি চমকে উঠল। ‘চল আমাদেরকে ডাকছে” বলে অরুণাংশু পূজারিনির হাত ধরে উঠে গেল মঞ্চে। পূজারিনির মাথায় কিছুই ঢুকছিল না, সম্মোহিতের মতো অনুসরণ করল অরুণাংশুকে।
বইপ্রকাশ শেষ হতে হলের বাইরে গিয়ে পূজারিনি জিজ্ঞাসা করল, ‘তুই এসব কবে কীভাবে করলি? কখনও কিছু বলিসনি তো?”
—তোর বোধহয় মনে আছে একদিন একটা কাজে আমি তোদের বাড়ি গিয়েছিলাম। তখনই কথায় কথায় আমি কবিতা লিখি শুনে ঠাকুমা আমাকে বলেছিলেন তাঁর নিজেরও লেখালেখির অভ্যাসের কথা। আমি সেগুলো দেখার জেদ করতে উনি চুপিচুপি আমাকে আর একদিন যেতে বলেছিলেন যেদিন তুই বাড়িতে থাকবি না। সেইমতো কয়েকদিন পরে আমি আর একদিন গেলে উনি বাক্স থেকে তাঁর পুরোনো ডায়ারিগুলো আর কিছু ছিঁড়ে যাওয়া লেখার খাতা বের করে দেখিয়েছিলেন। লেখাগুলো দেখে আমি অবাক হয়ে যাই এবং একপ্রকার জোর করেই সেগুলো নিয়ে আসি। তবে উনি বলে দিয়েছিলেন, আমি যেন এসব কথা কাউকে না বলি, এমনকী তোকেও না। তাই তোকে কিছু জানাইনি।
পূজারিনির মনে উঠল একই সাথে অভিমান ও বিস্ময়ের তুফান। অস্ফুটে বলল, “ওইটুকু সময়ের মধ্যে তুই ঠাকুমাকে একেবারে বশ করে ফেললি? ঠাকুমা তোকে এত ভালোবেসে ফেলল? দিয়ে দিল তার যত্ন করে রাখা প্রিয় ডায়ারিগুলো?”
—হ্যাঁ দেবিজি’, অরুণাংশুর মুখে দুষ্টুমির হাসি। শুধু কি তাই? ঠাকুমা তাঁর আরও একটি প্রিয় জিনিস আমার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন, করতে চেয়েছিলেন প্রায়শ্চিত্ত।
পূজারিনি তো আরও অবাক, ‘কী জিনিস? আর প্রায়শ্চিত্ত কীসের?”
—কথায় কথায় ঠাকুমা যখন জানতে পারল আমি ঘাটালের সুবিমল সামন্তর নাতি, তখন ভারী গলায় বলেছিলেন, তোর দাদুকে তো কিছু দিতে পারিনি, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমার নাতনিকে তোকে দিলাম। ওকে তুই গ্রহণ করিস।
পূজারিনির মনে পড়ে গেল ঠাকুমার ডায়ারির লেখাগুলো। তাহলে সে যা ভেবেছিল সেটাই ঠিক? মনটা কড়কড় করে উঠল ‘সতিন’-এর জন্যে। আজীবন কত না অপূর্ণ সাধ, অপূর্ণ ইচ্ছা নিয়ে বাঁচতে হয়েছে তাকে।
—কী রে, কী ভাবছিস এত?
—কিছু না! চল বাড়ি যাই, বলে পূজারিনি হাতটা বাড়িয়ে দিল অরুণাংশুর দিকে।