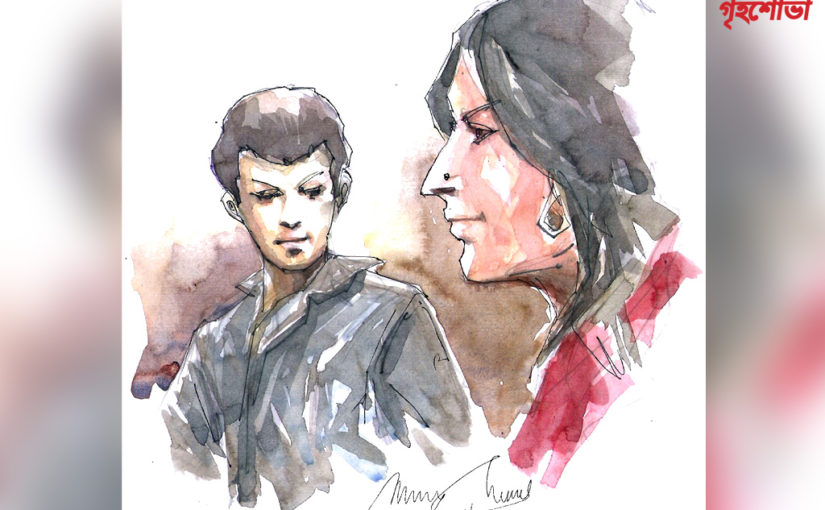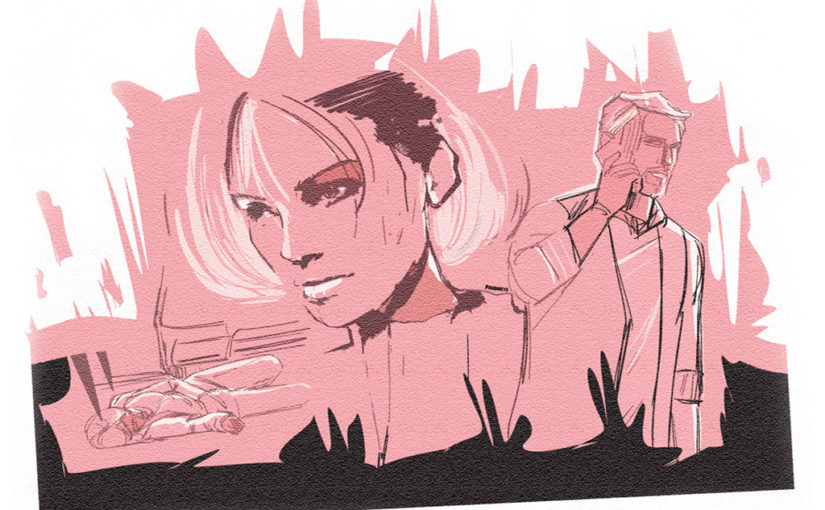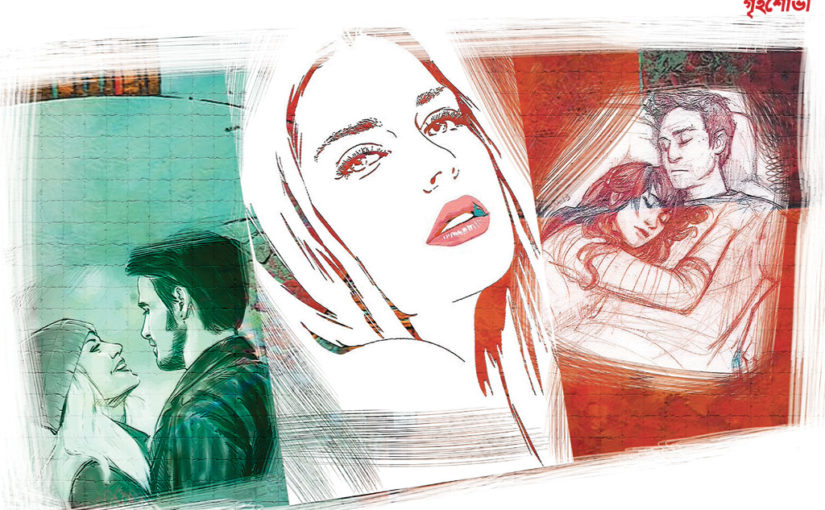মেঘলা, আকাশ মেঘা বলে ডাকে। নামটা বেশ রোমান্টিক। সূর্য হাপুচুপু খায়। ভিজে যায় শরীর। আবার কখনও ফুঁপিয়ে কাঁদে মন। আকাশ যখন মেঘা বলে ডাকে,মেঘার শরীরজুড়ে শীতল বাতাস ছুঁয়ে যায়। আকাশের চোখে মুখে মনে হয় পৃথিবীর সব সুখ লেপটে রয়েছে।
দীর্ঘ শীতাবকাশের পর আজ ছিল কলেজ খোলার দিন। কলেজ ফেরত আকাশ রোজকার মতো ফিরছে তার মেসে। কিন্তু মেঘার সঙ্গে দেখা হয়নি! এই পাহাড়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শীতের ছুটি পড়ে ডিসেম্বর মাস থেকে। মেঘা আসেনি কেন বুঝতে পারছে না আকাশ। অথচ, ওর তো আসার কথা ছিল। কিংবা একটা তো খবর দেবে। এমন তো করে না মেঘা!
কলেজের শেষ পিরিয়ডটা করে বেশ কিছুক্ষণ ক্যান্টিনে দু’কাপ চায়ের ধূমায়িত পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ভাবতে থাকে সেসব কথা। খুব দেরি হয়ে গিয়েছে মেসে ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি। কিছুটা আলো থাকলেও সন্ধ্যা নামতে দেরি নেই। এমন সময় আকাশের মুখ ভার। মেঘের গর্জন। মেঘলা আকাশের বুক চিরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি কিংবা বিদ্যুতের ঝিলিক। ঝোড়ো পরিবেশ। কারেন্ট নেই। বিদ্যুতের ঝলকানির আলোতে ঝাপসা পথটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।
বেশ কয়েকটা চড়াই-উতরাই পার করে আকাশের ছাত্রাবাস। সবুজ চা-বাগিচায় মোড়া সুখি উপত্যকার ঢালে মেস। স্থানীয় একজনের বাড়িতে প্রায় চার বছর ভাড়া রয়েছে। কাঠের সারি সারি ঘর, খুব পরিচ্ছন্ন আর লম্বা সরু এক ফালি বারান্দা। এই বারান্দা থেকে দূর পাহাড়ের বসতি ও উপত্যকায় চা-বাগিচার সবুজ যেন চুঁইয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের জন্য চোখের আরাম হয় বইকি।
এই পাহাড়ি শহরে অনার্স কমপ্লিট করে মাস্টার ডিগ্রি করছে আকাশ-মেঘলা। বিষয় ভূগোল। ফাইনাল ইয়ার। আর প্রথম যেদিন ভর্তি হতে আসে সেদিন মেঘলার সঙ্গে পরিচয়। মেঘলার মাস্টারমশাই মনোময়বাবু সজ্জন মানুষ। প্রথম দিনই আলাপ জমে যায় আকাশের সঙ্গে। মেঘলাকে ভর্তির পর ক্যান্টিনে মোমো খেতে খেতে সব কিছু মনের কথা উজাড় করে দিয়েছেন মনোময় স্যার। আকাশের সহযোগিতায় মেঘলার জন্য একটা ঘরে পেয়িং গেস্ট থাকবার ব্যবস্থা করেন মনোময়বাবু। কিছুটা গার্জেনের ভূমিকা পালন করেন।
আজ দুর্যোগের দিন। মনখারাপ করা বিকালে হাঁটতে থাকে একাকী আকাশ। সাতপাঁচ ভাবতে থাকে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি কিছুটা কমেছে। সবুজ কচিপাতায় ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি বিকালের রোদে মুক্তোর মতো ঝলমল করছে। পাহাড়ের সামনের ঢালে বৌদ্ধ মন্দিরে সান্ধ্য আরাধনার প্রস্তুতি চলছে। ঘন ধুপিগাছের সরলবর্গীয় কাণ্ডের ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্যের রশ্মি ঠিকরে পড়ছে চোখে মুখে। আরও কিছুটা পাহাড়ি রাস্তা পার হলেই হেয়ার পিন বেন্ড পথ। তামাটে বিকালের রং চোখে মুখে।
দুর্যোগ কিছুটা কমল মনে হচ্ছে। বাঁকটার কাছে আসতেই কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াল আকাশ। এই পথ যা স্মৃতির সরণি বেয়ে উঠে গিয়েছে শর্বরী পার্কে। বেশ কিছুটা ছায়া-সুনিবিড়, সমতল সবুজ ঘাসের মখমলে ঢাকা। দেখা যায় তুষারধবল কাঞ্চনজঙঘার মোহনীয় রূপ। কিছুটা পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া। রামধনু আকাশ ছুঁয়ে পাহাড়ের উপত্যকায় যেন জিরিয়ে নিচ্ছে। আকশের নীচে সবুজ উপত্যকা যেন সাতরঙের পেখম মেলেছে।
যেদিন শীতের ছুটি পড়ল সেদিন চুটিয়ে আড্ডা দিয়েছিল আকাশ মেঘলা এইখানে। সেইসব স্মৃতি উসকে দিচ্ছে। প্রায় দিন কলেজ শেষে এই পার্কে বসত। একটা ভিউ পয়েন্ট। পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায় মেঘেদের লুটোপুটি উপত্যকার বুকজুড়ে। দেখতে দেখতে কত সময় কেটে গেছে তাদের।
কখনও মেঘের দল এসে আকাশ-মেঘলাকে ঢেকে দিয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গিয়েও খুঁজে পেয়েছে। হারিয়ে খুঁজে পাওয়ার একটা আনন্দ আছে বইকি! গভীর খাদটা যখন ভরে যেত মেঘে মেঘে তখন মনে হতো মেঘের সাগর। বিকালের ফুরফুরে হওয়ায় একটা ফুরফুরে মেজাজ। মেঘার এলোচুল কপালে চোখে মুখে উড়তে থাকত। আর ছোটো সাদা ধবধবে হাত দুটো দিয়ে নিমেষে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত মেঘলা। একটা দূরত্ব রেখে বসত দুজনেই।
লাল টুকটুকে ঠোঁটের ওঠানামায় আর চোখে কী দারুণ একটা মাদকতা ছিল মেঘলার। দূর থেকে দেখত কীভাবে মেঘেরা ঘনিষ্ঠ হয়ে বৃষ্টি হয়ে ঝরছে। আবার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আকাশ। দেশলাই-বাক্সের মতো পাহাড়ি গাঁয়ের বসতি দেখা যায়। আর যে-পাথরটায় রোজ বসে গল্প করত সেই পাথরটাও খুব আপন হয়ে গিয়েছিল। দিনের শেষে বাগিচার শ্রমিকরা পিঠের ওপর দুধের শিশু নিয়ে ঘরে ফিরত। একটা সর্পিল পথ এই পাহাড়ের বাঁকটা ছুঁয়ে বেশ কিছুটা নীচে অন্য উপত্যকায় নেমে গিয়েছে। এই পথের নিয়মিত পথচারীরাও তাদের চিনে ফেলেছিল।
লেখাপড়ার গল্প আর বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে বেশি আলোচনা চলত। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারত না কেউই। ভাসা ভাসা কথার ভাঁজে লুকিয়ে থাকত নির্ভেজাল মনের গল্প। রাতের বিছানায় স্মৃতি রোমন্থনে দুটো মন সময়ের বয়সে ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে।
খুব দারিদ্রের মধ্যে বেড়ে ওঠা মেঘলার। মনোময় স্যার না থাকলে এই নামি কলেজটায় আসতেই পারত না। আকাশ প্রথম দিন কিছু কথা শুনেছিল মনোময়বাবুর কাছে।
এই সেই পাহাড়ি বাঁক, যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে জীবনের প্রায় সব কথাই বলেছিল মেঘলা। আকশের মনে পড়ছে এখন সে সব কথাকাহিনি। মেঘলা সেদিন বলেছিল, ছোটো বোন চন্দ্রিমার কথা। বাবার কথা মনে করতে পারি না। মেঘলার মা সীমা জ্যোৎস্না রাতে ফুটফুটে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শুনিয়েছে হারিয়ে যাওয়া পিতার গল্প। সেসব কথাও বলেছে মেঘলা আকাশকে একটু একটু করে। মায়ের কাছে শুনেছে, বাবা সইফুদ্দিন আকাশে তারা হয়ে জ্বলছে। পরে তারা দেখতে দেখতে যখন বড়ো হয়েছে সব বুঝেছে।
মেঘালয় রাজ্যের ডাউকি নদী সীমান্তঘেঁষা বাংলাদেশের সিলেট লাগোয়া অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত কিছু খাসি জনজাতির বাস। আর পাহাড়ের কোলে ছবির মতো ছোটো গাঁয়ে বসবাস করত মেঘলাদের আদি খাসি পরিবার। সইফুদ্দিন সিলেটের বাসিন্দা। পুরুষানুক্রম থেকে চলে আসা ওদের মৎস্যশিকার আর জমিতে কৃষিকাজ-ই ছিল জীবিকা। পরিবহণ ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল সইফুদ্দিন।
নৌকা নিয়ে প্রায় দিন ডাউকি নদীর জল ভেঙে মাছ ধরত! কখনও পর্যটকদের মনোরঞ্জন করতে নৗকাবিহার করাত। কিছুটা পর্যটনের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। ভালোই আয় হতো। আসা যাওয়ার পথে এই পাহাড়ি বসতির মানুষজন তার মুখচেনা হয়ে যায়। প্রথমে পরিচয়, মন দেওয়া নেওয়া তারপর বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়! সীমা সফি বলে ডাকত। সফির বাবা মা পরিবার তা মেনে নেয়নি। ঘর থেকে পালিয়ে সীমার বন্ধনে আবদ্ধ হয় সফি।
খাসি পাহাড়ের পাদদেশে সুখের সংসার পেতেছিল সীমা-সফি। সইফুদ্দিন চোস্ত খাসি ভাষায় কথা বলতে পারত। বিয়ের পর দায়িত্ব বেড়ে যায় সফির। পরবর্তীতে পর্যটকদের সঙ্গী করে নৌকাবিহার পর্যটন ব্যবসায় যুক্ত হয়। তার নৗকাটাও বেশ সাজানো। নৌকার গায়ে আঁকা থাকত নদী, বিভিন্ন মাছের ছবি। ডাউকি বাজারলাগোয়া ডাউকি নদীর ঘাট পর্যটন মরশুমে পর্যটকদের ভিড়ে ঠাসা থাকত। নিশ্বাস ফেলার সময় হতো না সফির। নদীর স্বচ্ছ জলে নৌকা বিহার এখানে খুব জনপ্রিয়। আবার অফসিজনে কখনও মালবাহী ছোটো গাড়ি নিয়ে শিলং চেরাপুঞ্জি রওনা দিত। প্রায় দিন পাহাড়ি পথে সন্ধ্যা নামার আগেই ঘরে ফিরত।
সীমা ভুট্টা খেতে ভালোবাসত। সারাদিন স্টিয়ারিং ধরে ক্লান্ত অবসন্ন শ্রান্ত শরীর এলিয়ে দিত সীমার কোলে। সন্ধ্যায় ওরা দুজনে ডাউকির তীরে ভুট্টা খেতে খেতে গল্প করত। ডাউকি নদী যেন সীমা সফির কাছে ভালোবাসার পূণ্যতোয়া। রামধনু রঙে মাখামাখি জলে হরেক রকমের মাছের ছোটাছুটি দেখতে দেখতে বাসায় ফিরে যেত। এ ছিল তাদের রোজকার রুটিন।
মেঘলার মা সীমা সেই স্মৃতিচারণ করতে করতে প্রিয় সফিকে খুঁজে পেত। স্মৃতির চাতালে আজও দপদপ করে সেইসব দিনের কথা। মায়ের কাছে শুনেছে মেঘলা– তখনও সন্ধ্যা নামেনি, হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি। নিমেষে থরথর করে কেঁপে ওঠে পাহাড়, যেন নৃত্য করছে। ডাউকির মাছরাঙা জল, উথলে উঠছে আকাশ ছোঁবে বলে। এমন একটা ধবংসলীলার চলচ্চিত্র সেদিন স্বচক্ষে দেখেছিল মা।
বাবা গাড়ি নিয়ে চেরাপুঞ্জির রাস্তায় ছিল সেদিন। শুনেছি বহু মানুষ সেই ভূমিকম্পে মারা গিয়েছিল। তারপর চোখ ছলছল হয়ে আসে মেঘলার। কিছুটা সামলে আবার বলতে থাকে– সেই সন্ধ্যায় আর ফেরা হয়নি সফির। আসলে সেই সময়টায় কে কোন দিকে গিয়েছে জানা যায়নি। আত্মীয়স্বজন অনেকেই খবর নিয়েছে কিন্তু খোঁজ মেলেনি বাবার। মেঘলা বলে, মায়ের কাছে শুনেছে বীভৎস সেই রাতের কথা।
সবুজ শৈলশিরাটা যেখানে শিকলের মতো নদীর স্রোত ছুঁয়েছে সেই ঢালে বিক্ষিপ্ত জনবসতি সেখানেই দু-কামরার সীমা-সফির সাধের ছোটো সাংসার। কুটির বলাই ভালো। নদীর কাছে কিছুটা সমতল জায়গায় কয়েকজন মিলে তাড়াহুড়ো করে বার হয়ে আসে তাই বেঁচে যায়। বহু ছবির মতো পাহাড়ি বসতি এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। তারপর সরকারি ব্যবস্থাপনায় ত্রাণশিবিরে আশ্রয়।
তখন মা সন্তানসম্ভবা। একটি ত্রাণশিবিরে প্রথম প্রসব! সেদিন ছিল মেঘলা আকাশ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। যদিও বৃষ্টি-মেঘের খেলা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সীমা যমজ কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। ত্রাণশিবিরের সকলে নাম রেখেছিল মেঘলা, চন্দ্রিমা।
এরপর ডাউকি নদী দিয়ে বহু জল গড়িয়ে গিয়েছে। সীমান্তঘেঁষা উত্তর-পূর্বের মেঘালয় রাজ্যের পশ্চিম জয়ন্তিয়া পাহাড়ে অবস্থিত ডাউকি নদীর সীমান্তঘেঁষে মেঘার পাহাড়ি গ্রাম। ঢিলছোড়া দূরত্বে বাংলাদেশের সিলেট শহর। খাসি ভাষা একটি অস্ট্রো-এশীয় ভাষা যা মূলত ভারতের মেঘালয় রাজ্যে প্রচলিত।
ত্রাণ শিবিরের পর কোনওরকম একটা তাঁবুর মতো ছেঁড়া প্লাস্টিকের ছাউনিতে ঠাঁই হয়। কিংবা বর্ষার দিন প্রাইমারি স্কুলের বারান্দায় ঠাঁই নিত। মেঘালয়ের ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমির মতো বিচ্ছিন্ন ছিন্নমূল দরিদ্র পরিবার। খাসি রমণী সীমা পরিশ্রমী। দুই কন্যাসন্তানকে শিক্ষায় আচার-আচরণে উন্নত করেছে সে। মায়ের স্থানীয় হোটেলে রান্নার কাজ নেওয়া, কখনও-বা ডাউকি নদীর ঘাটের কাছে ছোটো দোকান দিয়ে রোজগারের ব্যবস্থা করা। এসব জীবনযন্ত্রণার কথা দিনের পর দিন বলেছে মেঘলা আকাশকে।
ডাউকি নদীর বর্ডার প্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক পর্যটন। নদীর মনোলোভা সৗন্দর্য চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে পর্যটকদের। এরকম মনোরম পরিবেশে বেড়ে ওঠা মেঘলার।
ছোট্ট বয়সে বিয়ে হয়ে যায় চন্দ্রিমার। ভীষণ জেদ ছিল মেঘলার। বড়ো হবার জেদ। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পর্যটকদের খুব কাছ থেকে দেখেছে নদীতে নৗকা বিহার করতে। মায়ের সঙ্গে ডাউকি নদীর ধারে দোকানদারি করেছে সে। স্কুল পড়াশোনা, পাহাড়ের ঢালে জ্বালানি সংগ্রহ এই ছিল রোজকার রুটিন। শুকনো কাঠের জ্বালানি সংগ্রহ করতে গিয়ে কতবার কাঁটাঝোপে দুই বোনের আপেলের মতো গাল চিরে রক্ত ঝরেছে। সেই রক্ত রোদে জলে ধুয়ে গিয়েছে। খেয়ালই নেই মেঘলা, চন্দ্রিমার। ডাউকি নদীর আয়নার মতো জলে যখন সূর্যাস্ত হতো সিঁদুর মেঘের প্রতিচ্ছবি দেখা যেত, তারপর ক্রমশ ঘন রাত আঁকড়ে ধরত ডাউকির এই পাহাড়ি গ্রামকে।
ডাউকির জনপথলাগোয়া ফুটপাথেই ছিল সীমা-মেঘলা-চন্দ্রিমার বাস। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা। তারপর হাইস্কুল উচ্চমাধ্যমিক স্তর পার করেছে চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বুঁদ হয়ে থাকত মেঘলা। দূর পাহাড়ের চূড়া থেকে সমতলে সিলেট শহরের রূপ দেখতে কখন সে আনমনা হয়ে পড়ত।
খাসি ভাষার কবি সো সো থামের কবিতা পড়তে ভালোবাসত মেঘলা। খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে এই প্রাচীনতম জনজাতির বাস। প্রকৃতি, প্রেম, কল্পনা, মননশীলতায় ভরপুর সো সো থামের খাসি কবিতার পুস্তকটি ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছে মেঘলা। এমন সুন্দরী সবুজ উপত্যকায় বসে দেখেছে পাহাড়ি ঝরনা আর সূর্যমেঘের লুকোচুরি। পিতৃহারা মেঘলা-চন্দ্রিমা দেখেছে তাদের মায়ের কঠোর শ্রম।
কল্পনা, প্রকৃতি আর বাস্তবতা এসব নিয়ে তাদের ছোটো সংসার।নংক্রেম নৃত্যও অতি প্রসিদ্ধ খাসি উৎসব। লোক নাচে বেশ দক্ষ ছিল মেঘলা চন্দ্রিমা। পুরোনা অ্যালবাম ঘেঁটে কয়েকটা স্কুলজীবনের নাচগানের ছবিও দেখিয়েছে। চন্দ্রিমা ভালো গান গাইত। জয়ন্তিয়া পাহাড়ের উপজাতীয়দের পার্বণ বেহদিয়েংখ্লাম পালিত হয় প্রতি বছর জুলাই মাসে। গারোরা পালন করেন ওয়াংগালা উৎসব যা আদতে সূর্যের উপাসনা। এসব কথা শুনতে শুনতে সন্ধ্যা নেমেছে পাহাড়ের পাকদণ্ডি পথে। এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বলত মেঘলা। দার্জিলিং পাহাড়ের সিঙ্গালিলা শৈলশিরায় বসে কলেজপড়ুয়া আকাশ জয়ন্তিয়া পাহাড়ের মেঘলার কথা শুনেছে।
‘প্রাইমারি স্কুল, হাইস্কুল, মাধ্যামিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে বেশ কিছুদিন বাড়িতেই বসেছিলাম। কয়েকজন প্রতিবেশীর বাচ্চাদের টিউশন পড়াতাম।’ আকাশকে তাদের পরিবারের অনেক কথাই বলেছে মেঘলা। ‘জানো, স্যার আসত প্রায় খোঁজখবর নিতে। বোনের খুব ছোটোতে বিয়ে হয়ে যায়। পরির মতো টুকটুকে সুন্দরী বোন। ঘটকের পাল্লায় পড়ে আমারও বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল বহুবার। কিন্তু রাজি হইনি। বাড়ির কোণে ফুঁপিয়ে কেঁদেছি। পরে একদিন স্যার কে সব কথা বললাম। আমি শুধু পড়তে চাই।
স্যার আমাদের ক্লাসে বলতেন, ‘মেয়েদের পড়তে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।’ সে অনেক কথা– বলতে বলতে চোখ ছলছল হয়ে আসে মেঘলার। মনোময় স্যার প্রবাসী বাঙালি। শিলং শহরে তাদের বাস। প্রাচীন বাঙালি পরিবার। অবিভক্ত দেশের এই পাহাড়ি স্কুলটা ডাউকি সীমান্তে অবস্থিত। মনোময় স্যার এই স্কুলের একজন শিক্ষক। তাঁর উদ্যোগে মেঘলার এতটা পথ আসা। মেঘলা বলেছিল, সে পড়তে চায়! বড়ো হতে চায়। এদিকে মনোময় স্যার অবসর নেন যে-বছর, সেই বছরই উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে মেঘলা।
মাধ্যমিক পাস করবার পর থেকে অভাবী ঘরের মেধাবী ছাত্রী সকলের নজর কাড়ে। মনোময় মেঘলাকে স্নেহ করতেন। তিনি দুঃস্থ অসহায় পরিবারকে সব রকম সহযোগিতা করতেন। মনোময়বাবুর সহযোগিতা নিয়ে দার্জিলিঙে ভূগোল পড়তে আসা মেঘলার। সব কথাই আকাশকে বলেছিল মেঘলা দার্জিলিঙের শর্বরী পার্কের নির্জনতাকে সাক্ষী রেখে। কোনওদিন সন্ধ্যা গড়িয়ে গাঢ় অন্ধকার নামত পাহাড়ে।
ভোঁ ভোঁ শব্দে মেঘের চাদর ফুঁড়ে ফিরতি জিপগাড়িগুলো পাকদণ্ডি পথে হর্ন বাজিয়ে চলছে। সার্চলাইটের মতো গাড়ির হেডলাইট মেঘার কখনওবা আকাশের চোখে মুখে পড়ছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক আড্ডা দিয়ে ফিরে যেত আপন আপন মেসে। একদিন তো ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। এসব থরেথরে সাজানো স্মৃতি কথাগুলো মনে করতে করতে আজ মেসে ফিরল একলা আকাশ। সঙ্গে মেঘলা নেই । কিন্তু মেঘলার স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে কখনও পথে থমকে দাঁড়িয়েছে। আবার হাঁটা শুরু।
মূল সড়ক থেকে কিছুটা এবড়োখেবড়ো পথ নেমে গিয়েছে হ্যাপিভ্যালি চা বাগানের দিকে। এখন বৃষ্টি নেই। পরিচ্ছন্ন মেঘমুক্ত আকাশ। কয়েকটা ধাপ পা ফেলে ফেলে উঠলেই বারান্দা তার পর গভীর খাদ। ভেজানো দরজা খুলে লাইটের সুইচে হাত দিতেই আলোকিত হল ঘর। লাইট জ্বালিয়ে লেপটা বিছানায় বিছিয়ে দেয়। কারণ রাতের দিকে সব কিছু হিমশীতল হয়ে যায়।
সেই সকালে নীচের ঝরনা থেকে সংগৃহীত পানীয় জল বালতিতে কতটুকু রয়েছে দেখে নেয়। এর পর রান্নার তোড়জোড়। ডিম আলু ডাল একসঙ্গে সেদ্ধ করে নেওয়া। খিদে পেটে সব কিছুর স্বাদ অমৃত। রাত আটটার পর সব নিঝুম। তারার মতো দূর পাহাড়ের গায়ে গায়ে জ্বলজ্বল করে আলো। টগবগ করে ফুটছে ভাতের হাঁড়ির জল। কাঠের ছোটো ঘরের ফাঁকে খবরের কাগজ সাঁটানো।
শীতের রাতে গুনগুন করে গাইতে থাকে নেপালি গান, হিজো রাতি কিনো? কিনো? নিদ্রা লাগিনো, কসতো মায়া… কসতো মায়া… গানের কলি। ডেকচি উপচে ভাতের ফ্যানা পড়ছে।
ডালে-চালে আর আলু সেদ্ধ পেঁয়াজ লংকার তরিবতের খানা রেডি। কিছুক্ষণ সব ভুলে কলেজের পড়াসংক্রান্ত কাজ।
আকাশ রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে এখন ব্যালকনিতে। নিঝুম রাতের নিস্তব্ধতা ভাঙে পাহাড়ি কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে। এই সময়টা সে তার পড়া আর ভাবনাগুলোকে এক সূত্রে গাঁথে। আরও কয়েকটা মাস কাটাতে হবে পাহাড়ি শহরে। মনের মানুষের সান্নিধ্য বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে।
পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে নদী বিষয়ে গবেষণার বড়ো ইচ্ছা আকাশের। সব ইচ্ছা তো আর পূরণ হয় না। এসব এলোমেলো ইচ্ছের কথাও বলে ছিল আকাশ মেঘলাকে। বলেছিল, ডুয়ার্সের ছবির মতো তার গ্রামের কথাও! কখন যে মেঘালায়ের ডাউকি আর আকাশের রায়ডাক মিলেমিশে একাকার হয়েছে মনের মোহনায়, হয়তো টের পায়নি কেউ। বন্ধুত্ব থেকে ভালোলাগা ভালোবসায় রূপান্তরিত হয়েছে সময়ে সময়ে। দিনের পর দিন ভালোবাসা ঘন হয়েছে।
আসলে এই তো সেদিন ডুয়ার্সের ভূটান সীমান্ত গাঁ থেকে আকাশ এই পাহাড়ি শহরে এসেছিল অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। পাহাড়ে খরচ বেশি। কিন্তু ভূগোল বিষয়ে সব কলেজে তখন পড়ার সুযোগ ছিল না। জমি বিক্রি করে টাকা জোগাড়! মাসে মাসে আবার খরচ আছে। আকাশদের একান্নবর্তী পরিবার। বাবা বিমল রায় একজন কৃষিজীবী।
আকাশের বাবারা ছিল তিন ভাই। বাকিরা সকলেই ব্যাবসাবাণিজ্য সরকারি চাকরি নিয়ে থাকত। ডুয়ার্সের কুমারগ্রাম ব্লকের খোঁয়াড়ডাঙা এলাকার নারারথলি গ্রামের এটাই সব চেয়ে বড়ো পরিবার। আকাশের বাবা খেতি কাজের পাশাপাশি ভেষজ চিকিৎসার মাধ্যমে ভাঙা হাড় জোড়া লাগানোর কাজও বেশ সফলতার সঙ্গে করেন।
স্থানীয় জঙ্গলের বিভিন্ন লতাগুল্ম দিয়ে হাড়গোড় জোড়া লাগাতেন আকাশের বাবা। ভোর থেকে লেগে থাকত ঘরময় রোগীর ভিড়। আকাশকে বড়ো মানুষ করে গড়ে তোলবার ইচ্ছা। সাত-পাঁচ করেই দার্জিলিং পাহাড়ের কলেজে ভর্তির বন্দোবস্ত করেছেন। আসলে, আকাশের দাদু হাড়ভাঙা ডাক্তার নামে এই সীমান্ত লাগায়ো আসাম-ভূটান স্ললাকায় বেশ পরিচিত ছিলেন।
কলেজ ছুটির ফাঁকে পাহাড় থেকে নেমে পড়ত আকাশ। জীবনের গতি এখানে যেন ধীর। আলিপুরদুয়ার ছুঁয়ে জাতীয় সড়কটা অসমের দিকে গিয়েছে। আর তেলিপাড়া থেকেই বাঁ দিকে পিচ ঢালা এক ফালি রাস্তা ছুটছে খোঁয়াড়ডাঙা অভিমুখে! যা ভূটানের গা-ছমছম গভীর জঙ্গলে ঢুকেছে। রাস্তার দু-ধারে ছায়াসুনিবিড় গাছ গাছালি। চরম গ্রীষ্মে যখন হাঁসফাঁস করে মানুষ তখন রোদের তীব্রতাকে এই পথছায়া গোগ্রাসে গিলে খায়। আর শরীরে এক মনোরম শীতল অনুভূতি জেগে উঠে। এমন একটা রূপকথার গাঁয়ে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছে মনে মনে দানা বাঁধত মেঘলার।
আকাশের গ্রামের ঢিলছোঁড়া দূরত্বে ভূটান। জমজমাট গ্রামীণ বাজার। হাটের দিনগুলোতে উপচে পড়ে মানুষের ভিড়। শনি ও মঙ্গলবার হাট বসে। আকাশ যখন ছোটো ছিল বাবার সঙ্গে ঘরের মুরগি ও মরশুমের সবজি নিয়ে হাটে বসত। স্থানীয় নদ-নদীর তাজা নদীয়ালি মাছ যেমন পাওয়া যায় তেমনি ঘরের পোষা মুরগি হাঁস নিয়েও হাটুরেরা হাজির হয়। বিভিন্ন জনজাতীর মনপছন্দ খাদ্যতালিকা অনুযায়ী রকমারি সব কিছু হাটে মিলবে।
এখানকার গ্রামীণ হাটগুলো মেলার রূপ নেয়। এলাকাটি যেন মিনি ভারতবর্ষ। বিভিন্ন জাতি উপজাতি ধর্মের আর সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র। সহজসরল জীবনযাপন আর অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর মানুষজন। ভাষা পোশাক ধর্ম আচার ভিন্ন হলেও কোথায় যেন একটা ঐক্যের সুর বাঁধা আছে। কৃষিপ্রধান এলাকা। রয়েছে বন বস্তি। আধুনিকতার ছোঁয়ায় ঘরবাড়ি পোশাকেও ছাপ পড়েছে। সব কথা মেঘলাকে শুনিয়েছে আকাশ। সকলকে আপন করে নেওয়ার কি অসাধারণ জাদু আছে আকাশের!
কলেজ জীবন শেষ করে এবার ঘরে ফেরা। তাঁর প্রিয় অধ্যাপকের পরামর্শ মতো নদী বিষয়ে গবেষণা শুরু করবে। ছোটো থেকেই নদীকে সঙ্গী করে জীবন। খুব কাছ থেকে দেখেছে কীভাবে ভূটান থেকে নেমে আসছে বিভিন্ন নদনদী! সংকোষ, রায়ডাকের মতো আন্তর্জাতিক নদী যেমন রয়েছে, তেমনি ঘোড়ামারা, জোড়াই, কুলকুলি প্রভৃতি নদী শিরা উপশিরার মতো ছড়িয়ে রয়েছে। অতি বর্ষণে বন্যা এই এলাকার স্থায়ী সঙ্গী। ভূটান পাহাড়ের অবৈজ্ঞানিকভাবে ডোলোমাইট উত্তোলন একটা কারণ। এই অঞ্চলের ঢাল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।
আকাশ দেখেছে নদীগুলোর পূর্ব দিকের পাড় ভাঙার প্রবণতা। হঠাৎ করে পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসায় নদীর গতিবেগ কমে যায়। নদী পাথরনুড়িতে বোঝাই হয়ে থাকে। ফলত বন্যার কবলে পড়ে এলাকা। এখান থেকে যেদিকে চোখ যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। নদীমাতৃক বাংলার রূপসী রুপ যেন এখানে উপচে পড়ছে। এলোকেশী-নারী যেন ভরা বর্ষায় ফুঁপিয়ে কাঁদে। ভীষণ গর্জন করে ভাসিয়ে দেয় গ্রাম। শীতের মরশুমে শুধু শোনা যায় নদীর কুলুকুলু শব্দ আর নিস্তব্ধতা ভাঙে কোকিলের কুহু কুহু ডাকে।
বনবস্তির চরে বেড়ানো গরু-ছাগলের গলায় ঝুলানো টিনের তৈরি ঘণ্টা জানান দিচ্ছে তাদের অস্তিত্ব। নদী যেন একা নীরবে শুয়ে থাকে। এমন এক অনাবিল প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা আকাশের। নদী পাহাড় তাকে আজও চুম্বকের মতো টানে।
শীতের ছুটির পর আর ফেরা হয়নি মেঘলার। ফিরবে কি করে! ফেরার দিন ঘটে গেল অঘটন। প্রতিদিন শিলং-গৗহাটি মেল নামে দুধসাদা বাসটা সাতসকালে হর্ন বাজিয়ে ডাউকি বাজার থেকে ছাড়ে। আর তখনই মেঘলাদের পুরোনো ঘড়িটা পেন্ডুলাম দোলাতে দোলাতে পাখির কিচিরমিচির আওয়াজ করে ঘড়ির কাঁটা মিলে যায় সাতের ঘরে।
সকাল সাতটা বাজে। এই সাত-পুরোনো ঘড়িটার একটা ইতিহাস আছে। মেঘলার বাবা সইফুদ্দিন বাংলাদেশ থেকে যখন চলে আসে তখন সীমাকে উপহার দিয়েছিল। সীমা দেওয়াল ঘড়িটা আগলে থাকে।
আজ মেঘলার দর্জিলিং ফেরার দিন। কিন্তু মা সীমার ঘুম ভাঙেনি। চলে গিয়েছে ঘুমের দেশে। হার্টের পেশেন্ট। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। শোকের ছায়া ঘরজুড়ে! মাস্টারমশায় মনোময়বাবুর কাছে খবর যায়। মেঘলার বুকে তখন একটা নোনা বঙ্গোপসাগর তৈরি হয়েছে। ঘড়িটার দিকে নিঃষ্পলক তাকিয়ে থাকে মেঘলা।
কিছুদিন মনোময়বাবুর ঘরে থাকে। পরে একটি বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত হয়। আকাশকে সেসব কথা জানিয়ে চিঠিও লিখে রেখেছিল। কিন্তু চিঠিটা ফেলা হয়নি ডাকবক্সে! কচিকাঁচা ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। প্রতিদিন সাতসকালে রাস্তায় পথ চলতি গাড়ি ধরে স্কুলে যায় মেঘলা। দুষ্টু-মিষ্টি শিক্ষার্থীরা তার বেঁচে থাকার রসদ। মনে মনে ভাবে জীবনটা যেন একটা অসম্পূর্ণ সনদ।
এদিকে দার্জিলিঙের পাট চুকিয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ঘরে ফিরেছে আকাশ। ফিরেই সংবাদ পেল আকাশ গবেষণার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। কৃষকের ছেলের এমন সাফল্যে গোটা গ্রামে উৎসবের মেজাজ। উত্তর-পূর্ব ভারতের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারারশিপ ও নদী বিষয়ে গবেষণার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। গবেষণার কাজ শুরু করতে রওনা দিল আকাশ।
ডুয়ার্সের গা ঘেঁষেই অসম। গুয়াহাটি হয়ে সেদিন শিলং পৌঁছোল আকাশ। আবার একটা মেসের মতো কোয়ার্টারে থাকবার ব্যবস্থা। উত্তর-পূর্ব ভারতের নদনদী চরিত্র ও নদী অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত টাটকা তথ্য সংগ্রহ করতে পাহাড়ি রাজ্য চষে ফেলেছে আকাশ। যখন কাজ শেষে রুমে ফেরে মেঘার কথা মনে পড়ে।
যাইহোক যদি পথে দেখা হয় কোনওদিন কি বলবে মেঘলাকে! কখনও রাগ অভিমানে গাল ফুলে যায়। আবার গবেষণার কাজে ডুবে যায় আকাশ। ভোলার চেষ্টা করে সব কথা। এবার ডাউকি নদী সীমান্তে যাবে। মেঘালয় মালভূমি থেকে আগত একটি পাহাড়ি নদী। ডাউকি চ্যুতির নাম অনুসারে নদীটির নাম ডাউকি। জল স্বচ্ছ কাচের মতো নান্দনিক সৗন্দর্যের যেন লীলাভূমি।
আকাশের গা ছমছম করে। সবে ডাউকি ব্রিজটা পার হয়ে গাড়িটা থামল। হকারের কাছে পায়ে পায়ে এগিয়ে একটু কফি কাপে চুমুক। শিলং থেকে যখন গাড়িটা ছাড়ে তখনই বৃষ্টি শুরু। আজ সকাল থেকে খুব মেঘলা। ডাউকি ঢোকার মুখে ব্রিজ। মনে পড়ছে মেঘলার কথা। ডাউকি মেঘলা মেঘালয় যেন অজান্তেই তার নিজের হয়ে গিয়েছে। শরীরটা যেন হিমশীতল হয়ে আসে!
গাড়িটা স্টার্ট দিতে আবার ঝমঝম শিলা বৃষ্টি। বৃষ্টির ফোঁটায় নদীর জলে বুদবুদ উঠছে। হু হু করে পাহাড়ি ঝরনা মূল সড়কে ধুয়ে খাদে পড়ছে বীভৎস গর্জন করতে করতে। অগত্যা গাড়ি থামাল চালক! মেইন রোডের পাশে একটা বেসরকারি স্কুল। নাম রিভার পয়েন্ট নার্সারি। এখানে কিছুক্ষণ বিরতি। মেঘে ঢাকা আকাশ। দিনের বেলায় যেন অন্ধকার নেমে আসছে।
গাড়ির জানলার কাচটা খুলতেই আকাশ দেখে বেশ চমকে গেল, পরির মতো অপ্সরা একজন মহিলা মেঘেঢাকা পাহাড়ের সর্পিল পথ বেয়ে নেমে আসছে। লুকস লাইক আ ফাউন্টেন, হয়তো মূল সড়কে উঠবে! হাত নেড়ে গাড়িটাকে ইশারায় অপেক্ষা করতে বলছে। যদিও আকাশদের গাড়িটা এমনি অতিবৃষ্টির দরুন দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ কিছুটা হতোভম্ব হয়ে গাড়ির গেটটা খুলে দিল। সটান গেটে ছোটো হাতটা চেপে গাড়িতে উঠে পড়ল মহিলা।
খুব চেনা খুব জানা। কিন্তু দুজনেই নির্বাক। তখন আবার মেঘেঢাকা আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের রক্তিম আভায় টুকটুকে গাল দুটো স্মৃতির আলোর ঝরনাধারা। চোখের তারায় তারায় আনন্দ অশ্রুর প্লাবন।
জীবনের গাড়িটা হয়তো ছুটল পাহাড়ের পাকদণ্ডি পথ পেরিয়ে আলোর ঠিকানায়।