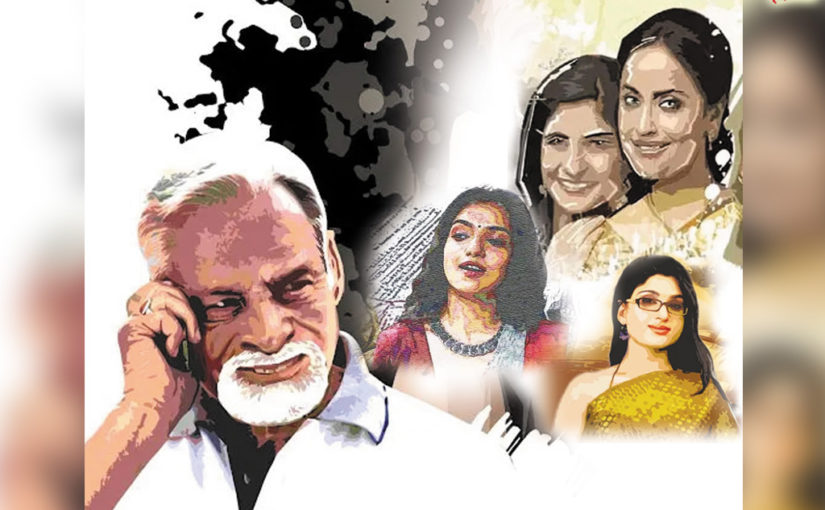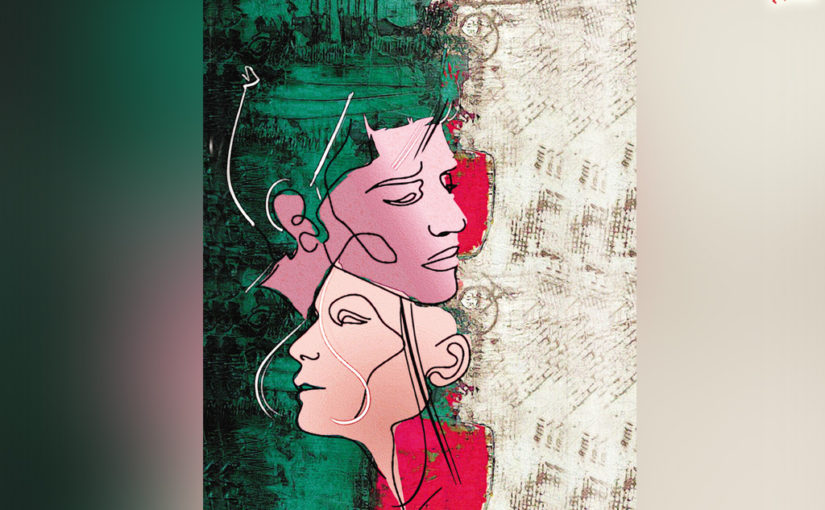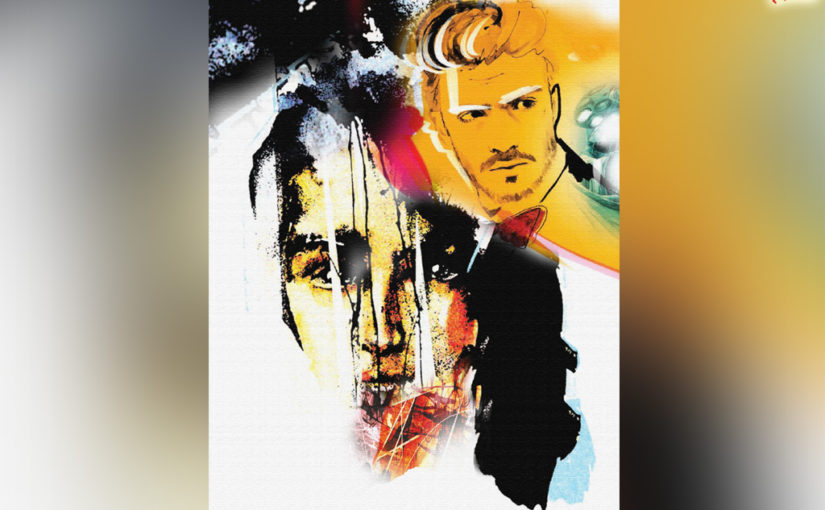হঠাৎ নাকে একটা অদ্ভুত সবুজ গন্ধ এসে লাগল। যদ্দুর মনে হয়, পাহাড়ের গায়ের ভিজে শ্যাওলার গন্ধ। মুখের ওপর ভারি টর্চের আলো। চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। আলোর পিছনে আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আলো আর আমার চোখের মাঝখানে একটা কুয়াশার টুকরো ঝুলে আছে। হঠাৎ দপ করে আলোটা নিভে গেল। আলকাতরার মতো একটা অন্ধকার কে যেন ঢেলে দিল আমার চোখে। তারপরই একটা হিমশীতল ধাতুর স্পর্শ লাগল আমার পিঠে। পরক্ষণেই গুরুগম্ভীর একটা প্রশ্ন কালো রাত ফুঁড়ে আমার দিকে ধেয়ে এল, ‘আপনি কে? কোত্থেকে আসছেন?”
আমার গলা তখন ভয়ে আর মহুয়ার নেশায় পুরো জড়িয়ে গেছে। বেশির ভাগটাই হাতের ইশারায় আর বাকিটা অস্ফুট শব্দে বলে উঠলাম, ‘বাড়ি রাজগাঙপুর। জঙ্গলে পথ হারিয়ে গেছি।’ আমার দুটো হাত দু’জনে ধরল। তারপর মাটিতে হেঁচড়েই ওরা পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উঠতে লাগল। এরপর আমার আর কিছু মনে নেই।
এবার আমার কথা একটু বলে নেওয়া দরকার। আমার বেড়ে ওঠা উড়িষ্যার রাজগাঙপুরে। রাউরকেল্লা থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। চারপাশে পাহাড়ের পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল আমাদের এলাকা। পাহাড়ের গায়ে থোকা থোকা শালের জঙ্গল, আবার কোথাও রুক্ষ। তবে সেই শুষ্ক পাথরের বুক ফেটেই নেমে এসেছে একটা রুপোলি ফিতের মতো নদী। নামটি ভারি মিষ্টি, কোয়েল। সেই নদীর গা ঘেঁষেই আমাদের কোয়ার্টার। মাঝেমধ্যে চাঁদের আলোয় দেখতাম সেই পাহাড়ের গা বেয়ে ভাল্লুক নেমে আসতে।
খুব গরমের সময় ভুট্টা খেতে পাহাড়ি জঙ্গল থেকে হাতির পালও নেমে আসতে দেখেছি। ভুট্টা খেয়ে নদীতে দাপিয়ে চান করত তারা। তবে ওই অরণ্যে চিতাবাঘ আছে শুনলেও কোনও দিন দেখিনি। কিন্তু আছে এটা বিশ্বাস করতাম, কারণ মাঝেমধ্যে দু’একটা গরু ছাগল উধাও হয়ে যেত। তবে এখন সবচেয়ে ভয় মানুষের। কেন? সে কথায় একটু পরে আসছি।
গ্রামে মূলত দু’ধরনের মানুষের বাস। এখানকার বেশিরভাগ মানুষই হল আদিবাসী সম্প্রদায়ের। অনেকেই অভাবের তাড়নায় খ্রিস্টান। ব্রিটিশ সাহেবরা খাবার আর পোশাকের লোভ দেখিয়ে এদের খ্রিস্টান করেছিল। আর কিছু আশেপাশের কারখানায় কর্মজীবী শহুরে মানুষ। যেমন আমরা। আমার বাবা কাজ করতেন কাছেই উড়িষ্যা সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে। আমি পড়তাম ওখানকার ‘রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়’ স্কুলে। গ্রামের আদিবাসীরাও ওই স্কুলেই পড়ে।
বাবার কারখানার পাশেই ছিল আমাদের কোয়ার্টার। তার পাশেই বিরাট হাতিশালা। হাতিশালায় দশ বারোটা হাতি ছিল। গ্রাম থেকে এক কিলোমিটার দূরেই ডলোমাইট খনি। কারখানায় লাইমস্টোন আসত মালগাড়িতে। ইঞ্জিন মালগাড়ি রেখে দিয়ে চলে যেত। হাতি সেসব কামরা ঠেলে আনত। আমরা ছোটোবেলায় খুব মজা করে সেই সব দৃশ্য দেখতাম।
সবার ঘরেই হাঁস মুরগি ছিল। বিকেলে মাঠ থেকে খেলে ফিরে, বাড়ির হাঁস মুরগি চই চই করে ঘরে ঢোকানোর দায়িত্ব ছিল আমার। বিনিময়ে আমি ডিমের বেশি ভাগ পেতাম। সকালবেলা দুধ আনতে গেলে ঝগড়ু ভালোবেসে খেতে দিত পূর্ণ গর্ভবতী গরু মোষের সাঁজো দুধ। ধোঁয়া ওঠা গাঢ় হলুদ রঙের দুধ। ওটা বেচার নয়। এসব খেয়ে আদিবাসীদের মতোই বেশ তাগড়াই হয়েছিল চেহারাটা। তবে গায়ের রংটা শুধু ফরসা ছিল, এই যা! পাহাড়ি গ্রামের ছবি আঁকার ফাঁকে একটু স্কুলবেলার কথা বলে নিই।
আমার সাথে স্কুলে পড়ত যেমন আমাদের কোয়ার্টার-এর চাকুরিজীবীদের ছেলেরা, তেমনি আসত অ্যালেক্স ওঁরাও, জুয়েল মূর্খ, বিরজু মুণ্ডা, শিবু হেমব্রম, এইসব আদিবাসী ছেলেরা। ওদের গ্রাম ছিল পাহাড়ের কোলে মহুয়া গাছ দিয়ে ঘেরা। শীতকালে আদিবাসীরা এই মহুয়া জ্বাল দিয়ে ‘মাহুল’ বানাত। মহুয়ার গন্ধে সারা এলাকা ম-ম করত। সেই গন্ধে অনেক সময়েই পাহাড় থেকে ভাল্লুক নেমে আসত। তারপর দু’হাত দিয়ে মানুষের মতো মহুয়ার হাঁড়ি তুলে ‘মাহুল’ খেত। খাওয়ার পর সে কী হাঁটা! টলতে টলতে মাতাল পায়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে যেত।
এছাড়াও ওরা ভাত পচিয়ে হাঁড়িয়া বানাত। নেশা বেশি হওয়ার জন্য তাতে ‘বাখর’ বলে একরকম গাছের ফল মিশিয়ে দিত। তবে হাঁড়িয়া ফুটিয়ে ঠান্ডা হওয়ার সময়, হাঁড়ির গায়ে যে-বাষ্প জমা হতো, তার নাম ‘রাশি’। এর নেশা মারাত্মক। আদিবাসীরা খেত। আমি কোনও দিন খাইনি। পাকা নেশাড়ু ছাড়া অন্য কেউ সহ্য করতে পারবে না। বুধিয়া বারলা বলে আমার এক বন্ধু ছিল। পাখি মারায় ওস্তাদ। গুলতি দিয়ে কত নানা জাতের পাখি মেরে যে, তার মাংস আমায় খাইয়েছে, এখন ভাবলে প্রায়শ্চিত্ত করতে ইচ্ছে হয়।
আর একটা সাংঘাতিক কথা না বললে গল্প সম্পূর্ণ হবে না। ওরা ঠিক সন্ধে হওয়ার আগে ঘুড়ির সুতোয় বঁড়শি দিয়ে বাদুড় ধরত। বাদুড়ের ডানার চামড়ায় বঁড়শি গেঁথে যেত। তাই বলে আমি কোনও দিন বাদুড়ের মাংস খেয়ে দেখিনি। তবে বাদুড়ের হাড় ফোটানো তেল বাড়ি নিয়ে আসতাম। ব্যথায় বেশ কাজ দেয়। এই সবের ফাঁকেই কখন স্কুল পেরিয়ে গেলাম, বুঝতেই পারলাম না। এবার একটু অন্য কথায় যাব।
আমরা যখন মাঠে বিকেলে ফুটবল খেলতাম, তখন দূরে কবাডি খেলত মুনিয়া, নাচনী, বিজলি। এরা সব আদিবাসী গ্রামেরই মেয়ে। এই বিজলি আবার বিরজুর বোন। ওদের বাবা বীরসা মুণ্ডা হল আদিবাসীদের সর্দার। বিজলির শরীর ছিল কালো পাথরের মতো। যত বড়ো হতে লাগল, মনে হল যেন কোনও ভাস্কর ছেনি হাতুড়ি দিয়ে ওকে কেটে কেটে নির্মাণ করছে। কষ্টিপাথরের মূর্তির মতো। গোধূলির আবির মাখা আকাশে যখন সূর্যটা কপালের লাল টিপের মতো হয়ে যেত, পাহাড়ের কালো ছায়া এগিয়ে আসত ওদের গ্রামে। কিন্তু ভুট্টা খেতটা তখনও সোনালি বাগিচা। ঠিক যেন কানে মাকড়ি, নাকে নোলক আর হলুদ ফ্রক পরা বিজলি।
আমি এখনও যেন বিজলিকে দেখতে পাই বউবাজারের সোনার দোকানে। কাচের শো-কেসের ভেতর। কালো পাথরের গয়না পরা আবক্ষ মূর্তি, ঠিক যেন বিজলি! এখনও মনে হয় সেই দোলের দিনের আবির মাখানোর আবদার কাচ ভেঙে পূরণ করে দিই। সে এক আমার জীবনের উথালপাথাল ঘটনা। আজও মনে পড়ে সেই দোলের দিনের কথা। মানে ওরা যাকে বলত ‘ফাগুয়া’।
ক্রমশ…