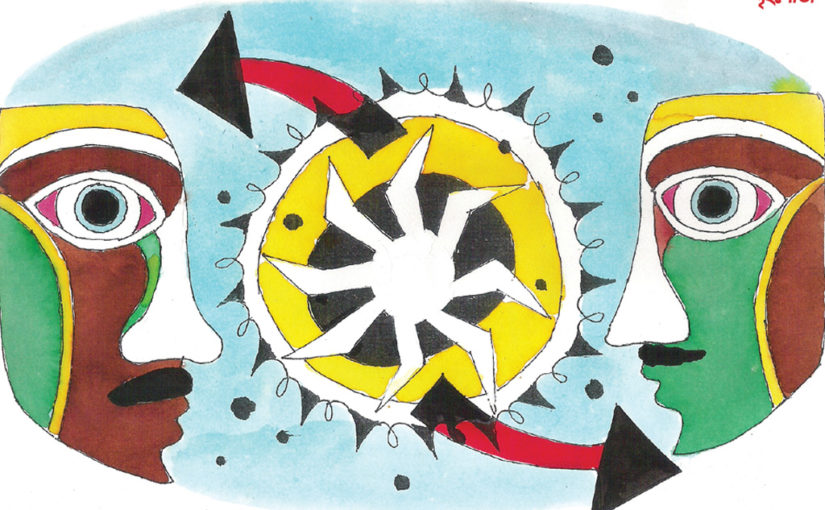বুনো বিড়ালটা এক মোক্ষম শিকার ধরেছে। ঠিক ধরেনি। হদিশ পেয়েছে। পাহাড়ের গর্তে মুখ ঢোকাচ্ছে আবার পিছিয়ে আসছে। দু’পা এগোচ্ছে আবার পিছিয়ে আসছে। শিকার যে একটা জবরদস্ত পেয়েছে সেটা বোঝা যায়, লেজ নাড়ানোর বহর দেখে। তিড়িক তিড়িক করে লেজ নাড়িয়েই চলেছে। এটা তার শিকার ধরার আক্রমনাত্বক শানিত অস্ত্র। শিকার রেঞ্জে এলে তবেই সিওর শট। শিকার পিঙ্গলাও পেয়েছে। তিনটে ছোটো ছোটো পাথরের টুকরো বসিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে। একটা ভাঙা কড়াইয়ের ভিতরে উই পোকার ডিম ফ্রাই হচ্ছে। পিঙ্গলার দৃষ্টি এড়ায়নি। ঘরের থেকে বর্শাটা এনে উনুনে লাল করতে থাকে। ঘর বলতে পাহাড়ের গুহা। গুহাটা বেশি বড়ো নয়। একটু বড়ো সাইজের ফোকর। তারই মধ্যে জঙ্গলের কাঠ দিয়ে তক্তপোশ বানানো। বুড়া বাপটার জন্য। বুড়া বাপটা একটানা কেশেই চলেছে। সূর্যের উদয় অস্ত আছে। বুড়ার কাশিতে উদয় আছে, অস্তটা নেই। থেকে থেকে চ্যাঁচায়– এ বিটিয়া ভুখ লাইগছে রে।
গর্তের মধ্যে মুরগিটা ঘাপটি মেরে বসেছিল। বেচারা মুরগি! পালাবার বিকল্প পথও নেই। দেহটা মুরগির মতো। মুখটা মুরগির মতো নয়। মুখটা থ্যাবড়ানো। প্যাঁচার মতো। বনবিড়ালটা তাক করেছে মুরগিটাকে। পিঙ্গলা ভাবছে, আর বিড়ালটার গতিবিধি নজর করছে। পাহাড়টা সবার জন্য খাবারের বন্দোবস্ত করেছে। যত উন্নাসিকতা মানুষ নামক জীবগুলোর খাদ্যের বেলায়। বিড়ালটা এক কিম্ভূত কিমাকার আওয়াজ করে লেজটা সটান বীর বিক্রমে খাড়া করে মুরগির মাথাটা কামড়ে ধরে। হতভাগা মুরগি। মরণ যন্ত্রণার আর্তনাদটুকু করার পর্যন্ত সময়ও পেল না। ততক্ষণে পুরো মাথাটাই বিড়ালের মুখের ভিতর। পিঙ্গলার মনে এক অদ্ভুত রকমের জিঘাংসার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন ছিটকে বেরোতে চায়। দু’দুটো দিন অনাহারে থাকতে থাকতে তারই সামনে বনবিড়ালটা খাবারটা চিবোচ্চে। পিঙ্গলা ঠিক থাকতে পারে না। আগুনের ভেতর থেকে তপ্ত বর্ষাটা বার করে হিংস্র বাঘিনীর মতো বিড়ালটার পুচ্ছদেশে সেদিয়ে দেয়। হত্যার উন্মত্ত আনন্দে পিঙ্গলার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে।
দেবার মেজাজ আজ বেশ রিলাক্সড মুডে। গতকাল ত্রিদেবের মেয়ের বিয়ের ভূরিভোজনে শরীর মন দু’টোই বেশ চাঙ্গা। ভুরিভোজনের চাইতেও বড়ো, খাবারের পুঁটুলি লাঠির ডগায় নিয়ে পরমানন্দে পাহাড়ের বেষ্টনী ডিঙিয়ে চলেছে কুঠুরির দিকে। উদরস্থ খাদ্যবস্তুর পঁচাত্তর শতাংশ পথেই খরচ করেছে। বাকিটা এখনও পেটে গজগজ করছে। এসব অনায়াসে হয়নি। আমদানি করা খাসি কেটে মাংস থেকে জ্বালানি জোগাড় করা ছাড়াও নানা রকম ফাইফরমাসের বিনিময়ে হয়েছে।
পিঙ্গলা বসেছে বর্শার ফলা দিয়ে মৃত বিড়ালটার চামড়া ছাড়াতে। থেকে থেকে গুহার ভিতর থেকে বুড়ার সেই ফাটা কাশির আওয়াজ– পিংলা, ভুক্ষ লাইগছে রে। পিঙ্গলা সাড়া দেয় না। আপন মনে কাজ করে আর গজগজ করে। বুড়ার অভিভাবক পিঙ্গলা। অভিভাবকের ক্ষুদা তৃষ্ণা থাকতে নেই। পেছন দিক থেকে দেবা লম্বা লাঠির মাথায় পুটুলি নিয়ে পিঙ্গলার পিছনে দাঁড়ায়।
– এ পিংলা, এ-তু কি করছিস বটেক? পিঙ্গলা ঘাড় ঘুরিয়ে এক নজর দেখে নিয়ে বলে– কেনে, দিখতে লাইরছিস? জ্বলন, পেডের জ্বলন। ঘরকে দ্যাখ, বুড়ার মরণ ভুক্ষ লাইগছে। আবার সেই আওয়াজ– কুছ খেতে দে নারে। দেবা এক পলক দেখে নিয়ে বলে– তুয়ার ভুক্ষ লাগে নাই?
– হুঃ, মুয়ের ভুক্ষ লাইগতে নাই রে, দেবা। দেবা লাঠির মাথায় বাঁধা পুটুলিটা খুলে নিয়ে বলে– পিংলা, এ কামডা মু করছি। তু ঘরকে যা। এ খাবারডা তু খা, আর বুড়াকে দে।
– তু খাবেক নাই কেনে? মু তো খাইছি বটেক।
তিলাবনী পাহাড়। ছোটো নাগপুরের মালভূমি অঞ্চলের এক মিনি সদস্য। দৈত্যাকার নয়। শান্তস্নিগ্ধ। শীতের কুয়াশায় অলসতায় আকাশের বুকে মাথা এলিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ভৌগোলিক অক্ষরেখায় নামটা আছে। বাহ্যিক দাম্ভিকতা নেই। অন্তরে আছে। কোলে কোলে অজস্র গ্রাম। শ্রাবণের ধারা কৃষি জমিকে উর্বর করে। তিলাবনী বুক চিরে লোকালয়ের সঙ্গে রাস্তা তৈরি করেছে। জীবনযাত্রা বর্ণময় না হলেও দুর্বিষহ নয়। তারই অপর প্রান্তে বেজম্মার মতো জন্ম নিয়েছে জিয়ারা গ্রাম। বঞ্চিত। অবহেলিত। পদদলিত। শ্রাবণের রক্তরস নিংড়ে ছিবড়ে করে সমৃদ্ধ করেছে পাশেই পিচুলা গ্রাম। কোল দিয়ে অবারিত জলধারা সমতলে নদীর চেহারা নিয়েছে। পোশাকি নাম দ্বারকেশ্বর। জিয়ারা তার অবাঞ্ছিত বেয়ারা জারজ সন্তান। জিয়ারা অপভ্রংশ নাম।
রুক্ষ শুষ্ক। বছরের পর বছর ধরণে (খরা) বাঁজা মরুভূমিতে পরিণত। আর্তনাদ নেই। কলরব নেই। শক্তি নেই বলে। তিলাবনীর রুক্ষ পাথরের দেয়ালে সেঁদিয়ে থাকা মৃতদেহের দুর্গন্ধ চিল-শকুনের নাকে বিরিয়ানির স্বাদ এনে দিচ্ছে। নীল আকাশ কবে দেখা গেছিল কে জানে। গোটা আকাশ চিল-শকুন দখল করে নিয়েছে। ভাবলেশহীন তিলাবনী নীরব দর্শক। নীরব দর্শক সরকারি ত্রাণ দফতরও। ত্রাণ নিয়ে এ গ্রামে কেউ পা মাড়ায় না। ভোটও নেই। রাস্তাও নেই। বেজম্মা গ্রামে কারও মমত্ববোধ কাজ করে না।
শীতে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা। গ্রীষ্মে সূর্যের অগ্নিবৃষ্টি। এসবে তিলাবনী ভাগ বসায়নি। কেড়ে নিয়েছে শুধু শ্রাবণের ধারা। দেবা বসেছে উনুনের পাশে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া দেহটাকে সেঁকে নিতে। ঠিক সেঁকে নিতে নয়। বিড়ালের ঠ্যাংটাকে আগুনে ঝলসে নিতে। আলকাতরার পোঁচ লাগানো মুখে কোটরগত চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। অনাহারে শীর্ণ হয়ে যাওয়া হাত দুটো দিয়ে বিরানির মাংস খেতে খেতে পিঙ্গলা বলে– বেসাম খাবারডা ভালাই আনছিস বটেক। ইতে হরদিন কুছু খিতে লাইরবেক। দেবা, ই খাবার তু কুথা থেকে আনছিস? কেনে, পিচলার তিদেব বাবুয়ার মিয়ার বিয়া লাইগছে যে।
– ওহঃ, তা তু চোরি করিছ নাই ত?
– কেনে? বাবুয়ার ডেড়াতে কাম করলাম যে। উস লাইগা খাবারডা দিল ত। দেবা আগুনে লাকড়িটা খানিক ঠেলে দিয়ে বলে– বুড়া খাবারডা খাইছে? পিঙ্গলা ক্ষিপ্রতা নয়, অনুযোগের সুরে বলে– মুর বাপকে বুড়া বলবিক নাই। দেবা অনুযোগের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারপর রান্নার রসদ যুগিয়ে বলে– গুস্সা করছিস কেনে পিংলা। তুয়ার বাপ ত মুয়ার বাপ আইনছে বটেক।
পেটে মা লক্ষ্মী গিয়ে পিঙ্গলার খিটখিটে মেজাজ এখন শান্ত। বুড়া বাপটা ফাটা কাশি বন্ধ করে শীতের আড়ষ্টতায় দুই হাঁটু মাথা এক করে তিন মাথার বুড়া। মন বুঝে দেবা সুপ্ত ইচ্ছাটা বলেই বসে।
– পিংলা মিলায় যাবি কেনে?
– মিলা! কোন মিলা?
– শবর মিলা
– কুথা সে?
– রাজনা গাড়ে।
– আরে বা প! সে তো বহত দূর আছে বটেক। টঙ্কা লাগবেক তো।
– মুয়ের আছে। চলনা কেনে?
– ডাকাইতি করলি না-কি রে?
– কেনে কাম জুটাইছি যে। উ বাবুয়ার ডেড়ায়। হপ্তায় শ-টংকা দিবে। একশো টাকার একটা নোট বের করে বলে– ই দেখ না কেনে।
ত্রিশংকর হালদার এখানকার আদিবাসী নয়। বহুদিন আগে পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল ছেলেটা জীবিকার সন্ধানে ভাসতে ভাসতে তিলাবনীর পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। পেশায় কোয়াক ডাক্তার। কুমিরের সাথে সখ্যতা না করলে জলে বাস করা যায় না। শ্রম দিয়ে চিকিৎসায়, সেবায়, ধীরে ধীরে অপরাধপ্রবণ শবর জাতিদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে ওঠে। হয়ে ওঠে শবর জাতির দেবতা। কতকটা বেঁচে থাকার তাগিদ কতকটা মানবিকতা, মূল্যবোধের তাগিদে সমাজের মূল স্রোতে ফেরাবার মরিয়া চেষ্টা। ত্রিশংকর এখন দেবতা ত্রিদেব। তিলাবনীর কোলে মাথা গুঁজেই ত্রিশংকর জীবনের ধারাটা বদলে ফেলেছে। এরা বড়ো অসহায়। অশিক্ষা অজ্ঞতা যাদের একমাত্র অবলম্বন, হিংস্রতা ছাড়া বেঁচে থাকার পথ থাকে না। কাজটা যে সহজ, অনায়াসলভ্য তাও নয়। অনেক অত্যাচার, লাঞ্ছনা সহ্য করেও একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে জীবনের মধ্যগগনে বসে ভাবছে– সভ্যতার বিকাশ, উন্নত প্রযুক্তির ছোঁয়া স্পর্শ করাতে পারলাম কই? অশিক্ষা, নির্বুদ্ধিতাকে কাজে লাগিয়ে সম্পদ লুঠেরা অতি বিপ্লবীর দল বারে বারে কাজে লাগাচ্ছে। একদম বিফলে গেছে ঠিক তাও নয়। একজনকে অন্তত পেরেছে। দেবা। কাক কাকের মাংস খাওয়ার অনাবিল আনন্দে নয়। ধবংস নয়। দেবা আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মত্ত।
দীর্ঘ অনাহারে গুরু ভোজনের গুরু ভার বুড়া বহন করতে পারেনি। চিল শকুনের দল পজিসন নিচ্ছে। একটু একটু করে রাতের আঁধার নেমে আসছে। চিল-শকুনদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। গুটি গুটি পায়ে সরে যাচ্ছে। জায়গা নিল তিলাবনীর ফোকরে। হিমেল হাওয়ায় উনুনের পাশে বসে পিঙ্গলা আর দেবা উষ্ণতার নির্যাস নিচ্ছে। দেবা বলছে
– ভোর রাইতে এক স্বপন দিখলাম বটেক। পিঙ্গলার তর সয় না।
– কি স্বপন দিখলি? দিখলাম, জিয়ারা থিকা রাস্তা বানায়ছি পিচলাতক। কোতো গাড়ি আইছে। কোতো গাড়ি যাইছে। তিলাবনীর বুক ফাটায়ে জলের তোড় আনছি। মাঠ ডোবা জলে টইটম্বুর হইছে। মাঠ সবুজ। সগগলে কাম লইছে। পিঙ্গলা উদাস মনে দেবার স্বপ্নের বাসনা গিলছিল। এ বাসনা পিঙ্গলারও ছিল। সুপ্ত রেখেছে। প্রতিদিন যাদের মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে হয়, এ স্বপ্ন পাহাড়ের চূড়ায় বসে ভৈরবী রেওয়াজের মতো। বাস্তবে ফিরেছে পিঙ্গলা।
– তিলাবনীর বুক ফাটায়ে রাস্তা বানায়ছিস?
– হ।
– জল আনছিস?
– হ।
– কোতো দিন সিনান করিস না বল না কেনে? তুয়ার মাথাডা গরম হইছে।
– কেনে?
– তু পাগল হইছিস বটেক।
– পাগল হই নাইরে পিংলা। উ রাস্তা হামি বানাবই। দিখে লিবি। উ চিল-শকুনের দল মু তাড়াবই। সগ্গলে জমিনে কাম করবেক। বাবুয়া কইছে– তু-ই পারবিক দেবা। আরও কইছে– হামাদের ভদ্দর হইতে হবেক। ভদ্দর সমাজ তৈয়ার কইরতে হবেক।
– তু থাম দেবা। উ বাবুয়া তোর মাথাডা খাইছে। উয়ারা ভদ্দরলোক বাবুয়া আছে। পেটে দানা পানি আইনছে। তাই উসব কতা কইছে। মু-দের পেটে দানা পানি নাই।
– উ সব কুথা মুদের মানাইছে না।
– চুপ যা পিংলা। উ বাবুয়া দেব্তা আইনছে রে। পাশে রাখা পুঁটুলিটার ভিতর থেকে একটা নাইটি বার করে বলে– ই দেখ্ না কেনে। ইটাকে মিয়াদের ডেরেস বলে।
– পর। পর না কেনে। দাঁড়া মু পড়ায় দিছি। দেখ্, দেখ্ মুকেও দিছে। প্রথম। এই প্রথম পিংলাকে নতুন রূপে, নতুন ভাবে দেখল। চোখ ফেরায় না। শরীরে, মনে এক অদ্ভুত শিহরণ। কি অপরূপ শোভা! গুছিয়ে ভাবতে পারে না। সদ্য উত্থিত যৌবনের চিহ্নগুলো শুকিয়ে ফলন্ত লাউগাছ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। ভাবছে মিয়াটা পেট পুরে দুটো খিতে পাইরত! উঠে দাঁড়ায়– নাঃ ঘরকে যাই।
ত্রিশংকর হালদারের বাজার আজ বড়ো খারাপ। সকাল থেকে টেবিল চেয়ার পরিষ্কার করে চুপচাপ বসে। কোনও পেশেন্ট নেই। মেয়েটার বিয়ের পর ঘরটা একেবারে শুন্সান। বউ মরেছে মেয়েটাকে জন্ম দিতে গিয়েই। বয়েস বাড়ার সাথে সাথে সে স্মৃতি আজ ঝাপসা হয়ে আসছে। পেশেন্ট যে একেবারে হয়নি ঠিক তাও নয়। বউনি খদ্দের। একটি কচি মেয়ে গণশাকে ধরতে ধরতে চেম্বারের বেঞ্চে শুইয়ে দেয়। কচি বউটা রাগে গরগর করতে করতে বলে– দ্যাখ্ কেনে বাবুয়া, ডেড়ায় চাউল নাই। বাচ্চা দুটো খিতে লাইরছে। আর উ কাম করবেক নাই। শুধু হাড়িয়া গিলবে। হর রাইত ঘরকে যায় নাই। সক্বালবেলা দিখি জমিনে শুইয়া ঘ্যোৎ ঘ্যোৎ কইরছে। সারা শরীল থিকে খুন ঝইরছে। উ মুয়ার শরীলে জ্বলন ধরায় দিল। ত্রিশংকর ডেটল জল দিয়ে ধুয়ে, বেটাডিন তুলায় লাগাতেই গণশার আর্ত চিৎকার।
জ্বলন ধইরচে রে ডাক্তার বাবুয়া। ত্রিশংকর ওর চিৎকারে কান দেয় না। ব্যান্ডেজটা ভালো করে বেঁধে দেয়। তারপর টক্সাইড ইঞ্জেকশান প্রস্তুত করতেই আবার চিৎকার– বাবুয়া জ্বলন ধইরছে। তু আবার সূঁচ লাগাইছিস? মরে যাবেক বাবুয়া। উটা তু দিস না বাবুয়া। ত্রিশংকর ডাক্তার মিচকি মিচকি হাসছে। ডাক্তার আদিবাসীদের ভাষা বোঝে। বলতে পারে না। এরাও ডাক্তারের ভাষা বোঝে। ভাব বিনিময়ের বোঝাপড়াটা এরকমই। ডাক্তার বলছে– জ্বলন ধরছে? মরে যাবি? জখমটা তো বেশি হয়নি। তা সারারাত জমিনে পড়েছিলি যখন জ্বলনটা কোথায় ছিল? ছাইপাঁশ গিলবার সময় জ্বলনের কথাটা মাথায় ছিল না? এভাবে বেঘোরে প্রাণটা দিচ্ছ কেন বাপু? এসব ছাড়। বেঘোরে মরবি। মন দিয়ে কাজ কর।
সংসারে অভাব থাকবে। কষ্ট থাকবে। বউ বাচ্চা নিয়ে দুঃখ কষ্টে সংসারটা চালা। এর মধ্যেই শান্তির ঠিকানা খুঁজে পাবি। বুঝলি তো। বাধ্য ছাত্রের মতো গণশা ঘাড় নাড়ে। পকেট থেকে ত্রিশংকর পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বার করে বউটাকে দিয়ে বলে– নাও, আজকের মতো বাচ্চাগুলোকে কিছু খাওয়াও। বউটা কোঁচড়ে টাকাটা গুঁজে নিয়ে পা দুটো ধরে প্রণাম করে বলে– বাবুয়া, তু দেবতা আছিস বটেক। গণশা কিছু বলল না।
বউ-এর ঘাড়ে হাত রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল। শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে ছলছল দৃষ্টিতে এক ঝলক দেখে নিল। মনের অভিব্যক্তি। হে মহামানব, তুমি আছ বলেই শবর জাতি আছে। অবহেলিত, ঘৃণিত মানুষগুলো এখনও অতল তিমিরে চলে যায়নি। সকালবেলা বউনি দক্ষিণাটা এভাবেই হ’ল ত্রিশংকর হালদারের।
নিকম্মা দিন। কাজ না থাকলে ত্রিশংকর ভাবে। টেবিলের উপর বাঁ কনুইটা রেখে গালে হাত রেখে অনাবিল ভাবনার নদীতে ডুব দেয়। কতটুকু সামর্থ্য আমার। ভাবে জিয়ারা গ্রামের কথা। সেখানে শবর আদিবাসীদের কথা। বছরের পর বছর খরা। পাহাড়ের ঝরনা ধারা নামে না। অনাহার অপুষ্টিতে ক্রমশ ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে গ্রামের মানুষ। শিক্ষিত সমাজ গায়ে অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠীর লেবেল সেঁটে দেয়। কালেভদ্রে ছিটেফোঁটা বৃষ্টিতে যা ফসল হয়, সেখানেও সম্পদ লুঠেরা অতি বিপ্লবীর মুখোশ পরে চালায় নিরীহ মানুষের উপর তাণ্ডব। কাজে লাগায় এই অশিক্ষিত অজ্ঞ বুভুক্ষু শবর জাতিদের। ভাবনার শ্বাস সীমিত। সেই ভাবনার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসলে আর এগোতে পারে না।
দেবার ঘরটা বেশ মজবুত। এখানটা তিলাবনীর ঢালটা নেমে এসে লম্বা একটা ছাদের আকার নিয়েছে। দেবা বেশ খানিকটা জায়গা বুনো জঙ্গলের ডালপালা দিয়ে বেড়া দিয়ে নিয়েছে। ঝড় বৃষ্টি রোদের তাপ নেই। বেশ নিরাপদ। দেবা বসেছে ছেনি ঘষে ঘষে ধার দিতে। মনে দিগন্ত বিস্তৃত স্বপ্ন। তিলাবনী যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে পিচুলা আর জিয়ারা গ্রামকে বিভক্ত করে রেখেছে। পাহাড়ের বুক চিরে রাস্তা তৈরি করবে। দুটি গ্রাম থাকবে একই মায়ের সহোদরের মতো। দেবা অশিক্ষিত। তথাকথিত মূর্খ। প্রযুক্তিটা জানে। মনে মনে রাস্তার ব্লু প্রিন্ট ছকে নিয়েছে। তিলাবনী দেবার কাছে মায়ের মতো। শুধু দেবা কেন সমস্ত শবর, কুর্মী আদিবাসীদের কাছেই মাতৃতুল্য। তবু কেন জানি কোন এক অজ্ঞাত কারণে জিয়ারা গ্রামের উপর তার এই বৈমাত্রেয় আচরণ। অভিমানে, ক্ষোভে চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে। তবু মা-তো! ধরিত্রীর উপর সুবিস্তৃত এলাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার ভারসাম্য বজায় রাখার দায়ভার তো সন্তানকেই নিতে হয়। দেবা মনে মনে ভাবছে কীভাবে রাস্তাটা সেপ্টিপিনের মতো ঘুরে ঘুরে পিচুলা গ্রামে মিশবে। দু’টো গ্রাম মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। পরিকল্পিত সৃষ্টির আনন্দে আরও একবার চোখ দুটো চিক্ চিক্ করে ওঠে।
কার্তিকে চলেছে দুর্ভেদ্য পাহাড় ডিঙিয়ে এঁকেবেঁকে এবড়োখেবড়ো পাথরের খাঁজে খাঁজে পা চালিয়ে। কাঁধে দু’হাত দিয়ে ধরা একটা ছাগল। দেবা দেখেছে। ছেনিতে শান দিতে দিতে হাঁক পাড়ে– এ কার্তিকে, এ কার্তিকে। সাড়া দেয় না, আরও তরতর করে পা চালায়। ছেনিটা রেখে পিছু নেয় দেবা। কার্তিকে দাঁড়ায় না। আরও তাড়াতাড়ি পা চালায়। দেবা এবার দৌড়। হাঁপাতে হাঁপাতে সামনে এসে দাঁড়ায়।
– ছাগলটা তু কুথা থিকা আনছিস বটেক? কার্তিকে নিরুত্তর। তাড়াতাড়ি পা চালাতে গিয়ে গল্পটা তৈরি করতে পারেনি। সত্যিটা বলতেও মনের সাহস জোগায় না। দেবার কাছে গোটা গ্রাম ঋণী। বিপদে আপদে সবসময় পাশে দাঁড়ায়। শরীরের রক্তরস নিঃশেষিত করে অপরাধপ্রবণ লেবেলটা মোছার চেষ্টা করছে। ভদ্র সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছে। এ শিক্ষাটা পেয়েছে ত্রিদেব বাবুয়ার কাছ থেকে।
– তু চোরি করলি বটেক?
ছাগলটা ছেড়ে দিয়ে মাথা নীচু করে থাকে। তারপর বলে
– ছিনায়ে আনছি বটেক।
– ছিনায়ে আনছিস? ভদ্দর হবিক নাই? ভদ্দর সমাজ মুদের ঘৃণা কইরছে। উ দাগ মুছতে দিবিক নাই?
– হ হ ভদ্দর সমাজ! পেডের জ্বলন ভদ্দর সমাজ মুছে নাই রে, দেবা। বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে।
– তুয়ার খাওন হয় নাই তো মুকে জানালি না কেনে? চল্, চাড়ে চাড়ে চল।
– কুথা?
– কেনে মুয়ার ঘরকে। মুয়ার খাবারডা যা আছে ভাগ করে লিবেক। যেতে যেতে দেবা বলে– মুয়ের স্বপনডা মুই একা পূরণ কইরতে লারবেক। এ গিরামের সগ্গলে কাম কইরতে হবেক। স্মরণে রাইখবি, তুয়ের খতরা তো মুয়ের খত্রা। সগ্গলের খত্রা।
বুদ্ধিটা ত্রিশংকরই দিয়েছিল। বলেছিল
– শোন দেবা, রাস্তাটা প্রথমে বেশি চওড়া করবি না। একজন যাতায়াত করার মতো। মনে রাখবি তিলাবনী তোদের মা-বাপ। পাহাড়ের আড় দেখে দেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাস্তাটা হবে? জনপ্রতি দু’টাকা করে নিবি। তারপর বড়ো রাস্তা। পেটে লক্ষ্মী-নারায়ণ ঢুকে গেলে কার্তিকের ভোঁতা বুদ্ধির খোলসটা থেকে খানিকটা সতেজ হয়েছে। তা ইখন পেড চালাইছি কি করে? ঘরে ইকটা বাচ্চা। বউ-ডার আবার পেড হইছে। হব হব কইরছে। চইলতে লাইরছে।
– তু এক কাম কর। মুয়ের লগে বাবুয়ার ডেড়াই যাবেক। উ দেবতা একটা কাম জুটাই দিবেক। ই নে, পিরানডা পর। ছাগল ডা লিয়ে যা, কাল মালকিনকে ফিরায়ে দিবেক। একটা পুঁটুলিতে কিছু চাল দিয়ে বলে– ইটা লিয়ে যা। বউ-ডা, বাচ্চা খাবেক কি? মনের ক্ষিপ্ততার, ঝাঁঝ কেটে গিয়ে এখন লাউডগা সাপ। শুধু মনে মনে ভাবে। বয়সে দেবা আমারই মতো। অথচ আমাদের মতো এই জংলা মানুষটার মধ্যে মহামানবের মহা-প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল কে? শান্ত, অবনত মস্তকে বলে– ইকটা কুথা বলবেক দেবা? বল্ না কেনে? কার্তিকে ছাগলটার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে– ইটা তুয়ার কাছে রাইখ রাইতডা। কাল দু’য়ে দু’য়ে ফিরায়ে দিবে।
মহাপ্রাণটা প্রতিষ্ঠা করেছিল ত্রিশংকর। প্রতিষ্ঠা করেনি। দেবার মধ্যে উন্নত সভ্যতার চেতনা জাগিয়েছিল। দিয়েছিল বেঁচে থাকার লড়াইয়ের মন্ত্রণা। সেই মন্ত্রণার বীজ দেবা একটু একটু করে শবরদের মধ্যে রোপন করেছে। সবটা পারেনি। কিছুটা পেরেছে। সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে কার্তিকে, পিঙ্গলার মধ্যে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে। ত্রিশংকর শবরদের দিয়েছে অনেক কিছুই। ত্রিশংকর পরামর্শ দিয়েছে। হেমন্ত চলে গিয়ে শীত আসব আসব করছে।
– দেখ দেবা, ধানপাকার সময় হয়েছে। পিচুলার গ্রামে এখন অনেক কাজ। প্রতিষ্ঠিত পরিবারে পুরোনো লেপ কম্বল কিছুটা মজুরির বিনিময়ে চেয়ে নে। আর একটা কথা মনে রাখবি। যেখানেই সম্পদ, সেখানেই লুঠেরা। যত সম্পদ। তত লুঠেরা। সেই সম্পদ লুঠ করার চেষ্টা চলে অবিরত। স্বনামে। বেনামে। কখনও অতি বিপ্লবী মুখোশ পরে তাণ্ডব চালায়। ভণ্ড সাধুর দল আড়াল থেকে সাহায্য করে। হিংস্র পশু গেরস্থের সংসারে এসে পোষ মেনেছে। সব কথার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। এটুকু বুঝতে পেরেছে, মনের ভিতর ঘুমন্ত সৈনিকটা জাগিয়ে তুলতে হবে। আসন্ন শীতে রাতের আকাশটা মেঘমুক্ত। খোলামেলা জায়গায় তারাগুলো কিত কিত খেলছে। দেবা সেই আকাশে চোখ রেখে একান্তে ভেবে চলেছে। দেবা ডেরায় বসে জংলি কাঠ বিছানো শুকনো জঙ্গলে একসময় শ্রান্ত দেহটাকে নিদ্রার কোলে ছেড়ে দেয়।
মানবিক মূল্যবোধ, চেতনা কম দামে পাওয়া যায় না। মূল্য দিতে হয়। অনেক মূল্য। হয়তো বা জীবন দিয়েও। মনের দিক থেকে ত্রিশংকর প্রস্তুতই ছিল। জীবনের সুখ, দুঃখ, বাঁচা মরা সব কিছুই ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে যারা নির্লিপ্ত থাকে, ত্রিশংকর সে ধাতুতে গড়া নয়। রাতের আকাশ। এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। ওই এক মুঠো আকাশটার ভাগীদার তো সবাই। অথচ তারাগুলো অনাবিল আনন্দে যখন খেলে বেড়াচ্ছে, পিছন থেকে লম্পট মার্কা মেঘগুলো চুপিচুপি গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। মেঘ না মেছো চিল! জীবনটা আসলে সবলের জন্য। কৌশলবাজদের জন্য। সবলেরা গিলতে চায় দুর্বলকে। কৌশলবাজ ক্যারাটে প্যাঁচ মারে সরল নির্ভেজাল মানুষগুলোকে। এটা আদি অকৃত্রিম।
ত্রিশংকর এখন অনেক বস্তুনিষ্ঠ। জীবনদর্শনটা খুব কাছ থেকে দেখেছে। ত্রিশংকর ঘরে ঢুকে দরজার খিলটা এঁটে দেয়। শুয়ে শুয়ে ভাবছে। সময় বেশি নেই। আক্রমণটা আসবে। প্রথম আঘাতটা তার উপরই। অনেক ঘুরপথে অস্ত্রটা দেবার হাতে তুলে দিলাম। আগ্নেয়াস্ত্রের ভারটা বইতে পারবে তো? এলোমেলো ভাবনা। সেই ভাবনাগুলি মনে ক্লান্তি এনে দেয়। সেই ক্লান্তিতেই ত্রিশংকর ঘুমিয়ে পড়ে। পাতলা ঘুম। হঠাৎই ঘুম ভেঙে যায়। একঝাঁক বুটের আওয়াজ। এগিয়ে আসছে। ঝরে পড়া শুকনো পাতাগুলির ভুষ্টিনাশ করে বাড়ির চারপাশ ঘিরে ফেলছে। পালাবার পথ নেই। দরজায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে গোটাকতক হায়েনা। চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে। সারা মাথা মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা। শুধু হায়েনার দাঁতগুলো চিক্ চিক্ করছে। মত্ত উল্লাসে বলছে। ই বাবুয়া, তু ডাইকলি না। মুয়েরা আইছি। তুয়ার ব্যামো সারাইতে। পাশ থেকে আর এক হায়েনা বলছে– তু কে সূঁচ ফুটাইছিল না? তুয়ার ব্যামো সারাইবার লিগা। তু এক কাম কর। উয়ার ব্যামো সারাই দে বটেক। সূঁচ ফুটাই দে না কেনে? উয়ার ব্যামো সারবেক। অনেকক্ষণ থেকে গলার আওয়াজটা পরিচিত মনে হচ্ছিল। ‘ব্যামো’র কথাতে ত্রিশংকরের চিনতে অসুবিধা হয় না।
– তুই গণশা না? তু-ই আমাকে মারতে এসেছিস? গণশা মুখে কথা নেই। শুধু মনে মনে বলে
– তুমি দেবতা। যদি পারো ক্ষমা করে দাও প্রভু। তুমিই তো পারো অধমকে ক্ষমা করতে। যে জালে আমি জড়িয়েছি। এছাড়া আমার যে আর পথ খোলা ছিল না। হায়েনার দল সাংকেতিক নামে কথা বলছে। ‘র’ ‘গ’ ‘শ’ নামে। পাশ থেকে বলছে
– ‘গ’ মশিনডা চলা কেনে?
‘গ’ বলছে,
– মশিনডা কাম কইরতে লাইরছে। সময় নষ্ট করে না। দুম দুম করে দুটো আওয়াজ। বার্ধক্যে শক্তি বেশি ধরে না। ত্রিশংকরও মৃত্যু যন্ত্রণায় বেশি সময় নষ্ট করেনি। অল্প ক্ষণেই ঘরের কড়িকাঠে চোখ দুটো স্থির করে শান্ত হয়ে যায়। প্রস্তাবটা গণশাই দিল। বলে – ইকটা কাম করি। ডেড়ায় আগ লাগাই দি কেনে?
– লগই দে। গণশা সাইকেলের টায়ারগুলি সারা ঘরে ছড়িয়ে দেয়। সদর থেকে বাতিল টায়ার কাঁধে করে নিয়ে আসে। আগুন লাগাতে এগুলি উপাদেয় পদার্থ। আগুন লাগায়। মনে মনে বলে– দেওতার সৎকারডা ত হউক বুটেক।
অমাবস্যার রাত। বাইরে মিশকালো ঘন অন্ধকার তিলাবনীকে গ্রাস করেছে। আবার দুম দুম করে আওয়াজ। ‘র’ ‘শ’ ইত্যাদি পিছন ফিরে তাকায়। টর্চ মারে। গণশা পড়ে আছে। তখনও ঠোঁটটা থর থর করে কাঁপছে। কিছু বলতে চাইছে। নব আগন্তুকেরা সে ভাষা বোঝে না। তিলাবনী বুঝেছে। সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি। দেব্তা তুয়ার মরণ হয় নাই। মরণ হইছে মুয়ের। মরণ হইছে শবরদের। সেই অন্ধকারে হিংস্র দানবের দল মিলিয়ে গেল।
বসন্ত আসতে ঢের দেরি। হোলি খেলাও শুরু হয়নি। শুরু হয়েছে রক্তের হোলি খেলা। ত্রিশংকরের রক্ত দিয়ে। গল্পটা এখানেই শেষ হলে হয়তো ভালো হতো। সব গল্প তো শেষ হয়েও হয় না। কারণ ত্রিশংকরের রক্তের বীজ দিয়ে জন্ম নিয়েছে আগামীদিনের লড়াইয়ের বুনিয়াদ। শবরদের লড়াই। বেঁচে থাকার লড়াই।
শীতকাল না এলেও শীত এসে পড়েছে। গ্রীষ্মেও অনাহুতে দল আগে ভাগে ঢুকে পড়ে। তিলাবনী শত সহস্র হাত প্রসারিত করে চারিদিক বেষ্টন করে রেখেছে। তিলাবনীর অবাঞ্ছিত জিয়ারা গ্রামের জলবায়ুর বন্দোবস্তটা এরকমই। দেবার কাঁধে লম্বা লাঠির মাথায় এক পুঁটুলি। পুঁটুলি ঠিক নয়। একটা বস্তা। গা দিয়ে তখনও গলগল করে ঘাম ঝরছে। বস্তাটা পিঙ্গলার ডেরার সামনে ধপাস্ করে ফেলে। একটা বিরাট কম্বল বার করে ললিত মোহনের বুকে চাপিয়ে দেয়। মনের ভিতর এক আনন্দের ঝিলিক মারে।
– ই বাপ, শরীলডা গরম হইছে না বটেক? জারে বহুত কষ্ট পাইছিস বটেক। আর কইরতে লাইরবেক। আর একটা কম্বল পিঙ্গলার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বলে– পিঙ্গলা কিমন লাইগছে বটেক।
ভিন্ গাঁয়ে ভিন্ মজুরিতে দেবার পকেট ভারী। আচমকাই পিঙ্গলার পিঠে হাত পড়ে যায়। মুহূর্তে পিঙ্গলার সমস্ত শরীরটা চনমন করে ওঠে। চোখে চোখ রেখে দুটি হৃদয় ভালোবাসাময় হয়ে ওঠে। পিঙ্গলা মনে মনে বলে– মু ত তুয়ার পরানে হারায়ে গিছি বুটেক। যৌবনের বুকে ফুটে ওঠে নব পত্রিকার জৌলুস। দেবার বুকে তখন দহনীয় বৈশাখ। মনের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ছে রং মশালের আলো। দু’টি হূদয় ভালোবাসার গাঙে হারিয়ে, সময়কে বয়ে যেতে দেয়। বাধা দেয় না। ডেরার বাইরে আগাছার মতো বেড়ে ওঠে পাহাড়ি ফুলের ঝাড়। দেবা এক গোছা ফুল নিয়ে বলে– চুলডা জড়ায়ে নে না কেনে? বসন্ত আসতে ঢের দেরি। এলেও এ গাঁয়ে উঁকি মারে না। না এলেও পিঙ্গলার মনে এসেছে। সেই বসন্ত পিঙ্গলাকে করেছে লজ্জাবতী ফুল। লাজুক চোখে তাকিয়ে বলে– কেনে?
– জড়াই দেনা কেনে। পিঙ্গলা অবাধ্য হয় না। জড়িয়ে দেয়। দেবা সেই চুলে পাহাড়ি ফুল গুঁজে দিয়ে বলে,
– বড়ো বাহারি লাইগছে বুটেক। শীতের হিমেল বাতাস চুপিসারে বলছে দেখেছি, দেখেছি। সব দেখেছি। সাক্ষী আছে হিমেল বাতাস। সাক্ষী আছে তিলাবনী। সমাজে ফিরেছে দেবা। বলছে– পিংলা, একটা কথা বইলবার মন চাইছে বুটেক। পিঙ্গলার কালো গাল দুটো লজ্জায় রাঙা হয়ে গেছে। লাজুক গলায় বলে
– বল্ না কেনে।
শরম লাইগছে বুটেক। দু’টো চোখ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নের জাল বোনে। দেবার মুখ থেকে শোনার অপেক্ষা। সময়ের দণ্ড পলের তর সয় না। অবশেষে অমৃত স্বাদের গন্ধ ঝরে পড়ে।
গুসসা করবিক নাইন ত বুটেক? মু তুকে বিহ করবারে মন চাইছে। দুয়ে দুয়ে ঘর করবেক। বাপটা থাইকবে মুদের মালিক। তু নারাজ নাইন ত বটেক?
সরম পিঙ্গলারও লাগছে। এক ছুটে ডেড়ার বাইরে গিয়ে মাথা নীচু করে নখ খুটতে থাকে। কিছু ত বল্ না বুটেক? পিঙ্গলা ফিস্ফিস করে বলে– পিরিতডা ত করি বুটেক।
– তা হইলে শুন্ না কেনে।
– ই অগ্রানে টুসু পরবে ঠাকুর মশাইকে স্মরণ দিবে। উ ঠাকুর মুদের বিহডা করাই দিবেক।
– উ কানুনডা মুদের ত নাইন বটে।
– নাইন থাক। ছাড়ান দে জংলি কানুন। ভদ্দর সমাজের কানুডাই বিহ করবেক।
ভালোবাসার রংমশালের আলোটা আচমকাই দপ করে নিভে গেল। ললিত মোহনের বুক থেকে অদ্ভুত একটা ঘড়ঘড়ানি শব্দ। দেবা এক লাফে বুড়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। চোখ দু’টো যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে। এক ভয়ংকর শ্বাস টান উঠছে। দেবা উদ্ভ্রান্ত, বিভ্রান্ত। চিৎকার করে বলে– পিংলা, চাড়ে চাড়ে আয় কেনে। দ্যাখ বাপ কিমন কইরছে বটে। তবু অশক্ত কম্পিত হাতটা দিয়ে দেবার হাতটা খপ্ করে ধরে। দেবা মরিয়া চেষ্টা করে। বলে– পিংলা, বাপকে মু লিয়ে যাব।
– কুথা?
– সদরে।
– আর সময় লাইরে দেবা। বাপটাকে থিরে যাইত দে। শেষবারের মতো পিংগলার হাতটা টেনে নিয়ে দেবার হাতে মেলাবার চেষ্টা করে। পারে না। শুধু অপূর্ণ স্বপ্নের বার্তাটা থরথর করে কেঁপে ঠোঁটটা স্তব্ধ হয়ে যায়।
চঞ্চলতা, অস্থিরতা, ব্যস্ততা কাঠবেড়ালির আছে। সে ব্যস্ততার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। উদভ্রান্ত, অস্থিরতা ব্যস্ততার কারণ কার্তিকের আছে। কার্তিকে ছুটছে। পাগলের মতো। হোঁচট খাচ্ছে। পড়ছে। আবার ছুটছে। তিলাবনীর পাঁজরে আঘাত লেগে সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত। রক্ত ঝরছে। ভ্রূক্ষেপ নেই। মুখে শুধু আকাশ ফাটা আর্তনাদ। এই মুহূর্তে দেবাই সর্বনাশের আসান। পিঙ্গলার মনটা বিষাদগ্রস্ত। অসহায়ের মতো গালে হাত দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। বাপটা চলে গেল। এইমাত্র দাহ করে ফিরেছে। মাথার উপর থেকে অশক্ত ছাদটুকু চলে গেল। সমস্ত অভিভাবকত্ব, অনুশাসন, শাসনের অবসান ঘটিয়ে ঘরে ফিরেছে। দেবা স্ত্বান্না দেয় না। ভাষা নেই যে। বসে আছে হাঁটু মুড়ে মাথা নীচু করে। পিঙ্গলার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে কার্তিকে। বয়ে আনছে আরও এক ভয়ংকর বিপর্যয়ের ঝোড়ো হাওয়া। মনটা আরও উতলা হয়ে ওঠে।
– দেবা, উ আইছে কার্তিকে না? দেখ্ না কেনে উ আঙ্গাস ফাটা চেচাইছে। মাথা নীচু করে দেবা চলে গেছে ভিন জগতে। পিঙ্গলার উত্তেজনায় সম্বিত ফিরেছে।
– হ, লাইগছে বটে। কার্তিকে আরও কিছুটা সামনে এলে দেবা উঠে দাঁড়ায়।
– কার্তিকে, চেঁচাইছিস কেনে? কী হইছে বল্ না বটে? তিলাবনীর পাজরে আরও একবার আছাড় খেয়ে দেবার সামনে ছিটকে পড়ে। উত্তেজিত দেবা সস্নেহে বসিয়ে বলে
– চাড়ে চাড়ে বল্। কি হইছে বটেক?
– দেব্তা নাইরে দেবা। উ শয়তানরা দেব্তাকে মারি দিলা। উয়ার ঘর জ্বালাইন দিছে। গণশাও ছিল বটেক। আকস্মিক বজ্রপাতে দেবা দিশেহারা। উন্মাদ। শুধু আর্তনাদে একটা কথাই শোনা গেল। দেব্তা মু আইছি বটেক। সব শয়তান মু নিধন করবেক। পিতৃহীন, অভিভাবকবিহীন পিঙ্গলা এখন বড়ো অসহায়। পাশে আছে দেবা। বলিষ্ঠ অবলম্বন। ভালোবাসার রঙিন স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন ছুটে চলেছে ভয়ংকর দুর্যোগের অকুস্থলে। অসহায় পিঙ্গলা স্বপ্নকে ধরে রাখতে ছুটতে থাকে। মুখে শুধু আকুল আর্তি – দেবা, মুয়ার ডর লাগিছে বটেক। ইখন তু নাইন যাইছ। দুপহর গড়াইছে। রাইত নাইমছে। পথের বিপদ আইনছে। তু নাইন যাইছ। পিঙ্গলার সেই আকুল আর্তি তিলাবনীর পাঁজরে প্রতিধবনিত হতে থাকে। দেবার কানে সেই আর্তি পৌঁছোল কি না, কে জানে! দূর থেকে একটাই প্রতিশ্রুতি ভেসে আসল।
– ডরাইস না পিংলা। মু আসবেই। মু চাড়ে চাড়ে যাব আর আসব। পাথরের চড়াই উৎরাই পার করে মুহূর্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আর দেখা গেল না।
ত্রিদেবের চিতা নিভে গেছে অনেক আগেই। শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে তিলাবনীর চূড়া ছুঁয়ে উঁচুতে। আরও উঁচুতে। ত্রিদেবের চিতার পাশে বসে দেবা নিস্পলক দৃষ্টিতে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার দিকে চেয়ে আছে। দেবা শুধু ভাবছে। পিঙ্গলাকে নিয়ে ঘর করার স্বপ্ন, রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা, সুস্থ সামাজিক মানুষ গড়ার কারিগর সব কিছুই দলা পাকিয়ে তিলাবনীর চূড়া ছাড়িয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে নীল নীলিমায়। ঘোর দুঃস্বপ্নের মধ্যেই ভেসে আসে অমোঘ বার্তা। ভয় পাস না দেবা। আমার দেহটা নেই। আছি তোদের মাথার উপর। লড়াইটা চালিয়ে যা। ভয় কি? তোর সঙ্গে আছে পিঙ্গলা, কার্তিকে। জিয়ারা গ্রামের সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যা। দেবা উঠে দাঁড়ায়। জীবন যুদ্ধের নির্ভীক সৈনিক। জিয়ারাকে কোমর সোজা করে দাঁড়াতে হবে। জিয়ারা হবে সভ্য সমাজের মডেল গ্রাম। সে যুদ্ধ হবে পিঙ্গলাকে সঙ্গে নিয়েই।
তিলাবনী রাস্তা দেয়নি। দেয়নি জল। কিন্তু সব কেড়ে নেয়নি। দিয়েছে অসংখ্য গাছ। সেই গাছের অসংখ্য প্রসারিত ডালের ঝুরি নামিয়ে দিয়েছে। ত্রিশংকরের আশীর্বাদপুষ্ট দেবার বুক ভরা আর্তনাদ। আর একদিকে আন্দোলিত হচ্ছে অপরাজিত সংকল্প। এগিয়ে চলেছে দেবা। সামনে বিশাল রাক্ষুসে খাদ। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে তিলাবনীর বুক চিরে বিশাল জলধারা দড়ির মতো পাক দিয়ে। এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অসংখ্য গাছের ডাল। অগণিত ঝুরি নেমে গেছে খাদের দিকে। দেবার মনোবল এখন অনেক মজবুত। মজবুত মনের শক্তি যুগিয়ে গেছে ত্রিশংকর। সেই মনোবলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে গাছের ঝুরি ধরে। একটার পর একটা। রাতের জমাট বাঁধা অন্ধকার।
তিলাবনীর বুকে রাতের আঁধার বড়ো তাড়াতাড়ি নামে। পায়ের নীচে মরণখাদ। শ্রান্তিহীন, ক্লান্তি বিহীন অকুতোভয় ছেলেটা এখন মৃত্যুঞ্জয়ী। হাত ফসকালেই চলে যেতে হবে মৃত্যুর কোলে। প্রান্তিক ঝুরি। তারপরই সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর। জিয়ারা আর পিচুলা গ্রামকে বিভাজন করে রেখেছে। আচমকাই দুর্ঘটনা। চড়চড় করে একটা শব্দ। নিভে গেল দেবার মনের সব আলো। গড়িয়ে চলে গেল দেবার নিথর দেহটা গহিন খাদে। সেই ঘন অন্ধকারে আর দেখা গেল না। জিয়ারার স্বপ্ন, পিঙ্গলার চোখে রংমশালের আলো, রাস্তা তৈরির কারিগর, সব কিছুই চলে গেল অনন্ত তিমির লোকে।
দেবার চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে। সমস্ত গ্রাম আজ শোকের হাট। সুখ চায়নি। বাঁচতে চেয়েছিল। সভ্য সমাজে মাথা উঁচু করে। তিলাবনী কেড়ে নিয়েছে তাদের ন্যূনতম স্বপ্ন। দেবা যে তাদের লড়াইয়ের সেনাপতি। সামনে দেবার চিতা। পিঙ্গলার চোখে মুখে আগুনের ঝলকানি। চোখ দুটো হিংস্র বাঘের মতো জ্বলছে। রোদের ঝাঁঝ কমে আসছে। তবু সেই আলোয় পরিষ্কার বোঝা যায়, তিলাবনী ভয় পেয়েছে। কোনও দাম্ভিকতা নেই। নেই কোনও বিদ্বেষ। ঈশান কোণে জমে ওঠা জমাট বাঁধা মেঘটা ঘনীভূত হচ্ছে। ধেয়ে আসছে এক প্রবল ঝড়। সে ঝড়ে তিলাবনী তার অস্তিত্ব কতটুকু ধরে রাখতে পারবে? কে জানে।
এই বিয়োগান্তক গল্পের পরিসমাপ্তিটা এখানেই হলে হয়তো ভালো হতো। আসলে লড়াইয়ের পাটিগণিত কোনও সূত্র ধরে চলে না। আসলে লড়াইটা যে এখান থেকেই শুরু। পিঙ্গলা এক দৌড়ে দেবার আস্তানা থেকে ছেনি হাতুড়িটা নিয়ে আসে। ঘৃণা, ক্ষোভে সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে। চিতার লেলিহান অগ্নিশিখা পিঙ্গলার মনেও আগুন ধরিয়েছে। এক বজ্র হুংকারে তিলাবনীর পাথরে প্রতিধবনিত হতে থাকে।
– এ তিলাবনী, তুয়ার বহুত দিমাক হইছে না রে? মুয়াদের রাস্তা নাইন দিলি। কোল গড়ায়ে জল দিছিস নাই। কষ্ট করছি। কুছু বলি নাইন। মুয়াদের ভুক্ষা মারবি? ইখন মুয়ার ভাবী মরদকে ছিনায় নিলি? তুয়ার ইত জ্বলন কেনে রে? ত দেখ কেনে, মু কি কইরতে লাইরছি? কোনও ভূমিকা নেই। কোনও গৌরচন্দ্রিকা নেই। ছেনির উপর হাতুড়ির এক একটা আঘাত আগুনের ফুলকি হয়ে ক্ষোভের বর্হিপ্রকাশ ঘটতে থাকে। রাস্তার নক্সাটা পেয়েছিল দেবার কাছ থেকেই। অবিরত ছেনির উপর হাতুড়ির আঘাত। ঠন্ ঠন্ ঠন্।
সতেরোটা বছর ধরে
– ছেনি হাতুড়ির আঘাতে পাথরের এক একটা চাঙ্গড় ধসে পড়ছে। অনিদ্রা অনাহারে শরীরটা ক্লান্ত। মনের জোরটা অটুট। সেই জোরেই সেফটিপিনের মতো রাস্তাটা ঘুরে ঘুরে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হঠাৎই কানে আসে একটা অজানা সোঁ সোঁ শব্দ। বুঝতে পারে না। উৎসে যাওয়ার চেষ্টা করে। বুঝতে পারে না। পাথরের গায়ে মাথা ঠেকায়। একটা বিশাল জলের গর্জন। পিঙ্গলা সময় নষ্ট করে না। শুরু হয় ছেনি হাতুড়ির আঘাত। আঘাতের পর আঘাত। তারপরই কুল কুল শব্দে জলের ধারা। আসন্ন বিপদ বুঝতে দেরি হয় না। পিঙ্গলা ছুটে বেরিয়ে আসে। মুহূর্তে বিশাল আওয়াজ। বিরাট পাথরের চাঙড় খসে পড়ে। তারপরই ভয়ংকর গর্জনে আছড়ে পড়ে জলের ধারা জিয়ারা গ্রামে। অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণ মাঠ, পুকুর, ডোবা হয়ে ওঠে কল্লোলিনী গর্ভবতী। শরীরের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে মনের অনাবিল আনন্দে পিঙ্গলা নাচতে থাকে। আত্মহারা জিয়ারা শবরবাসী।
রাস্তা ফিনিশিং-এর কাজ চলছে। কাশিটা ধরেছে অনেকদিন ধরেই। পালা করে জ্বরও আসছে প্রতিদিন। তবু তিলাবনীর পাঁজরে সেই আওয়াজ। ঠন্ ঠন্ ঠন্। কার্তিকে বুঝতে পারছে, পিঙ্গলার শরীরের অবস্থা ভালো না। বলছে– পিংলা, রাইত হইছে বুটেক। ঘরকে চল। তুয়ার শরীলডা অর দিছে নাই। ছলকে যাবি বুটেক। কাশির সঙ্গে গলগল করে খানিক রক্ত। হাঁপাচ্ছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। হাত দিয়ে রক্ত মুছে পিঙ্গলা বলে
– তু ঘরকে যা। তুয়ার গরে বহু, বাল-বাচ্ছা আইনছে। তুয়ার অনেক দায় আইনছে। ই রাস্তাডা মুয়ার পরান। ইটাই মুয়ার দেবা আইনছে রে, কার্তিকে। তু ঘরকে যা।
সদর থেকে মাল বোঝাই ট্রাকগুলো ধুলো উড়িয়ে পিচুলা ছুঁয়ে জিয়ারা দিয়ে বেরিয়ে যায়। জিয়ারাবাসী আজ অপরাধপ্রবণ অসভ্য লেবেলটা মুছে ফেলেছে। সে শিক্ষাটা দিয়ে গেছে দেবা পিঙ্গলা। কালের নিয়মে, সময়ের মলিনতায় নব প্রজন্মের স্মৃতির অতলে তারা তলিয়ে গেছে। সাক্ষী আছে তিলাবনী। জিয়ারা পিচুলা যে একই মায়ের গর্ভজাত। তবু তিলাবনীর পাঁজরে কান পাতলে আজও শোনা যায় পিঙ্গলার ছেনি-হাতুড়ির শব্দ। ঠন্ ঠন্ ঠন্।