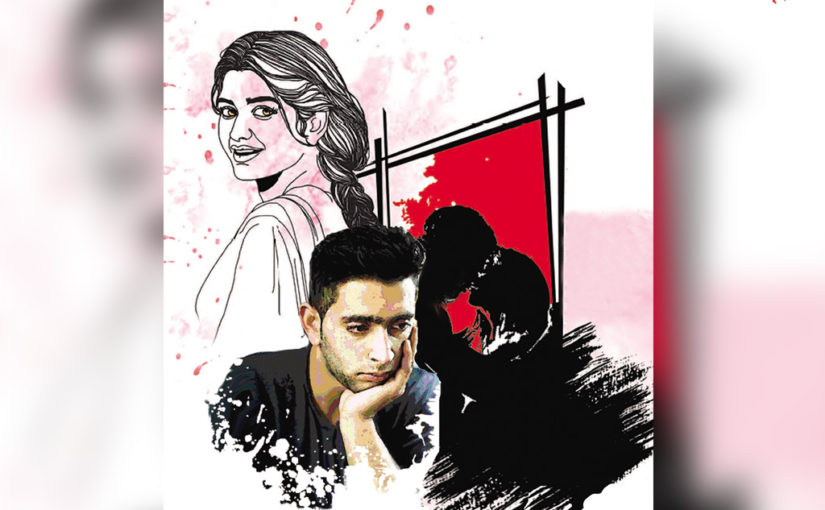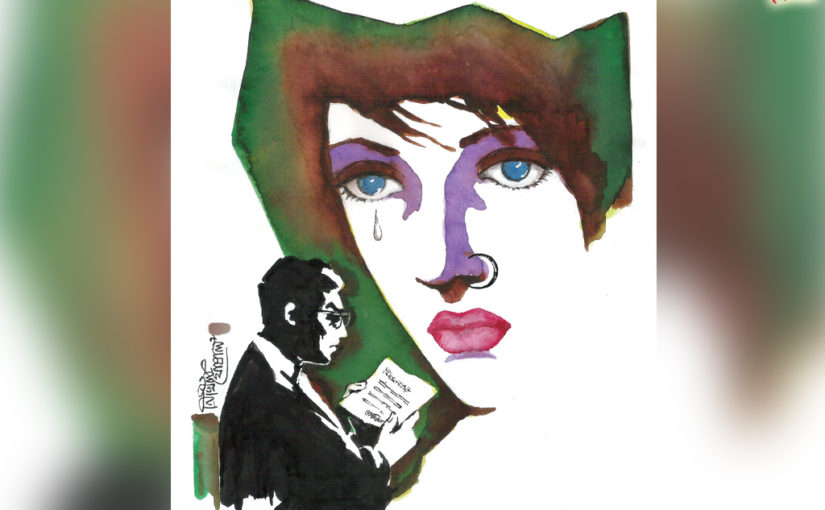দুপুর একটা পঞ্চান্নর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে চেপে শিলিগুড়ি। সেখান থেকে দার্জিলিং। এমনটাই ঠিক ছিল। কিন্তু ট্রেনটা ওরা মিস করল।
তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া সেরে বিছানায় একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছিল সুবিমল। ঘুম ভেঙেছিল মোবাইলের রিংটোনে। ফোন ধরতেই মায়ার গলা, কোথায় আছেন? কতক্ষণ ধরে ফোন করছি, ফোন ধরছেন না কেন?
এই আসছি, ট্রেন তো এখনি ঢুকবে!
ব্যাগ গোছানোই ছিল। তাড়াহুড়ো করে দরজায় তালা দিয়ে বেরোয় সুবিমল। টোটো ধরে স্টেশন। মায়া তার মেয়েকে নিয়ে অপেক্ষা করছিল। কোনওমতে টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে ঢুকেই ওরা দেখে ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। একা থাকলে লাফিয়ে উঠে পড়ত সুবিমল। কিন্তু মায়া আর দিয়াকে নিয়ে তো সেটা সম্ভব নয়।
এবার কী হবে? মায়ার গলা কাঁদো কাঁদো শোনায়।
এনকোয়ারিতে গিয়ে ওরা জানল চারটের আগে আর শিলিগুড়ির দিকে যাবার কোনও ট্রেন নেই। তার মানে আরও দুঘন্টা স্টেশনে বসে থাকতে হবে। সুবিমল বলল, চলো ফিরেই যাই। মায়ার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। বলে, আমায় নিয়ে আপনি দার্জিলিং যেতে চান না তাই তো?
এরকম ভাবছ কেন? আসলে ট্রেন পেতে দেরি হলে শিলিগুড়ি যেতে যেতে অনেক রাত হয়ে যাবে। আর তখন হোটেল-টোটেল পাব কিনা…
হোটেল না পেলে স্টেশনে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেব। কিন্তু বেরিয়েছি যখন যাবই! সুবিমলকে চুপ থাকতে দেখে আবার বলল মায়া, দার্জিলিং নিয়ে কত কথা বললেন। কম্পিউটারে ছবি দেখালেন। আর এখন যেতে চাইছেন না?
দার্জিলিং-এর কথাটা বলতেই মায়ার মুখটা কেমন নরম হয়ে গেল আর চোখদুটো চকচক করে ওঠে, একটা কষ্ট অনুভব করল সুবিমল। বেচারি! কখনও দূরে কোথাও যায়নি। কিছু দেখেনি। পাহাড়, সমুদ্র কিছু না। কেউ নিয়ে যাবার নেই!
আচ্ছা মা, দার্জিলিং-এ তো এখন খুব ঠান্ডা তাই না? পাশ থেকে দিয়া বলে।
সেটা তোর কাকুকেই জিজ্ঞেস কর না।
আঃ তুমিই বলো না। ওখানে কি এখন বরফ পড়ছে? কী মজা!
মেলা বকিস না তো। এখন যাওয়া হবে কিনা তারই ঠিক নেই, আর ইনি চোখে বরফ দেখছেন।
বকুনি খেয়ে একটু চুপ করে যায় মেয়েটা। একটু পরেই আবার বলে, আমি কিন্তু দার্জিলিং গিয়ে টয়ট্রেনে চড়ব।
হ্যাঁ, তুমি টয়ট্রেন চাপবে! কত টাকা টিকিট লাগবে জানিস? তুই দিবি?
টয়ট্রেনের ছবি দেখিয়েছিল সুবিমল কিন্তু তার টিকিট-ফেয়ার নিয়ে কিছু বলেনি। সে নিজেও ঠিক জানে না। তবে মায়া হয়তো ধরেই নিয়েছে, এত সুন্দর দেখতে একটা ট্রেনে উঠতে অনেক টাকা লেগে যাবে। এসব কথা হতে হতেই একটা ট্রেন চলে এল।
পুরি-কামাখ্যা এক্সপ্রেস।
মায়া তড়িঘড়ি বলল, দেখুন না, এই ট্রেনটা শিলিগুড়ি যাচ্ছে কিনা?
এখন তো ওদিকে যাবার কোনও ট্রেন নেই, শুনলে না?
আঃ দেখুনই না একবার।
কী মনে করে সুবিমল সিট ছেড়ে এগোয়। ট্রেনের জানলার ধারে বসে থাকা একজন প্যাসেঞ্জারকে জিজ্ঞেস করে। লোকটা হিন্দিতে জবাব দেয়, শিলিগুড়ি যায়েগে কেয়া নহি জানতে, পর ইয়ে এনজিপি যায়েগা।
এনজেপি মানে নিউ জলপাইগুড়ি। শিলিগুড়ির আগের স্টেশন। ওখান থেকেও তো দার্জিলিং যাওয়া যায়! মায়া ততক্ষণে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সুবিমল ব্যস্ত হয়ে বলে, চলো চলো এটা যাবে। মালপত্র নিয়ে ছুটতে ছুটতে ওরা সামনের কামরাটাতে উঠে পড়তেই ট্রেন ছেড়ে দিল।
এনকোয়ারির লোকটা এই ট্রেনটার কথা বললই না। ভাবো এরা কি জন্যে যে চাকরি করে, সুবিমল সিটে বসতে বসতেই বলে।
দেখলেন তো, আমার কথা শুনলেন বলেই… মায়ার মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটেছে। জানলার পাশে দিয়াকে বসিয়ে সে নিজেও বসেছে। কামরা একদম ফাঁকা। রিজার্ভেশন হয়নি বলে আসতে চাইছিলেন না। এখন দেখুন শুয়ে শুয়ে যাওয়া যাবে। আমার বেড়াবার ভাগ্য কী ভালো।
সুবিমল ঘর থেকে তিনটে বড়ো বড়ো ক্ষীরসাপাতি আম আর লিচু নিয়ে এসেছে। বার করল সেগুলো। ট্রেনে উঠলেই তার খিদে পায়, কেন কে জানে!
নাও আমগুলো কাটো। লিচু খাও।
আম কেটে, টিফিনবাটির ঢাকনায় তুলে প্রথমেই সুবিমলের দিকে এগিয়ে দেয় মায়া। তারপর মেয়েকে দিয়ে নিজেও নেয়। সিটের ওপর পা তুলে গুছিয়ে বসে, আম খায়।
আঃ পাটা নামিয়ে বসো না, সুবিমল বলে।
কেন, কী হয়েছে?
সুবিমল আর কিছু বলে না। মুখ ফিরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। কেন যে আসতে গেল এদের সাথে। নোংরা পা দুটো একেবারে সিটের ওপর তুলে বসল। যেন ঘরের বিছানা! কম শিক্ষিত হলে যা হয়। এই যে, আবার পিচিক পিচিক করে থুতু ফেলা হচ্ছে জানলা দিয়ে। এত থুতু আসে কী করে মুখে ও বুঝে পায় না! দিয়ার ওপর চোখ পড়তেই মাথা আবার গরম হয় সুবিমলের। কালো মুখে রং মেখেছে!
দার্জিলিং-এর ছবিগুলো আবার দেখান না, আবদারের সুরে বলে মায়া।
সুবিমল বিরস মুখে ব্যাগ খুলে তার ল্যাপটপটা বার করে, সুউচ অন করে। মোডেম লাগায়। ইউ টিউব চালায়।
ওই তো টয়ট্রেন, লাফিয়ে ওঠে দিয়া।
চিৎকার করছিস কেন? মেয়ের দিকে কটমটিয়ে তাকায় মায়া। দিয়ার মুখ শুকনো হয়ে যায়।
টয়ট্রেন ততক্ষণে ঘুম স্টেশনে এসে থেমেছে। কুয়াশায় আবছা দেখা যাচ্ছে। এবার দার্জিলিং-এর বাজার দেখাচ্ছে নেপালি মেয়েটা, রংবেরং-এর উলের পোশাক বিক্রি করছে। দোকানে দোকানে কত জিনিস সাজানো, নীল সবুজ পাথরের মূর্তি। বাজার ছেড়ে পথ ওপরে উঠছে। এবার ম্যালে এসে থামল।
কী চমৎকার জায়গাটা। এটাই তো বলেছিলেন মল। তাই না?
মল নয়, ম্যাল সুবিমল হাসে।
ওঃ ম্যাল। লজ্জা পেয়ে মাথা ঝাঁকায় মায়া। তারপর বলে, আপনি বলেছিলেন না, ম্যালে গেলে কোনও না কোনও পরিচিত লোকের সাথে দেখা হয়ে যাবেই।
হ্যাঁ, লোকে তো সেরকমই বলে, একটু অন্যমনস্ক হয় সুবিমল। আমি যখন খুব ছোটোবেলায় মা বাবার সাথে দার্জিলিং গিয়েছিলাম, ম্যালে গিয়ে মনে আছে একজন দূর সম্পর্কের রিলেটিভ মানে আত্মীয়ের সাথে দেখা হয়ে গেছিল। পরে আর কখনও ওনাকে দেখিনি। এখনও মনে আছে, উনি আমাকে গাল টিপে আদর করেছিলেন, ঘোড়ায় চড়িয়েছিলেন।
আমিও ম্যালে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ব।
সুবিমলের চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায়। বিরক্ত হয়ে সে দিয়ার দিকে তাকায়।
আঃ কতবার তোকে বলেছি, কথার মাঝখানে কথা বলবি না। দেব কানপাট্টিতে এক থাপ্পড়। তারপর বলুন না কী হয়েছিল?
সুবিমলের মনে তখন অন্য একটা চিন্তা জন্ম নিয়েছে। ম্যালে গিয়ে যদি… ম্যালে তো যেতেই হবে। গিয়ে যদি আবার কোনও আত্মীয়ের সাথে দেখা হয়ে যায় অথবা তারই স্কুলের কোনও কলিগের সাথে! তখন সে কী করবে। কী পরিচয় দেবে মায়ার আর মায়ার মেয়ে। কী বলবে সে?
কী হল, কী ভাবছেন?
কিছু না লিচুর খোসা ছাড়ায় সুবিমল।
এসব কথা বলতে বলতে ওরা যখন নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছোল তখন রাত আটটা বাজে।
ট্রেন থেকে নেমেই দিয়া বলল, মা দেখেছ, কত্ত বড়ো স্টেশন! সঙ্গে বেশি টাকা আনেনি সুবিমল। স্টেশনের পাশে একটা ছোটো দেখে হোটেলেই ওঠে।
হোটেল মালিক টাকা নিয়ে খাতা খুলে সুবিমলকে সই করাল। তারপর বলল, আপনাদের আধার কার্ডটা দেখাবেন। মায়ার কার্ডটা দেখে বলল, আপনার পদবি তো দেখছি দাস আর ওনার ভট্টাচার্জি।
সুবিমল বুঝতে পারল না লোকটা কি বলতে চাইছে। কিন্তু মায়া একবার সুবিমলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, এটা বাবার নামে করেছিলাম তো। বিয়ে পর আর পালটানো হয়নি।
আপনারা সত্যিই ম্যারেড তো?
কেন, আপনার সন্দেহ হচ্ছে বুঝি?
সুবিমল বলল, রেজিস্ট্রি পেপার দেখাতে হবে?
না, না, ঠিক আছে। আচ্ছা আপনারা ঘরে যান।
ঘরে গিয়ে ওরা আর বসল না। মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। কাল যত সকাল সকাল বেরোনো যায় ততই ভালো।
ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছেই অনেকগুলো খাবার হোটেল। তারই একটায় ঢুকে ওরা বসে। সুবিমল মাছ ভাত বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মায়া বলল ডিম ভাত নিতে। খরচ যেটুকু বাঁচানো যায়।
রাতে বিছানায় শুয়ে ওদের চোখে ঘুম আসে না। মায়া আর সুবিমলের মাঝে দিয়া শুয়েছে। সে বলে, মা ঘুম পাচ্ছে না। একটা গল্প বলো না। ওই দুষ্টু শেয়ালের গল্পটা।
হ্যাঁ, আমার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। তোকে এখন গল্প বলব। চুপ করে ঘুমো। ভোর ভোর উঠতে হবে।
না, বলো না একটা।
মায়া কী ভেবে বলে, তোর কাকুকে বল। কাকু অনেক ভালো ভালো গল্প জানে।
অন্ধকারের মধ্যেই সুবিমলকে উদ্দ্যেশ্যে করে সে বলে, আপনার কি ঘুম পাচ্ছে? নাহলে ওকে একটা গল্প বলুন না। আমিও শুনব।
সুবিমল ভাবছিল, দিয়া এখন সঙ্গে না থাকলে কত ভালো হতো। মায়াকে এখন সে জড়িয়ে ধরে আদর করতে পারত। বদমাইস মেয়েটা একেবারে তাদের মাঝখানে এসে শুয়েছে। মায়া বলেছিল একপাশে শুতে। কিন্তু শুনলে তো! তবে এটাও মনে হয়েছে ওর, দিয়া সঙ্গে না থাকলে হয়তো হোটেলে ঘর পেতে অসুবিধে হতো। ও আছে বলেই সবাই ওদের একটা পরিবার বলে ধরে নিচ্ছে। স্বামী, স্ত্রী ও তাদের মেয়ে ঘুরতে বেরিয়েছে। মনটা হঠাৎই জ্বালা করে ওঠে সুবিমলের। পরিবার! সত্যিই কি কোনও দিন তার নিজস্ব পরিবার হবে? তার নিজের সন্তান, তার নিজের বউ। চল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেল। আর কবে সে বিয়ে করবে?
বলবেন একটা গল্প, বলুন না। মায়ার গলায় আবদারের সুর।
মায়ার সাথে প্রথম পরিচয়টা একটু অদ্ভুত ভাবেই হয়েছিল। বাউল মেলা দেখতে গিয়েছিল সুবিমল। দিয়াকে একটা এগরোলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দ্যাখে। ভিড়ের মধ্যে ওর হাত ছুটে নাকি ওর মা হারিয়ে গেছে। সুবিমলই শেষপর্যন্ত দিয়ার হাত ধরে মায়াকে খুঁজে বার করে। সেদিন মনে আছে একটা চুমকি বসানো জংলা সবুজ রঙের শাড়ি পরেছিল মায়া। বেশ লাগছিল। বিশেষ করে ওর ফিগারটা। এক মেয়ের মা বলে ওকে বোঝাই যায় না! মেলাতেই ফোন নম্বর দেওয়া নেওয়া হয়েছিল। তারপর কীভাবে যে ওরা দুজন কাছে চলে এল। স্বামী নেই বলে মায়ার দিক থেকেও নিশ্চয়ই একটা শারীরিক চাহিদা ছিল!
ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?
হঠাৎ করেই মায়ার কথা ভেবে মনটা কেমন নরম হয়ে যায় সুবিমলের। বেচারি। বিয়ে হতে না হতেই বর মারা গেছে। শুধু একটা ছোটো দোকান রেখে গেছে, পান-বিড়ি-সিগারেটের, আর এই মেয়েটা। ওকে বোনের বাড়ি রেখে বেড়াতে আসবার কথা মায়া বলেছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত পারেনি। মায়ের মন। বলল, আমি ঘুরব আর ও পাহাড় দেখবে না?
সুবিমল পাশ ফিরে বলে, আচ্ছা শোনো। এই দিয়া শোন, একটা গল্প বলছি। হ্যাপি প্রিন্স ও সোয়ালো পাখির গল্প। এক দেশে এক রাজার ছেলে ছিল। দুঃখ কাকে বলে সে জানত না, তারপর একদিন সে মারা গেল।
এত তাড়াতাড়ি মারা গেল?
কথা বলছিস কেন? ধমকে ওঠে মায়া চুপ করে শোন।
সুবিমল বলতে থাকে, দিয়া চুপ করে শুনছে। কতটা বুঝছে বলা মুশকিল কিন্তু সুবিমল যখন যখন বলল সোয়ালো, সোয়ালো, ও লিটল সোয়ালো। দিয়াও সুর করে বলল, সোয়ালো সোয়ালো ও লিটল সোয়ালো…
গল্প শেষ হলে মায়া বলল, ওরা দুজন দুজনকে কত ভালোবেসেছিল। সত্যিই কি কেউ কাউকে এত ভালোবাসতে পারে? তারপর তিনজনেই ঘুমিয়ে পড়ে। মায়ার ডাকাডাকিতেই ঘুম ভাঙল সুবিমলের।
আর কত ঘুমোবেন?
উঠে বসে সুবিমল। এঃ, পৌনে ছটা বাজে। রোদ উঠে গেলে তো পাহাড়ে ওঠার আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে। বিছানা ছেড়ে তড়িঘড়ি বাথরুমে যায় সুবিমল। হাত মুখ ধুয়ে বেরোয়। দিয়াও এইমাত্র উঠল। ঘুমচোখে বিছানার ওপর বসে আছে। মায়া ওকে টেনে হিঁচড়ে নামায়।
শিলিগুড়ি সদর মোড়ে এসে ওরা ট্রেকার থেকে নামে। একটু দূরেই দুটো বোলেরো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। একটা গাড়ির চালক হাঁক দিচ্ছে দার্জিলিং দার্জিলিং। মায়া সুবিমলের হাত চেপে ধরে, একটু তাড়াতাড়ি চলুন, গাড়িটা বোধহয় ছেড়ে দেবে এক্ষুনি কিন্তু সুবিমল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।
কী হল চলুন,
সুবিমল এবার এগোয়। গাড়ির চালককে গিয়ে জিজ্ঞেস করে। কালিম্পং যাবার কোনও গাড়ি নেই?
এই তো পাশের গাড়িটাই যাবে, যান উঠে পড়ুন। মায়া অবাক হয়ে সুবিমলের দিকে তাকায়।
কী হল? আমরা তো দার্জিলিং যাব।
না মায়া। একটু ইতস্তত করে সুবিমল বলে, সাত হাজার টাকায় দার্জিলিং ঘোরা যাবে না। ওখানে হোটেল ভাড়াই অনেক হবে।
কেন, আমার কাছেও তো কিছু টাকা আছে, এতে হবে না?
না, তোমার টাকায় আমি হাত দেব না। কালিম্পং কাছে। খরচ কম পড়বে। চলো ওখানেই ঘুরে আসি। মায়ার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।
দার্জিলিং যাব বলে এলাম আর এখন বলছেন…
না মায়া, দার্জিলিং-এ খুব ঠান্ডা পড়ে। তুমি তো জানো আমার বেশি ঠান্ডা সহ্য হয় না।
কেন, গরম কাপড় তো সঙ্গে এনেছেন। এতে হবে না?
না।
ঠোঁট কামড়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় মায়া। ওর জন্য কষ্ট হয় সুবিমলের। বেচারি কত আশা করে এসেছিল!
গাড়ি সমতল ছেড়ে সেবকের কাছে এসে পাহাড়ে ওঠার পথ ধরতেই মায়ার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। দিয়া জানলার পাশে বসেছে। বাইরে হাত দেখিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, মা দ্যাখো নদী কত নীচে। মায়া জানলা দিয়ে মুখ বাড়ায়। সুবিমলকে ডেকে বলে, দেখুন পাহাড়ি নদী।
কী নাম নদীটার? জলটা কেমন সবুজ। দেখবে কী করে সুবিমল। সে বসেছে মাঝখানে।
বাঃ, বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে সে, আর সে-ই কিছু দেখতে পাবে না! একটু রাগ রাগ মুখ করেই বসে থাকে সুবিমল। থাক, ওরাই দেখুক। একটু পরে অবশ্য সে নিজেও সরে এসে মুখ বাড়িয়ে নীচে তাকায়। আর কী আনন্দই যে হয়। দিয়ার মতো বয়সে সে এই পথ দিয়ে গিয়েছিল। এই সুবিস্তীর্ণ পাহাড়, পাহাড়ের খাদ থেকে উঠে আসা এই লম্বা লম্বা গাছ, আর গাছের ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা ওই রূপসি রঙ্গীত এরা কি তাকে চিনতে পারছে! দার্জিলিং যাওয়া হল না!
কাকু তোমার কাছে স্মার্ট ফোন নেই? তাহলে ছবি তুলব, দিয়া বলে।
মাথা নেড়ে না বলে সুবিমল। অন্য যাত্রীরা জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মোবাইলে ভিডিও করছে। দিয়া মায়ের কাছ থেকে ছোট্ট কমদামি মোবাইলটা নিয়ে তাতেই ছবি তুলতে থাকে। দেড় ঘন্টা বাদেই ওরা মেঘের রাজ্যে পৌঁছে যায়। পাহাড়ের বুকে শুয়ে থাকা মেঘগুলো সদ্য ওঠা সূর্যের আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে।
কী সুন্দর! মায়া অস্ফুটে বলে, এরকম জিনিস দেখতে পাব কখনও ভাবিইনি।
মেঘ দেখা ভুলে গিয়ে সুবিমল চেয়ে থাকে মায়ার ঝলমলে খুশিভরা মুখের দিকে।
কালিম্পং গাড়ি স্ট্যান্ডে এসে নামার পর মায়া অবাক হয়ে চারদিকে তাকায়। পাহাড়ের এত ওপরে এত বড়ো সুন্দর শহর! ওরা প্রথমেই একটা দোকানে ঢুকে লুচি মিষ্টি খেয়ে নেয়। তারপর হোটেল খুঁজতে বার হয়। বেশি খুঁজতে হয় না। স্ট্যান্ডের পাশেই প্রচুর হোটেল। শেষপর্যন্ত হোটেল প্যারাডাইস বলে একটা দোতলা ঝকঝকে সুন্দর হোটেলে ওরা সাহস করে ঢোকে। আর এমনই ভাগ্য, মাত্র হাজার টাকায় একটা বড়ো ঘর পেয়ে যায়। ঘরে দুটো সিংগল বেড, টিভি সেট আছে, বড়ো আয়না আছে, জানলায় শৌখিন পর্দা ঝুলছে, টাইলস বসানো বাথরুমের সাইজটাই শিলিগুড়ির হোটেল ঘরটার থেকে বড়ো।
ওরা আরও অবাক হল যখন হোটেল ম্যানেজার ওদের কাছে আধার কার্ড দেখতে চাইল না, এমনকী আগাম ভাড়াও চাইল না। শুধু খাতায় নাম তুলে নিল। তারপর বলল, যান, মালপত্র রেখে ফ্রেশ হয়ে নিন। সাইট সিযিং করবেন তো? আমার চেনা ভালো ড্রাইভার আছে। বারোশো টাকা নেবে, সেভেন পয়েন্টস ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে।
সেভেন পয়েন্টসটা কী? প্রশ্ন করে সুবিমল।
কালিম্পং-এ মেইন দেখার জায়গা সাতটা। নতুন আসছেন বুঝি?
হ্যাঁ।
মায়া বলল, আমরা স্নান খাওয়া সেরেই বেরোব। আপনি ড্রাইভারকে বলে দিন।
ঠিক বারোটা বাজতেই ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে হোটেলের গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। ওরা তখন সবে ভাত খেয়ে হোটেলে ঢুকছে। তড়িঘড়ি ওপরে উঠে ওরা ড্রেস চেঞ্জ করে। মায়া বলে, দেখুন না কোন শাড়িটা পরব?
শাড়ি কেন, যে-সবুজ সালোয়ারটা এনেছ ওটা পরো।
ওটা পরব? একটু ছোটো হয় আমার। গায়ে চেপে বসে।
পরোই না।
সালোয়ার গায়ে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায় মায়া। পেছন থেকে সুবিমল বলে, তোমায় দেখতে সেই হট লাগছে।
যাঃ, মায়ার মুখে লজ্জা। তারপরেই জিভ কেটে বলে, ওড়নাটাই আনতে ভুলে গেছি। ওড়না না পরে বেরোব?
ভালোই হল, সুবিমল হাসে। বলে আরও বেশি সেক্সি লাগবে।
মা, সেক্সি মানে কি? দিয়া বলে।
গাড়ির ড্রাইভারের চেহারা একেবারে সিনেমার হিরোর মতো। লম্বা, ফরসা, ধারালো চোখ মুখ। ওরা আসতেই গাড়ির দরজা খুলে দেয়।
ডেলো আর দুরপিন, এই দুটো উঁচু পাহাড়ের মাঝে কালিম্পং। ড্রাইভারটা প্রথম ওদের ডেলো পিকে নিয়ে যায়। পিকের ওপরে একটা খুব বড়ো হনুমানজির মূর্তি। পাশে ফুলের বাগান। সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে ওঠে দিয়া, হনুমানজির পায়ে কাছে রেলিং ঘেরা জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ায়। চেঁচিয়ে বলে, মা দ্যাখো মেঘ। সত্যিই, একেবারে হাতের কাছ দিয়ে শরীরের ওপর দিয়ে মেঘ উড়ে যাচ্ছে।
সুবিমল মায়াকে বলে, দ্যাখো এই মেঘগুলো যেন আমাদের স্বপ্নের মতো তাই না? মনে হচ্ছে ধরা যায় কিন্তু হাত বাড়ালেই মিলিয়ে যাচ্ছে।
মায়া হেসে বলে, আপনার আবার কী স্বপ্ন আছে? দার্জিলিং, মনে মনে বলে সুবিমল। একদিন আমি দার্জিলিং যাব।
সিঁড়ি দিয়ে ওরা নামছে, পাশেই দুহাত উঁচুতে পাথরের খাঁজে খাঁজে অদ্ভুত সুন্দর এক ধরনের জংলি ফুল ফুটে আছে দেখতে পায় সুবিমল। জুতো খুলে রেখে, ওপরে ওঠবার চেষ্টা করে। একবার পা পিছলে পড়ে। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ফুলগুলোর কাছে হাত পৌঁছোয়। কয়েটা তুলে এনে দিয়াকে দেয় আর একটা মায়ার চুলে গুঁজে দেয়। মায়া সলজ্জ মুখে হাসে, কী যে ছেলেমানুষি করেন, পায়ে লাগল তো?
ডেলো পার্কটাও চমৎকার জায়গা। সেখানে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ার বায়না ধরে দিয়া। কিন্তু দশ মিনিট ঘোরাতে দুশো টাকা নেবে শুনেই না করে দেয় মায়া। এরপর মর্গান হাউস, নেচার মিউজিয়াম ইত্যাদি আরও কয়েটা ভালো ভালো জায়গা দেখে সন্ধের সময় ওরা হোটেলে ফেরে।
বিছানায় বসে মায়া বলে, ড্রাইভারটা কী ভালো বলুন। আমরা যেখান থেকেই ঘুরে বেরোচ্ছি, একেবারে সামনে গাড়ি নিয়ে এসে দরজা খুলে দাঁড়াচ্ছে, একটুও হাঁটতে হয়নি। অন্যদের গাড়িগুলো কিন্তু দূরেই দাঁড়িয়েছিল। কত সামান্য জিনিসও মেয়েদের চোখে পড়ে, ভাবে সুবিমল।
একটু তাড়াতাড়িই বাইরে বেরিয়ে রাতের খাবার খেয়ে নেয় ওরা। ফেরার পথে ওপরে তাকায় সুবিমল। এই আকাশ সমতলে দেখা যাবে না। তারাগুলো কী ঝকঝক করছে, যেন কাছে নেমে এসেছে। তারপরেই দূরের পাহাড়ে চোখ পড়তে চমকে ওঠে সুবিমল। মায়ারাও দেখেছে। প্রথমটা বুঝতে পারেনি ওরা। যেন হাজার হাজার প্রদীপ জ্বলছে! তারপর ভালো করে দেখে বুঝল, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সারি সারি বসতবাড়ি। তার আলো।
দুটো সিংগল বেড পাশাপাশি এনে ওরা শুতে যায়। দিয়া সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ে। মায়াও। সুবিমল জেগে থাকে। আর একটু রাত হলে মায়া এসে ওর পাশে দাঁড়ায়। কখন ঘুম ভাঙল ওর!
মায়া ফিসফিসিয়ে বলে, চলুন, আপনার খাটটা ওই পাশে সরিয়ে নিই।
এর আগেও তো কতবার ওরা মিলিত হয়েছে। কিন্তু আজকের রাতটা আলাদা। মাটি থেকে চার হাজার ফিটের ওপরে, মেঘের রাজ্যে। অনেকটা সময় পার করতে করতে এই ঠান্ডা রাতেও তারা ঘেমে গেল। তারপর, সেই ভিজে ভিজে সুখ মেখেই তারা ঘুমিয়ে পড়ল। একটু বেলা করেই ঘুম ভাঙে ওদের।
দিয়া উঠেই বলে, কাকুর খাটটা ওখানে কেন? সুবিমল মায়ার দিকে তাকায়।
মায়া মুখে ক্রিম ঘষতে ঘষতে বলে, রাতে তোর কাকুর একা শুতে ইচ্ছে হল, তাই খাটটা সরিয়ে নিল।
সত্যি কাকু? দিয়া সুবিমলকে দ্যাখে।
মুখ-টুখ ধোওয়া হলে সুবিমল বলে, বেল টিপে ম্যানেজারকে ডাকব? চা দিতে বলি আর সঙ্গে কিছু খাবার।
ডাকবেন? ঘরে এসে দিলে হয়তো বেশি দাম চাইবে।
তা হোক।
চা, লুচি-তরকারি এল। সবাইকে ভাগ করে দিয়ে খেতে খেতে মায়া বলল, এটা আমার মনে থাকবে। একেবারে হাতের কাছে এসে দিয়ে গেল, হোটেলের বিছানায় বসে খাচ্ছি।
কালিম্পং দেখা শেষ। এবার ফেরার পালা। নীচে এসে হোটেলের খাতায় সই করার সময় ম্যানেজার বলল, ফিরে যাচ্ছেন? এখানে এলেন যখন লাভা ঘুরে যান। ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম। খুব শান্ত। একটা গুম্ফা আছে, ভালো লাগবে আপনাদের। লাভার নাম আগে শুনেছে সুবিমল। কিন্তু জায়গাটা ঠিক কীরকম সে জানত না।
বাইরে বেরোতেই ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হল। ভিজতে ভিজতেই ওরা গাড়ি স্ট্যান্ডে এল। ওযেদার খারাপ, শিলিগুড়ি ফিরে যাবে কিনা ভাবতে ভাবতে শেষে লাভায় যাবার গাড়িই ধরল সুবিমল। মায়া আর দিয়া খুব খুশি। গাড়ি যখন ছাড়ল তখনও বৃষ্টি পড়ছে। ড্রাইভার যদিও বলল, পাহাড়ের এই বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকে না। আর হলও তাই। মিনিট কুড়ি পরেই আকাশ একেবারে পরিষ্কার। ঝলমলে রোদ।
যেতে যেতে কম্পিউটার বার করল সুবিমল। লাভা সম্বন্ধে একটু জেনে নিলে ভালো হয়। আর যা জানল তাতে সে অবাকই হল। লাভার উচ্চতা সাত হাজার ফিটের বেশি। দার্জিলিং-এর চেয়ে কয়েকশো ফিট ওপরে। চেঁচিয়ে ওঠে সুবিমল, মায়া, আমরা দার্জিলিং-এর চেয়ে বেশি উঁচুতে উঠছি।
আধঘন্টা পর থেকেই ওদের ঠান্ডা লাগতে শুরু করল। আর এই প্রথম ওদের ব্যাগ থেকে গরম পোশাক বার করতে হল। সোয়েটার পরেও সুবিমল কাঁপছে। মায়া ওর হাতে নিজের শালটা দিয়ে বলল, কানে জড়িয়ে নিন। আপনার তো আবার ঠান্ডা সহ্য হয় না।
একদম সরু পথ দিয়ে গাড়ি ওপরে উঠছে। ভাঙাচোরা রাস্তা। বেশি টুরিস্ট বোধহয় এদিকে আসে না। ডানপাশে খাদের তলা থেকে অতিকায় লম্বা লম্বা গাছ আকাশে উঠে গেছে। কুয়াশায় ভিজে ভিজে তাদের গুঁড়ির রং কালো। তাদের গা থেকে মোটা মোটা দড়ির মতো সবুজ শ্যাওলা ঝুলছে। কি সুবিপুল গাম্ভীর্যে পূর্ণ চারিদিক। একটা অদ্ভুত অনুভতি হল সুবিমলের। এই অমর্তলোকে ওরা যেন অনধিকার প্রবেশকারী!
লাভা পৌঁছোতে দুঘন্টার বেশি লাগল। ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকেই একটা সরু পথ নীচে নেমে গেছে। খোঁজ নিয়ে জানল, গুম্ফা দেখতে এই রাস্তাটা ধরেই যেতে হবে। খাড়াই পথটা ধরে ভারি ব্যাগ হাতে নিয়ে তরতরিয়ে নামতে থাকে মায়া। সুবিমল পিছিয়ে যায়। চেঁচিয়ে বলে, একটু আস্তে হাঁটো না। মায়ার হাসি শোনা যায়, আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন।
বহুদূর থেকেই গুম্ফাটা দেখা যায়। রাস্তার দুপাশে ছোটো বড়ো দোকান। সবজির বাজার। লোকজন কম। গাড়ি চলছে না। দুএকজন সাইকেল চেপে যাচ্ছে। পথ ঘেঁষে রঙিন কাঠের বাড়ি। বড়ো বড়ো কিছু হোটেলও অবশ্য দেখা যাচ্ছে।
দূর থেকে যা মনে হয়েছিল গুম্ফাটা তার থেকেও অনেক বড়ো। কালিম্পং-এও গুম্ফা দেখেছে ওরা। কিন্তু সেগুলো আয়তনে এর অর্ধেকও হবে না। পাহাড়ের কিনারা ঘেঁষে প্রায় আধ কিলোমিটার লম্বা পাঁচিল চলে গেছে। তার ওপরে সারি সারি রঙিন নিশান উড়ছে। ভেতরে ঢুকে ওরা একটুক্ষণ পাঁচিলের ধারে এসে দাঁড়ায়। নীচেই কুয়াশা ঢাকা গভীর খাদ। দিয়া হাঁটতে হাঁটতে একটু এগিয়ে যায়। আশপাশে কেউ নেই।
সুবিমল বলে, এখান থেকে লাফ দিতে পারবে মায়া? মায়া ভুরু কুঁচকে তাকায়।
যত অদ্ভুত কথা আপনার।
না বলছি, ওই কুয়াশার মধ্যে লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে না?
বাজে কথা রাখুন, চলুন দিয়া কোথায় গেল দেখি।
একটা বাঙালি পরিবারের সাথে দেখা হয়। স্বামি-স্ত্রী আর তাদের মেয়ে। বউটি ফরসা ও সুন্দরী। মেয়ে কিন্তু দিয়ার মতোই কালো তবে খুব স্মার্ট। কনভেন্ট স্কুলে পড়ে। ওরাও কালিম্পং ঘুরে এসেছে শুনে ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করেন, ডেলো পার্ক তো গিয়েছিলেন, ওখানে প্যারাগ্লাইডিং করেছিলেন?
প্যারাগ্লাইডিং, কাঁধে নকল ডানা বেঁধে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেওয়া, ডেলোতে ছিল বটে। না ওটা হয়নি।
করেননি! সাচ্ আ প্লেজন্ট এক্সপেরিযে্নস। একেবারে কুয়াশার ভেতর দিয়ে উড়তে উড়তে এসে নীচে নামলাম। কিন্তু রেটটা একটু হাই। তিনজনের সাতহাজার টাকা পড়ে গেল।
সাত হাজার! একটা লাফের জন্য! তিনহাজার টাকায় ওদের কালিম্পং ঘোরা হয়ে গেল।
মহিলা ও তার মেয়ে সাথে গল্প করতে করতেই সুবিমল এগোয়। মায়ারা পিছিয়ে যায়। একবার মুখ ঘুরিয়ে দ্যাখে সুবিমল, বউটির হাজব্যান্ড মায়ার পাশে পাশে আসছে। এক ঘন্টার বেশি লাগল পুরো জায়গাটা ঘুরে দেখতে। একটা জপযন্ত্র দেখল, দুমানুষ সমান উঁচু। তার চাকা ঘুরিয়ে প্রার্থনা করতে হয়। ওরাও একটু ঘোরাল।
লাল জোব্বা পরে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এদিক ওদিক ঘুরছে। নিজেদের ভাষায় কিসব কথা বলছে। প্রত্যেকেই খুব হাসিখুশি। এই বিশাল সুন্দর প্রকৃতির কোলে, ভগবান বুদ্ধের অর্চনায় এরা যেন সত্যিকারের শান্তি খুঁজে পেয়েছে। একজন সন্ন্যাসীকে দেখল, মেঝেতেই বসে বসে খাচ্ছে। সাধারণ ডাল ভাত একটা তরকারি তাতেই মুখে ওনার কি অপরূপ আনন্দের ছাপ।
কী পিসফুল জায়গাটা বলুন। ভদ্রমহিলা বল্লেন, মনে হচ্ছে সব ছেড়েছুড়ে এখানেই থেকে যাই।
ভালোই হয় তাহলে! সুবিমল ভাবে। সেও এর সাথে থেকে যেতে রাজি আছে।
প্রার্থনা ঘরটা বিশাল। দেয়ালে কী সুন্দর রঙিন কারুকাজ। উঁচু আসনের ওপর নিমীলিতচোখ বোধিসত্ত্বের মূর্তির সামনে এসে একটু দাঁড়ায় সুবিমল। হাজার বছর বা তারও আগে, রাজার প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল যেই রাজার কুমার, সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে বলে। সেই বিশাল-হৃদয় পুরুষের জন্য হঠাৎ করেই এক অপরিমেয় শ্রদ্ধায় সুবিমলের মন অভিভত হল, কেন যেন হ্যাপি প্রিন্সের গল্পটা মনে পড়ে গেল। চোখ বুজে মনে মনে উচ্চারণ করল সে, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি হে অমিতাভ, হে তথাগত বুদ্ধ আমার প্রণাম নাও।
প্রার্থনা ঘর থেকে বেরিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আসুন আপনাদের নিয়ে একটা ছবি তুলি। তাঁর হাতে বড়ো লেন্সওয়ালা দামি ক্যামেরা। বললেন, আপনার কি কম্পিউটার আছে? তাহলে মেইল করে ছবি পাঠিয়ে দেব। মায়া খুব খুশি। লাভার একটা তো স্মৃতি থাকল। চলে যাবার সময়ে বউটা দিয়ার গাল টিপে একটা ক্যাডবেরি দিয়ে যায়।
ওরা যেতেই মায়া হাসতে হাসতে বলে, ভদ্রলোক আমার ফোন নম্বর চাইছিলেন।
দিলে?
না। দিলে বুঝি খুশি হতেন?
হতাম, সুবিমল হাসে।
ভদ্রলোক কিন্তু বুঝতে পেরেছেন আমরা বিবাহিত নই।
কী করে বুঝলেন?
ছবি তোলবার সময় আপনি আমার থেকে দূরে দূরে দাঁড়াচ্ছিলেন।
ওঃ!
আপনি তো ওই বউটা আর তার মেয়ে সাথেই সারাক্ষণ গল্প করে গেলেন। একটু থেমে মৃদু গলায় বলে মায়া, মা-মেয়ে দুজনেই কী সুন্দর ইংরেজি বলছিল। আপনার তো ভালো লাগবেই।
দিয়ার দিকে কটমটিয়ে তাকায় মায়া, আর এই ভ্যাবলা মেয়েটা সারাক্ষণ চুপ করেই থাকল। আন্টি যখন চকোলেট দিলেন একটা থ্যাংক ইউ বলতে পারলি না?
আঃ ছাড়ো। ছোটোদের অত থ্যাংক্স বলতে হয় না।
গুম্ফা থেকে বেরিয়ে ওরা সেই রাস্তাটা ধরে উঠছে। মায়া আর দিয়া একটু এগিয়ে ছিল। হঠাৎ করেই ওরা হারিয়ে গেল! একঝাঁক মেঘ এসে ওদের ঢেকে দিল। বেশ কিছুক্ষণ ওদের দেখতে পেল না সুবিমল। তারপরেই মেঘ সরে গেল। ওই তো মায়া। আবার নতুন একদল মেঘ এসে তাদের আড়াল করে দাঁড়াল। মায়া নেমে এসে সুবিমলের হাত ধরল। বলল, কী দারুণ না? সুবিমল মায়ার হাতটা চেপে ধরে। মেঘের ভেতর সাঁতার কাটতে কাটতেই ওরা একটা রেস্টুরেন্টের সামনে এসে দাঁড়ায়।
মায়া বলে, চলুন এটায় ঢুকি। দিয়ার খিদে পেয়েছে। রেস্টুরেন্টটা পুরোই ফাঁকা। দরজার কাছের টেবিলটায় এসে ওরা বসে। এখান থেকে রাস্তায় উড়ে যাওয়া মেঘ দেখা যাচ্ছে।
মায়া আর দিয়ার জন্য দু-প্লেট চিকেন চাউমিন আর নিজের জন্য থুপ্পা চাইল সুবিমল। থুপ্পা সেই মনে আছে দার্জিলিং-এ খেয়েছিল। কিন্তু এটায় সেই স্বাদ পেল না। মায়া নিজের প্লেট থেকে চাউমিন তুলে সুবিমলের প্লেটে দিল। খেয়ে দেখুন কি চমত্কার করেছে।
রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গিয়ে ওরা জানল, শিলিগুড়ি যাবার শেষ গাড়ি বেরিয়ে গেছে। তার মানে আজ রাতটা হোটেলেই থাকতে হবে।
সবজিবাজারের গলির ভেতর একটা ছোটো কিন্তু সুদৃশ্য হোটেল। চয়েস লজিং অ্যান্ড ফুডিং। সেটাতেই ঢুকল ওরা। ম্যানেজার অল্পবয়সি একটা ছেলে।
সুবিমল প্রশ্ন করল, ইঁহা কেয়া রুম মিলেগা?
ছেলেটি একটু হেসে বলল, দোতলায় একটা ঘরই খালি আছে, চাইলে দেখতে পারেন?
তুমি বাংলা বলতে পারো!
আমি শ্যামনগরের ছেলে, নাম রাজা। আপনারাও তো বাঙালি, দেখেই বুঝেছি।
বাঃ, তাহলে তো খুব ভালোই হল সুবিমল খুশি হয়ে ওঠে।
আসুন আপনাদের ঘরটা দেখিয়ে দিই।
সিঁড়ি দিয়ে ওদের ওপরে নিয়ে আসে রাজা। এটা বোধহয় হোটেলের পেছন দিক। একটা সরু করিডর দিয়ে হেঁটে ওরা একটা ছোটো বারান্দায় এসে দাঁড়াল আর দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেল। পুরো বারান্দাটাই ঝুলছে পাহাড়ের খাদের ওপর। একদিকে পাহাড়ের দেয়াল। সামনে মেঘে ঢাকা উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়া। হু হু করে কুয়াশা উঠে আসছে নীচ থেকে। বারান্দার লাগোয়া ঘরটাই ওদের দেখায়। সুন্দর সাজানো ঘর। পাশেই অ্যাটাচড বাথরুম।
ওদের অবাক করে দিয়ে মাত্র আটশো টাকা ঘর ভাড়া চায় রাজা। মায়া তবু বলে, ছশো টাকায় হবে না?
কম পড়ে যাবে দিদি।
না ওটাই রাখো।
আর কিছু না বলেই খাতায় ওদের নাম লিখে ঘরের চাবি তুলে দেয় রাজা।
ঘরের বিছানায় পা ছড়িয়ে বসে মায়া বলে, কখনও কল্পনাই করিনি এরকম ঘরে থাকব। ঘর থেকেই পাহাড় দেখা যাচ্ছে।
একটু রেস্ট নিয়ে ওরা বাইরে বার হয়। অন্ধকার নেমে এসেছে এখনই। ট্যাক্সিস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে একটু এগোতেই একটা বড়ো রাস্তা সোজা চলে গেছে। তার দুপাশে গভীর জঙ্গল। পুরো নির্জন পথ। কোনও শব্দ নেই, একটাও আলো নেই। শুধু উজ্জল তারার আলোয় নিরুদ্দেশ হাঁটতে থাকে ওরা।
মায়া বলে, দিয়া এখন যদি বাঘ বেরোয় তো কী করবি?
দিয়া একটু ভেবে বলে, বাঘ এলে যেন আমাকেই খায়।
কেন?
বাঃ, তোমাদের বাঘে খেলে আমি কার সাথে বাড়ি ফিরব? সুবিমল হেসে ওঠে। মায়াও। ফেরার পথেই রাতের খাবার খেয়ে নেয় ওরা।
হোটেলে ফিরে দিয়া টিভি চালায়। চ্যানেল পালটায় সুবিমল। জি সিনেমায় এসে দ্যাখে অনুসন্ধান সিনেমাটা চলছে। দ্যাখা ছবি, তবু আবার দেখতে বসে ওরা।
জানো তো, এই ছবিটার শুটিং পুরোটাই দার্জিলিং-এ হয়েছিল।
তাই?
ভোর হচ্ছে। ছবির মতো সাজানো চা বাগানের মধ্যে দিয়ে বেতের ঝুড়ি পিঠে ঘুরে ঘুরে নামছে পাহাড়ি মেয়েটা।
সত্যি কি সুন্দর! মায়া বলে।
অন্ধ নায়িকা গান করছে, ওঠো ওঠো সূর্যাইরে, ঝিকিমিকি দিয়া, কালকে তুমি আঁধার রাতে, কোথায় ছিলে গিয়া।
ইস, ওর কী কষ্ট তাই না?
কেন?
ও তো কোনওদিন সূর্যটা দেখতেই পাবে না।
সিনেমা দেখতে দেখতেই ঘুমিয়ে পড়ে দিয়া। ওরা জেগে থাকে। সিনেমা শেষ হচ্ছে, অমিতাভ বচ্চন রাখির কাঁধে হাত রেখে হাঁটছে।
সুবিমল বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। সিগারেট ধরায় একটা। ভেতরে গান চলছে, আমার স্বপ্ন যে সত্যি হল আজ।
মায়াও কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, বইটা সত্যিই খুব ভালো তাই না?
হ্যাঁ, কিন্তু অবাস্তব!
এমন কেন বলছেন?
অমিতাভের মতো একজন হ্যান্ডসাম পুলিশ অফিসার একটা অন্ধ মেয়েকে বিয়ে করছে। অবাস্তব নয়?
কেন, এরকম কি হতে পারে না?
জানি না। একটু চুপ করে থেকে সুবিমল বলে, এই যে তুমি আর আমি একসাথে ঘুরছি, রাতে শুচ্ছি। কিন্তু আমি কি তোমায় বিয়ে করতে পারব কোনও দিন?
না। আপনি করবেন না, আমি জানি।
তাহলে?
চুপ করে যায় মায়া। কিছুক্ষণ কেউই কথা বলে না। মুখ না ফিরিয়ে সুবিমল কেমন করে বুঝতে পারে, মায়া কাঁদছে। কোনও শব্দ না করেই।
আচ্ছা মায়া, এই যে আমি তোমাকে কোনও সম্মান দিতে পারি না। সবার কাছ থেকে আমাদের সম্পর্কটা লুকোতে চাই। এতে তোমার খারাপ লাগে না?
খারাপ লাগলেই বা কী করতে পারি।
মায়া বলে, আমি জানি তো আমি আপনার যোগ্য নই। আমি গরিব, পড়াশোনা জানি না। আবার একটা মেয়ের মা। আপনাকে বিয়ে করার কথা আমি নিজেই ভাবতে পারি না।
তুমি তো জোর করতে পারো।
কেন করব। জোর করে কি সব কিছু পাওয়া যায়?
কিছুক্ষণ আবার চুপ থাকে দুজনে।
আমি জানি কেন আপনি দার্জিলিং যাননি…
কেন?
আসলে বিয়ের পর বউকে নিয়ে দার্জিলিং যাবেন ভেবেছিলেন, তাই না?
কেন এরকম মনে হল তোমার?
এমনিই। আগে ভাবিনি, এক্ষুনি মনে হল। বলুন, ঠিক বলেছি কিনা।
জানি না।
হঠাৎ করেই সুবিমলের পাশে সরে এসে তার বুকে চুমু দেয় মায়া, আর তাকে জড়িয়ে ধরে। সুবিমল বুঝতে পারে তার বুকের কাছটা মায়ার চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে।
মায়ার মাথায় হাত বুলিয়ে সুবিমল বলে, কাঁদে না মায়া। বেড়াতে এসে এমন করে না।
আমি আপনাকে ছাড়তে পারব না।
কে ছাড়তে বলেছে তোমাকে। কেঁদো না।
আমায় ছ়েড়ে চলে যাবেন না তো?
যাবো না।
ঠিক?
ঠিক।
বাইরে লাভার নক্ষত্রভরা আকাশ ভগবান বুদ্ধের করুণাঘন দ্যুতিরময় চোখের মতো তাদের দুজনের দিকে চেয়ে থাকে।