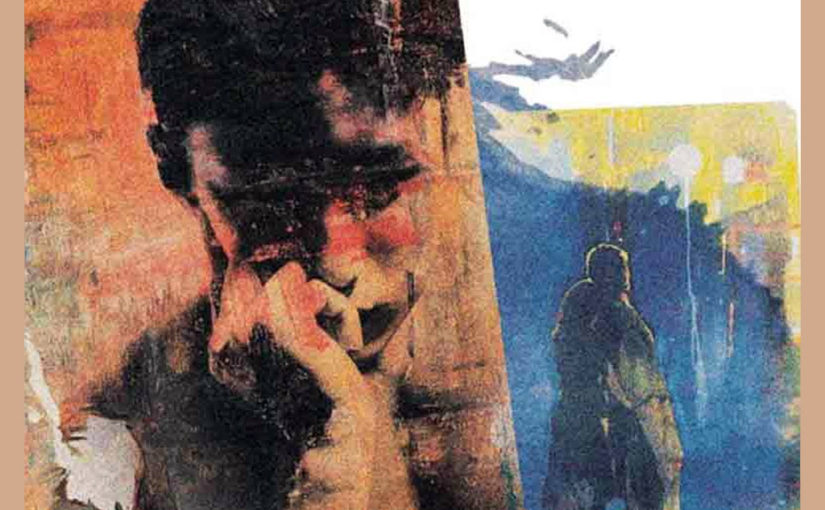বিডন স্ট্রিট পার হয়নি তখনও। ব্যাকসিটে হেলান দিয়ে সবে চোখ দু’টো একটু বুজেছে নীলোৎপল। শেষ কবে অটোয় উঠে এত আরামে বসেছিল মনে পড়ে না। বাঙালি গতরে বাড়ছে নাকি কলকাতার অটোগুলো বহরে ছোটো হচ্ছে ইদানীং কে জানে। দু’টোর পর তিনটে লোক যেই উঠল অমনি শুরু হল চাপাচাপি। অগত্যা সেই আগুপিছু করে বসা।
আজ প্রথমটায় একটু অবাকই লেগেছিল তাই। এই অটোটার পিছনের সিটে বসতে গিয়ে। আগে থাকতেই বসেছিল দু’টো লোক। তাকে উঠতে দেখে খুব একটা যে নড়েচড়ে বসল মনে হল না। কিন্তু সিটে পিঠ রেখেই টের পেল নীলোৎপল– বেঁকেচুরে বসার দরকার নেই কোনও। দিব্যি আরামে কাঁধ ছড়িয়ে বসা যাবে।
লোকগুলোর দিকে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছিল সে। সিড়িঙ্গে টাইপের চেহারা। গায়ে বেরঙা টি-শার্ট। একেবারে কর্নারের লোকটা কপালে হাত দিয়ে মাথা নামিয়ে বসেছিল। মুখখানা ভালো করে দেখতে পায়নি সে। যাকগে। কপাল করে অটোটা পেয়েছে। শোভাবাজার থেকে উলটোডাঙা কম রাস্তা নয়। আয়েশ করে যাওয়া যাবে। একসঙ্গে দু’ দু’টো এমনি রোগা রোগা লোক চট করে পাওয়া যায় না আজকাল। আর একজন এসে পড়লেই হয় এবারে। মোবাইল বের করে ফোন করে দিল সায়ন্তনকে, ‘শোভাবাজারে। এই অটোয় উঠলাম। আর-একজন হলেই ছাড়বে…’
‘শালা এতক্ষণে মোটে শোভাবাজার! সোনাগাছিতে ঢুকেছিলি নাকি?’
‘ক্যালানে। টাইম লাগে না নাকি বাসে আসতে। গ্লোবারের সামনেটায় দাঁড়া। সবাই এসে গেছিস?’
‘জয়ন্ত আর নির্মাল্যটা কোথায় কে জানে। বাকিরা এসে গেছি। তুই কুইক আয়…’
এরমধ্যেই গগলস্ চোখে সাতাশ আঠাশের একটা ছেলে ব্যাগ হাতে এসে বসে পড়ল ড্রাইভারের পাশের সিটে।
‘গৌরীবাড়ি…’
‘বসুন।’
অটো ছেড়ে দিল।
ফেব্রুয়ারির ফুরফুরে হাওয়ায় চোখ যেন লেগে আসছিল নীলোৎপলের। একেবারে ভর দুপুরে বেরিয়েছে। বাড়িতে থাকলে এতক্ষণে একঘুম হয়ে যেত। বিডন স্ট্রিট আসতে আসতে আপনা থেকেই বুজে এসেছিল চোখ দু’টো। আর ঠিক তখনই জিন্সের বাঁ পকেটে বেজে উঠল মোবাইলখানা। বিরক্তিতে এবার মুখচোখ রীতিমতো কুঁচকে উঠল তার। হারামজাদাগুলোর কি তর সইছে না একটুও! সেই গ্রে স্ট্রিট থেকে সমানে জ্বালিয়ে যাচ্ছে পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর। বিডন স্ট্রিট থেকে উলটোডাঙা অবধি কি সে উড়ে যাবে এখন। একবার ভাবল দরকার নেই ধরার। বেজে যায় যাক। কিন্তু ফোন আসতেই থাকবে সমানে। যতক্ষণ না ধরছে জ্বালিয়ে মারবে। বাধ্য হয়েই কলটা রিসিভ করতে হল। জয়ন্ত ফোন করছে। তারমানে সেও বোধহয় পৌঁছে গেছে এতক্ষণে।
ওপাশ থেকে সম্মিলিত গলায় ভেসে আসছে চার-পাঁচটা করে অক্ষর। আর কোনও কথা নেই। মনের সুখে গালি দিচ্ছে শালারা। নেহাত কাকার বয়সি লোকজন রয়েছে অটোয়। নইলে বাছা বাছা কয়েকখানা এখনই শুনিয়ে দেওয়া যেত বাছাধনদেরও। বিরক্ত গলায় শুধু বলে নীলোৎপল, ‘এই তো খান্নায় এখন। উড়ে যাব নাকি? অত তাড়া থাকলে চলে যা। বাপের বিয়ে লাগেনি আমার…’
কথা শেষ করে সুইচড অফ করে দিল নীলোৎপল। নে শালারা, এবারে যত পারিস ট্রাই করে যা। পৌঁছোনোর পর অবশ্য খিস্তি খেতে হবে কনফার্ম। তবে সেও ছেড়ে কথা বলবে না। অনেক তো দেখা আছে। এমন নয় যে পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে সেই প্রথম জব নামাল ক্যাম্পাসিংয়ে। জয়ন্ত, দেবরূপ, সায়ন্তন– সক্বলে আরও আগেই সব মোটা মোটা প্যাকেজের জব নামিয়ে বসে আছে। ট্রিট তো কে কেমন দিয়েছে দেখাই গেছে। সে তো তাও রাজি হয়েছে হাসিমুখে। নাকি তার চাকরিটা পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা ভাবছে সবাই! অন্যরা ক্যালকাটা বেল্টের এক একখানা নামি কলেজ থেকে বি টেক করছে। ভাল চাকরি তো পাবেই। আর সে যেহেতু জেলার একটা এলেবেলে কলেজ থেকে পড়ছে, কোনও গতি হতো না হয়তো। নেহাত ফাইনাল ইয়ারে অনেক হাঙ্গাম হুজ্জোত করে কলেজকে ক্যাম্পাসিং করাতে বাধ্য করে চাকরি জুটিয়েছে, তাই ট্রিট দেওয়াটা তার নৈতিক দায়!
কথাবার্তায় তো বোঝা যায়। স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে সবার আগে চাকরি পেয়েছিল অনুরাগ। ক্যাম্পাসিংয়ের আগের রাতে তাই তাকেই ফোন করেছিল নীলোৎপল, ‘কী টাইপের কোশ্চেন আসতে পারে বল তো। আমার তো কোনও এক্সপিরিয়েন্স নেই এসবের…’
‘তোদের টিচাররা কিছু বলছে না?’
‘ফার্স্ট টাইম ক্যাম্পাসিং হচ্ছে ভাই কলেজ হিস্ট্রিতে…’
‘আই সি। তা নামটা কি বললি যেন কোম্পানির?’
‘জিটিবি সল্যুশনস।’
‘কীসের কোম্পানি এটা? কথার সুরেই মনে হচ্ছিল নীলোৎপলের ফোনের ওপারে ভুরু কুঁচকোচ্ছে অনুরাগ।’
‘সফ্টওয়্যার।’
দায়টা তার নিজের। তাছাড়া সেই প্রথম ক্যাম্পাসিংয়ের পরীক্ষায় বসতে যাচ্ছে সে। অত গায়ে মাখাতে গেলে চলবে না তখন।
‘জন্মে নাম শুনিনি’, ফোনের ওপাশে বোধহয় ঠোঁট উলটাল অনুরাগ, মনে হল নীলোৎপলের। একটা গুঞ্জন ভেসে আসছিল অনেকক্ষণ থেকেই। দোকান বাজারে কোথাও রয়েছে নিশ্চয় অনুরাগ। তখনই নির্মাল্যর গলাও শুনতে পেল সে, ‘আর-একটা সোডা হবে দাদা এই টেবিলে..’
আরও কে কে আছে ওখানে সে কথা ভাবার সময় তখন নয়। তবুও মনে হয়েছিল এমন অসময়ে ক্যাম্পাসিংয়ের কোশ্চেন টাইপ নিয়ে ফোন এলে হয়তো বিরক্ত হতো সেও।
কিন্তু আশ্চর্য। বিরক্ত হয়েছে বলে মনেই হচ্ছিল না অনুরাগের গলা শুনে। অল্প কথায় কাজ মিটিয়ে ফেলার মতো কথাও বলছিল না সে। বরং নীলোৎপলের সঙ্গে যেন অনেক কথাই বলতে চাইছিল সে। হস্টেলের রুমের ভেতর থেকে টাওয়ার পাওয়া যায় না সবসময়। কথা বলতে বলতে আচমকা কেটে যায় ফোন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা লাগছিল নীলোৎপলের। শার্টের ওপরে স্রেফ একখানা চাদর জড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। কতক্ষণই বা কথা হবে– মনে হয়েছিল তখন, আবার উইন্ডচিটার পরবে! ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোপালপুরে কলেজ। সামনে দিয়ে স্টেট হাইওয়ে গেলেও সন্ধের পর মাইলের পর মাইল স্রেফ শুনশান। টাউন থেকে দূরত্ব প্রায় মাইল ছয়েক। বয়েজ হস্টেল ততোধিক নিশুতির রাজ্যে। কলেজ ক্যাম্পাস থেকে আরও এক কিলোমিটার উত্তরে। চায়ের দোকানটা বন্ধ হয়ে যায় সন্ধে নামার আগেই। জানুয়ারির মাঝামাঝি কেমন ঠান্ডা পড়তে পারে এমন তেপান্তরের দেশে, কলকাতায় বসে কল্পনাও করতে পারবে না কেউ। ক্যাম্পাসিংয়ের আগের সন্ধেটায় হুইস্কি নিয়ে বসারও প্রশ্ন নেই অনুরাগদের মতো। চাদরটা গায়ে বেশ করে জড়িয়ে নিচ্ছিল নীলোৎপল।
তখনই শুনতে পেল কলকাতার দিক থেকে অণুতরঙ্গে ভেসে আসা অনুরাগের কথাগুলো, ‘পুনে সাইডের কোম্পানি বললি না? রেপুটেড কিছু নয়। আসলে কি জানিস, তেমন অ্যাক্লেমড কোনও কোম্পানি হলে টাইপটা বলা যেত। কে কেমন টাইপ ফলো করে না করে। আসলে তোরা ঝামেলা করেছিস। ইমিডিয়েটলি কাউকে নিয়ে আসতে হবে। যা হয় আর কি। হুট করে তো রেপুটেড কারুর সঙ্গে কিছু ফিক্স করে ফেলা যায় না। তখন এই টাইপের ছোটোখাটো কাউকে ধরে আনে। যাদের কেমন কোশ্চেন প্যাটার্ন হবে কেউ বলতে পারে না।’
রাগারাগির কিছু নেই। একেবারে সত্যি কথাই বলছিল অনুরাগ। বরং এই অবস্থায় এতটা সময় হয়তো নীলোৎপল নিজেও দিত না কাউকে। গুঞ্জনের মাত্রা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে কলকাতায়। আর সেই তেপান্তরের অন্ধকার রাজ্যে একটুখানি আলেয়ার মতো জ্বলে থাকা বয়েজ হস্টেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ততক্ষণে বেশ ভালোই শিরশিরানি টের পাচ্ছে সে।
অনুরাগ বলে যাচ্ছিল, ‘একটা কাজ করতে পারিস। ওদের সাইটে ঢুকে দেখ তেমন কিছু পাস কিনা। সাইটে ঢুকলে ভুলভাল কিনা বুঝতেও পারবি। এরকম ধরে আনে তো অনেক এই টাইপের কলেজগুলো। এইরকম ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে। তোর কথা শুনে মনেও হচ্ছে তেমন যুতের কেউ নয় যারা আসছে। নইলে ভেবে দেখ না ক্যালকাটা থেকেই কেউ যেতে চায় না বীরভূমে ক্যাম্পাসিং করতে, আর পুনে থেকে এককথায় চলে আসছে…’
‘বীরভূম নয় এটা বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট,’ অনেকক্ষণ পরে একটা কথা বলেছিল নীলোৎপল।
তোরা শহিদ ধরে ফিরিস বলেছিলি না। শহিদ তো বীরভূম সাইডেই যায়…
বর্ধমান পেরিয়ে তবে তো বীরভূমে ঢোকে। অজয়ের ওপারে বীরভূম। তবে আমাদের কলেজ বীরভূম লাগোয়াই একরকম। গুসকরাতে নেমে…
‘আচ্ছা। আর সাইটে ঢুকে প্যাকেজটাও দেখে নিবি। আর-একটা কথা, বন্ডের ব্যাপারে কনশাস থাকবি। এসব আননোন কোম্পানির বন্ড তো! অরিজিনাল টেস্টিমোনিয়ালস জমা নিয়ে নেয় জয়েনিংয়ের সময় অনেকে। তারপর বন্ড পিরিয়ড যতদিন না শেষ হচ্ছে ওদের তাঁবে থাকে। আর পুনেতে মাসে কুড়ি হাজারে স্রেফ জলমুড়ি খেয়ে থাকতে হবে…’
‘ঠিক আছে। থ্যাংক্স ফর অ্যাডভাইস।’
আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে হয়নি। ঠান্ডা তো লাগছিলই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে একটা গরমও টের পেতে শুরু করেছিল। সেই হপ্তাখানেক আগে যেদিন বিকেলে কলেজের গেটে তালা মেরে ডিরেক্টর, রেজিস্ট্রার, ডিনদের মতো হোমরাচোমরাদের আটকেছিল গোটা ফোর্থ ইয়ার মিলে, সেদিনের মতো গরম।
হস্টেলের রুমে ঢুকে বেশ কয়েক মিনিট বসে খালি ভেবেছিল মদ খেয়ে একটুও কিন্তু নেশাড়ুর মতো কথা বলেনি অনুরাগ। কত সহজ স্বাভাবিক গলায় উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিল।
জিটিবির সাইটে অবশ্য ঢোকেনি আর সেই রাতে। চার বছরের সিলেবাসে তো কম সাবজেক্ট নেই। সাইট ঘেঁটে স্যালারি প্যাকেজের হিসেবনিকেশ করে ক্যাম্পাসিংয়ের আগের সন্ধেটা নষ্ট করার কোনও যুক্তি ছিল না। যা থাকে কপালে ভেবে যা যা দরকারি মনে হয়েছিল সবেতেই চোখ বোলাতে বোলাতেই বেজে গিয়েছিল রাত সাড়ে তিনটে।
ঠিক দু’ দিন বাদে সেই অনুরাগই যখন শুনল স্টার্টিংয়ে অ্যারাউন্ড ফর্টি প্লাস ও অ্যাকোমোডেশনের কথা, বলেছিল, ‘একদিন ট্রিট দিতে হবে কিন্তু বস। ম্যূলা রুঁজ। আর স্কচ। কোনও কথা শুনছি না। একেবারে ছক্বা মেরে দিয়েছিস। আমাদেরই শালা এই ছাতাপড়া ক্যালকাটায় ঘষতে হবে বসে বসে…’
এক বছরের পারফরম্যান্স দেখবে জিটিবি। ভালো করতে পারলে নেদারল্যান্ডস, ইটালি বা ব্রিটেনে পাঠিয়ে দিতেও পারে তারপর।
নীলোৎপল ভাবছিল দু’দিনের ভেতরেই দর কোথা থেকে কোথায় চলে যায় একলাফে। সত্যি সেই রাতে যা খেটেছিল সেমিস্টারের আগের রাতেও অত খাটেনি চার বছরে কোনও দিন। অবশ্য খাটতে হয়ও না সেমিস্টারে। ওই তো কলেজ। আর তার ওই তো সব ফ্যাকাল্টি। সিলেবাস শেষ করাতে কালঘাম বেরিয়ে যায় তেনাদের। চোতা সঙ্গে না থাকলে বোর্ডে একটা সার্কিট ঠিক করে অাঁকতে পারে না এমন লোকও আছে। তা স্যার ম্যাডামরা ক্লাসে চোতা নিয়ে আসবে আর তারা মাইক্রো জেরক্স নিয়ে হলে ঢুকলেই যত দোষ! অবশ্য ওইটুকু চক্ষুলজ্জা ফ্যাকাল্টিদেরও আছে। দু’একজন ঝামেলা করে না এমন নয়। প্রথম দেড়ঘন্টায় নিজে লিখতে হবে। পিছন ঘোরা যাবে না। তবে মোটের উপর নির্বিঘ্নেই কেটে যায় সেমের দিনগুলো।
একটু হেসে বলেছিল নীলোৎপল, ‘ঠিক আছে। আগে ফিরি। কলেজের এদেরও খাওয়াতে হবে। ফেব্রুয়ারি আঠের’র আগে নো চান্স।’
‘আচ্ছা’, অনুযোগের গলায় বলেছিল অনুরাগ, ‘এখন আমরা স্কুলের বন্ধুরা সব পুরোনো হয়ে গেলাম।’
‘তোরা তো পুরোনো বন্ধুই।’
ঠান্ডাটা অনেকটাই কমে এসেছিল মাঝের দু’দিনে। আর সেদিন ঘন্টার পর ঘন্টাও যদি কথা বলতে চাইত অনুরাগ, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে কোনওই আপত্তি ছিল না নীলোৎপলের।
সেই পুরোনো বন্ধুদের জন্যই ছুটির দিনের ভাতঘুমটা মাথায় তুলে আজ বেরোতে হয়েছে। আবার দশ মিনিট দেরি হচ্ছে বলে খিস্তিও খেতে হবে! কোথাকার লাটের বাঁট রে তোরা। পড়তিস তো কবে একসাথে মিত্র ইন্সটিটিউশনে। সেই খাতিরে গলাখানা ভালো করেই কাটার প্ল্যান করেছিলি সবকটায় মিলে। পার্ক স্ট্রিটের বাইরে তো বেরোতেই চাইছিলি না। অনেক দরাদরি করে উলটোডাঙার গ্লোবার অবধি নামা গেছে। শিয়ালদার টাওয়ারে নিয়ে গিয়ে শালা ট্রিট দেওয়া উচিত ছিল তোদের।
মনে আছে চার বছর আগে যখন ভর্তি হয়েছিল বিআইইএমে, কলেজের নামটা নিয়েও কি হাসাহাসি সক্বলের।
‘আর কলেজ পেলি না? বোর্দুরিয়া ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট! তার চাইতে প্রেসিডেন্সি বা জেভিয়ার্সে অনার্স করতে পারতিস ইংলিশেও…’
‘যাক, পরের উইকে ফিরবি যখন টিনটিনের অটোগ্রাফ নিয়ে আসতে ভুলিস না কিন্তু।’
‘দেখিস আবার কলেজটার অ্যাফিলিয়েশন আছে তো রিয়েলি? চার বছর বাদে যেন কলেজটাই না ইমাজিনারি হয়ে যায়।’
‘হ্যাঁ রে, এত কিছু থাকতে হঠাৎ বোর্দুরিয়া কেন নামের ডগায়?’
দেবরূপ, সায়ন্তন, জয়ন্তদের চাট খেতে খেতে বলতে হয়েছিল, ‘যতদূর শুনেছি ম্যানেজিং ট্রাস্টির মেয়ে টিনটিনের কমিক্স খুব ভালোবাসে। আর মেয়ে নাকি খুব লাকি লোকটার। মেয়ের জন্মের পরেই বিজনেস ফুুলে-ফেঁপে উঠেছিল ম্যানেজিং ট্রাস্টির। তাই যখন লোকটা এডুকেশন সেক্টরে এল…’
‘বোর্দুরিয়া নাম দিয়ে দিল! রগড় কিন্তু হেভি…’
সেই বোর্দুরিয়া ইন্সটিটিউট চাকরি দিয়েছে বলেই শালারা আজ ফোকটে গলা অবধি মদ খাবি। ভাবতে ভাবতে নীলোৎপলের মনে হয়, ট্রিট যদি অনেস্টলি দিতেই হয় বরং দেওয়া উচিত ছিল বিআইইএমের মেকানিক্সের টিচার তমাল রায়চৌধুরিকে। শুধু তার একার নয় সব স্ট্রিম মিলিয়ে গোটা ফোর্থ ইয়ারের যে-আটান্ন জন চাকরি পেয়েছে তাদের সক্বলের চাঁদা তুলে ট্রিট দেওয়া উচিত ছিল টিআরসি স্যারকে।
নইলে প্লেসমেন্ট সেল তো ওই ঠুঁটো জগন্নাথ। ষোলো তারিখ বিকেলে যখন তালা পড়ল কলেজের গেটে, কোন ফাঁকে যে প্লেসমেন্ট অফিসার পাঁচিল টপকে ভেগেছিল সবার আগে কেউ জানতেও পারেনি ঘুণাক্ষরে। কেমন করে যে সময় থাকতেই খবর পেয়ে গিয়েছিল লোকটা– সেও এক রহস্য। যাহোক, তারপর আর এক সপ্তাহ টিকিটাও দেখা যায়নি প্লেসমেন্ট অফিসারের। এক হপ্তা ধরে নিয়ম করে গোটা ফোর্থ ইযার সকালে এসে তালা মেরে দিয়েছে কলেজের গেটে গেটে। ফ্যাকাল্টিরা সেই তেপান্তরের মাঠে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। সিগারেটের পর সিগারেট ফুঁকেছে। হস্টেল থেকে ব্যানার বানিয়ে এনে ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্টরা মাঝেমধ্যে হল্লা তুলেছে। অন্যান্য ইয়ারের ক্লাসও শিকেয় উঠেছে। কিন্তু ম্যানেজমেন্টের হেলদোল নেই। ডিরেক্টর স্যার অবশ্য ফোন করে চলেছেন কলকাতার হেড অফিসে। কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি উঁচুতলা থেকে। একটা সপ্তাহ কাটার পর স্টুডেন্টদের নিজেদের মধ্যেই জল্পনা– এভাবে আর কতদিন? শেষ অবধি ভবিষ্যৎ কী?
এই সময় আচমকা একদিন খবর পাওয়া গেল প্লেসমেন্ট অফিসারের অবর্তমানে কোম্পানির সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল টিআরসি স্যারকে। তা নিজের ব্যক্তিগত চেনা পরিচিতির লিংক থেকে টিআরসি নাকি যোগাযোগ করেছেন পুনের জিটিবি সল্যুশনসের সঙ্গে। ঊনত্রিশ তারিখ নাকি কলেজে আসছে জিটিবি। বিশ্বাস অবিশ্বাসের একটা মিশ্র বাতাবরণ তৈরি হল স্টুডেন্টদের ভেতর।
ভর্তির সময় ব্রোশিওরেও লেখা ছিল না সেভেন্টি পারসেন্ট ক্যাম্পাসিং ফেসিলিটি, এসি ক্লাসরুমের গল্প…
হস্টেল মে সেপারেট রুম ভি লিখা হুয়া থা। কাঁহা গয়া ভাই উয়ো সব? এক রুম কে অন্দর ইধার তো চার চার লোগোকো শেয়ার করনা পড়তা হ্যায়।
ইতনা ঘাটিয়া খানা ভি জিন্দেগি মে নেহি মিলি
লেকিন আভি ইসি ওয়াক্ত অ্যায়সা ঝুট ক্যাহেগা ইয়ে লোগ?
সেটাই। এই কন্ডিশনে পাগল না হলে কেউ এরকম গুজব রটাবে না…
পরের দিনই নোটিস পড়ে গেল মেন গেটের সামনে। ঊনত্রিশ তারিখ জিটিবির ক্যাম্পাসিংয়ের খবর দিয়ে। হইহই করে তালা খুলে দিল ফোর্থ ইয়ার। কলেজের নোটিস বোর্ডে এতদিন খালি সেমিস্টারের আগে অ্যাটেডেন্স কমের অজুহাতে ফাইনের নোটিসই বেরিয়েছে। চার বছরে এই প্রথম
ক্যাম্পাসিংয়ের নোটিস ঝুলল সেখানে। স্ট্রাইক তুলে সবাই ছুটল হস্টেলে। ধুলো ঝাড়তে হবে বইপত্রের।
দু’একজন বলাবলি করে সন্ধের পরে, ‘বেশ ছিল কিন্তু ভাই। দিনে স্ট্রাইক আর রাতে মাল। পড়তে পড়তে এখন কেলিয়ে যাচ্ছি।’
আঠাশ তারিখ সকাল থেকে ঝাঁট পড়তে লাগল গোটা কলেজ বিল্ডিংয়ে। লনের ঘাস ছাঁটা হল। গাছের পাতা সরিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেলা হল ক্যাম্পাস। চার বছরে কেউ কখনও যা দেখেনি সেটাই ঘটল ঊনত্রিশ তারিখ সকালে। আটটার মধ্যে ডিরেক্টর, রেজিস্ট্রার, ডিনের মতো হোমরাচোমরারা সক্বলে স্যুট, টাই পরে হাজির। কলকাতা থেকে হেড অফিসের লোক চলে এসেছিল আঠাশ তারিখ রাতেই। মেন টাউনে লজ ভাড়া করে ছিল রাতে। তারাও গাড়ি নিয়ে হাজির সাড়ে ন’টার ভেতর। বিল্ডিংয়ের প্রত্যেক ফ্লোরে বারান্দায় বারান্দায় টবে করে ফুলগাছ এনে বসানো হয়েছে। সুগন্ধে ম ম করছে সব ক’টা ফ্লোর়, মায় টয়লেট অবধি। সাড়ে দশটার পর স্যুট বুট পরে হাজির জিটিবির এইচআর পার্সোনেলদের টিম। কলেজের মাথাদের সঙ্গে সঙ্গে টিআরসি স্যারও এগিয়ে গিয়ে হ্যান্ডশেক করল জিটিবির লোকজনের সঙ্গে।
‘খুচরো দেবেন দাদা,’ অটোওলার কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফেরে নীলোৎপলের। গৌরীবাড়ি এসে গেছে। সামনের সিটের সেই গগল্স পরা ছেলেটা পার্স থেকে একটা কুড়ি টাকার নোট বের করেছিল। অটোওলার কথায় নোটটা আবার পার্সে ঢুকিয়ে কয়েন বের করতে থাকে।
তার কাছে আছে তো খুচরো পয়সা? এই এক হয়েছে ঝামেলা। বাসে ট্রামে দোকানে বাজারে যেখানেই যাও, আজকাল খুচরো নিয়ে ঝঞ্ঝাট। তিরিশ টাকার মিষ্টি কিনে একশো টাকার নোট ধরালেও বিনা বাক্যব্যয়ে সত্তর টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছে ময়রা। কিন্তু তিন চার টাকার খুচরো নিয়ে কথা কাটাকাটি বেধে যাচ্ছে। সব খুচরো কয়েন শালা নাকি ব্লেড বানাতে চলে যাচ্ছে। তার কাছে আছে তো খুচরো কিছু? বাসভাড়া দেওয়ার সময় বেরিয়েছে একবার। দেখে নেওয়া ভালো এখনই। বাঁদিকে একটু আড় হয়ে নীলোৎপল ডান পকেট থেকে পার্সটা বের করতে যায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অটোর ব্যাকসিটের আরোহী একেবারে ডান কর্নারের লোকটার মুখের উপর নজর পড়ে যায় তার। কপাল থেকে হাত সরিয়ে সিড়িঙ্গে লোকটা গৌরীবাড়ির গলির দিকে তাকিয়েছিল একদৃষ্টে।
আরে, এই লোকটাই তো জিটিবির এইচআর টিমের হয়ে বিআইইএমে গিয়েছিল। নীলোৎপলের ফাইনাল রাউন্ড ইন্টারভিউ এই লোকই নিয়েছিল। বেশ মনে আছে। দু’একটা কথা ইংলিশে হওয়ার পর লোকটা সটান জিজ্ঞেস করেছিল, ‘আর ইউ কমফর্টেবল ইন হিন্দি? আই থিঙ্ক সাচ। সো মাচ নন বেঙ্গলিজ ইন ইওর ক্যাম্পাস। মাস্ট ইউ নো হিন্দি।’
একটু অবাক হলেও তখন মনে হয়েছিল ভালোই হল। শালা মনে মনে ট্রান্সলেট করে করে ইংলিশ বলার থেকে তো হিন্দিটা বলতে পারবে তুরন্ত। জন আব্রাহামের এত সিনেমা নইলে কেন বেকার বেকার দেখল এতদিন! তাছাড়া কলেজেও বেশির ভাগ স্টুডেন্ট হয় বিহারি নয়তো ইউপির বলে স্যার ম্যাডামদের দু’একজন বাদে বাকিরা হিন্দিতেই পড়ান। ইংলিশে পড়ান দু’একজন টেঁটিয়া টাইপের স্যার। শালা অত দেমাক যখন বিআইইএমে পড়ে আছিস কেন? সেখানে পুনের কোম্পানির এইচআর ম্যানেজার কেমন সুন্দর সেধে হিন্দি বলতে চাইছে।
সেই লোকটির সঙ্গে এক অটোতে যাচ্ছে নীলোৎপল! স্বপ্নের মতো মনে হয় তার। বাবা মার কাছে শুনেছে, যে-লোক সত্যিকারের গুণী বাইরে সে অতি সাধারণ হয়। সেদিন ভদ্রলোকের পরনে ছিল ঝকঝকে স্যুট টাই। অফিসিয়াল কাজে ভিজিট। দামি পোশাক তো থাকবেই। অথচ আজ কেমন সাধারণ টি-শার্ট আর একটা স্যান্ডেল পায়ে অটোতে উঠে পড়েছেন। একটা রিস্ট ওয়াচ অবধি নেই কবজিতে। অটো তখন সবে স্টার্ট দিয়েছে আবার গৌরীবাড়ি থেকে। ভদ্রলোককে দেখে নীলোৎপলের মনে হল কোনও মেকি গাম্ভীর্য থাকা সম্ভবই নয় এই লোকের। নইলে সেদিন তাকে ভেবে ভেবে ইংরেজি বলতে দেখে ওইভাবে সরাসরি হিন্দি বলতে সাহস জোগাতেন না। আচ্ছা, আলাপ করলে হয় না ভদ্রলোকের সঙ্গে! নাকি ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু হবে! না, তা কেন। একটা কথা জিজ্ঞেস করে তো কথা পাড়াই যায়।
ভদ্রলোক রাস্তার বাঁদিকেই তাকিয়েছিলেন তখনও। একবার গলা খাঁকারি দিয়ে নীলোৎপল বলে ওঠে, ‘এক্সিউজ মি স্যার, আপলোগ ভিজিট কিয়ে থে না হামারে বিআইইএম কলেজ মে। পিছলে মাহিনে…’
ভদ্রলোক বোধহয় অন্যমনস্ক ছিলেন। হঠাৎ করে খেয়াল করতে পারেন না নীলোৎপলের কথা। একটা জিজ্ঞাসু চাহনিতে তাকালেন তার মুখের দিকে।
নীলোৎপল আবার বলে, ‘স্যার মুঝে পহেচানা? বিআইইএম কলেজ মে পড়তে হ্যায়। মুঝকো সিলেক্ট কিয়া স্যার আপনে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার কব ভেজেঙ্গে স্যার? জুলাই মে হি?’
ভদ্রলোক হঠাৎ এমন চমকে উঠলেন জীবনে কাউকে এতখানি চমকাতে দেখেনি নীলোৎপল। সে আশ্চর্য হয়ে যায়। ভদ্রলোকের মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে আচমকাই।
‘অ্যাই, রোকিয়ে। অটো ইধার হি রোকিয়ে। তুরন্ত রোকিয়ে ভাই…’
ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষার আওয়াজ। অটোওলা বিরক্ত হয়েছে স্বভাবতই। বলতে থাকে, ‘আরে ঠিকঠাক বাতাইয়ে কাঁহা ইতরেগা। উধার বোলা উলটোডাঙা…’
নীলোৎপলকে প্রায় টপকে নেমে যান জিটিবির এইচআর ম্যানেজার ভদ্রলোক। পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে দিয়েই আর তিলমাত্র অপেক্ষা করেন না ফিরতির। অটোওলাও অবাক হয়ে গেছে। মুখে বলে, ‘পাগলা নাকি রে ভাই। ফেরত পয়সাটা নিয়ে যাবি তো নাকি। এরকম লোক রোজ যেন ওঠে কয়েকটা করে…’
কী হয়ে গেল আচমকা বুঝতে পারে না নীলোৎপল। ভদ্রলোক এমন চমকে উঠলেন কেন তাকে দেখে? তবে এরই মধ্যে খেয়াল করেছে সে কোনও পার্স ছিল না ভদ্রলোকের সস্তার ট্রাউজার্সের পকেটে। পকেট থেকেই নোটটা বের করে দিয়েই প্রায় দৌড়ে উলটোমুখে যেন পালিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।
অটো আবার চলতে শুরু করে। বোকা বনে যাওয়ার মতো মুখ করে বসে থাকে সে। এই মুহুর্তে অটোয় আরোহী মাত্র দু’জন। রোগাভোগা চেহারার অন্য লোকটা একবার তাকায় তার মুখের দিকে। তার চোখেও জিজ্ঞাসু চাহনি।
অরবিন্দ সরণির মাথায় উঠে যানজটশূন্য পথ। তিরের গতিতে ছুটতে থাকে অটো। সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্রমশ বোকা বোকা ভাবটা কেটে যায় নীলোৎপলের। বিচারবুদ্ধি কাজ করতে থাকে আবার। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক কথাই পরিষ্কার হতে থাকে ক্রমশ। পুনের কোম্পানির এইচআর ম্যানেজার ক্যাম্পাসিং শেষ হয়ে যাওয়ার হপ্তাখানেক পরেও কেন কলকাতায় বসে আছে। যদি ছুটিতেও লোকটা থেকে যায় বাড়িতে তবে কেন প্রাইভেট গাড়ি নিদেনপক্ষে ট্যাক্সিতেও চাপেনি এই দরের একজন মানুষ। আর যদি স্রেফ তর্কের খাতিরেই অটোতেও চাপল তবে কেন গৌরীবাড়িতেই নেমে গেল সে। উলটোডাঙায় যাবে বলে উঠেছিল যেখানে অটোয়। তাকে দেখে ভূত দেখার মতো লোকটার চমকে ওঠার কারণটুকুও বুঝতে আর বাকি থাকে না।
উলটোডাঙার স্ট্যান্ডে পৌঁছে গেছে অটো। ধীরে ধীরে রাস্তায় নেমে আসে নীলোৎপল।
সেই মুহূর্তে মনে পড়ে যায় অনুরাগের কথাগুলো– ‘হুট করে তো রেপুটেড কারুর সঙ্গে কিছু ফিক্স করে ফেলা যায় না।’
অনুরাগরা নিশ্চয় এতক্ষণে অনেকবার ফোনে ট্রাই করে ফেলেছে তাকে। দঙ্গল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে গ্লোবারের সামনেটায়। দেখতে পেলেই চরম খিস্তিতে ভূত করে দেবে বলে।
কিন্তু অনুরাগদের মুখোমুখি দাঁড়ানোর মতো মুখ আর নেই তার। যদি অটোর সেই লোকটা ঊনত্রিশে জানুয়ারি না যেত তাদের কলেজে, তাহলেও বরং আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারত ওদের সামনে।
অটোর ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে রাস্তার মাঝখানটায় এসে দাঁড়ায় নীলোৎপল। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে শোভাবাজারের দিক থেকে দৈত্যের গতিতে তার শরীরের দিকে এগিয়ে আসা একটা বাসের দিকে।