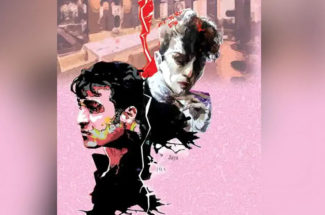( ১ )
পার্টিকুলার হরিণ নামটা কবে কে রেখেছিল জানে না ও। তবু মাঝে মাঝেই মনে হয় ঠিক ওই সাদামাটা নামটাই বড্ড বেশি উপযুক্ত ওর। ওই নির্দিষ্ট বুনো প্রাণীটার যা কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঈশ্বর যেন খুঁজে পেতে ওর মধ্যেই উপচে দিয়েছেন। পটলচেরা মায়াময় চোখ, পাতলা শরীর, আর ছটফটে দুখানা পাতলা কান,
যে-কানে দুনিয়ার যা কিছু খারাপ কেবল একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেই টের পায়, অনুভব করে। কিন্তু গলা ফেঁড়ে বলতে পারে না। কইতে পারে না কস্তুরী।
হ্যাঁ এটাই হরিণের পোশাকি নাম। বাবা দিয়েছেন। তেমন একটা ভালো লাগে না ওর নামটা। নামটার মধ্যে যেন একটা উগ্রতা মিশে আছে। একটা ধারালো উগ্রতা। জন্মের সময় ওর চোখ, মুখ, টিকালো নাক, এমনকী, মাস্ক ডিয়ারের মতো মাড়ির দু-পাশের গজদাঁত দেখেই মনে হয় পিতৃদেব নামকরণ করে ফেলেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কী, কস্তুরী তো হরিণেরই অংশ। তবে…? আবার এটাও সত্যি সব হরিণই কিন্তু কস্তুরী হরিণ নয়। ঠিক পরিষ্কার করে বোঝাবার নয়।
একদিক থেকে কস্তুরী নাভির গন্ধই যেমন হিমালয়ে পাদদেশের মাস্ক ডিয়ার নামক পুরুষ হরিণদের সবার থেকে ওদের আলাদা করে, ঠিক তেমনই ওই উগ্র নাভিগন্ধটুকুই তো কখনও কখনও নিরীহ প্রাণীটার প্রাণঘাতী। একথা সবাই জানে, কস্তুরীর সৌন্দর্য্য যতই সুন্দর হোক, তার বিনাশের কারণই হল তার অলৌকিক সৌন্দর্য্য। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কলেজবেলায় পড়া রবি ঠাকুরের লেখা গুটিকতক কথা—
সৃষ্টিকার্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য রহস্যময় কারণ জগত্রক্ষায় তাহার একান্ত উপযোগিতা দেখা যায় না। সৌন্দর্য্য অন্ন নহে, বস্ত্র নহে, তাহা কাহারও পক্ষে প্রত্যক্ষরূপে আবশ্যক নহে। তাহা আবশ্যকের অতিরিক্ত দান। তাহা ঈশ্বরের প্রেম। এইজন্য সৌন্দর্য্য অতীব আশ্চর্য্য রহস্যময়। মানুষ আপন সভ্যতাকে যখন অভ্রভেদী করে তুলতে থাকে তখন জয়ে স্পর্ধায় বস্তুর লোভে তুলতে থাকে যে-সীমার নিয়মের দ্বারা তার অভু্যত্থান পরিমিত। সেই সীমায় সৌন্দর্য্য, সেই সীমায় কল্যাণ। সেই যথোচিত সীমার বিরুদ্ধে নিরতিশয় ঔদ্ধত্যকে বিশ্ববিধান কখনওই ক্ষমা করে না। প্রায় সব সভ্যতায় অবশেষে এসে পড়ে এই ঔদ্ধত্য এবং নিয়ে আসে বিনাশ।
অপরকে আকর্ষণ করে নিজেকে মেলে ধরতে চায় না ও। চায় খুব সহজ স্বাভাবিক ভাবে জীবনের ভালোমন্দ খোপগুলো একে একে পেরিয়ে একটা শান্তির ঠিকানা! তাই কস্তুরী নয় উলটে হরিণ বলে বাড়ির কেউ ডাকলে ও মনে মনে খুশি হয়। চোখ বুজে খানিক ভেবে নেয় দিনের ভালোটুকু। কথাগুলো খুব বোকা বোকা তাই না? ও তো বোকাই, নাহলে এভাবে কেউ বারেবারে নিজের মানুষদের কাছে ঠকে…? বুকের ভেতরটা তিরতির করে ওঠে। গুঁড়ি মেরে হৃত্পিণ্ডের কাছে ঘুরঘুর করতে থাকে ভয়টা, সেই ভয়টা যা ওকে সবকিছু থেকে টেনে আনে পিছনের সারিতে।
আজকাল কেড়ে নেবার যুগ, ছিনিয়ে নেবার যুগ। জোর গলায় নিজের অধিকারকে জিইয়ে রাখার যুগ, অন্যের কাছে নিজের প্রযোজনকে জাহির করার যুগ। সেটা যে পারে না, তার কি সত্যি সত্যি এগোনোর স্বপ্ন দেখতে আছে? কিন্তু ভাবনাগুলো কি মনের আগলে বন্ধ করে রাখতে পারবে? যখন ঘরেই এত কিছু ঘটছে। মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। অস্থির পায়ে জানলার কাছটা দাঁড়ায়।
একতলা থেকে হালকা হাসাহাসি আর শাঁখের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। বল্টুমামা প্রতিবার এই সময় ঠিক ছুটি নিয়ে সপরিবারে কলকাতা আসেন। সরশুনায় গিয়ে নিজের মা বড়োদাদার সঙ্গে দেখা না করলেও কলকাতা আসেন বোনের বাড়ি, ফোঁটা নিতে। বউ আর ছেলেমেয়েকে ইছাপুর মামির বাপেরবাড়ি রেখে পাতপেড়ে আমোদ করে যান এক সপ্তাহ।
বল্টুমামা রেলের নামজাদা অফিসার। কস্তুরীর মায়ের ছোটো ভাই। পুজোয় ওঠা স্পেশাল শাড়ি আর এককাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে হাসিমুখে কস্তুরীদের বাড়ি এসে হাজির হন ঠিক ভাইফোঁটার আগের দিনে। ওর মা-ও সকালের লুচি তরকারি থেকে দুপুরে রাতে রুই মাছের কালিয়া, পাবদার ঝাল, সর্ষে ইলিশ, কষা মাংস, চিকেন রেজালা, দশ টাকা দামের রসগোল্লা, ঘরে পাতা টকদই প্রভতি এলাহি কারবার করে সাজিয়ে দেন ভাইয়ের পাতে।
মা-র কী একবারও বড়োমামার কথা মনে পড়ে না? কতবার জিজ্ঞেস করেছে কস্তুরী। শুনে এসেছে একটাই উত্তর, বড়দার শরীর খারাপ আসতে পারবে না। আমি তাই তো বড়দার জন্য দেয়ালে ফোঁটা দিয়ে দিচ্ছি। তাতেই হবে। এসব তো কথার কথা। ও জানে মনে মনে মা নিজের বড়োদাদাকে চায় না। আসলে বড়োমামা যে অসফল। বড়োমামা যে মুখচোরা। মায়ের জন্য দামি শাড়ির উপহার আনার ক্ষমতা তাঁর নেই।
দাদু রিটায়ার করবার আগে সংসারের বড়ো ছেলেকে রেলের যে-কোনও দফতরে ঢোকাতে চেয়েছিলেন কিন্তু বড়োমামা সেসময় ফুটবল ছাড়া আর কোনও স্বপ্নই দেখতেন না। চাকরি, রোজগার এসবে সিরিয়াস না হওয়ায় একটু একটু করে বড়োমামার বয়সটাও বেড়ে যায়। কিন্তু সময় কি কারও জন্য থেমে থাকে? চাকরি বড়োমামার হাত থেকে পিছলে ছোটোমামার দিকে চলে যায়।
ছোটোমামা রেলের চাকরিতে ঢুকে যান। সেই থেকেই ছোটোমামার টাকায় আর খানিকটা দাদুর পেনশনে দিম্মাকে নিয়ে বড়োমামা নিজের অবিবাহিত জীবন কাটাচ্ছেন। ওর বেশ মনে আছে, শেষবার যখন মামার বাড়ি গেছিল, ফেরার সময় বড়োমামা ওর হাত চেপে ধরে বলেছিল, একদিন তোদের বাড়ি যাব।
ও বুঝতে পেরেছিল মামা এখানে আসতে চায়। কিন্তু পারে না। পারে না তাঁর দুর্বল রোজগারের দিকে চেয়ে পারে না ছোটোবোন ভাইয়ের থেকে পিছিয়ে থাকার লজ্জায়। হোক লজ্জা, হোক পিছিয়ে থাকার ভয় তবু কস্তুরী এইসব মানুষগুলোকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে। মনে করে এই পৃথিবীর দূষণে এখনও কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের হৃদয়ে আজও দূষণের হদিশ মিলবে না। কোথাও একটা চাপা আনন্দের হদিশ পেয়ে ঝিলমিলিয়ে ওঠে ও। মন বলে, হরিণ তুমি একা নয়, আরও কিছু মানুষ আছেন যাঁরা অনেকটা তোমারই মতো।
আছেই তো…। ইশ অনেকটা সময় নষ্ট করেছে। তৈরি হতে হবে। দরজাটায় ছিটকিনি দিয়ে হলুদ রঙের কুর্তিটা পরে নেয়। কপালের ওপর ঝুঁকে পড়া ছোটো চুলটা ঠিকঠাক করে নেয় আলতো হাতে। এক ফাঁকে অগোছালো ঘরটাকেও গুছিয়ে নেয়। এই সাজটা ওর নিজের জন্য। নিজের ভালোবাসার জন্য। জানে অলক্ষে কেউ তো…। ওর পোশাক, কথা বলার ধরন, থুতনির নীচে ঢেউ খেলে যাওয়া টোলের কথা নাহলে জানবে কী করে ও?
বইয়ে তাক থেকে বার করে আনে চিঠিটা। সাদা পাতায় লেখা চারপাতার একটা লম্বা চিঠি। বাবাঃ লিখতে লিখতে মনেই হয়নি চিঠিটা এতটা বড়ো হয়ে যাবে। এভাবে লিখতে না বসলে কস্তুরী নিজে জানতেই পারত না ওর বুকের ধাপে এত কিছু আটকে রয়েছে। সেই অনেকটা পাঁককাদায় আটকে পড়া মাছগুলো যেভাবে খাবি খায়, বাঁচার জন্য আকুলিবিকুলি করে। তেমনই কথাগুলোও মাথা নীচু করে বসে হাপরের মতো দম নেবার চেষ্টা করছিল। কলমে ভর করে সরসরিয়ে বেরিয়ে এসেছে অক্সিজেনের আশায়।
ও পড়বে তো? নিশ্চয়ই পড়বে। পড়বে বলেই তো…
—দিদি।
ভাবনায় ব্যাগড়া দিয়ে একটা কিশোর গলা ডেকে ওঠে দরজার ওপারে। ঠুকঠাক আঙুলের আঘাত শুনতে পায়।
—আয় আয়।
একটা ছোট্ট সাড়া দিয়ে তাড়াহুড়োয় দরজার দিকে যেতে গিয়ে চটির স্ট্র্যাপটা পায়ে আঙুলের ফাঁকে জড়িয়ে যায়। উফঃ। কোনও মতে চটিটাকে সোজা করে দরজা খুলে পর্দা সরায়।
—এহে তুমি দেখছি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলে।
—যাহ কী যে বলিস। মুখ নামিয়ে নেয় কস্তুরী। বুঝতে পারে ওর গালদুটো লাল হয়ে উঠছে। ছেলেটা সাংঘাতিক ডেপো। হবে না? নিজেকে সামলে ছেলেটার হাত ধরে টেনে এনে বলে, থাক আর পাকামো করতে হবে না। চুপচাপ পাঁচ মিনিট বসবি। নো বকবক। বুঝলি?
—বুঝলাম। ও দিদি খুব দেরি হবে নাকি? ওদিকে যে-পায়চারি করেই চলেছে, করেই চলেছে একবার বারান্দা একবার ঘর একবার ছাদ আবার একতলা আবার ছাদ কত আর বলব তোমায়? আমি যাওয়া না পর্যন্ত। মুখে দেখায় কিছুই জানতে চায় না। কিন্তু পেটের খিদেটা কি মুখের হাবভাবে ঢেকে রাখতে পারে? আলগা একটা চাঁটি মারে কস্তুরী।
—উফঃ লাগছে।
—বেশ হয়েছে। বলছি না চুপচাপ থাক। আমার সবকিছু ভন্ডুল করে দিবি দেখছি।
টেবিলের ওপর থেকে একটা ১০০টাকার ডেয়ারি মিল্ক, একটা খয়েরি ডায়ারি, পেন আর প্লেটে করে কিছু দূর্বা ধান, মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে ছেলেটার সামনে এসে দাঁড়ায়।
ছেলেটা মেঝের দিকে নীচু হয়ে বসতে যেতেই কস্তুরী বলে, খালি মেঝেতে বসতে নেই। আসন নেই এই ঘরে। তুই বরং বিছানাতেই বস। এই যাঃ চন্দনটাই ভুলে গেছি। এখন মায়ের কাছে চাইতে গেলেই যে কী হবে?
—কেলো করেছে। আসল জিনিসটাই ভুলে গেলে? ছাড়ো ছাড়ো। জেঠির কাছে চাইতে হবে না। যা এনেছ তাতেই হবে।
—হবে বলছিস? আমি তো এমন করে কোনওদিন কাউকে ফোঁটা দিইনি চন্দন ছাড়া?
—হ্যাঁ হবে একশোবার হবে। হাজারবার হবে। তুমি শুরু তো করো।
কস্তুরী দুঃখী দুঃখী মুখে প্লেট সমেত মোমবাতিটা ঘুরিয়ে ধান দূর্বা মাথায় দিতে দিতে গেলাসের জলে আঙ্গুল ভিজিয়ে ছেলেটার কপালে দিয়ে বলে ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা। যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।
—ও দিদি হল তোমার? দাও দাও কী গিফট দেবে শিগগিরই দিয়ে দাও। আমাকে আবার বেরোতে হবে যে।
—বুঝেছি আমার কাছে এসেই তোর যত তাড়া নিজের দিদি নই তো তাই।
ক্যাডবেরির প্যাকেটটা ছিঁড়ে ছেলেটার মুখে দেয় কস্তুরী। ছেলেটাও নিজের ক্যাডবেরি থেকে খানিকটা কস্তুরীর মুখে পুরে দেয়।
—তুমি আমার নিজের দিদির চাইতেও আপন। হল? অমনি মেয়ে অভিমান। রাগ দেখালে হবে? আমি নিজে কিছু কিনতে পারিনি বটে কিন্তু একখানা যা হেব্বি গিফট এনেছি তোমার জন্য। পুরো চমকে যাবে। বোমকে যাবে। নাও নাও ধরো। একগাল হেসে ছেলেটা ওর হাতে একটা গোলাপি চারকোনা খাম ধরিয়ে দিয়ে ঢিপ করে পেন্নাম ঠোকে।