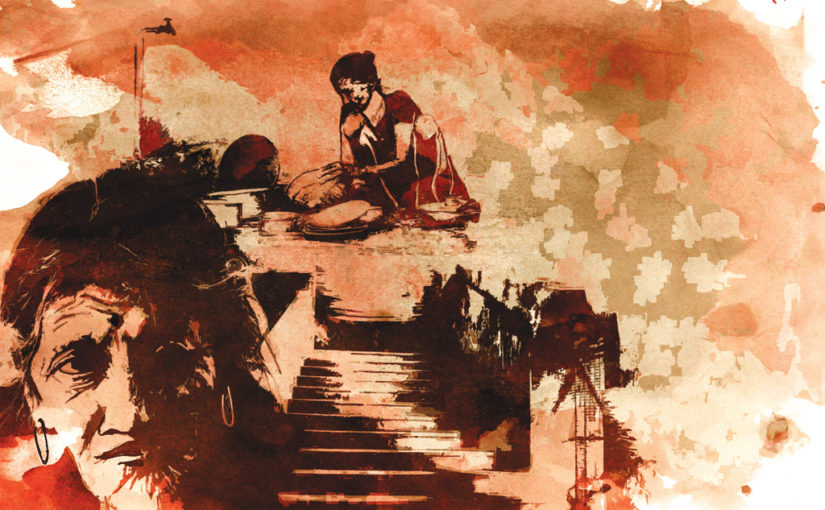সময় কারও জন্য থেমে থাকে না রাহুল। সে তার নিয়মেই বয়ে চলে। মানুষ বর্তমান নিয়েই বাঁচে। কাল কে দেখেছে বলতো?’
‘ফিলোজফি ঝেড়ো না তো অরিদা। যখনই দেখা হয়, তোমার সেই একই কথা। সবসময় মানুষের মনে আঘাত দিতে ভালো লাগে? তোমাদের মতো করে যারা ভাবে তাদের জন্যই আমাদের মতো কষ্টে জর্জরিত মানুষগুলো বাঁচার আশাই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।’
‘বাঁচার আশা ছাড়বে না, বরং আরও ভালো করে বাঁচতে শিখবে! কখনও কারও মনে দুঃখ দেবে না, আর কেউ কষ্টে থাকলে তাকে মাঝ দরিয়ায় ছেড়েও দেবে না। আমরা মানুষ রাহুল। সমাজে বাস করি। রোজ না জানি কত লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, তাদের সকলের সঙ্গেই যে আমরা ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে পারি এমনটা তো সম্ভব নয়। কখনও কখনও তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ফেলি। কটু কথাও বলে ফেলি। সেক্ষেত্রে তৎক্ষনাৎ একটা ‘সরি’ বললেই প্রবলেম সলভড্। কোনও কিছু কালের উপর না ছাড়াই ভালো, কারণ কাল কখনও আসে না।’
‘গতকাল দেরি করে অফিসে আসার জন্য আমি আমার চাপরাশিকে দু-চার কথা শুনিয়েছি। তাই বলে আমি তার কাছে ক্ষমা চাইব নাকি?’
‘ওনার দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেছিস একবারও? যদি তিনি রোজই দেরি করে অফিস পৌঁছন তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু যদি তিনি আগে কোনওদিন দেরি না করে থাকেন, শুধুমাত্র সেইদিনই… তাহলে নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ কারণ থাকবে। ওই ভদ্রলোক তোর বাবার বয়সি। সারাদিনে সকলের সঙ্গে কত তো কথা বলিস। তার থেকে যদি দু-চারটি বাক্য ওই মানুষটার জন্য ব্যয় করিস, তাতে তোর জাত যাবে? যদি একটা ‘সরি’ বলিস, কী হবে তাতে? মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?’
‘কী বলতে চাইছ বলোতো? তোমার কথা অনুযায়ী আমাকে তাহলে সুগার কোটেড ট্যাবলেট-এর মতো করে বাঁচতে হবে। বাইরে থেকে মিষ্টি আর ভিতরে তেতো।’
‘বাইরে মিষ্টি ভিতরে তেতো কেন হবে? তাহলে তো ভিতরে ভিতরে নিজেকেই জ্বলতে হবে। আমরা নিজেকেও জ্বালাব না আর কাউকে কষ্টও পেতে দেব না।’
রবিবার। কোথায় রাহুল ভেবেছিল আজ একটু বেশি ঘুমোবে, এগারোটার আগে কোনও মতেই বিছানা ছাড়বে না। রোজই তো সকাল সাতটায় উঠে কোনওরকমে নাকে-মুখে গুঁজে অফিস ছুটতে হয় তাকে। যদিও তার দুশ্চিন্তা তাকে কতটা শান্তিতে ঘুমোতে দেয় কে জানে! সে ছুটে বেড়ায় শান্তির খোঁজে। আজকাল বাড়িতেও ভালো লাগে না রাহুলের। সংসারে মোটে তিনটে প্রাণী। মা-বাবা আর সে। তারা কেউ কথা বলে না রাহুলের সঙ্গে। রাহুলও কথা বলার সাহস পায় না।
ঘড়িতে তখন সবে আটটা দশ। কানের কাছে বেজে উঠল মোবাইল ফোনটা। ঘুম চোখে বিরক্তিমাখা মুখে ফোনটা কানে দেয় রাহুল—
‘হ্যালো, কে বলছেন?’
‘আরে অরিজিৎ বলছি রে।’
‘আরে হ্যাঁ। বলো বলো। হঠাৎ কী মনে করে এত সকালে ফোন করলে? সিরিয়াস কিছু?’
‘না রে তেমন সিরিয়াস না হলেও তোর সঙ্গে কিছু দরকারি কথা আছে। তাছাড়া অনেকদিন দেখাও তো হয়নি। আজ বিকালে আমাদের বাড়িতে আয়, তখনই সব কথা হবে। তোর বউদিও বাপের বাড়ি গেছে। তুই এলে আমারও কম্প্যানি হবে।’
‘এই কথাগুলো একটু বেলায় বললে খুব অসুবিধা হতো? শুধুশুধু আমার ঘুমটা মাটি করে দিলে। আচ্ছা ঠিক আছে, কখন যেতে হবে বলো?’
‘এক কাজ কর সকালেই চলে আয়। একসঙ্গে লাঞ্চ করব। দুজনে মিলে যা হোক একটা কিছু বানিয়ে নেওয়া যাবেখন।’
‘ঠিক আছে, আমি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আসছি।’
অরিজিৎ, অতুলের বেস্ট ফ্রেন্ড। লম্বা, চওড়া, সুঠাম দেহ তার। দেখতেও বেশ সুদর্শন। কলকাতারই একটি নামিদামি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির চিফ্ অ্যাকাউন্ট্যান্ট, মাত্র সাত মাস বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে সে।
অতুলদের বাড়িতে নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল অরিজিতের। সে প্রায় বাড়িরই একজন হয়ে উঠেছিল। বাড়িতে হইহুল্লোড়, আনন্দ, হাসি-ঠাট্টা, মজা, সুখ-দুঃখ সবেতেই সামিল হতো সে। অতুলের মতো অরিজিৎও হয়ে উঠেছিল রাহুলের অরিদা। অতুলের অকাল মৃত্যুতে তার আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রাহুলদের বাড়িতে।
আজ সেই সম্পর্কের টানেই একটা ফোন পেয়ে অরিদার বাড়িতে ছুটে আসা রাহুলের। এর আগেও বহুবার এখানে এসেছে সে অতুলদার সঙ্গে। চার মাস আগে যখন এসেছিল তখন বারান্দায় বসানো বেলফুলের চারাগুলি সবে ডানা মেলছিল। আজ তাতে ফুল ভরে গেছে। পুরো বারান্দা গন্ধে ম ম করছে। কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল রাহুল।
— ‘কী রে শুনছিস কী বললাম? কোথায় হারিয়ে গেলি?’ অরিজিতের কথায় চমকে উঠল রাহুল।
‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে? মাঝে মাঝে কী যে হেঁয়ালি করে কথা বলো না, কিছুই বুঝি না। মাথার উপর দিয়ে যায়। লোককে ভুরিভুরি উপদেশ দেওয়ার রসদ কোথা থেকে পাও বলো তো। কপালে একটা বড়ো লাল তিলক আর গেরুয়া বস্ত্র গায়ে চড়িয়ে বসে যাও। প্রচুর টাকা কামাবে।’
‘দ্যাখ, ভগবানের দয়ায় টাকার অভাব নেই আমার। আর গেরুয়া বস্ত্র কেন পরব বলতো? যারা সংসার ত্যাগ করে তাদের ওই পোশাক মানায়। তাদের মতো আমি তো মহামানব নই, আর ভবিষ্যতেও সংসার ত্যাগ করার কোনও পরিকল্পনাও আমার নেই। আমি সংসারী মানুষ। সারাজীবন সংসার নিয়েই সুখে-দুঃখে কাটাতে চাই। দায়িত্ব থেকে পিছপা হওয়ার মতো ছেলে আমি নই। আর অতটা দয়িত্বজ্ঞানহীনও হতে পারব না।’ অরিজিৎ বেশ উত্তেজিত হয়েই কথাগুলি বলল।
‘কোথা থেকে কোথায় চলে এলে অরিদা? কী বলছ কিছুই বুঝলাম না। আর হঠাৎ করে এত উত্তেজিতই বা হয়ে গেলে কেন?’
‘এত ছোটো তো তুই নোস, যে আমার কথা বুঝতে পারছিস না। কী করছিস ভেবে দেখেছিস একবারও। নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছিস? মেয়েটার কী হবে বলতো?’
এতক্ষণে রাহুলের বোধগম্য হল যে অরিদা কী বলতে চাইছে। তার আর মৌসুমির সম্পর্ককে ঘিরেই এত জল্পনা। সেই সম্পর্ক যেটা না রাহুল বহন করতে পারে আর না সহন করতে পারে।
‘তুমি আমার জায়গায় থাকলে কী করতে?’
‘হয়তো আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতাম। দাদার মৃত্যুর পর কখনও তার বিধবা স্ত্রীকে গ্রহণ করতাম না। মা-বাবা যতই চ্যাঁচামেচি করুক, অন্যায় আবদার করুক, না বলে কাটিয়ে দিতাম। অন্তত তাদের রোজ তিল তিল করে মরার জন্য ছেড়ে দিতাম না। যদি সম্পর্ক রাখারই না ছিল তাহলে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিলি কেন? আমি এরকম সম্পর্কে কখনও আবদ্ধ হতাম না যেটা আমার নিজের এবং অন্যের জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে।’
‘যদি এই সম্পর্ক ওর মৃত্যুর কারণ হয়, তাহলে আমিও তো ক্রমশ সেই দিকেই এগোচ্ছি। না পারছি গিলতে, না পারছি ফেলতে। আমিও যে ভালো নেই অরিদা।’
‘ভালো থাকবি কী করে বলতো? চার মাস ধরে মেয়েটা বাপের বাড়িতে পড়ে আছে। অতুলের মৃত্যুর পর একবারও তাকে চোখের দেখা দেখতে যাসনি। এখনও সময় আছে রাহুল, সব দ্বিধা কাটিয়ে যা ওর কাছে। দায়িত্ব যখন নিয়েছিস ওকে ওর মর্যাদা দিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আন ভাই।’
চুপ করে থাকে রাহুল। এর কী জবাব দেবে সে নিজেই জানে না। বোধহয় সেই উত্তর খোঁজার জন্যই হারিয়ে যায় তার উদাসীন মন।
মৌসুমি বাবা-মায়ের আদরের একটিই মাত্র মেয়ে। লম্বা, ফর্সা, ছিপছিপে চেহারা। টানা টানা চোখ, টিকালো নাক, ছোট্ট কপাল–যাকে বলে প্রকৃত সুন্দরী। বিএ পড়তে পড়তেই বান্ধবীর সূত্রে অতুলের সঙ্গে আলাপ। তারপর প্রেম এবং পরে বিবাহ। অতুল সরকারি কর্মচারী এবং সৎ হওয়ার কারণেই মৌসুমিদের বাড়ি থেকে কোনও আপত্তি ওঠেনি।
শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর আর স্বামীকে নিয়েই ছিল তার সুখের সংসার। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সে সুখ তার কপালে বেশিদিন সইল না। বিয়ের সাত মাস পরেই ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট-এ মারা গেল অতুল। সেদিন মৌসুমির জন্মদিন ছিল। মৌসুমিকে উপহার দেওয়ার জন্য একটা লাল রঙের জরিপাড় শাড়ি এবং একতোড়া গোলাপফুল কিনেছিল সে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্য চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়েই এই দুর্ঘটনা। খবর পেয়ে তারা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছল, তখনও লাল টুকটুকে শাড়ি আর গোলাপের তোড়া সেইখানেই পড়ে ছিল। শাড়িটা হাতে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল মৌসুমি। একটা সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল সে।
তিনদিনে সমস্ত কাজ মিটে যাওয়ার পর অখিলেশবাবু তার মেয়ে মৌসুমিকে পাকাপাকি ভাবে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যেতে চাইলেন তাদের বেহালার বাড়িতে।
সেকথা শোনা মাত্রই রাহুলের মা-বাবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এমনিতেই পুত্রশোকে তারা মৃতপ্রায়, তার উপর আবার তাদের স্নেহের বউমার বাড়ি থেকে চলে যাওয়াটা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তারা কাঁদতে কাঁদতে শুধু অখিলেশবাবুর পায়ে ধরতে বাকি রেখেছেন। কত অনুনয়-বিনয় করেছেন মৌসুমিকে এ বাড়িতে রাখার জন্য। কিন্তু তাঁর একটাই কথা, এখানে থেকে সে কী করবে। কী পরিচয়ে থাকবে? অতুলের বিধবার পরিচয়ে! সেটা তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না। আবার তিনি অন্যত্র মেয়েকে পাত্রস্থ করবেন।
এ সমস্তকিছুই লক্ষ্য করছিল রাহুল। এমন সময় তাকে দেখে মা মীনাদেবী ছুটে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার হাত দুটি ধরে পীড়াপীড়ি শুরু করে দেন। একমাত্র সে-ই পারে মৌসুমিকে এ বাড়িতে রাখতে। সে যদি মৌসুমিকে বিয়ে করে তাহলে মৌসুমি এ বাড়িতে বউয়ের সম্মান নিয়েই চিরজীবন থেকে যেতে পারে।
কিন্তু সেটা রাহুলের পক্ষে কীভাবে সম্ভব? যাকে সে এতদিন বউদি বলে ডেকে এসেছে, বন্ধুর মতো মিশেছে তার সঙ্গে, তাকে সে কীভাবে নিজের স্ত্রী হিসাবে মেনে নেবে? শুধু তার কেন, কারওর পক্ষেই কি এটা সম্ভব?
কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এই প্রস্তাবটা নিয়ে কোনও জোরালো প্রতিবাদ করলেন না অখিলেশবাবু। শেষ পর্যন্ত শত চেষ্টা করেও মা-বাবার এই শোকার্ত আবেদন এড়িয়ে যেতে পারেনি রাহুল। সে বাধ্য হয়েছিল মৌসুমির মাথায় সিঁদুর তুলে দিতে। কিন্তু হায়, ভাগ্যের কী পরিহাস! যাকে নিয়ে এত বড়ো একটা সিদ্ধান্ত, সে স্থানুবত এক পুতুল। অতুলের নয়, রাহুলের স্ত্রী, হিসাবে জীবনটা অতিবাহিত করতে তার আপত্তি আছে কিনা তা নিয়ে কোনও মতামত চাওয়া হয়নি মৌসুমির।
এরপর অখিলেশবাবু প্রায় জোরাজুরি করেই পনেরো দিনের জন্য মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের বাড়িতে। তারপর কেটে গেছে চার চারটি মাস। এবাড়ির কেউ মৌসুমিকে আনেওনি, এমনকী ফোন পর্যন্ত করে খবর নেয়নি। এই নিয়েই যত অশান্তি। বাবা-মা রাগে কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন রাহুলের সঙ্গে। তাদের রাগ বাড়ির বউ আর কতদিন বাপের বাড়িতে পড়ে থাকবে।
সহসা কলিং বেল-এর আওয়াজে চমকে ওঠে রাহুল। দুধওয়ালা দুধ দিয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে আবার বলতে শুরু করল রাহুল। ‘সময় মানুষকে কখন কোন পরিস্থিতিতে দাঁড় করাবে আগে থেকে তা কে বলতে পারে অরিদা? মানছি ওর দায়িত্ব আমি নিয়েছি। দায়িত্ব এড়াতেও চাই না। ভেবেছিলাম যে, সমস্যা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা আরও জটিলাকার ধারণ করল। সব থেকে বড়ো সমস্যা হল আগে একরকম করতাম আর এখন অন্যরকম ব্যবহার। মৌসুমির সঙ্গে নতুন সম্পর্ক তো দূর, পুরোনো সম্পর্কটাই কীভাবে সামলাব বুঝতে পারছি না। ও ছিল আমার বউদি কাম বেস্ট ফ্রেন্ড। সমস্ত আলোচনাই করতাম ওর সঙ্গে। এমনকী কবে কোন মেয়ের পিছনে লাগলাম, কার প্রেমে পড়লাম সমস্ত কিছুই। মাঝেমধ্যে দাদা আমাকে বলত, ‘কখনও তোর বউদিকে আমার সঙ্গেও একটু-আধটু সময় কাটাতে দে।’
একদিন তো এমনও হয়েছে, ‘বউদি বউদি’ করে ডেকেই যাচ্ছি। বউদির কোনও সাড়া নেই। যে-বউদিকে ডাক দিলেই সমস্ত হাতের কাজ ফেলে ছুটে আসে, তার আজ কী হল! আবার ডাকলাম, – এল না। ‘বউদি একবার এসো, তোমাকে কিছু দেখানোর আছে।’ খেতে বসেও সেই একই ব্যাপার। সকলের সঙ্গে কথা বলছে, শুধু আমার সঙ্গে বলছে না।
এইসব দেখে মা ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করার কারণ। সেদিন কোনও উত্তর দিতে পারেনি সে। উত্তরের পরিবর্তে শুধু মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে ও।
পুরো ব্যাপারটাই বুঝতে পেরেছিল দাদা। বসে বসে মুচকি হাসি হাসছিল। পরে দাদার থেকে জানতে পারি দাদা নাকি ইয়ার্কি করে ওকে বলেছে, ও দাদার থেকে আমাকেই বেশি ভালোবাসে। তাই সারাদিন মুখ গোমড়া করে রেখেছিল।
কথাটা যে আমিও ভালোভাবে নিতে পেরেছিলাম তা কিন্তু নয়। আমারও কেমন যেন একটা খটকা লেগেছিল। শুধু মনের কোণে একটাই কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল, আমাদের দেওর-বউদির সম্পর্ককে দাদা অন্যরকম ভাবে নিচ্ছে না তো?
বাড়িতে বেশ একটা গুরুগম্ভীর পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। মৌসুমির মুখের হাসি ফিরিয়ে আনতে দাদা যখন ওকে আমার ঘরে নিয়ে এসেছিল, তখনও কাঁদছিল ও। আমাকে দেখে আরও বেশি করে কাঁদতে শুরু করেছিল। সেদিন প্রথম আমি ওর মাথায় হাত রেখেছিলাম।
সব শুনে অরিজিৎ বলল, ‘মৌসুমিকে ভালো যে বাসিস তা তোর কথায় স্পষ্টই বোঝা যায়। তবে এটা ঠিক যে তোর ভালোবাসার ধরনটা ছিল আলাদা। এখন তোদের সম্পর্কের সমীকরণটা বদলেছে। মানছি এক সম্পর্ক থেকে হঠাৎ করে অন্য সম্পর্কে যাওয়াটা খুব সোজা নয়। কিন্তু অসম্ভবও তো নয়। এই সংসারে কত লোকই তো আছে যারা এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, তারা কি সুখে ঘর করছে না বল?’
অতীত ভুলে যা ভাই, বর্তমানে ফিরে আয়। আমার বিশ্বাস তুই পারবি।’
‘কী করে বলো?’
‘আজ বিকেলে মৌসুমিদের বাড়িতে যা। ওর সঙ্গে কথা বল। আগের মতো ওর ভালো বন্ধু হয়ে যা। পাশে বস। তুই যেমন তোর ভাইকে হারিয়েছিস ও-ও তো স্বামীকে হারিয়েছে, তাই না?’
‘ওর স্বামী নাকি বন্ধু কোন পরিচয়ে গিয়ে দাঁড়াব ওর কাছে? তুমি যাবে আমার সঙ্গে?’
‘অবশ্যই যাব। এক কাজ করি আমি মৌসুমিকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসি। তখন কথা বলে নিস।’
‘না অরিদা। প্লিজ ওকে এনো না।’
রাহুল হঠাৎই থামিয়ে দিয়েছিল অরিজিৎকে। সে ভয় পেতে শুরু করেছিল। কীভাবে সে মৌসুমির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে?
রাতে বাড়ি ফিরে কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়ে রাহুল। মনে মনে ভাবতে থাকে তার সমস্ত সুখশান্তি দাদা কেড়ে নিয়ে গেছে। অরিদা ঠিকই বলেছে, কতদিন আর এরকম চলবে? কিছু তো একটা ডিসিশন নিতেই হবে। কিন্তু তার আগে এটাও তো জানা দরকার মৌসুমি তার ব্যাপারে কী ভাবে? সে কী চায়? এইসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে রাহুল।
পরদিন সকাল সাতটায় অ্যালার্মের আওয়াজে ঘুম ভাঙে রাহুলের। কোনও রকমে নাকে মুখে গুঁজে রওনা দেয় অফিসে। পথটাও অনেকটা। সেক্টর ফাইভ। প্রায় দশ কিলোমিটার। ভালো পোস্টে আছে রাহুল। বেতনও পায় বেশ মোটা অঙ্কের।
অফিস শেষ করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেয় রাহুল। চড়ে বসে গাড়িতে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা বাড়ি না গিয়ে এ কোথায় এল সে! তার অবচেতন মন তাকে কোথায় নিয়ে এল? এ যে মৌসুমিদের দরজার সামনে এসে গেছে সে! মৌসুমির মা-বাবা তাকে দেখতে পেয়ে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। তাদের কাছ থেকে সে জানতে পারে মৌসুমি অসুস্থ। অতুলের মৃত্যুর পর থেকেই সে অবসাদে ভুগছে।
মৌসুমির ঘরে ঢোকা মাত্রই চমকে উঠল রাহুল-এ কী অবস্থা তার। চোখে-মুখে কালি পড়ে গেছে, চুল উশকোখুশকো, জরাজীর্ণ চেহারা। ফর্সা টুকটুকে রং একেবারে কালো হয়ে গেছে।
অতুল মৌসুমিকে খুব ভালোবাসত। বলত ‘এই পাগলিটাকে নিয়ে কী করি বলতো? এই যুগে এত সহজ, সরল হলে সমাজে বাঁচবে কী করে। কী করে সামলাব এই মেয়েকে আমি?’
রাহুল বলতো, ‘ভালোই তো, আসল সোনা পেয়েছ, তাতে খাদ মেশানোর চেষ্টা করছ কেন?’
‘আমি মরে গেলে কী হবে ওর? বাঁচবে কেমন করে? সমাজে বাস করতে হলে একটু চালাক-চতুর হতে হয়।’
‘কেন বাজে কথা বলো, বলো তো। ভালো কথা বলতে পারো না।’ সেদিন দাদার এই কথায় চেঁচিয়ে উঠেছিল রাহুল। কী জানি, দাদা কী তার মৃত্যুর কিছু পূর্বাভাস পেয়েছিল, নাকি এমনিই! মৌসুমিকে দেখে রাহুলের মনে পড়ে গেল কথাগুলো।
মনে মনে ভাবতে থাকল বাবা-মা বিশ্বাস করে তার হাতে সঁপে দিয়েছিল মৌসুমিকে। আর সে কী করছে। তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। তার এই অবস্থার জন্য নিজেকেই দূষতে থাকে সে।
এমন সময় মৌসুমির বাবা বলেন, ‘মউ দ্যাখ মা আমার, কে এসেছে তোর সঙ্গে দেখা করতে। দ্যাখ রাহুল এসেছে। রাহুলের সঙ্গে কথা বল মা। কতটা দূর থেকে এসেছে তোর সঙ্গে দেখা করতে।’
চুপ করে বসেছিল মৌসুমি। আর কী কথাই বা বলবে? কী-ই বা বলার আছে? তাদের দুজনেরই ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আর অতীত তো চিরজীবনের মতো দিশাহীন করে দিয়ে গেছে। রাহুলের দিকে দেখল সে। সেই নিশ্চল চোখ। রাহুলের চোখে জল এসে যায়। দাদার মুখটা চোখের উপর ভেসে ওঠে। যেন আসল সোনা তার হাতে তুলে দিয়ে দাদা বলছে ‘দেখিস ভাই আমার মৌসুমির দায়িত্ব এবার তোর। তুই ছাড়া আর কাকেই বা এই গুরুদায়িত্ব দিতাম বল। বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যা রাহুল। বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যা।’
রাহুলের চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। সহসা নিজের হাতের উপর একটা স্পর্শ অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে কানে এল, ‘কেমন আছো রাহুল?’
উত্তর দিতে না পেরে হাউহাউ করে কেঁদেই ফেলল রাহুল। মনে হচ্ছিল যেন দাদার দাহ সংস্কার করে সবে ফিরেছে সে। দাদা মরে গিয়ে বেঁচে আছে, আর তারা বেঁচেও মরে আছে।
‘রাহুল। কাঁদছ কেন?’
অল্পক্ষণেই রাহুলের মনে হল যেন তার দেহ-মনের জ্বালা একেবারে জুড়িয়ে গেছে। কোথা থেকে যেন শান্তি ফিরে এসেছে। মৌসুমি তার আঁচল দিয়ে রাহুলের চোখ মুছিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকল।
মৌসুমির বাবা রাহুলকে ঘরে দিয়েই চলে গিয়েছিলেন। কেউ থাকলে মৌসুমিকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথাটা অন্তত পাড়তে পারত সে।
মৌসুমি বলে ওঠে, ‘সোজা অফিস থেকে এসেছ না? কিছু তো খাওয়াও হয়নি মনে হয়। তুমি বসো। আমি কিছু নিয়ে আসি।’ এই বলে কোনওরকমে দেয়াল ধরে ওঠার চেষ্টা করে সে।
‘না খেতে ইচ্ছে করছে না’, বলে মাথা নাড়ায় রাহুল।
‘সবাই কেমন আছে? আমার কথা বাবা-মায়ের মনে পড়ে?’
‘আগে বলো বাড়ি যাবে আমার সাথে? সবাই তোমাকে খুব মিস করে।’ সাহস করে বলেই ফেলে রাহুল।
‘এখন আর ওখানে গিয়ে কী করব, কে আছে আমার?’
‘কেন এরকম বলছ?’
‘তুমি খুব ভালো করে জানো রাহুল, ওখানে আর আমার আপন বলতে কেউ নেই, তবুও…।’
কথাগুলি শুনে দম বন্ধ হয় আসে রাহুলের। তাহলে কি মৌসুমি মনে করতে চাইছে না তাদের সম্পর্কটা এখন কী? হতবাক দৃষ্টি নিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে রাহুল। যদি তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ আসে। ওর মা-বাবা যে কেউ একজন।
‘কী হল রাহুল? তোমাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?’ মৌসুমি তার হাত দুটি ধরে বলল।
‘তুমি আমার সঙ্গে বাড়িতে চলো। তোমাকে ছাড়া কিছু ভালো লাগে না। বাড়ি যেন গিলতে আসে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়। কেউ কারওর সঙ্গে কথা বলে না’, বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেলে রাহুল।
‘আমি গিয়ে কী করব বলো তো? ভগবান ও বাড়িতে ওই পর্যন্ত অন্ন মেপেছিল আমার জন্য।’
‘বারবার অতীতটাকে ফিরিয়ে আনতে চাইছ কেন? যে গেছে সে কি আর ফিরে আসবে?’ বেশ চিৎকার করেই কথাগুলো বলল রাহুল। কথাগুলো যেন নিজের কানেই বড়ো বাজল রাহুলের।
চিৎকার শুনে ছুটে এল মৌসুমির মা-বাবা। কখন যে তার মধ্যে অধিকারবোধ জন্মাল সে নিজেই জানে না।
রেগেমেগে তার মা-বাবার উদ্দেশ্যে রাহুল বলতে থাকে, ‘আপনারা কেন সবকিছু জানাননি ওকে। আপনারাই তো জোর করেছিলেন। তাহলে ওকে বলেননি কেন? চুপ করে আছেন কেন? আমাকে মাটির পুতুল ভেবেছেন, যখন যা খুশি তখন তাই করাবেন। বোঝান ওকে সত্যটা কী। আমি আর পারছি না মৌসুমি। তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না, নাকি আমাকে যাচাই করছ? প্লিজ দয়া করো আমাকে, চলো বাড়ি চলো। আমি মানছি আমার ভুল হয়ে গেছে, বিগত চার মাসে একবারও তোমার খোঁজ নিইনি। কিন্তু সঙ্গে এটাও তো সত্যি একটা মুহূর্তের জন্যও তোমাকে ভুলতে পারিনি।’ বলতে বলতে সকলের সামনেই মৌসুমিকে জড়িয়ে ধরে সে।
এতদিন রাহুল-যে সম্পর্কটাকে বোঝা ভাবত, সেটা যে তার কাছে কী তা সে আজ টের পাচ্ছে। মৌসুমির তাকে অস্বীকার করা, সেটা কোনওভাবেই মানতে পারছে না সে।
‘আবার কাঁদে। আরে কাঁদছ কেন? কী হয়েছে তোমার রাহুল? আমি তো ভলোই আছি এখানে। এখানে আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।’
এমন সময় মৌসুমির বাবা অখিলেশবাবু রাহুলকে অন্য ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, ‘চার মাস একটা খবর পর্যন্ত নাওনি। আমার মেয়ে আমার কাছে বোঝা নয়। তাকে দুবেলা খেতে দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে। ঘাড় থেকে বোঝা নামাব বলে তোমার উপর মেয়ের দায়িত্ব দিইনি রাহুল। ভেবেছিলাম আমরা বুড়ো-বুড়ি আর ক’দিন। তারপর অন্তত মেয়েটাকে দেখার কেউ থাকবে।’
‘বাবা, তুমি রাহুলের সঙ্গে এইভাবে কথা বলছ কেন?’ কোনওরকম ভাবে মৌসুমি উঠে এসেছিল তাদের কাছে।
‘দাদার মৃত্যুর পর আমাদের এই আকস্মিক বিয়ে। তারপর থেকে আমিও তো ভালো নেই। শুধু ভেবেছি কী করব? ওর কী হবে? ও কীভাবে নেবে। প্রতিদিন একটু একটু করে মরছি। আর আপনারা ভাবছেন আমি চিন্তা করি না।’
‘রাহুল তুমি কি সত্যি কথা বলছ? তুমি মন থেকে মেনে নিতে পেরেছ এই বিয়ে? বলো আমাকে।’
‘ঘরে চলো তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।’, হয়তো বাবা-মায়ের জুড়ে দেওয়া সেই অধিকারের জোরেই মৌসুমির হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে রাহুল নিয়ে যায় পাশের ঘরে। দরজা বন্ধ করে দেয়। অল্পক্ষণের জন্য দুজনেই চুপ করে যায়।
জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় মৌসুমি। কাছে যায় রাহুল। বলতে থাকে—‘খুব কষ্ট দিয়েছি না তোমাকে? আচ্ছা তুমিও কি তাই মনে করো? আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই তোমার খোঁজ নিইনি? কিন্তু বিশ্বাস করো একটা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারিনি তোমার উপস্থিতির কথা। তখন বুঝতেই পারিনি তুমি আসলে আমার কী? দাদা চলে গেছে কিন্ত আমি তো বেঁচে আছি। তোমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাব না। সারাজীবন তোমার সঙ্গেই থাকব। যেদিন তোমার মাথায় সিদুঁর দিয়েছিলাম সেদিন যে-শপথ নিইনি আজ তা নিলাম।’
কথাটা শোনা মাত্রই চিৎকার করে হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে মৌসুমি। বাইরে থেকে মেয়ের কান্না শুনে পড়িমরি করে দরজা খুলে ছুটে আসেন মৌসুমির মা-বাবা। মেয়েকে চুপ করানোর জন্য এগিয়ে আসতেই হাত দেখিয়ে বাধা দেয় রাহুল। হাত জোড় করে বলে ‘দয়া করে আপনারা যান আমি সামলে নেব।’
‘মৌসুমি শোনো, আমার কথা শোনো। দ্যাখো আমার দিকে একবার দ্যাখো।’
তাকে কিছুতেই সামলাতে পারছে না রাহুল। একপ্রকার জোর করেই মৌসুমিকে চেপে জড়িয়ে ধরে রেখেছে কোনওমতে। ‘অভিমান হয়েছে? রাগ হয়েছে? বলো তুমি সত্যিই বোঝো না তোমার আমার সম্পর্ক?’
মৌসুমি শুধু একটা কথাই বলে চলে–‘না এটা হতে পারে না। আমি তোমার জীবনটা নষ্ট করে দিতে পারি না।’
রাহুল বাহুবলে আরও কাছে টেনে নেয় মৌসুমিকে। একেবারে বুকের কাছে। এতটাই কাছে যে তার প্রতিটি হূদয়ের স্পন্দন অনুভব করে সে। সে এক আলাদা অনুভূতি, যেটা সে আগে কোনওদিন অনুভব করেনি।
রাহুল বলতে থাকে-‘কে বলেছে তুমি আমার জীবন নষ্ট করেছ? তুমি জানো না তুমি আমাদের কাছে কী সোনা–বলতে বলতে মৌসুমির কপালে চুমু খায় রাহুল। যাকে গলার কাঁটা ভাবতাম সেটাই যে গলার হার হয়ে দাঁড়াবে তা কি আগে জানতাম? বুঝলামই যখন তখন…’
চুপ করে রাহুলের বুকে মাথা দিয়ে থাকে মৌসুমি। এখন সে অনেকটা শান্ত।
দুই হাত দিয়ে মৌসুমির মুখটি তুলে ধরে বলে, ‘যাবে তো আমার সঙ্গে, যাবে না? কিছু বলবে না? আচ্ছা ঠিক আছে বলতে হবে না।’
রাহুল বুঝে যায় মৌসুমির নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ।