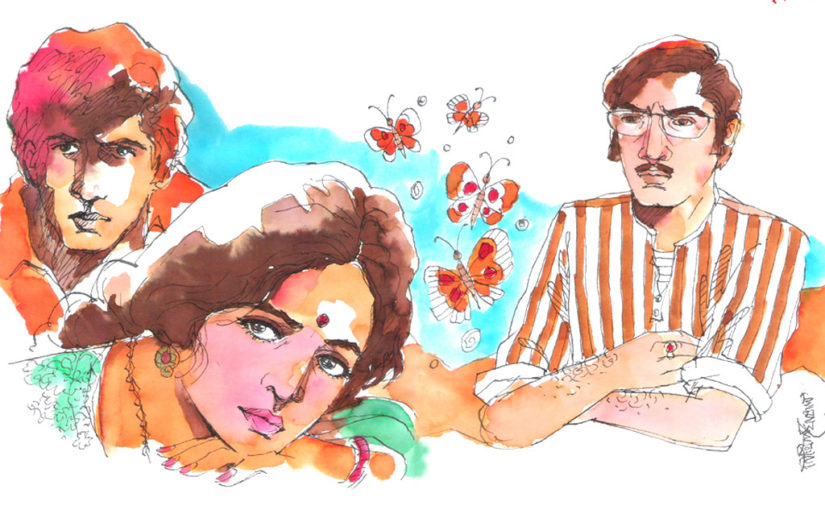এই সমাজে ছোটাটাই দস্তুর। কেউ কেউ পরিকল্পনা করেই ছোটে। মিশনটা ভোগ সাগরে ডুব দেওয়া। অনেকে শক্তি হারিয়ে সেই সাগরে অতল গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। আবার কেউ সব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে আসে। জীবনের মূল্যবোধ, পরম্পরা দায়দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ সব খুইয়ে সে রিক্ত। ভোগ সাম্রাজ্যের মাঝে বসে নিরেট ভোগ সামগ্রী তাকে গিলে খেতে চায়। প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরেরা শিকারিকে নিয়ে প্রথমে খেলা করে, তারপর একটু একটু করে ছিঁড়ে খায়। সেই ছিন্নভিন্ন মনের যন্ত্রণায় প্রলেপ দিতে কেউ আসে না।
সে আজ বড়ো একা। মিঠু যন্ত্রমানবে পরিণত হতে চায় না। ছোটোবেলা থেকে অতি মেধাবী মিঠুর স্বপ্ন ছিল অন্যরকম। জীবনবিমার তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী আজীবন দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে করতে পর্যুদস্ত। নিম্নবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা মিঠু আলোর দিশারি। মিঠুর হাত ধরে আদিত্য আকাশ ছুঁতে চায়। অফিস কলিগরা ইন্ধন দেয়– আদিত্যবাবু, মিঠুর মতো অসাধারণ মেধাবী মেয়েকে স্টেট লেভেলের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়ে পাতি ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন? ওর জন্য পড়ে রয়েছে তো গোটা জগৎ। ওকে তো আরও বড়ো জায়গায় পরীক্ষা দেওয়াতে পারতেন? ওর আসল জায়গা আইআইটি।
ভাগ্য খোলে তরুণ কর্মকারের লটারি ব্যাবসায়। ফুটপাথে চেয়ার টেবিল পেতে লটারি বিক্রিতে যা কমিশন হতো, সংসারের হাঁড়িতে তেমন একটা কালি পড়ে না। পড়ার কথাও নয়। মোড় ঘুরল এই কাউন্টার থেকে প্রথম পুরস্কার লেগে যাওয়ায়। প্রথম পুরস্কার পেয়ে ট্যারা গোবিন্দ কত নম্বর বিত্তশালীদের খাতায় নাম লিখিয়েছিল জানা যায়নি। তরুণ ফুলে ফেঁপে ঢোল। খদ্দেরের মন বুঝে মা কালীর ফটোতে প্রতিদিন তাজা জবার মালা, সিঁদুর পরিয়ে, ধুপকাঠি জ্বালিয়ে বসে। সামনে থাকে বড়ো প্লাইবোর্ডে কাগজ লাগানো বিজ্ঞাপন, আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারি প্রথম পুরস্কার এই কাউন্টার থেকে উঠেছে, ইত্যাদি। আওয়াজটা বহুদূর পেৌঁছে দেওয়ার তাগিদে রাখা আছে একটি সাউন্ড বক্স। চটুল হিন্দি গানের পাশে চলতে থাকে আনন্দ সংবাদ। খদ্দেররাও হঠাৎ বিত্তশালী হওয়ার বাসনায় পিল পিল করে টিকিট সংগ্রহ করে। প্রাচুর্য তরুণকে নিয়ে যায় নরক দর্শনে। অন্ধকার জগতে। সেই জগতে সে এখন মাফিয়া। জীবনের মূল্যবোধ দায়িত্ব কর্তব্যবোধ সব কিছুরই প্রয়োজন ফুরিয়েছে।
বাচ্চা হওয়ার সময়ই রূপাঞ্জনার মা সমস্ত দায়দায়িত্ব সন্তান বাৎসল্য সমস্ত কিছুই তরুণের হাতে সঁপে দিয়ে জগতের মায়া ছেড়ে কেটে পড়ে। এত দায়ভার বহনের ক্ষমতা হয়তো তরুণের ছিল না। ছোট্ট শিশুর মিষ্টি হাসি সন্তান বাৎসল্য উসকে দেয়। বিরক্ত হয় না। ক্লান্তি আসে না। তিল তিল করে হারিয়ে যাওয়া মায়ের সাহচর্য দিয়ে বড়ো করতে থাকে। দাম্পত্য জীবনের আশা আকাঙক্ষা স্বপ্ন সব কিছুরই মূর্ত প্রতীক রূপাঞ্জনা। সে আজ আকাশের বুকে লেপটে থাকা নক্ষত্র। কম্পিটিশনটা ছিল মিঠুর সাথে। মিঠু ফোন করে –– হ্যালো রূপাঞ্জনা পড়তে যাবি তো?
– না রে আজকে শরীরটা ভালো নেই।
– সে কি, আজ যে ফিজিক্সের ক্লাস।
– থাক আজ ভালো লাগছে না। মাথাটা কেমন ঘুরছে।
হঠাৎই মেয়ের এই পড়াশোনার উদাসীনতার উৎস বুঝতে পারে না। টিচাররাও মিঠু, রূপাঞ্জনার অগ্রগতিতে উৎসাহিত। শ্যামলবাবু তো প্রথমেই ডেকে বললেন– তোমরা আমার কাছে ফিজিক্স পড়বে। আর শোনো তোমাদের কোনও ফি দিতে হবে না। কোচিং দেওয়া নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে কম্পিটিশন ওঠে তুঙ্গে। ফোন ছাড়তেই তরুণ উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করে– কিরে, পড়তে যাবি না কেন? শরীর খারাপ? কি হয়েছে?
– না তেমন কিছু না।
– তবে? শেষ সময়ে এসে এই ফাঁকি কতবড়ো সর্বনাশ ডেকে আনবে বুঝতে পারছিস না। তোকে যে বড়ো ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। তোর মা যে হাঁ করে বসে আছে। তাকে কি কৈফিয়ত দেব?
রূপাঞ্জনা চুপ করে থাকে। বাবার এই উৎকন্ঠা, আবেগ প্রলেপ দেওয়ার রসদ জমা নেই। শরীরের মধ্যে এক অজানা অস্থিরতা যন্ত্রণা। সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনা যেন ক্রমশ নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তরুণের মনে হয় মেয়েটা কোনও বয়ফ্রেন্ডের পাল্লায় পড়েনি তো? সেক্ষেত্রে এই উদাসীনতা স্বাভাবিক। তরুণ ভিন গ্রহে হ্যারিকেন নিয়ে বয়ফ্রেন্ডের তল্লাশি চালাতে থাকে।
বাড়ির সামনে লোকের ভিড় দেখে তরুণের বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। পা যেন আর চলতেই চায় না। সামনে এসে অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করে– কি হয়েছে? পুলকের মা একটু বকে বেশি। নাম কিনতে চায়। লোকজন ঠেলে মুখ বাড়িয়ে বলে– আর বলো কেন। তুমি সাত সকালেই বেরিয়ে যাও। মেয়েটা মনে হয়, না খেয়েই পড়তে গিয়েছিল। তাই বোধ হয় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছে। জ্ঞান ছিল না। এখন এসেছে। তরুণ ঘরে ঢুকতেই বুলটির মাকে ঠেলা দিয়ে বলে– কি জানি বাবা। আজকাল ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারে যা শুনি, কোথায় কি করে এসেছে কি জানি। বুলটির মা সায় দিয়ে বলে– মা মরা মেয়ে। শাসন নেই। হতেও পারে। উৎকন্ঠিত তরুণ জিজ্ঞাসা করে– কিরে মা, কি হয়েছে? রূপাঞ্জনা ধীরে ধীরে উত্তর দেয় – শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বুকে একটা যন্ত্রণা।
তবে চল কাছাকাছি কোনও নার্সিং হোমে, বলেই তরুণ উর্দ্ধশ্বাসে বেরিয়ে যায় গাড়ির খোঁজে। অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার পর ডাক্তার পাল জানিয়ে দেয়– পেশেন্ট ইজ ভেরি সিরিয়াস। হার্টের দুটো ভালভ্ই প্রায় ব্লক। একটি হান্ড্রেড অপরটি সিক্সটি পারসেন্ট। ইমিডিয়েট অপারেশন করতে হবে। ওয়ার্ড মাস্টারের কাছে যান। সব বলে দেবে।
তরুণ দিশেহারা। উদ্ভ্রান্ত, এসব ব্যাপারে মুরারীপুকুরের ক্লাবের ছেলেরা হাত গুটিয়ে বসে থাকে না। টাকার সংস্থান হল। সেই টাকা নিয়ে ছুটতে ছুটতে নার্সিংহোমে তরুণ যখন পৌঁছোয় সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। অনেক আশা-আকাঙক্ষা স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার চোখ দুটি স্থির। নিস্পন্দ নিথর দেহখানি। সার্জন জানিয়ে দিলেন– সরি, মেয়েটি কোনও সুযোগই দিল না। ওটি-তে নেওয়ার আগেই সব শেষ।
আদিত্য অফিস থেকে ফিরেই আইআইটি-র ফর্মটা মেয়েকে দিয়ে বলে– নে এটা ফিল আপ কর। মিঠু দেখেই বলে এটা কী?
পড়ে দেখ। ফর্মের পাতা ওলটাতে ওলটাতে মিঠু খানিকটা ভীত হয়ে প্রশ্ন করে– বাবা, এ কি আমি পারব? আদিত্য নিজেই মনোবল উসকে নিয়ে সাহস জোগায়– পারবি মানে, তোর টিউটররা কি তাহলে ভুল মূল্যায়ন করেছে। আর ছিল রূপাঞ্জনা। সে তো আজ অতীত। তোর টিচাররা তো তোদের দুজনের ব্যাপারে হাই অ্যামবিশনের এক্সপেক্ট করছে।
– কিন্তু বাবা আমি চেয়েছিলাম, স্টেট লেভেলে ইঞ্জিনিয়ারিংটা দিতে। লোকালই কোনও একটা চাকরি নিয়ে তোমাদের কাছে থাকতে। আমি তো তোমাদের একমাত্র সন্তান। এটাতে পড়াশোনা করলে চাকরি নিয়ে তোমাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে।
– তা হোক। আমাদের কথা তোর ভাবতে হবে না। চোখ উপর দিকে রাখ, তোকে অনেক উঁচুতে উঠতে হবে। তুই আমাদের গর্ব। পাড়ার গর্ব। মিঠু তর্ক বাড়ায় না। চুপ করে যায়। যে কথাটা বলতে পারল না, এই যে বাবা উঁচুতে স্বপ্ন দেখছে, অর্থের প্রাচুর্য হয়তো একদিন গিলে খাবে। দায়িত্ব, কর্তব্য মূল্যবোধ সবই হয়তো একদিন পরিত্যাজ্য হবে।
তরুণ যাচ্ছিল আদিত্য মুখার্জীর বাড়ির পাশ দিয়ে। একটা চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে বাড়িতে প্রবেশ করে। তার চাইতেও বড়ো, কারণে অকারণে মিঠুকে দেখার অভিলাষ। সে যে তার রূপাঞ্জনারই প্রতিরূপ। রাঘব আগরওয়ালার কর্মচারী সুজন অধিকারীর কঞ্চির আস্ফালনে আদিত্য কুঁকড়ে ঢোঁড়া সাপ। মুখে ভাষা নেই। প্রতিশ্রুতির বাক্যবাণী নেই। অবনত মস্তকে চেয়ারে মাথা নীচু করে বসে থাকে। সুজনের অশ্রাব্য ভাষায় দরজা নেই। অবিশ্রান্ত আস্ফালন করেই চলেছে– বুড়ো ভাম, ভাড়া চুকোতে অসুবিধা কোথায়? ছিপলিটা দিয়ে দিলেই তো সব চুকে যায়। বাইরে দাঁড়িয়ে তরুণ বেকায়দায় পড়ল। আশা ছিল মেয়েটার সাথে দু-দণ্ড কথা বলে মনটা জুড়োবে। মেজাজটা হিঁচড়ে দিল। পকেট থেকে কানপুরি ছুরিটা বের করে সুজনের পেটের সামনে ঠেকিয়ে বলে– আবে এ কাঞ্চা, কি বললি? আবার বল। একদম পেট কামিয়ে দেব। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া সুজন ছুরি দেখে নীচের কাপড় আর শুকনো রাখতে পারে না, দুর্বল পরিবারে তড়পানোর শক্তি হারিয়েছে। তরুণের পা দুটি জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে বলে– দাদা আমার কি দোষ? মালিকের অর্ডার ছিল কড়া ভাষায় থ্রেট করতে।
– নে ওঠ শালা, তাই বলে আমার মাকে বেইজ্জত করবি। কত ভাড়া পাবি? সুজন করুন সুরে বলে– পাঁচশো টাকা করে ছয় মাস তিন হাজার টাকা।
পকেটের থেকে এক গোছা টাকা বের করে ছুড়ে দিয়ে বলে– নে এতে তোর তিনহাজার টাকার বেশি আছে। এর পরে যে টাকা বাকি পড়বে আমার মা চাকরি করে শুধবে। তার আগে যদি এ মহল্লায় পা দিয়েছিস তো, আসার সময় দত্তদের পুকুরটা দেখেছিস, একদম খাল্লাস করে ওখানে চালান করে দেব। চল হট শালা। মিঠুর দিকে তাকিয়ে বলে– মা-রে ও মালটার সাথে এভাবে কথা না বললে হল্লা করেই চলত। বারবার ঝামেলা করত। তোর সামনে লোকটার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করায় আমারও সংকোচ হচ্ছে। এছাড়া আমার যে আর কোনও পথও খোলা ছিল না। সংকোচ মিঠু করে না। শ্রদ্ধার পরিমাণটা অন্তরস্থলে আরও একটু জায়গা করে নেয়। আমি উঠি রে, তোর পড়াশোনার অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেল। বলে তরুণ দাঁড়ায় না।
পরিণতি তরুণকে নিয়ে যায় নরক দর্শনে। সে জাত বজ্জাত নয়। বেপরোয়া ঔদাসীন্যের সঙ্গে যারা পাপের পথে হাঁটে, কোয়ালিস হাঁকায়, সে ধাতুতে তরুণ গড়া নয়। পাপ তার পেশা নয়, নেশা। দারিদ্র্যকে বড়ো কাছের থেকে দেখেছে। সেই দারিদ্র্য নিয়ে স্ত্রী কন্যার সংসার সামলেছে। সব হারানোর যন্ত্রণা বিষাক্ত ভয়ানক নেশার মতোই তার মতো ইস্পাতে গড়া মানুষটাকে ধবংসের পথে নিয়ে যায়। বিদ্যার কারণেই হোক আর মস্তিষ্কের উর্বরা শক্তির প্রয়োগে বন্ধ কারখানায় মাল সরানোর কাজে সে এলাকার মাফিয়া ডন। তরুণের সমগোত্রীয় কেউ ধৃষ্টতা দেখানোর স্পর্ধা দেখায় না।
শ্রীজীবের আর এক দশা। বাপটা এক মেয়েছেলের খপ্পরে পড়ে তাকে নিয়ে ভেগেছে। দারিদ্র্য অনেক কিছু দেয়। দায়িত্ব কর্তব্য সুস্থ রুচিবোধের রসদ যোগায়। ক্ষিদের তাড়না মেটায় না। সেই তাড়নাতেই বাবুর বাড়িতে কাজ ধরে। শরীরে খাদ্য যোগানের বিনিময়ে পরিশ্রমের মাত্রা বেশি হলে শরীর তা সহ্য করে না। প্রতিদিন জ্বর হয়। বুকে কফের ভাব তৈরি হয়। সবসময় শুধু কাশে। শ্রীজীবটার কোনও কাজ জোটেনি। সব কারখানায় বড়ো বড়ো তালা ঝুলছে। তরুণের ফাইফরমাশ খাটে। তরুণ কিছু দেয়। শ্রীজীবটা কদিন তরুণের কাছে যায় না। মা টার শরীরটা বাড়াবাড়ি হয়েছে।
শ্রীজীব ধূর্ত নয়। সে পরিস্থিতির দাস। সেই দাসত্বের শৃঙ্খল মোচন করার শক্তি তার নেই। অকৃতজ্ঞতা, বিবেকদংশন মনকে কুরে কুরে খায়। যথাসম্ভব সেই যন্ত্রণাকে চাপা দিয়ে কৃত্রিম উত্তেজনা তৈরি করে হাঁপাতে হাঁপাতে তরুণকে গিয়ে বলে– তরুণদা, কোরা শিবুকে পুলিশ কৃষ্ণা রেপ কেসে সকালে তুলে নিয়ে গেছে। তরুণের মালের নেশাটা বেশ চড়েছে। চেয়ারে বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে ব্যালেন্স রাখছে। শ্রীজীবের কথা শুনে চমকে ওঠে– কি, কোরা শিবুকে পুলিশ পেল কোথায়? ওকে তো ঘোড়াডাঙায় পাঠিয়েছি। আজ বিকেলে ফেরার কথা। ফোন করেছিল তো কাল রাত্রে।
– তা জানি না, হয়তো সকালেই এসেছিল। পুলিশ বাগে পেয়েই অ্যারেস্ট করেছে।
– ও কেসে শিবুকে ধরবে কেন। ওটা তো কাঁকুরগাছির কেস। ঘাপলা কেস নয়তো?
– কি জানি, একবার গিয়ে দেখলে হতো না?
– চল তবে দেখেই আসি। শীতের পড়ন্ত বেলায় হাঁটতে ভালোই লাগছে। হাঁটতে হাঁটতে মালের ধুনকিটা অনেকটা কেটে এসেছে। প্রশস্ত রাস্তার দুই পাশে অজস্র এঁদো গলি। নদীর শাখা নদী। স্রোত কম থাকায় এসব নদীতে পাঁক প্রজাতির মাছের উৎপাদন ঘটে। এই এঁদো গলিতে সন্ধ্যার আগেই সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসে। চাঁদ এ গলিতে উঁকি মারে না। এদের দৈন্যদশা খোঁজ নেওয়ার তাগিদ নেই। পাঁচ ফুট রাস্তার দুই পাশে সরু নর্দমার পাঁক চলকে চলকে সমস্ত রাস্তাটা পাঁকময় করে রেখেছে। হাবু ডাবু গলি থেকে বেরিয়েই তরুণের সাথে দেখা।
– আরে তরুণদা কোথায় চললে?
– আর বলিস না, আমাদের কোরা শিবুটাকে রেপ কেসে পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে।
– হ্যাঁ তাই তো শুনলাম, তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে। চলো তো যাই। কেসটা কি? তরুণ আপত্তি করে না। মনে মনে দু-একজন সঙ্গী তরুণ খুঁজছিল। শ্রীজীব অনেকক্ষণ ধরে কেটে পড়ার ধান্ধা করছিল। তরুণকে বলে– তরুণদা মা টার শরীরের অবস্থা ভালো না। আমি তবে চলে যাব? আয় তবে। প্রশস্ত রাস্তা ছেড়ে এঁদো গলিতে কিছুটা পথ যেতেই তরুণের নেশার ঘোরটা কাটতে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরে– ইস, এ নোংরা গলিতে ঢুকলি কেন?
– আরে ইয়ার, এখান থেকে একটু তাড়াতাড়ি হবে।
– কেস দিয়ে দিলে সব লুচ্চা হয়ে যাবে না? মস্তিষ্কের উর্বরা শক্তি তরুণের কম নেই। সেই শক্তিতেই এক মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয়।
এখান থেকে পালাবার আর কোনও রাস্তা নেই, মৃত্যুর বদ্ধভূমিতে ঢুকে পড়েছে।
– আরে ইয়ার থোড়া রুক, একটু খালাস করে নিই। হাবু ডাবু বাধা দেয় না। একটু এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করে। পরস্পরের সঙ্গে শলা পর্ব সেরে নেয়। শালা এখান থেকে ভাগবে কোথায়? নে খালাস করে নে। একটু পরে তুই খালাস হবি। মতলবটা নরখাদক বাটপাড়েরা বুঝতে পারেনি। মিশকালো ঘন অন্ধকারে পকেট থেকে মেশিনটা বার করে। অত্যন্ত সন্তর্পণে লক্ষ্য স্থির রেখে পর পর শুট। আওয়াজটা বজ্রগর্ভ নয়। সাইলেন্সার লাগানো ছিল। হাবুটা ছিটকে এঁদো নর্দমায় পড়ে। বিষধর সাপ শেষবারের মতো ফণা তোলার চেষ্টা করে। পারে না। নর্দমার পাঁক মাথা ঠান্ডা করে। পাঁকেই সমস্ত শক্তি নিঃসৃত হতে হতে নিথর হয়ে যায়। ডাবু তলপেটে দানা খেয়ে বজ্রগর্ভে হুংকার দিতে দিতে বড়ো রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে। তরুণ পাঁকে দেহটাতে পাড়া দিয়ে বিজয়ের মুকুট চাপিয়ে দাম্ভিক শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বলে– শালা মারনেওয়ালা মর গই। পথের কাঁটা তরুণ উপড়ে, দ্রুত গতিতে বেরিয়ে আসে। নির্মূল হয় না। পশ্চিম আকাশে লাল দিগন্তে মৃত্যুর বলিরেখা অঙ্কিত হয়ে রইল, তাতে তরুণের পরোয়া নেই। আত্মরক্ষার কোনও দায় নেই। সে আজ পালহীন, উদ্দেশ্যবিহীন উত্তলিত জোয়ারে বয়ে যাওয়া নৌকা। সে নৌকায় সওয়ারী সে নিজেই।
মিঠু প্রথম প্রথম বাবাকে ফোন করত। সুদূর কেনটনে বসে মায়ের যত্ন, বাবার সাহচর্যের অভাবে মনটা শূন্যতায় ভরে উঠত। ট্রেনিং পিরিয়ডে তখনও, বৃহৎ কর্ম জগতে প্রবেশ করেনি। মা-বাবার মায়া মমতার তুচ্ছ মোড়কটার অভাবে জীবনীশক্তি কেমন স্তিমিত হয়ে যায়। মেয়ের সাফল্যের চূড়ার মসনদে আসীন হওয়ার মোহে মেয়ের শূন্যতা আদিত্যকে ভারাক্রান্ত করে না। সেটা ক্ষণিকের মোহজাল। অবসর গ্রহণের পর আদিত্যের একমাত্র ঠিকানা রাধিকারঞ্জনের দাবার ঠেক। দাবার ঘুটিতে চাল দেওয়ায় আদিত্যের অপরূপ কৌশল। সেই কৌশলেই রাধিকারঞ্জন কুপোকাত। একটার পর একটা চালে কখন যে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত, কখন যে জগৎটাকে ঘন অন্ধকার গ্রাস করেছে আদিত্য বুঝতে পারে না। এবার বাড়ি ফেরার পালা। ফিরতে হয়। সেই যাওয়া আর আসা। এরমধ্যে সবসময় যে সদর্থ ব্যাখ্যা থাকে তা নয়। তবু যেতে হয়।
ঘরে ফিরেই আদিত্য মৃন্ময়ীকে সুধোয়– মেয়েটা ফোন করেছিল? মৃন্ময়ী উত্তর দেয় না। ফুঁসতে থাকে। মৃত আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের রসদ সঞ্চয় করে। তারপর একসময় বজ্রনিনাদে বিস্ফোরিত হয়। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো বিচ্ছুরিত হতে থাকে– রোজ রোজ একই কথা বলো কেন। নিজে তো দাবার আড্ডায় সারা দিন কাটিয়ে, গভীর রাতে মেয়ের কথা মনে পড়ে। মা হয়ে আমার মন টেকে কি করে। ভেবে দেখেছ? টাকার লোভে মেয়েটাকে পরবাসী করে ছাড়লে। এখন লোক দেখানো হাপিত্যেস করে লাভ কি? লোভ আদিত্যের ছিল। লোভটা সহজাত নয়। দারিদ্রের অপমান লাঞ্ছনা তাকে লোভাতুর করে তোলে। মিঠুর নাম্বারটা ডায়াল করতেই অল লাইনস আর বিজি। কথাগুলো ফাটা কাঁসির মতো লাগে। আদিত্য ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হতাশা অবসাদে ফোন আর ধরে না। অবসর সময়ে আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।
ভয়, আতঙ্ক, সংকোচ এগুলি অপরাধী মনের সহজাত প্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তিতে শ্রীজীব নিজেকে আত্মগোপন করে রাখে। তরুণদাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিয়েছিল। মরেছে জল্লাদেরা। জল্লাদের হাতে দেবতাদের মৃত্যু হয় না। ইচ্ছা মৃত্যুতেই তাদের পরিণতি ঘটে। তরুণদার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি শ্রীজীবের মনের দৃঢ়তা আনে। সেই দৃঢ়তায় মনের সমস্ত সংকোচ ঝেড়ে ফেলে তরুণের পায়ে মাথা নীচু করে বসে। তরুণদা আমাকে শাস্তি দাও। আমি মাফ চাই না। যে অপরাধ আমি করেছি তার ক্ষমা হয় না। তরুণের শান্ত স্নিগ্ধ মমতা যেন শ্রীজীবের উপর বর্ষিত হয়, বাইরে কৃত্রিম ক্ষিপ্রতায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে– ওঠ শালা মাকড়া, ঘাপলা করে এসে ন্যাকামি মারাচ্ছে। কি এমন দরকার পড়ল, কত টাকা নিয়েছিস? ওদের তুই চিনিস? এবারে তো তোকে সরিয়ে দেওয়ার ছক করছে, সে খবর রাখিস?
– না না বস, টাকা নিইনি। মানে ওরা বলেছিল কাজ হলে টাকা দেবে।
– যাক, খাওয়াদাওয়া করেছিস? শ্রীজীবের মুখে ভাষা নেই। অপরাধীর মতো মাথা নত করে বসে থাকে।
– যা টেবিলের উপর পাউরুটি কলা আছে। খেয়ে নে। শ্রীজীব দুটো থালায় পাউরুটি কলা নিয়ে আসে। একটি তরুণদাকে দেয়, একটি নিজে নেয়।
– তোর মা কেমন আছে?
– ভালো না, সেই জন্যই ওরা বলল, তরুণকে আমাদের হাতে তুলে দে, তোর সব চিকিৎসার খরচ আমাদের।
– গর্ধব, সেটা তো আমাকে বলতে পারতিস।
– তোমার ঋণ আর কত বাড়াব। আমার যে আর মুখ ছিল না।
– তাই বলে আমাকে খরচা করে ঋণ শোধ করবি? এখন তোর বিপদটা ভেবে দেখছিস? তোকে যে ওরা খরচা করে দেবে। শোন, বিলাসপুরে আমার এক বন্ধু আছে। কাল দুপুরের মুম্বই মেলের টিকিট কেটে দিচ্ছি। মাকে নিয়ে ওখানে চলে যা। ওরা সব ব্যবস্থা করে দেবে। আমার সঙ্গে ঋত্বিকের কথা হয়ে আছে। ওখানকার চিরিমিরি কোলিয়ারিতে তোর একটা কাজেরও ব্যবস্থা করে দেবে। আর ড্রয়ারটা খোল, ওখানে লাখ খানেক টাকা আছে। ওই টাকা নিয়ে মায়ের চিকিৎসা করাবি। এটুকু সময় তোর বাড়ির চারদিকে আমার লোক থাকবে। এখানে তোকে রক্ষা করতে পারব না।
শ্রীজীব যে দেবতাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিতে গিয়েছিল সেই তাকে মারন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে এই মহান দায়ভার গ্রহণ করছে। বিপদ যে তার অন্তরস্থলের দেবতাকেও গ্রাস করতে চলেছে। দেবতার নাম সে শুনেছে। চোখে দেখেনি। শুখা নদীতে বান এসেছে। কৃতজ্ঞতার বানে উত্তলিত হয়ে তরুণের পা জড়িয়ে ধরে– তরুণদা, ঠাকুর আমি দেখিনি। তুমিই আমার ঠাকুর। তোমাকে এই বিপদের মধ্যে ফেলে আমি কোথাও যেতে পারব না। যা হবার হোক। আমি তোমার সাথেই থাকব।
– অনেক ভাট বকেছিস। এবার ওঠ। তোর যে সংসারে অনেক কাজ। আমার সংসারে প্রয়োজন ফুরিয়েছে।
– কি বলছ, তরুণদা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।
– বুঝতে হবে না। অনেক মেগাসিরিয়াল হয়েছে। এবার কেটে পড়। বাড়িতে গিয়ে গোছগাছ কর।
কতদিন ধরে মৃন্ময়ীর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। পেটে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা সমস্ত শরীরটা নাড়া দিয়ে উঠেছে। সেই যন্ত্রণা প্রবল হলে আদিত্য কাছাকাছি এক হাসপাতালে মৃন্ময়ীকে নিয়ে যায়। পেশেন্টকে দেখেই ডা. রায়ের সন্দেহ হয়। বায়োপসির রিপোর্ট হাতে আসতেই ডা. রায়ের সন্দেহের অন্ধকার কেটে যায়। রিপোর্ট পজিটিভ। লিভারে ম্যালিগন্যান্ট ক্যান্সার। অন্ধকারটা নেমে আসে আদিত্যর জীবনে।
ব্যাংকে যে ক’টা টাকা ছিল প্রাথমিক চিকিৎসাতেই শেষ। মৃন্ময়ীর আয়ুষ্কাল আর কতদিন, সেটা বলবে ভবিষ্যৎ। চিকিৎসার পরবর্তী ব্যয়ভার মেটাবে কীভাবে। সেটা তো গন্ধমাদন পর্বত।
যাদুকরের কেরামতিতে পুতুল নাচে। অর্থের যাদুকর দুর্বল হলে পেশেন্টও অচল হতে থাকে। মৃন্ময়ী ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ে থাকে। দৃষ্টি আবছা হতে থাকে। গলাতে আওয়াজে আর সেই ঝাঁঝ নেই। থেকে থেকে আদিত্যকে প্রশ্ন করে– মেয়েটা ফোন করেছিল গো? আদিত্যের দীর্ঘনিঃশ্বাসের আঁচ মৃন্ময়ী করতে পারেনি। বাইরে কৃত্রিম স্বাচ্ছ্যন্দে উত্তর দেয়– হ্যাঁ করেছিল তো। নানান ঝামেলায় বলা হয়নি। এই তো রাধিকার বাড়ি থেকে আসার পথে হঠাৎই মিঠুর ফোন। তোমার কথা, আমার কথা। পাড়ার সবার কথা। বলছে অফিসে খুব কাজের চাপ। তবে পুজোর সময় আসবে বলেছে। মৃন্ময়ী বাধা দিয়ে বলে– আমার শরীর খারাপের কথা বলোনি তো?– না না ওসব বলিনি। মেয়েটা ওখানে বসে ছটফট করবে। এতগুলি মিথ্যা কথা বানিয়ে বলতে আদিত্যেরও মনটা হিঁচড়ে যাচ্ছিল। বাস্তবটা যে বড়ো নিষ্ঠুর। মৃত্যু পথযাত্রীর কাছে এই মিথ্যেটাই যে বাঁচার রসদ। কিছুটা হলেও শরীর, মন চাঙ্গা হয়।
বিকেল হলেই রাধিকারঞ্জনের মনটা ছুকছুক করে। চোখ পড়ে দাবার বোর্ডের দিকে। ঘুটি সাজিয়ে বসে থাকে আদিত্যের অপেক্ষায়। আজ কতদিন হল আদিত্য এমুখো হয় না। দাবার নেশা তাকে আদিত্যমুখী করে তোলে। সদর দরজা হাট করা খোলা। মধ্য খাটালে একটা বিড়াল উচ্ছিষ্ঠ যা কিছু ছিল সাবড়ে দিয়ে মৌতাত করছে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে। ম্যাও করে নবাগত অতিথির আগমনি বার্তা জানান দিয়ে খাটের তলায় নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছে। খাটের উপর গোটা তিনেক বালিশে হেলান দিয়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। যে চাউনিতে আলোর রেখা নেই। অন্ধকারের করাল গ্রাস একটু একটু করে গিলে খাচ্ছে। ভাঙা হাটে প্রেম ভালোবাসা স্নেহের খদ্দেররা এক এক করে সরে যাচ্ছে। এখন আদিত্য শুধুই একা। অকর্মণ্য স্বামী মৃত্যু পথযাত্রী স্ত্রীর শেষ চিকিৎসাটুকু করতে অপারগ। অসহায় মানুষের চিন্তাটাই একমাত্র অবলম্বন।
দরজা খোলা পেয়ে ভিতরে ঢুকে হাঁক পাড়ে রাধিকারঞ্জন – আদিত্য, ও আদিত্য ঘরে আছ নাকি? নিস্তব্ধ নিঃস্পন্দ একটা মাত্র অল্প পাওয়ারের ল্যাম্পের ক্ষীণ আলো জ্বলছে। প্রাণহীন ইটের পাঁজরে চারদেয়ালে আদিত্য যেন বন্দিদশা কাটাচ্ছে। মুখমণ্ডল মনের আরসি। কোটরাগত চোখ, অসংখ্য চিন্তার ভাঁজ জানান দিচ্ছে আদিত্য ভালো নেই। – কি ব্যাপার? কত দিন তোমার দেখা নেই। আদিত্যর সাড়া মেলে না। গায়ে হাত পড়তেই ধড়মড় করে ওঠে। স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে। সবটা পারে না। উদ্বিগ্ন অশান্ত মন স্বাভাবিক হতে দেয় না। বয়সের ভারে রাধিকারঞ্জনেরও চেতনার পরিপক্বতা এসেছে। সেই পরিপক্বতায় তার বুঝতে দেরি হয় না।
– কি ব্যাপার, মনে হচ্ছে কোনও গভীর সমস্যায় পড়েছ?– হ্যাঁ ভাই, ভালো নেই। মিঠুর মা হাসপাতালে ভর্তি। উদ্বিগ্ন রাধিকা প্রশ্ন করে– কেন কী হয়েছে? অকারণ গৌরচন্দ্রিকা বাড়ায় না। আর সে মানসিকতাও নেই। সরাসরি বলে– লিভার ক্যান্সার। রাধিকা হতবাক স্তম্ভিত। সে জানে অশান্ত, উদ্বিগ্ন মনকে শান্ত করা যায় না। রাধিকা সে পথে হাঁটেও না। পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করে। তা চিকিৎসা ঠিকঠাক চলছে তো?
– চলছে, তবে প্রাথমিক পর্বটা মিটেছে। এখন দরকার পরের ধাপ। অপারেশন, কেমো এদিক সেদিক আরও খরচ। এ রাশ তো আমি আর টানতে পারছি না। এখন আমি সর্বশান্ত।
– তা এখনও খরচ কত কিছু জানতে পেরেছ?
– কি জানি, বোধহয় লাখখানেক হবে।
– মিঠুকে খবর দিয়েছ?
এক দীর্ঘনিশ্বাসে বলে– না, আসলে অতদূরে থাকে। তাছাড়া ওখানে ওর কাজের চাপও খুব বেশি। শুধু শুধু ব্যতিব্যস্ত করে লাভ কি বলো ভায়া।
এই দীর্ঘনিশ্বাসই রাধিকাকে জানান দেয় শেষোক্ত মনগড়া মন্তব্য অন্তরস্থলের হতাশার গভীরতা। বড়ো অজান্তে আদিত্যের দগদগে ঘায়ে খোঁচা দিয়ে বসেছে। রাধিকা কথা বাড়ায় না। আজ আসি– বলে রাধিকারঞ্জন রাস্তায় বেরিয়ে আসে।
বৃদ্ধ বয়সের দোসর বড়ো অবলম্বন। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সঙ্গীহীন হতে থাকে মানুষ। সে হতে থাকে নিঃসঙ্গ, একা। এই দোসর তখন পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়ে ধরতে চায়। এতগুলো টাকার দায়ভার সে বইবে কী ভাবে। ক্লাবের ছেলেদের বলবে? মন সায় দেয় না। আদিত্য তো তাকে দায়িত্ব দেয়ওনি। দিশাহীন, উদভ্রান্তের মতো চলতে চলতে হঠাৎই তরুণের সাথে দেখা হয়।
– পাশে এসো। একটা ভয়ংকর সমস্যায় পড়েছি।
সেটা তো দূর থেকে আসতে দেখেই বুঝতে পারছি। কি হয়েছে?
– আদিত্যের স্ত্রীর শরীর খুব খারাপ। হাসপাতালে ভর্তি। এখন ওর যা অবস্থা, তাতে চিকিৎসাটাও করতে পারছে না। ভাবছিলাম ক্লাবকে জানাব কিনা। মেয়েকে খবর দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলতেই মনগড়া কতগুলো কথা বলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল।
– মিঠুর নাম্বারটা, আচ্ছা দেখি বাড়িতে যাই।
– কি মিঠুর নাম্বার। দাঁড়াও। বলে বুক পকেট থেকে একতাড়া চিরকুট বের করে খুঁজে খুঁজে নাম্বারটা দিয়ে বলে– দ্যাখো, নবাব নন্দিনীর নাগাল পাও কিনা।
নাম্বারটা পকেটে গুঁজেই বলে– আমাকে দুটো দিন সময় দিন। আমি হাসপাতালে যাচ্ছি রাধিকাবাবু, এ চিকিৎসার খরচ আমিই দিতে পারতাম। আপনি তো জানেন আমার রোজগার সবই পাপের টাকা। বউদি বাঁচবেন কিনা জানি না, পাঁক তাঁর গায়ে লাগাতে চাইছি না।
তরুণ সময় নষ্ট করে না। মিঠুকে ফোন লাগায়। সেই ফাটা ক্যাসেট– অল লাইনস আর বিজি। তরুণ নাছোড়। হতাশায় শ্রান্ত হওয়ার ধাতুতে সে গড়া নয়। অবিশ্রান্ত ডায়াল করতেই থাকে। আচমকাই রিং বাজতে থাকে। শুখা নদীতে যেন জলের সঞ্চার ঘটে। প্রাচুর্যের মসনদে আসীন হলে কণ্ঠস্বরে আলাদা গাম্ভীর্য আসে। রুচি, চালচলনে সর্বত্র লেগে থাকে পরিবর্তনের ছোঁয়া।
– হ্যালো, তরুণ ভীত নয়। মনের দৃঢ়তাই শক্তি যোগায়। অথচ স্নেহশীল বাপের মতোই আর্জি জানায়– হ্যালো মিঠু? আমাকে চিনতে পারছিস মা, আমি তোর তরুণ কাকা।
– ও হ্যাঁ, বলো, বাবা-মা কেমন আছে, তুমি কেমন আছ? পাড়ায় সবাই? দাঁড়া দাঁড়া একবারে এত প্রশ্ন করিস না, সব গুলিয়ে যাবে। ফোনটা ছাড়িস না। আমার কথা, পাড়ার কথা ছাড়, তোর বাপ মায়ের খবরটা নিস। তারা কেমন আছে?
– কাকু, এখন আর আপশোশ করে কি হবে বলো? বাবা যে আমায় এই জায়গায় আসতে বাধ্য করেছে। এটা তো আমি চাইনি। প্রচুর টাকার বিনিময়ে কোম্পানি আমার চব্বিশ ঘণ্টাই কিনে নিয়েছে। আমার পার্সোনাল লাইফ বলে যে কিছুই অবশিষ্ট নেই। যাক মা-বাবা এখন কেমন আছে?
– ভালো নেই। তোর মায়ের শরীর খুব খারাপ। লিভার ক্যান্সার। চিকিৎসার সামর্থ্যও তোর বাবার নেই। বলিস তো চাঁদা তুলে তোর মায়ের চিকিৎসা করাই।
– সে কি? বাবা একটু আমাকে জানাতে পারত।
– তোর বাবা ফোন করে করে হতাশ হয়ে অভিমানে ফোন করা ছেড়ে দিয়েছে।
– কাকু বাবার অ্যাকাউন্ট নাম্বার আমার জানা আছে। আজকেই আমি দশ লাখ টাকা ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। তুমি একটু দাঁড়িয়ে থেকে চিকিৎসা করাও। লাগলে আরও পাঠাব। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি দেশে ফিরব।
টাকা এল। চিকিৎসাও হল। পেল না অন্তরাত্মার পদধ্বনি। সেই অন্তরাত্মার অভাবে শেষ জীবনীশক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল। এ রোগের শেষ পরিণতি বড়ো মর্মান্তিক। সেই মর্মান্তিকতার চরম মুহূর্তের আগে পর্যন্ত ঝাপসা স্থির দৃষ্টিতে শুধু একটাই প্রলাপ
– মিঠুর ফোন পেলে গো? আমার শরীর খারাপের কথা বলোনি তো। ও যে বড়ো কষ্ট পাবে। মিথ্যে আশ্বাস পাথেয় করে মৃন্ময়ী ভোরবেলা চলে গেল।
আজ সতেরোই শ্রাবণ। ঘন কালো মেঘে আকাশটা নীচে নেমে এসেছে। প্রকৃতির অশ্রুধারা দু’কূল প্লাবিত করছে। সে অশ্রু মোছাবার কেউ নেই। এই কালান্তক দিনটি তরুণের বড়ো একার। একা কাঁদবার দিন। মালা, ফুল, চন্দনে অপরূপ সাজে সেজেছে। আজ যে মা-মেয়ের জন্ম মৃত্যু দিন। ভরপেট্টা মাল টেনেছে এই উৎসবে। বেসামাল তরুণ মা-মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে অবুঝ বালকের মতো প্রশ্ন করে– আমাকে এভাবে ঠকালি কেন বল তো? এখানে ফেলে রেখে তোরা সুখে আছিস তো? এবার তরুণ আর সামলাতে পারে না। দু-চোখ বেয়ে অবিরত ধারা বেয়ে আসে। একটু থেমে বায়না করে– আমাকে তোরা নিবি? এ শরীরের বোঝা আর যে টানতে পারছি না। রূপাঞ্জনার প্রতিকৃতি জীবন্ত মূর্ত প্রতীক হয়ে আর্জি মঞ্জুর করে– চলে এস বাবা। ওখানে যে তুমি পাঁকে তলিয়ে যাচ্ছ। তিনদিন পর বাড়িটার ভেতর থেকে পচা দুর্গন্ধ এলাকা ভারী করে তুলল।
মালতিটা কাজ করে ভালো। বাসন মাজা, রান্না করা, কাপড় কাচা, দাদুর স্নানের জল তোলা। এসব কাজে খুঁত রাখে না। তবে একটু টকেটিভ। চান্স পেলেই ডিভিডি চালাবে। আদিত্যর অসুবিধা হয় না। বোবা ঘরে তবু একটা কথা বলার লোক তো আছে। যতক্ষণ থাকে ঘরটা কথাময় করে রাখে। আদিত্য খাটে শুয়ে খবরের কাগজটা সামনে নিয়ে পুরু লেন্সের চশমাটা নাকের ডগায় রেখে রাজনীতির দুবৃত্তায়ন হজম করছিল। মালতি বাইরে থেকে ছুটতে ছুটতে এসে আদিত্যকে সংবাদটা দেয়– দাদু বাইরে বিশুর চায়ের দোকানে চ্যাঁচামেচি হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ না?
আদিত্য ভাবলেশহীন কৌতুক প্রকাশ করে বলে– কই না তো।
– সে কি, কত লোক জড়ো হয়েছে, তুমি শুনতে পাচ্ছ না?
– তাহলে চ্যাঁচামেচিটা বোধহয় আস্তে আস্তে হচ্ছে। একরকম জোর করে মালতি আদিত্যকে বাইরে টেনে আনে।
দিশেহারা ভীত সন্ত্রস্ত চান্দ্রেয়ী কোলের ছেলেটাকে বিশুর চায়ের দোকানে বসায়। বাচ্চাটা ক্ষিদের ক্লান্তিতে কেমন নেতিয়ে পড়ে। চান্দ্রেয়ী এ ব্যাগ সে ব্যাগ থেকে এক প্যাকেট দলা পাকানো বিস্কুট বের করে। বিশুর দিকে তাকিয়ে করুণ ভাবে বলে– দাদা এক গেলাস দুধ দেবেন? বিশু না করে না। দুধ বিস্কুট খেয়ে শক্তি ফিরে পায়। স্বভাবসিদ্ধ চরিত্রে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে থাকে। উদ্দেশ্যবিহীন চান্দ্রেয়ীকে বাঁশের খুটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখে বিশুর কৌতুহলী মন জিজ্ঞাসা করে– এই মেয়ে তোমার নাম কি? চান্দ্রেয়ী নির্বাক। তুমি কোথায় থাকো? মনের বিভ্রান্তি তাকে আড়ষ্ট করে রাখে।
– আরে এ মেয়ে তো কোনও কথার উত্তর দেয় না। তোমার স্বামীর নাম কি? কোনও উত্তর না পেয়ে বিশুর মেজাজ এবার সপ্তমে।
– দুধ চাইবার বেলা তো বেশ কথা ফুটছিল। দাও তো বাপু, পয়সাটা দাও। লেডিস ব্যাগটা খুলে এদিক ওদিক ঝাঁকিয়ে করুণভাবে চান্দ্রেয়ী বলে,
– দাদা পয়সা যে নেই।
– সেটা তো আগে বলতে হয়। আগে বললে বাচ্চাটার জন্য বিশু দুধ দিত কি আদৌ দিত না সে প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু পাড়ার চায়ের দোকানে তার বচনে লোক সমাগমের সূত্রপাত এখানেই। আদিত্য কাছে এসে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে– বাপু তোমরা একটু সরো তো। মেয়েটা আসলে ঘাবড়ে গেছে। আদিত্যকে এ পাড়ার লোকজন কতকটা বয়সের কারণে কতকটা সজ্জন ব্যক্তিত্বের কারণে মান্য করে। তারা একে একে সরে যায়। বেশি দূর যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে।
– এ-ই মেয়ে তোমার নাম কী? স্নেহমাখা এই প্রশ্নে পিতৃমাতৃহীন মেয়েটা বাপের অজস্র স্নেহ ধারা বইতে থাকে। মেয়েটার মুখে কথা ফোটে– চান্দ্রেয়ী মিত্র।
– বাড়ি কোথায়?
– রায়গঞ্জ, বকুলপুর।
– থানা পোস্টঅফিস জানা আছে?
– না তা তো জানি না।
– তোমার স্বামীর নাম কি?
রজতশুভ্র মিত্র।
– মোবাইল নাম্বার আছে
– না, আমার মোবাইলটাও তো ফেলে এসেছি।
– তাহলে এভাবে তো কারও হোয়্যার এবাউটস জানা যাবে না। তুমি চাইলে আমার বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারো। আমার ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। মেয়েমানুষ এখন কোথায় যাবে? তারপর দেখছি কী করা যায়। স্বামীর সাথে মান-অভিমানের পালা চলছে? পাগলি মেয়ে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মান-অভিমান মনোমালিন্য এসব হয়ই। তাই বলে এভাবে নিরুদ্দেশের পথে কেউ পা বাড়ায়? আর দেরি কোরো না, চলে এস। পালহীন নৌকো তীর খুঁজে পেয়েছে। দেবদূতের মতো সন্তানস্নেহে যে মানুষটা তাকে আশ্রয় দিতে চাইছে, সে যে তার বাবারই সমগোত্রীয়।
আদিত্য বুড়োর একাকিত্ব ঘুচেছে। চান্দ্রেয়ী, মালতির সেবাযত্নে নিভে যাওয়া প্রদীপের সলতে আবার তিরতির করে জ্বলে উঠেছে। আর ছোট্ট শিশুটির আধো আধো বুলিতে গোটা বাড়িটা বর্ণময় করে তুলছে। তাকে জিজ্ঞাসা করে
– দাদুভাই তোমার নাম কি?
– ছিচন মিত্ত।
চান্দ্রেয়ী শুধরে দেয়– বলো দাদুভাইকে সিঞ্চন মিত্র। ছোট্ট কথাকলির দস্যিপনায় বুড়ার হাড়গোড়ের মরচেগুলো ছাড়তে শুরু করেছে। কখন যে সকাল গড়িয়ে রাতের আঁধার নেমে আসছে, সে হিসেবের খাতা খোলার বুড়োর সময় নেই। হঠাৎই কাগজে নিরুদ্দেশের প্রতি, এক বিজ্ঞাপনে আদিতের নজর পড়ে। আদিত্যের বুঝতে অসুবিধা হয় না। পোস্টআফিসে চিঠিখানা ড্রপ করে দিন গুনতে থাকে। প্রদীপের তেল একটু একটু করে নিঃশেষিত হচ্ছে। জেগে ওঠা দীপ্তিময় জীবনে রাতের আঁধার নেমে আসছে।
সিঞ্চন বাইরের বারান্দায় খেলা করছিল। বলে ওঠে– বাবা বাবা। বাসন মাজতে মাজতে মালতি ঘরে ঢুকে বলে– দাদু, বাইরে কে একজন তোমার কাছে এসেছে।
– ও এসে গেছে। ঘরে আসতে বল। রজত ঘরে ঢুকেই আদিত্যকে প্রণাম করে। আদিত্যর অনুমতিতে বসে। এদিক-ওদিক তাকায়।
– তাহলে তুমিই রজতশুভ্র মিত্র।
– আজ্ঞে হ্যাঁ
– বেশ। মালতিকে উদ্দেশ্য করে বলে। – মালতি, চান্দ্রেয়ীকে ডেকে দে তো মা। রজতকে দেখে তার দুচোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে থাকে। এ অশ্রুবর্ষণের গভীরতা বহুদূর বিস্তৃত। স্বামী দর্শনের ভিতর থেকে নির্দিষ্ট হয়ে যায়, যে সংসারের প্রদীপ সে তুচ্ছ অভিমানে নিভিয়ে এসেছিল, সেই প্রদীপ আবার জ্বেলে সংসারকে সে আলোকিত করবে। এক চোখে বইছে অনাবিল আনন্দের অশ্রুধারা, আর ওই যে অসহায় বৃদ্ধ মানুষটা সন্তান বাৎসল্যে, সস্নেহে এই কটাদিন লালিত করেছে, নাতিকে পেয়ে জীবনের দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছিল, রজতের হাত ধরে বেরিয়ে যেতেই তার প্রদীপের শিখা যে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হবে। সে চোখের জল সম্বরণ করা যায় না। আবেগ মানুষের চিরন্তন ধর্ম। সেই আবেগ হাসায়। সেই আবেগ চোখের জলে বুক ভাসায়। আবেগে ছেদ পড়ে আদিত্যের ডাকে– মা রজতকে খেতে দেওয়ার বন্দোবস্ত করো। ছেলেটা কতদূর থেকে এসেছে। রজতের দিকে তাকিয়ে বলে– তা বাবা আজ রাতটা থেকে কালকে না হয় সকালেই যেও, অতদূরের পথ। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রজত বাধা দেয় না।
সেই রাতে আদিত্য বুড়োর প্রবল জ্বর আসে। প্রলাপ বকতে থাকে– দাদু ভাই, আমার ঘোড়াটা দিয়ে যা। আমি যে হেরে যাচ্ছি। খবরটা মালতিই রাধিকারঞ্জনকে দেয়। রাধিকারঞ্জন দেরি করে না। হাসপাতালে ভর্তি করে বাইরে বেরিয়েই মিঠুকে ফোন লাগায়। রিং বাজতেই মিঠু ফোনটা ধরে– হ্যাঁ জেঠু বলো, বাবা, তোমরা কেমন আছ?
– হ্যাঁ মা, এখনও তোর আসার সময় হল না– এবার যে তোর বাবাও চলেছে রে। এক ভয়ংকর অজানা জ্বরে সঙ্গাহীন। জেঠু ফোনটা রাখ, আমি আসছি।
এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছোয়। উদভ্রান্ত উন্মাদের মতো ছুটতে ছুটতে বাবাকে জড়িয়ে ধরে– বাবা আমি এসেছি। এই দেখো তোমার মিঠু। আর তোমাকে ফেলে যাব না। আদিত্য আবছা প্রলেপে তখনও প্রলাপ বকেই চলেছে– দাদুভাই এলি? ঘোড়াটা দিয়ে যা। আমি যে মাত হয়ে যাচ্ছি। আমাকে যে জিততেই হবে।
দুরন্ত ঘোড়া একসময় শান্ত হয়। প্রাচুর্যের ঢক্বানিনাদে বসে দায়িত্ব, কর্তব্য, মূল্যবোধ, জীবনের সার্থকতার তাৎপর্য সে বুঝতে পারে না। সে তখন ফিরতে চায়। অবহেলায় ফেলে যাওয়া সেই রত্নভাণ্ডারকে সংসারের ধ্বংসস্তূপের ভিতর খুঁজতে থাকে। পায় না। কোনওদিন পাবে কিনা, কে জানে।