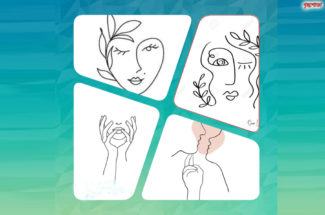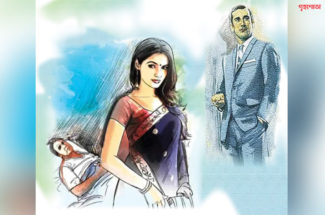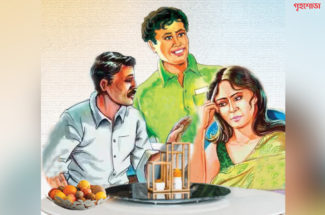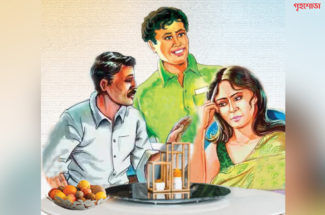আকাশ মেঘলা থাকায় সামনের সবুজ ঢেউয়ের মতো পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে লেপটে থাকা ছোটো ছোটো জনপদ, আঁকাবাঁকা পথরেখা, ইউক্যালিপটাস, সাইপ্রাস আর পাইন বনের শোভা উপভোগ করা যাচ্ছিল না। আচমকা পাহাড়ের ওপর থম মেরে দাঁড়ানো মেঘেরা সরে গেল। নাটকের মঞ্চের মতো কোনও এক অদৃশ্য আলোক পরিকল্পকের অমোঘ ইশারায় মেহগনি ছোপ পড়তে শুরু করল পালানি হিলসের গায়ে। গাঢ় ছায়া সরে গিয়ে ঝলমল করে উঠল কোদাইকানালের পাহাড়।
ঝেড়েঝুড়ে একটা বেঞ্চে বসলাম। পাশের বেঞ্চে মিলিটারি গোঁফওলা এক প্রবীণ খবরের কাগজ পড়ছেন। পাখির দল এসে বসছে গাছে। একটা গাঢ় নিস্তব্ধতার ছায়া চারদিকে। পাহাড়ি অর্কিড আর পাইন গাছের পাতায় লেগে আছে ভেজা শিশির আর মেঘবাষ্প। এখানে গাড়ির মিছিল নেই, মর্নিংওয়াকারের কলরব নেই, হকারের উৎপাত নেই, বাচ্চাদের প্র্যামগাড়ির অত্যাচার নেই– এই পার্ক যেন কোলাহলবিহীন প্রকৃতির এক স্বর্গরাজ্য।
রুনুদার হার্টের আর্টারিতে একটা ব্লকেজ ধরা পড়ায় তড়িঘড়ি চলে আসা হয়েছিল বেঙ্গালুরুতে। রিন্টির এখন উঁচু ক্লাস, প্রাইভেট টিউশন থাকে সপ্তাহ জুড়ে। রিন্টি আসেনি ওর বাবা মায়ের সঙ্গে। তবে অসুবিধে কিছু হয়নি, মা রুনুদাদের ফ্ল্যাটে এসে রিন্টির সঙ্গে আপাতত থাকছে। বেঙ্গালুরুতে ডক্টর আয়েঙ্গার অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করলেন দু’দিন পর। যতটা সময় লাগবে ভাবা হয়েছিল তার আগেই সব মসৃণভাবে হয়ে গেল। ডাক্তারবাবু ওষুধপত্র দিয়ে ছেড়ে দিলেন রুনুদাকে। বলে দিলেন ফ্যাট-ফ্রি ডায়েট চলবে এক বছর আর সামনের বছর চেক-আপের জন্য একবার আসতে হবে তাঁর কাছে।
রুনুদা বেড়াতে ভালোবাসে। ওর ইচ্ছেতে সায় দিয়ে আমরা এসেছি কোদাইকানালে। হোটেলের পাশেই কোদাই লেক। গতকাল একটা গাড়ি ভাড়া করে সিলভার ক্যাসকেড, পিলার রকস আর গ্রিন ভ্যালি ভিউ দেখে বিকেলে আমরা এলাম বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন মানমন্দির সোলার অবজারভেটরিতে। ফেরার পথে ড্রাইভার জানাল সিজন টাইমে কোদাই নাকি টুরিস্টে গিজগিজ করে। নেহাত বর্ষাকাল বলে এখন লোকজন একটু কম।
সাইট সিইং করে রুনুদা একটু টায়ার্ড। মেঘলা মেঘলা দিন, দিদিও বলল হোটেল থেকে বেরোবে না। মশালা ধোসা আর মোটা করে চা খেয়ে সকালে আমি একাই বেরিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ হেঁটে যে জায়গাটায় এসেছি এর নাম কোয়েকার্স ওয়াক। সিমেন্টের ফলক দেখে জানা গেল কোয়েকার নামে এক সাহেব দেড়শো বছর আগে কোদাই শহরের মানচিত্র তৈরি করতে এসে এই জায়গাটা দেখে অভিভূত হন। এক কিলোমিটার লম্বা পায়ে চলা পথ বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সেটাই কোয়েকার্স ওয়াক।
তলপেটে চাপ অনুভব করছি কিছুক্ষণ থেকে। গলা খাঁকারি দিয়ে মিলিটারি গোঁফওলা ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কড়ে আঙুল উঁচিয়ে দেখালাম। তাতে কাজ হল। ভদ্রলোক চশমাটা নাকের ডগায় এনে আমাকে একবার জরিপ করে আঙুল দিয়ে সামনের দিকে ইশারা করে আবার কাগজে মন দিলেন। দেখি রাস্তার ওপাশে একটা একতলা পাকা বাড়ি। ওপরে অবোধ্য তামিল ভাষায় লেখা আছে কিছু। নীচে ইংরেজিতে ‘ইউজ মি’।
ভেতরে এসে দেখি এক দক্ষিণী তরুণী হলদে সিল্কের শাড়ি আর গোলাপি স্টোল গায়ে বসে রয়েছে একটা চেয়ারে। মাথায় সাদা ফুলের গজরা। সামনে একটা কাঠের টেবিল। ওপরে টিনের বাক্স। তামিল আর ইংরেজি দুটো ভাষাতেই লেখা আছে বড় বাইরে করলে খরচ দশ টাকা, ছোটো বাইরে দু’টাকা। পাশাপাশি দুটো ইউরিনাল। একটায় ছবি পাগড়ি পরা গোঁফওলা একজন পুরুষের। পাশেরটায় শাড়ি পরা হাসিখুশি এক মহিলার।
মাঝারি সাইজের কমন চত্বর। দু’দিকে দুটো দরজা। ঠেললে খোলে, আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। টয়লেটে ঢুকতেই চমক। সরকারি প্রস্রাবাগার এমন হতে পারে সেটা ভাবিনি। মার্বেলের মতো টাইলের মেঝে। দাগ নেই কোথাও। ঘরের তিন দিকের দেয়াল ঝকঝকে সাদা। ভেন্টিলেটরের মতো একজস্ট ফ্যান ঘুরছে। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো গোটা দশেক বেসিন। ওপরে ফিট করা আয়না। সাবানদানিতে শোভা পাচ্ছে সাবান। ইউরিনাল থেকে বেসিন সব জায়গায় দেওয়া আছে দুধসাদা ন্যাপথলিন। সব কিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।
দু’টাকা দিতে গিয়ে বিপত্তি। আমার পার্সে পাঁচ টাকা তো দূরস্থান একটা দশ টাকা অবধি নেই। একটা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিতে মেয়েটি তামিলে কিছু বলল। মুখে বিড়ম্বনার একটা ভাব ফুটিয়ে জানালাম খুচরো নেই। মেয়েটি মনে হল যেন ভাবনায় পড়ল। আটানব্বই টাকা সে এখন কী করে ফেরত দেয়! অন্য কেউ হলে নির্ঘাত আমার গুষ্টির তুষ্টি করত। কিন্তু এই মেয়ে রাগ দেখাতে জানে না বোধ হয়। এদিকে আমাকে ফ্রি-তে ছেড়ে দিতে তার নীতিবোধে বাধছে কোথাও। একটু ইতস্তত করে দক্ষিণী তরুণীর নাম জিজ্ঞেস করলাম।
মেয়েটির চোখেমুখে কিশোরীসুলভ সারল্য, নাম বলল, রাধিকা পিল্লাই।
রাধিকাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম, একশো টাকা একদিনের জন্য তার কাছে জমা থাক। কাল সকালে কোয়েকার্স পার্কে এসে দু’টাকা খুচরো দিয়ে একশো টাকা ফেরত নিয়ে যাব। নিরুপায় রাধিকা কী ভাবল খানিক। তারপর নিমরাজি হল আমার কথায়।
হোটেলে ফিরে আসার পর কোয়েকার্স পার্কের ঘটনাটা সবিস্তারে বললাম দিদি আর রুনুদাকে। রাধিকার কাছে আমার একশো টাকা জমা রেখে আসার গল্প শুনে দুজনেই খুব হাসল। দিদি বলল, কাল সকালে তাহলে কী করবি? যাবি টাকাটা ফেরত নিতে?
–আলবাত যাব। একশো টাকা কি সস্তা নাকি?
রুনুদা মুচকি মুচকি হাসছে, মেয়েটা কি সুন্দরী নাকি? আমাদের ফেরার টিকিট কিন্তু তিনজনের। একস্ট্রা কাউকে নিয়ে যেতে হলে কোলে বসিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেটা মনে রেখো।
পরদিন সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট সেরেই চলে এসেছি কোয়েকার্স পার্কে। রাধিকা বসে আছে মাথায় গজরা ঝুলিয়ে। পরনে কালকের সেই হলদে শাড়ি আর গোলাপি স্টোল। দু’টাকার একটা কয়েন এগিয়ে দিলাম রাধিকার দিকে। হাসল রাধিকা, নিজের বটুয়া থেকে একশো টাকার একটা নোট বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিল। কয়েনটা ফেলে দিল টিনের বাক্সে।
টাকাটা পকেটে রেখে জিজ্ঞেস করলাম, এই সরকারি ইউরিনাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব কি তোমার ওপর?
রাধিকা বলল, সারাদিন নয়। প্রতিদিন ভোর পাঁচটা থেকে সকাল এগারোটা অবধি আমার ডিউটি।
আমি জিজ্ঞাসু, তাহলে তো রাত ফুরোবার আগেই উঠে পড়তে হয় তোমাকে?
রাধিকা ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলল, অন্ধকার ঘুমন্ত নৈঃশব্দ্যের পাহাড়ি পথে হেঁটে হেঁটে ডিউটিতে চলে আসে সে। ওয়াচম্যান তখন বসে বসেই ঘুমে অচৈতন্য। তাকে না জাগিয়েই দরজা ঠেলে টয়লেটে ঢুকে পড়ে রাধিকা। সমস্ত দেয়াল, মেঝে, আয়না, সাবান আর ফিনাইল দিয়ে ঝেড়েমুছে তকতকে করে রাখে। সব ক’টা বেসিনে লিকুইড সোপ আর ওডোনিল রাখে ঠিক করে। তারপর স্নানঘরে ঢুকে স্নান সেরে পরিষ্কার হয়ে সারাদিনের জন্য সে তৈরি।
–তোমার ভাইবোন নেই?
রাধিকা দু’-চার সেকেন্ড চুপ করে থাকল। হয়তো মনে মনে ভেবে নিল আমার মতো একজন অপরিচিত লোকের কাছে কথাটা বলা যায় কিনা। তারপর বলল, আমার এক দাদা আছে, তার নাম কার্তিক। সে-ই এই টয়লেটের দেখাশোনার দায়িত্ব পেয়েছিল। কিন্তু একটা অ্যাক্সিডেন্টে তার একটা পা হাঁটু থেকে কাটা যায়। অন্য পায়েও বড়ো জখম। ও এখন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। ফলে আমাকেই এই দায়িত্ব নিতে হয়েছে। আমাদের এক বোন আছে। ওর নাম পদ্মাক্ষী, কলেজে পড়ে।
–তোমার বাবা কী করেন?
মনে হল রাধিকা একটা শ্বাস বুঝি গোপন করল, আমার বাবা ছিল ড্রাইভার, সরকারি বাস চালাত। লেভেল-ক্রসিং না থাকা রেললাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনের সঙ্গে ধাক্বা লেগেছিল বাবার বাসের। হাসপাতালে নিতে নিতেই সব শেষ। আমার বয়স তখন দু’বছর। তখন আমরা চেন্নাইতে থাকতাম।
আনম্যানড লেভেল-ক্রসিং পার হতে গিয়ে কত অ্যাক্সিডেন্ট হয় কাগজে দেখি। একটুক্ষণের জন্য মনটা ভার হয়। এক সেকেন্ড পরেই নিস্পৃহমুখে পাতা উলটে অন্য খবরে চলে যাই। এই মুহূর্তে রেল আর বাসের সংঘর্ষে মৃত বাস ড্রাইভারের একজন মেয়ে আমার চোখের সামনে বসা। সেই কালান্তক সময়ে কী দুঃসহ ঝড় রাধিকাদের ওপর দিয়ে গিয়েছে কে জানে! জিজ্ঞেস করলাম, সরকার ফ্যামিলি পেনশনের ব্যবস্থা করেনি?
–হ্যাঁ করেছিল। দাদার বয়স তখন পাঁচের মতো। পদ্মাক্ষী সবে হয়েছে। ওই অল্প টাকায় আমাদের তিন ভাইবোন নিয়ে মা সংসার চালাতে পারছিল না। তবে ইউনিয়নের লোকেরা সে সময় হেল্প করেছিল। ওদের সাহায্যেই ছ’মাসের মধ্যে মা বাস চালাতে শিখে নিয়েছিল। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না এক বছরের মধ্যেই মা সিটি-বাস চালাবার চাকরি পেয়ে গেল। চেন্নাইয়ের হাতে গোনা মহিলা বাস ড্রাইভারদের মধ্যে একজন ছিল আমার মা।
অচেনা অদেখা এক মহিলার জীবনযুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াবার দুর্জয় সাহস আমাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল ভেতর থেকে। আন্তরিক স্বরে বললাম, তোমার মা-র মনের জোরের কথা শুনে খুব ভালো লাগল। ওঁকে আমার প্রণাম জানিও।
রাধিকা আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল। ঠোঁট টিপে বলল, সে উপায় নেই। আমার মা মারা গেছে এগারো বছর আগে।
আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, মানে?
রাধিকা বলল, বাবার মারা যাবার পর বারো বছর ধরে মা আমাদের তিন ভাইবোনকে বড়ো করল। তারপর ঘটল সেই ঘটনা। একদিন মা ডিউটি করে সন্ধেবেলা বাড়ি এল। সেদিন মায়ের চেহারাটা একটু যেন কেমন কেমন। সকাল থেকেই নাকি বুকে ব্যথা। কার্তিক গিয়ে দোকান থেকে গ্যাসের বড়ি কিনে নিয়ে এল। সে ওষুধ খেয়ে কিছু হল না। একটু পরে ব্যথা আরও বাড়ল। যন্ত্রণায় ছটফট করা শুরু করল মা। ডাক্তারকে খবর দিতে দিতেই সব শেষ।
রাধিকার কথায় কী যেন ছিল মনটা দ্রব হয়ে গেল। সেই ভয়ংকর সন্ধের প্রত্যেকটা দৃশ্য চোখের সামনে অভিনীত হতে দেখলাম যেন। এই বিরাট স্বার্থপর পৃথিবীতে তিন কপর্দকহীন নাবালক সন্তানের বেঁচে থাকা যে কতটা কঠিন সেটা অনুমান করাটা শক্ত নয়। আর্দ্র স্বরে বললাম, ইস্ তোমরা তো তখন অথই জলে পড়লে।
রাধিকা বলল, সে তো পড়লাম ঠিকই। চেন্নাই ছেড়ে আমরা চলে এলাম কোদাইতে। মামার ব্যাবসা আছে এখানে। টুরিস্টদের রেলের টিকিট, প্লেনের টিকিট, বাসের টিকিট কেটে দেয়। অনেক লোকের সঙ্গে খাতির আছে। এক পরিচিত অফিসারকে ধরে মামা কার্তিককে ঢুকিয়ে দিয়েছিল এই সরকারি ইউরিনালে। কিন্তু সেটাও আমাদের কপালে সইল না। একদিন ডিউটি করে কার্তিক বাড়ি ফিরছিল। একটা গাড়ি পেছন থেকে এসে ধাক্বা দেয়। খাদে পড়ে যায় কার্তিক। মারাত্মক চোট লাগে তার। একটা পা হাঁটু থেকে কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। ওর জায়গায় আমি ঢুকেছি কয়েক মাস আগে।
আমাদের কথার মধ্যেই টুকটাক লোকজন দেখি টয়লেটে আসছে যাচ্ছে। টিনের বাক্সে কয়েন ফেলে দিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকে। রাধিকা জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে আপনার জামাইবাবুর?
জানালাম, হার্টের সমস্যা ছিল। বেঙ্গালুরুর এক হসপিটালে অপারেশন করা হয়েছে। এখন ভালো আছে। ডাক্তার বলে দিয়েছেন সামনের বছর চেক-আপের জন্য আর একবার আসতে হবে।
রাধিকা স্মিতমুখে বলল, তাহলে তো ভালোই হল। সামনের বছর আপনারা সকলে বেঙ্গালুরু থেকে কোদাইতে চলে আসবেন। বারো বছর পর পর পালানি পাহাড়ে ফোটে করৌঞ্জি ফুল। সামনের বছর আবার সেই ফুল ফুটবে। সে এক অসাধারণ দৃশ্য।
আমি হেসে বললাম, কাল আমরা মুরুগানের মন্দির গিয়েছিলাম। সেখানেও তো প্রচুর করৌঞ্জি গাছ রয়েছে দেখলাম। তবে ফুল ফোটেনি সে গাছে।
রাধিকা বলল, বললাম যে ফুল ফুটবে সামনের বছর। আসলে করৌঞ্জি ফুল দেবতা মুরুগানের খুব প্রিয়। দেবতা মুরুগানের ছয় অধিষ্ঠানের একটা আমাদের এই পালানি পাহাড়ে। আপনারা মুরুগানকে চেনেন কার্তিক হিসেবে। দক্ষিণ ভারতে তিনি ইন্দিবর নামে পরিচিত। ইন্দিবর মানে হল পাহাড়ের অধীশ্বর।
আমি হাসলাম, আমাদের গাড়ির ড্রাইভারের মুখে শুনেছি করৌঞ্জি ফুল কোদাইয়ের সৌভাগ্যের প্রতীক।
রাধিকা ঘাড় নাড়ল, আমাদের ফ্যামিলিতে ব্যাপারটা উলটো। আমার বাবা যখন মারা যায় সেবার করৌঞ্জি ফুল ফুটেছিল পালানি পাহাড়ে। ঠিক বারো বছর পর আমার মা মারা যায়। পরের বছর আবার করৌঞ্জি ফুল ফুটবে। আমাদের আবার কী ক্ষতি হবে কে জানে!
রাধিকার কথায় ঝাঁকি খেয়েছি একটু। মনে মনে অঙ্ক কষে ফেললাম। হ্যাঁ ঠিকই তো। ওর বাবা মারা যাবার ঠিক বারো বছর পর ওর মা-র মৃত্যু হয়েছিল। তারপর এগারো বছর কেটে গেছে। সামনের বছর আবার করৌঞ্জি ফুল ফুটবে পালানি পাহাড়ে। তাহলে কি সামনের বছর কার্তিকের জন্য একটা বড়ো ফাঁড়া অপেক্ষা করে আছে? মুখে সেই উদ্বিগ্ন ভাবটা ফুটতে দিলাম না। ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললাম, ধুস এটা নেহাতই কাকতালীয় ব্যাপার। ওসব নিয়ে উলটোপালটা ভেবে দুশ্চিন্তা কোরো না।
–আপনি আমাদের পরিবারের লোক হলে টেনশনটা বুঝতেন। কী হাসিখুশি ছেলে ছিল কার্তিক। প্রচুর পরিশ্রম করতে পারত। দারুণ ফুটবল খেলত। সেই ছেলে এখন শুয়ে থাকে বিছানায়। কার্তিকের ট্রিটমেন্ট চালাতে গিয়ে মামার জমানো টাকা শেষ হয়ে যাচ্ছে জলের মতো। তাছাড়া… রাধিকা কথাটা বলবে কি বলবে না ভেবে শেষে বলেই ফেলল, তাছাড়া আমার বিয়েতেও তো অনেক টাকা লাগবে। মামা যে কী করে সবকিছু সামাল দেবে কে জানে!
আমি হাসলাম, কবে তোমার বিয়ে?
– সামনের বছর মাঝামাঝি হতে পারে। রাধিকা একটু লজ্জা পেল, তবে ডেট এখনও ঠিক হয়নি।
আমার কৌতূহল একটু বাড়ল, ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ, কী করে তোমার উড বি?
– ওর নাম মুরলিধর আইয়ার। তামিল ব্রাহ্মণ। কর্পোরেশন অফিসে চাকরি করে। ওর বাবা সরকারি চাকরি করত। কোদাইতে ওদের নিজেদের বাড়ি আছে।
–কনগ্র্যাচুলেশনস রাধিকা। আমি বললাম, কিন্তু একটা কথা তোমাকে না বলে পারছি না। তোমাদের মুরুগান কিন্তু বেশ রসিক দেবতা। তিনি রাধিকার জন্য খুঁজে খুজে ঠিক একজন মুরলিধর জোগাড় করে দিয়েছেন।
রাধিকার মুখে আবির ছিটিয়ে দিল কেউ। লজ্জা পেয়ে বলল, আমার বন্ধুরা তো এই বলেই আমার পেছনে লাগছে সারাক্ষণ।
আমি হাসছি। রাধিকা কেজো গলায় বলল, আপনার ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যান এই কাগজটায়। আপনার বাড়িতে বিয়ের কার্ড পোস্ট করে দেব।
–ঠিকানা আর ফোন নম্বর দুটোই লিখে দিয়ে যাচ্ছি। সামনের বছর যখন কোদাই আসব তখনই যদি তোমার বিয়ের তারিখটাও পড়ে যায় তাহলে কথা দিচ্ছি পুরো কবজি ডুবিয়ে ভোজ খেয়ে যাব!
রাধিকা বলল, আমাদের আমিষ চলে না। আপনার ভেজ থালিতে আপত্তি নেই তো?
আমি বললাম, একেবারেই আপত্তি নেই। সত্যি বলতে নিরামিষই আমি ভালো খাই। তাছাড়া সাউথ ইন্ডিয়ান ডিশ তো আমার ভীষণ পছন্দের।
রাধিকা হেসে ফেলল আমার কথায়।
রাধিকার বিয়ের কার্ড পাইনি। খুব যে প্রত্যাশা ছিল তা অবশ্য নয়। কোথাও বেড়াতে গিয়ে কত লোকের সঙ্গেই তো আলাপ হয়। ফোন নম্বরও বদলাবদলি হয়। কিন্তু ব্যস্ত নাগরিক জীবনে যত একটার পর একটা দিন চেপে বসে তত সেসব আপাতসখ্যের জোড় আলগা হয়ে যায়। ফোন আর করা হয়ে ওঠে না কাউকেই। এক্ষেত্রেও তাই হল। স্বস্থানে ফিরে আসার পর রাধিকার কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। ফের মনে পড়ল বেঙ্গালুরু থেকে কোদাইকানাল যাবার বাসের সিটে বসে। এখন কেমন আছে রাধিকা? বিয়ের পর চাকরিটা কি করছে এখনও? কোদাই গিয়ে ওর দেখা মিলবে তো? মনটা হঠাৎ উচাটন হল রাধিকার কথা ভেবে।
বেঙ্গালুরুতে রুণুদাকে নিয়ে চেক-আপে আসা হয়েছিল। ডক্টর আয়েঙ্গার পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়ে সার্টিফিকেট দিলেন সবকিছুই নর্মাল। রুনুদা এখন যাকে বলে ফাইটিং ফিট। সেদিন সন্ধেবেলা হোটেলের ঘরে বসেই ঠিক হল আমরা আবার কোদাইকানালেই যাব। দীর্ঘ এক যুগ পর আবার করৌঞ্জি ফুল ফুটবে কোদাই পাহাড়ের উপত্যকা জুড়ে। সেটা মিস করা যাবে না কিছুতেই।
কাল পৌঁছেছি কোদাইতে। আজ সকাল থেকে আকাশ মেঘে ঢাকা। সঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি। তার মধ্যেই আমরা বেরিয়েছি গতবার যে জায়গাগুলো দেখা হয়নি সেগুলো দেখতে। প্রথমে শোলা ফরেস্টে গিয়েছিলাম। এখানেই আছে পাম্বার ফল্স। সেখান থেকে এলাম বেরিজাম লেকে, যে হ্রদ থেকে পানীয় জল সরবরাহ করা হয় কোদাই শহরে। সারাদিন ধরে আকাশ গোমড়া থাকার পর বিকেলের দিকে আকাশ পরিষ্কার হল। আমাদের ড্রাইভার নিয়ে এল এদিকের বিখ্যাত লা সালেথ চার্চে।
ফিরে আসছিলাম যখন তখন বিকেল। একটা জায়গায় ঘ্যাস্স করে গাড়ি দাঁড় করাল ড্রাইভার। গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমাদের তিনজনের চোখ স্থির হয়ে গেল। পাহাড়ের চুড়োতে পাইন গাছগুলোর মাথায় উঁকি মারছে নীল আকাশ। বর্ষার ধূসর মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে সেই আকাশে। সূর্য উঁকি দিচ্ছে মেঘের ফাঁক দিয়ে। সোনালি রোদ এসে পড়েছে উপত্যকায়। সৃষ্টি হয়েছে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। মায়াবী নীলচে বেগুনি আলো বিছিয়ে আছে গোটা উপত্যকা জুড়ে।
আগে পিছে আরও অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। খাদের একেবারে ধারে হাঁটু গেড়ে বসে এসএলআর ক্যামেরা তাক করে আছে এক বিদেশিনি। ওদিকে একটা জটলা। এক গাইডকে ঘিরে রেখেছে কিছু মঙ্গোলয়েড মুখের পর্যটক। সেই দক্ষিণ ভারতীয় গাইড টিপিকাল সাউথ ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্টের ইংরেজিতে বলছে, দীর্ঘ এক যুগের প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। দেবতা মুরুগান তাঁর করুণা বর্ষণ করেছেন পালানি পাহাড়ের উপত্যকায়।
প্রকৃতি বোধ হয় সেই আয়না যার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের অবয়ব ধরা পড়ে। দিদি কেঁদে ফেলল এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে। প্র্যাক্টিক্যাল ম্যান রুণুদা প্রকৃতির রূপ দেখে বিহ্বল। আমাদের ড্রাইভার, যে কিনা স্থানীয় মানুষ, সে পর্যন্ত হাঁ।
রাশি রাশি করৌঞ্জি ফুলের দল যেন নীলচে বেগুনি রং দিয়ে হোলি খেলছে এখানে। এমন অপার্থিব দৃশ্য দেখার জন্য একশো মাইল হেঁটে আসা যায়। বড়ো একটা শ্বাস ফেললাম। এই অপার্থিব সৌন্দর্যের এক আনাও যদি ক্যামেরাবন্দি করা যেত!
এবার আমরা কোয়েকার্স পার্কের দিকে এগোচ্ছি। সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে সোজা হোটেলে ফিরব। পার্ক লাগোয়া সেই সরকারি টয়লেটে রাধিকার ডিউটি ছিল ভোররাত থেকে দুপুর পর্যন্ত। এই পড়ন্ত বিকেলে কি ওর দেখা পাব? তাছাড়া বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দিয়েছে কিনা সেটাও তো জানা নেই।
ড্রাইভার গাড়ি পার্ক করল। দিদি আর রুণুদা টিকিট কেটে কোয়েকার্স পার্কের ভেতরে ঢুকল। আমি গেটের উলটোদিকের সরকারি টয়লেটের দিকে তাকালাম। বছরখানেক বাদে এলাম কিন্তু একদম একই আছে সেই ছোট্ট পাকা বাড়িটা।
রাধিকা নয়, নীল সিল্কের শাড়ি পরা এক কিশোরী বসে রয়েছে চেয়ারে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। ভাবলেশহীন মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, টু রুপিজ ফর ইউরিনাল। টেন ফর টয়লেট।
বিনা ভূমিকায় সরাসরি প্রশ্ন করলাম, রাধিকা পিল্লাই নামে একজন সকালের শিফটে ডিউটি করত এখানে। তার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। ওর ডিউটি কি সকালবেলাতেই আছে এখনও?
মেয়েটি ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখল একটুক্ষণ। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, হাও ডু ইউ নো রাধিকা?
রাধিকার সঙ্গে আমার এই সরকারি ইউরিনালে কীভাবে আলাপ হয়েছিল সেটা ভেঙে বললাম। নীল শাড়ি কিশোরী বলল, আমার নাম পদ্মাক্ষী। আমি রাধিকার ছোটো বোন। মর্নিং কলেজ করে এখানে চলে আসি। দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত আমিই এখানে ডিউটি করি।
প্রশ্নের বাণ ছুড়লাম পদ্মাক্ষীর দিকে, রাধিকা বিয়ের পর কাজ ছেড়ে দিয়েছে? নাকি সকালের শিফটে আছে এখনও? কার্তিক কেমন আছে এখন?
লক্ষ্য করলাম পদ্মাক্ষীর মুখে কেমন একটা ভাঙচুর হচ্ছে। চোখ ভিজে উঠছে জলে। আঙুল ইশারা করে পাশের দেয়ালে দিক নির্দেশ করল পদ্মাক্ষী।
সাদা ফুলের মালা দেওয়া রাধিকার একটা ফটো টাঙানো রয়েছে দেয়ালে। চোখ যে দৃশ্য দেখল তার ছবি পাঠাল মস্তিষ্কে। কিন্তু মস্তিষ্কের ধূসর অংশ সেই সিগনালের মানে করতে পারল না। বিমূঢ় গলায় বললাম, এটা কেন টাঙিয়ে রেখেছ এখানে?
পদ্মাক্ষী নিজেকে সংযত করল চোয়াল শক্ত করে। তারপর যা শোনাল তার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না।
কয়েক মাস আগে এক ফরেনার কোয়েকার্স পার্কে ফটো তুলছিল। চারজন মাতাল ক্রমাগত বিরক্ত করে যাচ্ছিল সেই বিদেশিনিকে। মহিলা তার প্রতিবাদ করায় দু-তরফে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। ঝামেলা বাড়ে একটু একটু করে। এক সময় মদ্যপের দল সেই মহিলাকে টেনে নিয়ে যায় পার্কের ভেতর। পার্কে যে দু-একজন ছিল তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল ঘটনাটা। শুধু একজন ছাড়া। শান্তশিষ্ট মেয়ে বলে যাকে সকলে চিনে এসেছে এতদিন, সেই রাধিকা দৌড়ে গিয়েছিল পার্কের ভিতর। ততক্ষণে সেই বিদেশিনিকে বিবস্ত্র করে ফেলেছে লোকগুলো।
আমি রুদ্ধশ্বাসে বললাম, তারপর?
–একটা ইট কুড়িয়ে নিয়ে রাধিকা ছুড়েছিল ওদের দিকে। একজনের মাথায় গিয়ে লাগে সেটা। ইটটা কুড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে আসে লোকটা। কাছে এসে ঠান্ডা মাথায় থেঁতলে দেয় রাধিকার মাথা। কানের নীচে আঘাত লাগায় সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারায় রাধিকা। লোকগুলো পার্ক ছেড়ে বেরিয়ে যায়। কেউ তাদের আটকাবার সাহস দেখায়নি। রাধিকাকে নিয়ে যাওয়া হয় কোদাই হসপিটালে। পরদিন বিকেলেই তার লড়াই শেষ হয়ে যায়।
মাথাটা শূন্য হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। পদ্মাক্ষীর মুখোমুখি ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। নিভে যাওয়া গলায় বললাম, ওই ছেলেগুলির কী হল? অ্যারেস্ট হয়নি ওরা?
–পুলিশ ধরেছে চারজনকে। সেই মহিলা ফ্রান্সের হিউম্যান রাইটস সংক্রান্ত একটা এনজিও-র সঙ্গে যুক্ত। পুলিশ থেকে টিআই প্যারেডের ব্যবস্থা করেছিল। সেখানে সেই মহিলা আইডেনটিফাই করেছে প্রত্যেককে। স্থানীয় আদালতে সাক্ষ্যও দিয়েছে। সেই মহিলা বলেছে এর শেষ দেখে ছাড়বে। লোয়ার কোর্টে অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে গেলে হাইকোর্টে যাবে।
ফটোটার দিকে বিহ্বল হয়ে তাকালাম। চব্বিশ বছর আগে রাধিকা হারিয়েছিল তার বাবাকে। বারো বছর আগে মারা যায় তার মা। এ বছর আর সকলের মতো রাধিকা নিজেও কার্তিকের জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। কিন্তু নাটকের তৃতীয় অঙ্কে কী ঘটতে চলেছে তা কি আঁচ করেছিল ওদের পরিবারের কেউ? তার নিজের জীবন যে এভাবে শেষ হয়ে যাবে সেটা কি ঘুণাক্ষরেও টের পেয়েছিল রাধিকা? পারেনি। আসলে এই পুতুলনাচের সব সুতো হয়তো দেবতা মুরুগানের হাতে। যেমন টানেন তেমন নাচে মর্ত্যলোকের পুতুলের দল। নইলে সেদিন শান্তশিষ্ট রাধিকা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেন ছুটে গিয়েছিল পার্কের ভেতর? তাও আবার এমন একজনকে ধর্ষকদের হাত থেকে বাঁচাতে, যাকে সে জন্মে দেখেনি!
ধীর পায়ে বাইরে এসেছি। অন্যমনস্ক হয়ে কোয়েকার্স পার্কে ঢুকেছি। খানিকটা হাঁটার পর এক জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। এই ভিউপয়েন্ট থেকে উপত্যকার অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। এখন যতদূর দৃষ্টি যায় সামনে নীল মেশানো বেগুনি রঙের এক অপরূপ প্রপাত। মেঘের ফাঁক দিয়ে গুনে গুনে ঠিক তিনটে আলোর রেখা এসে পড়েছে পাহাড়ি উপত্যকায়। ভারি অদ্ভুত লাগছে ভ্যালিটাকে। প্রগাঢ় আঁধার আর হিরণ্যবর্ণ রোদের জাফরিকাটা আলোছায়াতে গোটা পাহাড়ি উপত্যকাটাকে মনে হচ্ছে যেন নাটকের মঞ্চ।
নাটকের মঞ্চই তো। তবে এই নাটকের নিয়মটা একটু অন্যরকম। এখানে একবার যবনিকা পড়লে আবার পর্দা ওঠে ঠিক একযুগ পরে।