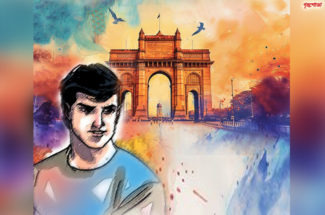আমরা তখন ক্লাস ইলেভেনে পড়ি। আমাদের বাংলা বই-এ পাঠ্য ছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরণ্যক উপন্যাসের অংশবিশেষ। আমার এক বন্ধু আমার সঙ্গেই পড়ত, একই ক্লাসে। তার আবার লাইন বাই লাইন মুখস্থ ছিল। আরণ্যক থেকে কিছু জিজ্ঞেস করলেই পাতার নম্বর আর পুরো অনুচ্ছেদ মুখস্থ বলে দিত। আমি বুঝতে পারতাম না, ওই দোবরু পান্না বীরবর্দি আর জংলী দেবতা টাঁরবাড়ো-র মধ্যে কি এমন লুকিয়ে ছিল যে এত আগ্রহ! টীকা লেখার সময়ে টের পেতাম যে, এ এক স্বযংসম্পূর্ণ ঐতিহ্য যার বহির্জগতে কোনও সামাজিক মর্যাদা নেই। বিভূতিভূষণের হাত ধরে তা যেন আমাদের হাতে এক আয়না ধরিয়ে দেয়। যত বয়েস বেড়েছে, বুঝেছি কী রহস্য নিহিত ছিল ওই শালবনে।
সবে তখন কোভিডের প্রথম ঢেউ শেষ হয়েছে। নিজের বাড়ি যেন গিলে খাচ্ছে সবাইকে। এক একটা দিন নিয়ে এক একটা একাঙ্ক নাটক হয়ে যাবে। আইসোলেশন আর কোয়ারেন্টিনে থাকতে থাকতে দম বন্ধ হয়ে উঠেছে। মানসিক স্থৈর্য ফেরাতে কোথাও একটা যেতে হবে। হোটেল-রিসর্ট আবার খুলেছে সবেই। কিন্তু ট্রেন চালু হয়নি তখনও। গাড়িটা কাজ দিল। চললাম Jhargram। গাড়িতে করে যাত্রা সেখানে দু-দিন-এক-রাতের জন্য। কলকাতা থেকে একশো সত্তর কিলোমিটার পথ। ভাগ্যক্রমে রাতারাতি বুকিং পাওয়া গিয়েছিল একটি নতুন রিসর্টে, একদম জঙ্গলের গায়ে, শুনেছি রিসর্টের মধ্যে তাঁবু-ও আছে। ঘরের থেকে ভাড়া একটু বেশি।
সক্কাল বেলায় দুটি পরিবার, ছয়জন, বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তা খুবই সুন্দর। শুধু খড়গপুরের কাছের অংশের রাস্তা সত্যিই মালভূমির মতো। তারপর সোজা লোধাশুলি। সেখান থেকে আর ফ্লাইওভারে না উঠে, সেটিকে ডানদিকে রেখে বাঁদিকের গাঁয়ে রাস্তা ধরে দ্বিতীয় মোড় থেকে ব্রিজের নীচ দিয়ে ডানদিকে বাঁক নিলাম। এবার গন্তব্য ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ির আগে রিসর্ট।
রাস্তার দু-পাশে শুধু দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। তারপর আস্তে আস্তে যে, টাঁরবাড়ো-র রাজ্যে ঢুকছি মালুম হতে লাগল চারপাশের শালবন দেখে। বিশাল বিশাল শালগাছের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ফুঁড়ে চলে গিয়েছে রাস্তা। যেন ঘন সবুজ চুলের মধ্যে একফালি কালো সিঁথি। মনে হতে লাগল, সেই গানের লাইন এই পথ যদি না শেষ হয়…!
রিসর্টে পৌঁছে জানা গেল আমাদের তখনও ঘর পাওয়ার সময় হয়নি, কারণ আমরা একটু বেশি আগে পৌঁছে গিয়েছি। তাই রিসেপশনে লাগেজ রেখে ব্রেকফাস্ট সেরে ঘুরতে বেরোলাম আশেপাশে। প্রথমেই গন্তব্য কাছের, ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি। হিসেবে আদর্শ এই Jhargram জায়গাটা৷
ছায়া ঘনাইছে বনে বনে…। প্রকৃতি-ই যেন মহুয়া, এমন নেশা ধরানো। দু-পাশের জঙ্গলে রাস্তার মাঝখানে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে এক জায়গায় থামতেই হল। বিশাল বিশাল শালের বন, লাল মাটি, উই-এর ঢিবি। তারা যেন এই বনাঞ্চলে পিকনিক করতে এসেছে, সংখ্যায় এতই বেশি। দু-পা অন্তর উই-এর ঢিবি। অনেকগুলো বেশ বড়ো। আবার তাদের মধ্যে বেশ কিছু পরিত্যক্ত। শঙ্কা হল, তাদের পেট থেকে না বিশাল কোনও বিষধর সাপ বেরিয়ে আসে! উই-এর বাসা শুনেছি সাপেদের দারুণ ভালো লাগার আস্তানা। কিন্তু সে রকম কিছু ঘটল না। আমরা মন দিয়ে ছবি তুলতে লাগলাম। ছবির প্রাণ হল গিয়ে আলো। অত সুন্দর আলো সত্যি-ই আমাদের প্রকৃতির বুকে অনেকটাই সুন্দর করে তুলল, ক্যামেরার চোখে।
মানুষের চোখ মিথ্যে বলে, ক্যামেরা মিথ্যে বলে না। কিন্তু ওই আলোছায়া সেদিন আমাদের যাত্রাপথে যে-মায়াবী মিথ তৈরি করে দিল, সেখানে আর কিছু গভীরে গেলেই দবরু পান্না বীরবর্দি-র কাছে পৌঁছে গেলে আশ্চর্য হব না। এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। বন্ধুর উৎসাহে প্রথম চেষ্টা করা হল ব্লগিং-এর, যা আজকাল ট্রেন্ডিং। Travelogue বা ভ্রমণবৃত্তান্ত আউটডেটেড নাকি। কিন্তু আমার খুব ভরসা লেখাতেই। অন্ধের মতো বিশ্বাস করি যে-কোনও লিখিত রূপ-কে। নতুন যা-ই আসুক না কেন। যে-কোনও লিখিত রূপ এক চিরকালীন দলিল হিসেবে মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে অমর ছাপ রেখে চলে যায় বলে আমার বিশ্বাস। সঙ্গে শব্দসজ্জা এমন এক দৃশ্যকল্প তৈরি করে যে, আমরা তাতেই একাত্ম হয়ে যাই।
আমি লেখার রসদ চোখ দিয়ে গিলতে গিলতে মাথায় ছেপে নিচ্ছিলাম। তারপর পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছোলাম ঝাড়গ্রাম রাজবাড়িতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিকৃত এই রাজকীয় সম্পত্তি আমাদের মতো অতি সাধারণ মানুষ-ও ভোগ করতে পারেন। ফোন ও অনলাইনে বুক করা যায়। ভাড়া রিসর্টের থেকে কম। হেরিটেজ হোটেল হিসেবে উন্নীত হওয়ার দরুন মূল ফটকেই আটকে যেতে হল। আমদের থাকার বুকিং থাকলে তবেই অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার নতুবা ওই গেট থেকেই বিদায়। আমরা এ বারের মতো ভিতরে প্রবেশ করতে পারলাম না। ইচ্ছে রইল, এই রাজবাড়ি ঘিরে যা ইতিহাস আছে তা আমাদের ওই প্রাসাদে প্রবেশের ইচ্ছাপূরণের সঙ্গে সঙ্গে একসাথে মাননীয় পাঠককুলের কাছে নিবেদন করব। না হলে ব্যাপারটা খুব খাপছাড়া হয়ে যাবে।

দরদর করে ঘামছি সবাই। ভরা নভেম্বরেও। লাঞ্চ টাইম ছিল দুপুর একটা। সেরকমই বলা ছিল। কিন্তু এ কোন অরণ্য যা আমাদের নেশাগ্রস্তের মতো ধাবিত করছে তাতে সমাহিত হতে! আমরা কেউ টায়ার্ড হচ্ছি না। এমনকী আমাদের সঙ্গে থাকা দুই নেটিজেন বলছে না, এসব কী বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ! চলো আমাদের কী খিদে পেয়েছে বা ওহ মাই গড, হোয়াট আ টেরিবল প্লেস! দেয়ার ইজ নো ডেটা নেট অল অ্যারাউন্ড। দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনও অভিযোগ নেই। শুধু ঠান্ডা জল চাইছে মাঝে মাঝে। সে ব্যবস্থা আমি করেই রেখেছিলাম, চিলড বোতলে পানীয় জল কিনে তোয়ালে দিয়ে মুড়ে খবরের কাগজ দিয়ে ডিকি-তে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম। কাজে লেগে গেল।
যাই হোক, রাজবাড়ি থেকে এবার আমরা যাব কনকদুর্গার মন্দিরে। কী যে অসাধারণ রাস্তা আবার! মাঝে মাঝে ধানখেত, আবার মাঝে মাঝে বনানী। মূল রাস্তা থেকে বাঁদিকে আরও পাঁচ কিলোমিটার যেতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ধানখেতের গায়ে ডানদিকে একটি তোরণ। সেখান দিয়ে গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করে খানিকটা যেতেই পার্কিং। মন্দিরে পৌঁছোতে হলে শপাঁচেক মিটার পদব্রজে যেতে হবে। পাকা রাস্তা, ঘন বনের মধ্যে দিয়ে রাস্তার দুধারে পুরোটাই জাল দিয়ে ঢাকা। বন্য প্রাণীদের আনাগোনা আছে নাকি, তাই।
আর এই জঙ্গল শালবনের মতো নয়। আমি জীবনে লতাগুল্মের এত দুর্ভেদ্য জঙ্গল কাছ থেকে দেখিনি। সব থেকে বড়ো কথা, রাস্তার দু’ধারে যত রকমের গাছ আছে, ঠিক বোটানিক্যাল গার্ডেনের মতো প্রতিটির গায়ে নাম লেখা। তেলাকুচো গাছ ভর্তি। ভাবলাম নিশ্চয়ই অনেক টিয়া পাখি আসে সেই লোভে। কিন্তু পাখি খুব একটা দেখলাম না, কোনও রকমেরই, ওই রাস্তায় ধানখেতের মাঝে চলে যাওয়া হাই-টেনশন বিদ্যুতের তারে সার দিয়ে বসে থাকা ফিঙে পাখি ছাড়া। সে যেন সংগীতের স্টাফ নোটেশন-এর লাইন। যাই হোক বোর্ড দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখে পড়ল তিনটি দাঁতাল হাতি। আশেপাশে কেউ নেই। বুক শুকিয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড। তারপর বুঝলাম ওগুলো নকল। কিন্তু এমন অবিকল তৈরি করে এমন স্বাভাবিক ভাবে তাদের বসানো হয়েছে যে, দেখে বোঝার উপায় নেই।
গুল্ম এখানে এত মোটা, পোক্ত ও ঘন যে, চলাই কঠিন হয়ে পড়বে যদি কেউ চেষ্টা করে এই জঙ্গল ভেঙে এগোনোর। প্রথম চাক্ষুষ করলাম, আসল দুর্ভেদ্য জঙ্গল বলতে কী বোঝায়। শালের জঙ্গল বেশ ঘন, রোদ্দুর প্রায় ঢোকে না বললেই চলে। কিন্তু তা দুর্ভেদ্য নয়। কিন্তু কনক অরণ্য আক্ষরিক অর্থেই দুর্ভেদ্য। সব লতা-গুল্ম-বৃক্ষের মধ্যে খুব প্যাঁচালো আর অজগরের মতো মোটা একটি গুল্ম অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই তার নাম পাচ্ছিলাম না। অবশেষে পেলাম রক্তপিতা।
শব্দের ধাঁধা নিয়ে মনের মধ্যে খেলা শুরু হল। রক্তপিতা কী এর অর্থ? ব্যাসবাক্যে ভাঙলে অনেক কিছু দাঁড়ায়। এক, রক্ত এবং পিতা (ঠিক মনে ধরল না)। দুই, রক্ত রূপ পিতা (কিন্তু লালের কোনও চিহ্ন নেই)। তিন, তাহলে কি রক্ত পিতা যাহার বা সেরকম কিছু, নাকি বাংলা-হিন্দি মিশিয়ে রক্ত পান করেন যিনি (এটা আমার কাছে সব থেকে গ্রহণযোগ্য নামকরণের সার্থকতা বলে মনে হয়েছে)!
এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এসে পড়লাম একটা বিশাল উঠোনের মতো প্রায় গোলাকৃতি ফাঁকা জায়গায়। ডানদিকে আধুনিক মন্দির। ঠিক মাঝখানে একটি বিশাল অশ্বত্থ গাছ। গোড়াটা চাতাল করে বাঁধানো যাতে মানুষ শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে পারে। ঠিক প্রবেশদ্বারের ডানহাতে কোনাকুনি একটি পোড়ো মন্দির জরাজীর্ণ। তার পাশে সন্ন্যাসীদের থাকার ব্যবস্থা। আর পোড়ো মন্দিরের পাশ দিয়ে নেমে গিয়েছে সিঁড়ি।
আমার মনে ভক্তি-শ্রদ্ধা একটু কম, কিন্তু কারুবাসনা চিরজাগ্রত। নতুন নয় ভাঙা মন্দিরটা আমাকে টানল। অনবদ্য সে মন্দির। মন্দিরের চড়ো থেকে ভিত পর্যন্ত আপাদমস্তক ইঞ্চি ছয়েক চওড়া ফাটল। এই ফাটল যেন নিখুঁত ভাবে গোটা মন্দিরটাকে কেক-এর মতো দু’টো আলাদা টুকরো করে দিয়েছে। ফাটলের দাগ এমনই নিখুঁত যে, দরজার পাল্লাদুটোও যেন দু-ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। হাসি পেল দেখে যে, এমতাবস্থায় সেখানে দরজার দুটো প্রায় কব্জাবিহীন পাল্লা পেল্লায় একটা তালা দিয়ে জোড়াতালি দেওয়ার প্রচেষ্টাকে। প্রশ্ন হল, এমন ফাটল হল কী করে। জানা গেল ভূমিকম্প নয়, বাজ পড়ে। এই আদিমন্দির নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলেই নবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা। সত্যি বলতে নতুন মন্দির আমাকে আর টানলই না!
সাপ-হাতি-ভাল্লুক ইত্যাদি বন্য জন্তু চাক্ষুষ না হলেও এখানে ঢুকেই হঠাৎ যাঁদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে, তাঁরা হলেন কালোমুখো হনুমান। বাঁদর নয়। পুরো জায়গাটা জুড়ে তাঁদের আধিপত্য। আমি যখন পুরোনো সেই শ্যাওলা পড়া মন্দিরের স্থাপত্যকীর্তিকে ক্যামেরায় ফ্রেমবন্দি করার চেষ্টা করছি, অশ্বত্থ গাছের নীচ থেকে একটি সরু গলায় চিৎকার। দেখলাম এক ভদ্রমহিলা স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছেন, আর সামনে একটি গোদা হনুমান হাতের দানাদারটিকে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। তার মুখের অভিব্যক্তি ভাবলেশহীন। আর মহিলার মুখ, রক্তশূন্য। এগিয়ে গেলাম নির্ভয়ে জানলাম, মহিলা মন্দিরে পুজো দিয়ে অশ্বত্থতলে নিজের সারাদিনের উপোস ভেঙে ওই বাক্স থেকে মিষ্টি খেয়ে জল খেয়ে আবার ওই বাক্স নিজের কাঁধের চেনটানা ঝোলা ব্যাগে রেখে বিশ্রামে রত ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ কিঞ্চিৎ ব্যাগের দিকের কাঁধে টান পড়ায় ফিরে দেখেন, অবাক কাণ্ড। ব্যাগের চেন খোলা। মিষ্টির বাক্স যথাস্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু একটি খোয়া গিয়েছে এবং তা তার পাশে বসা হনুমানটির হাতে। সবটা শুনে বুঝলাম বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে কেন তারা আমাদের থেকে কম নন, রাম কেনই বা তাদের নিজের সহযোদ্ধা করেছিলেন এবং কেনই বা ওদেরকে আমাদের আদি পূর্বপুরুষ বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে!
আমার বন্ধু আর তার মেয়ে ততক্ষণে উধাও। ফোন করে জানা গেল ওরা ভাঙা মন্দিরের পাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে কোথাও একটা চলে গিয়েছে। আমিও ধাবিত হলাম সেই পথে। পুরো রাস্তা বাঁধানো ও নিম্নমুখী। সোনার কেল্লার ভাষায় বললে, পুরো রাস্তাই মাঙ্কি ইনফেস্টেড। পাঁচ মিনিট হন্টনের পরে উপনীত হলাম চরম বিস্ময়ে সম্মুখে একটি ভাঙা বাঁধানো ঘাট পেরিয়ে নদীগর্ভ। শীতে হাঁটুজল, যেখানে যেখানে গভীর, ডান আর বাঁ দিকে, সেখানে দুপুরে স্নান করছেন একদিকে স্থানীয় পুরুষ আর অন্যদিকে নারীরা। প্রায় একশো মিটার দূরে দুদিকেই।
নদীগর্ভে ছোটো বড়ো পাথর। ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলা বিপজ্জনক, কারণ স্নানরতা মহিলাদের অনেকেই বস্ত্রহীনা। কী থেকে কী হয়। তাই ক্যামেরার সব খাপ গুটিয়ে রাখতে হল। কিন্তু এমন সুন্দর জায়গায় ছবি না তুলে কি থাকা যায়! আমাদের সহায় হলেন আমাদের স্ত্রী-রা। ওনারা আসতে আর লেন্সের লাজ লজ্জা থাকল না, না থাকল ভয়। ফ্রেমে বন্দি হল খুব সূক্ষ্মও কিন্তু বিশদে। লেন্সের খিদে মেটানোর পরে চোখের-টা মেটাতে হবে। আর পেটের-টা সম্পর্কে তখনও বেলা আড়াইটের সময়ে কারও কোনও হুঁশ নেই। সব খিদে মিটে যাচ্ছে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে। অপূর্ব সেই দৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অনুভত হতে লাগল আমিই যেন বিভতিভষণ… বই-এর পাতা ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছি সেই বিরাট অভিজ্ঞতার মাঝে।
– ক্রমশ…
ছবি সৌজন্য: অরিন্দম তিওয়ারী