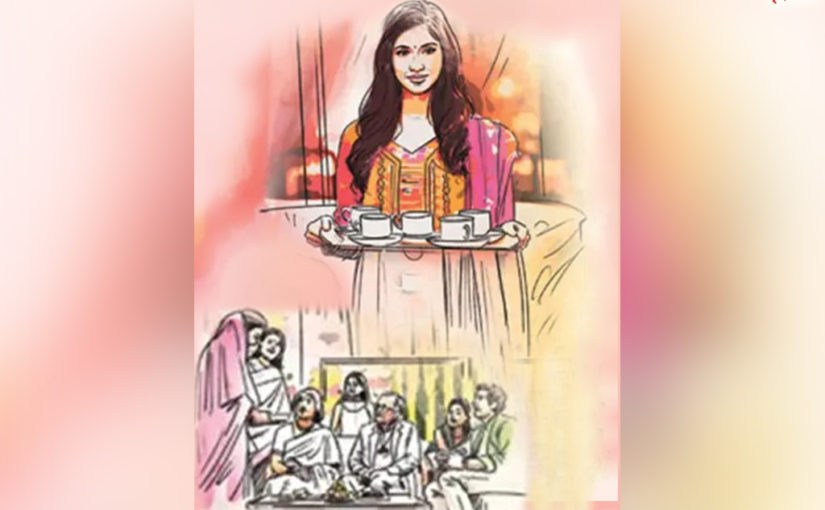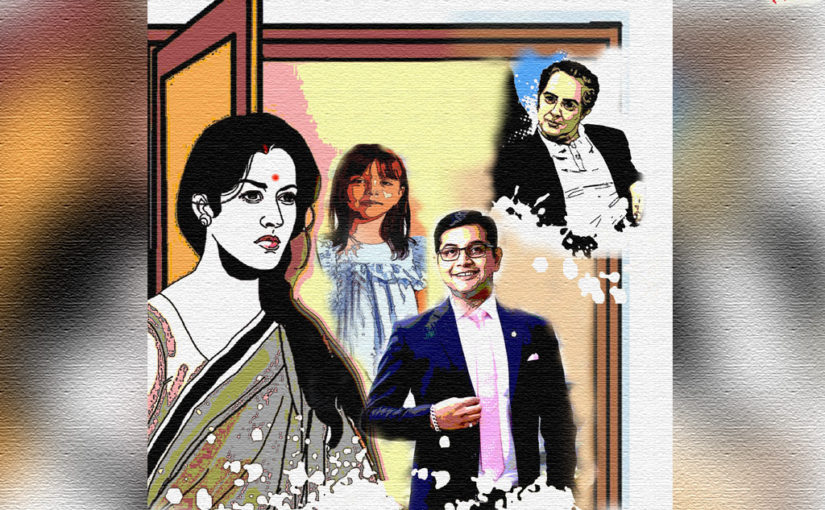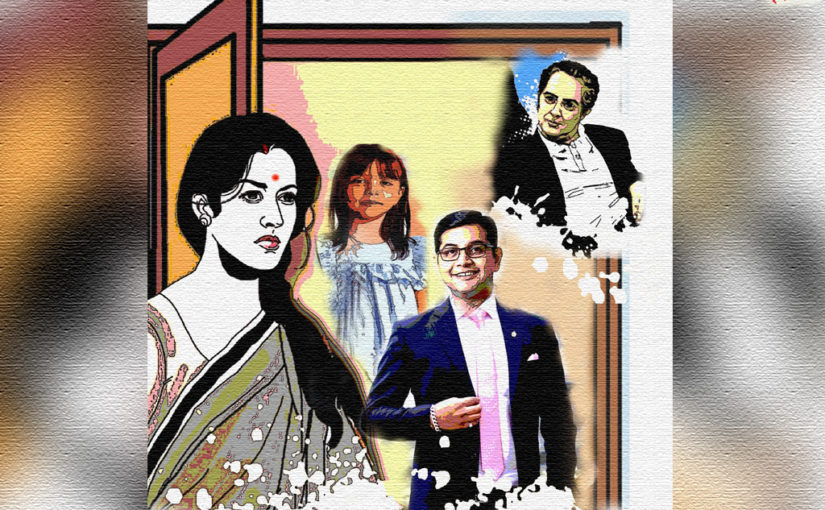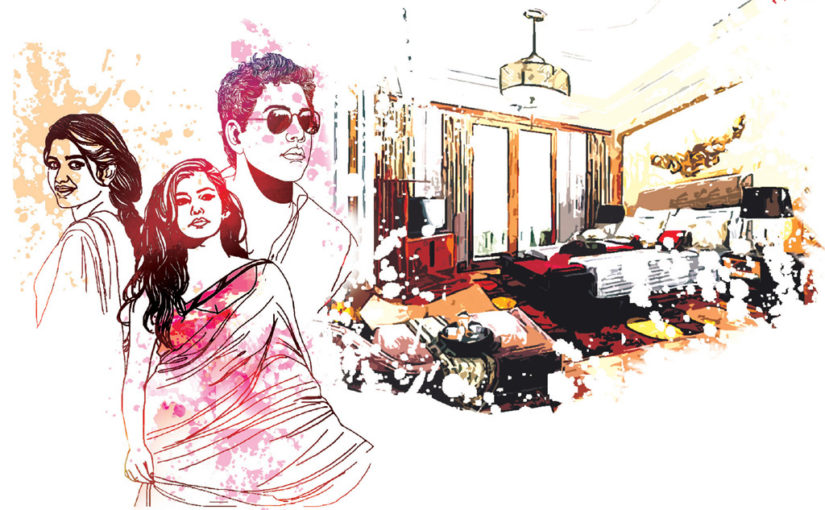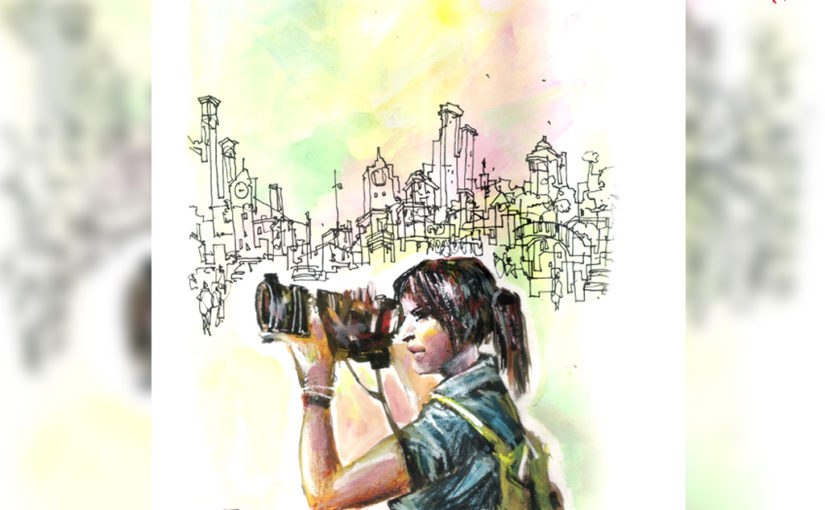হোয়্যার ইজ দ্য রিভার?
সকালে উঠেই সিঁড়ি বেয়ে সোজা নীচে। সে রিসেপশনে হামলে পড়ল। কেতাদুরস্ত (যেমন হয়) রিসেপশনিস্ট যুবকটিকে সামান্য সুপ্রভাত জানানোর সুযোগটাও দিল না। তার হাঁসফাঁসে চেহারাটা দেখে ছেলেটি নিজেকে সামলে নিল, হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল– দেয়ার ইউ হ্যাভ আ ব্যাক ডোর, ওপ্ন ইট, অ্যান্ড দেয়ার ইউ গো। বাট ইট্স অফুলি কোল্ড আউটসাইড, মর্নিং ইন জার্মানি ইজ ভেরি ভেরি চিলি। হোয়্যার ইজ ইওর ওভারকোট ম্যাম? ইট্স আ মাস্ট বিফোর ইউ থিংক অফ গোইং আউট।
রিমি এক মুহূর্ত ভাবল। নদী তার জন্য অপেক্ষা করবে না? সামান্য একটা শীতের পোশাক পরে বেরোতে? এই নদী তো আজন্ম তার, হ্যাঁ, তারই জন্য সে অপেক্ষা করেছে। যেমন সুদূর কলকাতায় তার জন্য অপেক্ষা করছে অভি।
সে সিঁড়ির রাস্তা ধরছিল। রিসেপশনিস্ট ছেলেটি তাকে আগের মতোই মধুর গলায় বলল– হ্যাভ আ লুক অ্যাট ইওর লেফট, দেয়ার ইজ আ লিফট।
রিমি লিফটে উঠল। উঠেই মনে হল, দয়ালু ছেলেটিকে সে একবারও ধন্যবাদ জানায়নি। লিফটের দরজা বন্ধ হওয়ার মুহূর্তে সে ফাঁক দিয়ে চেঁচিয়ে বলল– ডাঙ্কে, ডাঙ্কে শ্যুন।
জার্মানিতে আসার পর সে হাতে গোনা যে ক’টি জার্মান শব্দ শিখেছে তার মধ্যে এই একটা– ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।
ওভারকোটটা পরে সে যখন রিসেপশন ডেস্কের পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরোল, মুখে এসে ঝাপটা মারল তীক্ষ্ম তিরের মতো ঠান্ডা হাওয়া। কিন্তু রিমি তা আগ্রাহ্য করল। সামনে দিয়েই চলে গেছে একটা সোজা চকচকে রাস্তা, আর তার ওপারে… রিমি স্বপ্নেও ভাবেনি তার সঙ্গে রাইন-এর কোনওদিন দেখা হবে! কিন্তু না, দেখা তো হল! সত্যি! সে রাস্তাটা দৌড়ে পার হল। এরপর তার সামনে সেই নদী। রিমি প্রাণ ভরে তাকে দ্যাখে। ওভারকোটের পকেট থেকে ক্যামেরা বার করে। ছবির পর ছবি, তারও পর ছবি।
সে রাইন-এর ধার ধরে ধরে হাঁটতে শুরু করল। বিশ্বাস হচ্ছে না। পটাপট ছবি তুলছে। ছবি তুলতে গেলে দস্তানা পরলে একটু অসুবিধে হয়। কিন্তু ঠান্ডাটা বড্ড বেশি। সে ছবি তোলায় ক্ষান্ত দিয়ে ওভারকোটের পকেটে ক্যামেরাটা পুরে ফেলে দস্তানা হাতড়ায়। সর্বনাশ, সে দস্তানা না নিয়েই বেরিয়ে পড়েছে! এবার কী হবে!
এই ঠান্ডায়!
রিমি হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা চলে এসেছে। নদীর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার উচ্ছ্বাসে আর ছবি তোলার উৎসাহে এতক্ষণ দস্তানার অভাবটা মালুম পড়েনি। এখন পড়ছে। ওভারকোটের পকেটে দু’হাত ঢুকিয়ে সে ফেরার পথ ধরে। কিন্তু এতক্ষণ সে হেঁটেছে হাওয়ার দিক বরাবর। এবার হাঁটতে হচ্ছে হাওয়ার উলটোদিকে। আপাতত তার নাক বলে কিছু নেই, জমে পাথর হয়ে গেছে। একটা জায়গায় নদীর ধারে ছোট্ট একটা খাঁড়িতে কিছু হাঁস খেলা করছে, ওদের শীত লাগছে না? রিমি পকেট থেকে ক্যামেরা-সহ হাত বার করল, সঙ্গে সঙ্গে তার আঙুলগুলো যেন ঠান্ডায় বেঁকে গেল। সে দ্রুত হাত আর ক্যামেরা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। যথেষ্ট হয়েছে, আর হাত বার করা যাবে না, শুধু চোখ দিয়ে প্রাণ ভরে দ্যাখো, দেখে যাও। কিন্তু সেখানেও কি শান্তি আছে! ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটায় চোখ জ্বালা করে জল পড়ছে। এত ঠান্ডা! বাপ রে বাপ!
রিমি জার্মানি এসেছে একটা প্রোজেক্টের কাজে। সে মানবীবিদ্যার ছাত্রী। যেসব দেশের রাষ্ট্রপ্রধান নারী, সেখানকার নাগরিকেরা কেমন আছে, এই তার গবেষণার বিষয়। নানা শহর ঘুরে সে এসেছে এই বন শহরে। যা পূর্বতন পশ্চিম জার্মানির রাজধানী ছিল। ভারি সুন্দর সাজানো শহর। আর ওই নদী, যেন তার গলার হার। কিন্তু আপাতত কাব্যি করার চাইতে হোটেলের নিয়ন্ত্রিত উষ্ণতায় ঢুকে পড়া তার পক্ষে বিশেষ দরকারি।
হ্যাঁ, সে কবিতা লেখে। সেসব তেমন কিছু নয়। নিজের ল্যাপটপের এক কোণায় সেভ করে রাখা। তারা ওখানেই নিশ্চিন্তে ঘুমায়। তাদের বাইরে টানাটানি করাটা রিমির পোষায় না। ওসব তার একান্ত ব্যক্তিগত আবেগের প্রকাশ, কারও সঙ্গে সে তা ভাগ করে নিতে চায় না।
সে সোজা ডাইনিং হলে ঢুকে পড়ল। এখানে হোটেলের চার্জের সঙ্গে প্রাতরাশটাও মুফতে। সে পরে হবে’খন। আগে পরপর দু’কাপ কফি। তারপর অন্য সব। বাব্বা, ঠান্ডা কাকে বলে!
প্রাতরাশ সেরে সে যখন লিফটে উঠছে, রিসেপশনিস্ট ছেলেটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সুভদ্র হেসে বলল– হাউ ডিড ইউ লাইক ইট?
– হোয়াট? মাই ব্রেকফাস্ট?
– ও নো নো, দ্য রিভার।
– অ্যসাম বিউটি, অফুলি চিলি!
– আই টোল্ড ইউ। হোপ ইউ ওন্ট ক্যাচ কোল্ড।
– গড ব্লেস মি, আই হ্যাভ লোড্স অফ ওয়ার্ক টু ডু।
– ইউ উইল বি হিয়ার ফর থ্রি ডেজ, নো?
– ইয়াপ, মাই ওয়ার্ক ডিমান্ডস দ্যাট।
– ওকে, মাই বেস্ট উইশেস ফর ইওর ওয়ার্ক, হোয়াটেভার ইট মে বি।
– ডাঙ্কে, ডাঙ্কে শ্যুন।
– ওহ, ইউ গট ইট, হা হা হা, মোস্ট ওয়েলকাম!
রিমি ঘরে ঢুকল। এতক্ষণে সে একটু ধাতস্থ হয়েছে। কিন্তু গ্লাভ্সগুলো কোথায় গেল? তার তো ঘরে বসে থাকলে চলবে না। বেরোতে হবে, বাইরে ঘুরতে হবে। সে সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজে দেখল, কোত্থাও নেই। তাহলে সে কি আগের কোনও শহরে ফেলে এল তাদের। তবে তো গ্লাভ্স একজোড়া কিনতেই হচ্ছে। রিসেপশনের ছেলেটিকেই জিজ্ঞেস করতে হবে কোথায় কোন দোকানে পাওয়া যেতে পারে।
সে ল্যাপটপ খুলে বসে। কিছু তথ্য সে সংগ্রহ করেছে। সেগুলো গোছাতে হবে। এমনিতে সে কাজের ক্ষেত্রে খুব গোছানো। ফেলে ছড়িয়ে কাজ তার পোষায় না। তবু… ওই দস্তানা জোড়া… ধ্যুৎ… কোথায় যে গেল।
হারিয়ে যাওয়া দস্তানা থেকে তার মনও যেন কোথায় হারিয়ে যেতে চাইছে। সে ল্যাপটপে নতুন একটা পাতা খুলল…
আমাকে একাকী ফেলে
কোথায় হারিয়ে গেলে
উষ্ণতা, এসো ফিরে
প্রিয় নদীটির তীরে…
এরপর আর কাজ হয় না। সে রিসেপশনে একটা ফোন লাগাল।
– ইয়েস ম্যাম, হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ?
– লিসন, আই লস্ট মাই ওল্ড পেয়ার অফ গ্লাভ্স, আই নিড টু বাই আ নিউ ওয়ান। ক্যান ইউ সাজেস্ট মি আ মার্কেট অর আ শপিং মল হোয়াটেভার হোয়্যার আই ক্যান গেট দ্যাট?
– উপ্স, ইউ ওয়াক্ড বাই দ্য রিভার উইদাউট ইওর গ্লাভ্স!
– ইউ বেট!
– আর ইউ ফ্রি টুডে?
– ইন দ্য মর্নিং, ইয়েস। আফটার ওয়ান আই অ্যাম অকুপায়েড।
– ওকে, আই সার্টেনলি ক্যান ডু ওয়ান থিং, আয়্যাম গিভিং সামওয়ান টু অ্যাকম্পানি ইউ টু দ্য শপ ফ্রম হোয়্যার ইউ ক্যান বাই ইট, উইল দ্যাট বি ওকে?
– ও থ্যাংক ইউ, থ্যাংক্স ভেরি মাচ।
– ওহো, ইউ ডোন্ট রিয়েলি লাইক মাই সাজেশন।
– হোয়াট মেক্স ইউ থিংক লাইক দ্যাট!
– আদার ওয়াইজ ইউ উড হ্যাভ সেড ডাঙ্কে, ডাঙ্কে শ্যুন।
– ওহ্, হা হা হা …আই উইল সেভ দ্যাট ফর আ বেটার
মোমেন্ট, ওকে?
– ওকে! অ্যাজ ইউ উইশ ম্যাম!
এগারোটা নাগাদ ছেলেটি ফোন করল রুমে। তার পথপ্রদর্শক এসে গেছে। এবার গ্লাভ্স কিনতে বেরোতে হবে। রিমি ভালো দেখে বেছে এক জোড়া গ্লাভ্স কিনল। তাতে হাত গলিয়ে এমন আরাম হল, যেন হাত দু’টো গ্লাভ্সের মধ্যে ঘুমিয়েই পড়বে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে তো চলবে না। অনেক কাজ, সামনে অনেক কিছু করা বাকি।
সে তার সঙ্গের ছেলেটিকে ধন্যবাদ ও বিদায় জানিয়ে হোটেলে ফিরল। রিসেপশনের ছেলেটির দিকে তাকিয়ে একটা ধন্যবাদ
(ইংরেজিতেই) জানিয়ে সোজা চলে গেল রুমে। হাতগুলো দস্তানার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ছে। না, না, ওদের জাগাতে হবে, জাগাতে হবে।
সে ল্যাপটপটা খুলে রেখেই বেরিয়ে গেছিল। খোলা সাদাপাতা, তাতে চারটি পঙ্ক্তি, তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে কি আরও কিছু বলতে চায়? সে দস্তানা জোড়া বিছানার ওপর ছুড়ে ফেলল, তারপর ল্যাপটপটা কোলে টেনে নিয়ে…
আমাকে একাকী ফেলে
কোথায় হারিয়ে গেলে
উষ্ণতা, এসো ফিরে
প্রিয় নদীটির তীরে…
আমার নগ্ন হাতে
ছোঁয়াছুঁয়ি কার সাথে
নদী, বলো তার নাম
কাকে ভালোবাসলাম…
দুপুরের পর থেকে রিমি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একটু দেরিই হয়ে গেল বেরোতে। তারপর পাঁচ জায়গায় ঘোরাঘুরি। দস্তানা জোড়া সে খুব সাবধানে রাখল। আবার যেন না হারায়। হোটেলে ফিরতে ফিরতে সাতটা বাজল। এখন ভারতে রাত সাড়ে এগারোটা। অভি, তার প্রেমিক অভিমন্যু ফোন করবে। কিংবা সেও অভিকে ফোন করতে পারে। যে-কোনও একজন আগে করে ফেলতে পারে, এতে অত হিসেবের কিছু নেই। রুমে ঢুকে ল্যাপটপের ব্যাগ, কাগজপত্তরের আরেকটা ঢাউস ব্যাগ, ওভারকোট, মাফলার, আর হ্যাঁ, দস্তানা জোড়াও সে বিছানার ওপর ছড়িয়ে ফেলল। ডাবল বেড, কাজেই একপাশে তার শোওয়ার মতো জায়গা আছে। সে জুতো মোজা না খুলে হাত-পা ছড়াতে না ছড়াতেই রুমের ফোনটা বাজল। নিশ্চই অভি। মোবাইলে না পেলে হোটেলেও ফোন করে। রিমি এলিয়ে পড়েছিল, একটু কষ্ট করে উঠল
– হ্যালো!
– ইউ হ্যাভ আ কল ফ্রম ইন্ডিয়া ম্যাম। উড ইউ লাইক টু টেক ইট ইন ইয়োর রুম?
– ইয়েস, প্লিজ।
– রিমি, কখন ফিরলে?
– এই মাত্র। আজ খুব খাটনি গেছে। তোমার খবর বলো।
– আমি ঠিক আছি। আমিও একটু আগে ফিরলাম। শোনো, তুমি ওখানে থাকাটা আর বেশি বাড়িও না। মা খুব তাগাদা দিচ্ছে। তোমার মায়ের সাথে আজ কথা হল, উনিও চাইছেন না তুমি আর বাইরে থাকো।
রিমির ক্লান্ত লাগে। এই একটাই কথা অভি আজকাল প্রায়ই বলে। এটা নাকি দু’জনের বাড়ি থেকেই চাইছে। মা’ও সেদিন ফোনে একই কথা বলছিল। আশ্চর্য, সে কি মজা করার জন্য এই নির্বান্ধবপুরীতে একা একা খেটে মরছে! সেই হতাশাটাই তার উত্তরে প্রকাশ পেল – অভি, আমি কাজটা শেষ করি তুমি চাও না?
– নিশ্চই চাই, কিন্তু তাই বলে এতদিন বাইরে বাইরে থাকাটা… আমাদের বিয়েটা সেরে ফেললে হতো না?
– বিয়ে তো সারা হবেই, সোনা। তার আগে আমায় আরেকটু সময় দাও। প্লিজ। এই প্রোজেক্টটা সাকসেসফুল হলে তোমার আনন্দ হবে না? কত আর বেশি দেরি হবে? মাস তিন-চার? এর মধ্যে আমরা কি বুড়োবুড়ি হয়ে যাব?
– তা বলছি না, কিন্তু একা একা…
– একা বলেই তো তোমার কাছে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি, তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করে নিয়েই এক লাফে তোমার পিঠে চেপে বসব, রাইট?
অভিমন্যু মানতে চায় না। রিমির আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না। সে বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে। এখন সে একটু বাথটবে গরমজল ভরে শোবে, শুয়ে শুয়ে একটু রেড ওয়াইন পান করবে, তারপর সোজা বিছানায়, লেপের তলায়। এর মধ্যে তার মনে হয় যত দিন যাচ্ছে অভি বড়ো ঘ্যানঘ্যান করছে। তার মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে।
– সরি অভি, আজ আর কথা বলতে পারছি না, সারাদিন বড্ড ঘোরাঘুরি হয়েছে, এবার একটু রিল্যাক্স করতে চাই।
– তোমার উড-বি-হাজব্যান্ডের সঙ্গে কথা বলাটা কি রিল্যাক্সেশনের মধ্যে পড়ে না? আর শোনো, আমিও আজ সারাদিন অফিস করেছি। বসের সঙ্গে ঝামেলা করেছি। ফেরার পথে আমার গাড়িটাকে একটা স্কর্পিও ফ্রম নো হোয়্যার এসে রিয়ার ভিউটা ঠুকে দিয়ে গেল। আমিও যথেষ্ট ক্লান্ত। তোমার সঙ্গে কখন কথা হবে সেই কথা সারাদিন ভাবি, আর তুমি আজকাল কথাই বলতে চাও না!
– ওহ্ না না অভি! কে বলেছে কথা বলতে চাই না? অন্যদিন তো বলি! আজ কেন কে জানে… শোনো, আমি শিগগিরি একটা ডিসিশন নিয়ে নেব ফেরার ব্যাপারে… আমার কাজটা তার মঝ্যে ঝটপট করে ফেলতে হবে… জাস্ট বিয়ার উইথ মি ফর সামটাইম… ঠিক আছে সোনা আমার? …লাভ ইউ লাভ ইউ লাভ ইউ…
– ওকে
– তুমি লাভ ইউ বললে না?
– হ্যাঁ, লাভ ইউ, ছাড়ছি।
– গুড নাইট বেবি!
ওদিক থেকে আর কোনও সাড়া এল না। অভিমন্যু লাইন কেটে দিয়েছে।
রিমির কেমন যেন একটা লাগে। উঠে বাথটাবের গরমজলের কলটা খুলে দিয়ে আসা দরকার। জল ভরতে ভরতেই কাগজপত্রগুলো গোছগাছ করে রাখা দরকার। জামাকাপড় ছাড়া দরকার। একা থাকার এই এক সুবিধা। ইচ্ছেমতো নগ্ন হওয়া যায়। কিন্তু সে কিছুই করল না। বিছানায় হামাগুড়ি দিয়ে ব্যাগ থেকে ল্যাপটপটা বার করল… কী যেন লেখা ছিল ওই পাতাটায়?
আমাকে একাকী ফেলে
কোথায় হারিয়ে গেলে
উষ্ণতা, এসো ফিরে
প্রিয় নদীটির তীরে…
আমার নগ্ন হাতে
ছোঁয়াছুঁয়ি কার সাথে
নদী, বলো তার নাম
কাকে ভালোবাসলাম…
রিমি তার ক্লান্ত আঙুল কি প্যাডে রাখতেই তারা কেমন আপনা থেকেই সচল হয়ে উঠল,
তাকে বলো, ভালোবাসি
বলো, তোমার কাছে আসি
পেতে এতটুকু ওম
কী নরম কী নরম!
এবার এখানে ঠান্ডা বেশি পড়েছে। আজ সকাল থেকে শহরে তুষারপাত হচ্ছে। জানলা দিয়ে সেই ঝরে পড়া ছোটোছোটো তুলোর বলের দিকে তাকিয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। রিমির আজ কাজে বেরোতে মন চায় না। লেপের তলায় শুয়েই থাকে। কী একটা অবসাদ জড়িয়ে ধরেছে তার হৃদয়। তাকে আরও অনেকদিন এখানে থেকে যেতে হবে। তার দেশের থেকে দূরে, তার পরিবার থেকে দূরে, তার প্রেমিক, যে তার ভাবী স্বামী, তার থেকে দূরে। কিন্তু, ব্যাপার হল, তার মানসিক অবসাদ ঠিক এই জন্য নয়। কী জন্যে যে, সে নিজেই ভালো বোঝে না।
হ্যাঁ, একটা বিয়ে তার আশু কর্তব্য। কিন্তু কেন! তার যদি অভিকে আর ভালো না লাগে! এই অবধি ভেবে রিমি তার মনকে নিয়ন্ত্রণে আনল। ছি, এসব আবার কী কথা। সে কি চিরদিন একা একা এইখানে পড়ে থাকবে নাকি! সে দেশে ফিরবে, তার বহুদিনের প্রেমিক অভিকে বিয়ে করবে, তাদের একটি-দু’টি সন্তান হবে, সন্তানেরা বড়ো হবে, তাদের স্কুলে ভর্তি করতে হবে, তারা ভালো চাকরিবাকরি করবে, তাদের বিয়ে হবে, নাতিপুতি হবে… হা হা হা– মানুষের জীবনে এই গতানুগতিক সুখের চেয়ে বড়ো আর কিছু হয় কি?
অবসাদ… অবসাদ… এরকম একটা জীবনের কথা মনে আসতেই কেন কে জানে রিমির বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে। সে লেপের তলায় পাশ ফিরে শোয়।
তখনই তার রুমের ফোনটা বেজে ওঠে,
– হ্যালো!
– হ্যালো ম্যাম, গুড মর্নিং
– গুটেন মর্গেন
– হা হা হা গুটেন মর্গেন ইনডিড, বাট মর্নিং শোজ দ্য ডে। উই আর গোইং টু হ্যাভ আ মিজারেবল ডে।
– ইউ নো ইট বেটার।
– এনি ওয়ে, ম্যাম, হ্যাভ ইউ হ্যাড ইওর ব্রেকফাস্ট?
– নট ইয়েট। আয়্যাম স্টিল ইন বেড।
– ওহো, আয়্যাম সরি।
– নো নো, ইট্স অলরাইট, টেল মি।
– অ্যাকচুয়ালি… মাই ডিউটি আওয়ার ইজ ওভার। আই জাস্ট এনকোয়ার্ড হোয়েদার ইউ নিড সামথিং।
– ওহ, সো নাইস অফ ইউ। রাইট নাউ আই নিড সাম স্লিপ। দেয়ার মাস্ট বি সামওয়ান দেয়ার আফটার ইউ লিভ। আই উইল লেট হিম অর হার নো ইফ আই নিড এনিথিং।
– রাইট ম্যাম। আই অ্যাম লিভিং। হ্যাভ আ বেটার ডে।
– হা হা হা, ইউ বেট! ডাঙ্কে শ্যুন!
– মোস্ট ওয়েলকাম, ম্যাম!
ছেলেটি ফোন কেটে দিল। রিমি হঠাৎ দেখল তার মন ভালো হয়ে গেছে।
তুষারপাত হয়েই চলেছে। রিমি রেস্টুরেন্টে গিয়ে কাপুচিনোর মাগ নিয়ে বসল। সে মোবাইলে সর্বদা অনলাইন। কে একটা মেসেজ পাঠাল কোনও চেনা নাম নয়। অরূপ মহাজন। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে। রিমি তার প্রোফাইলে গেল। মনে হয় নতুন প্রোফাইল খুলেছে। কোনও ছবি নেই, ওয়ালপেপার নেই। কোনও কিছু আপলোড করা নেই। সে ইনবক্সে জিজ্ঞেস করল – আপনি কে?
কোনও উত্তর নেই। তারপর – ক্যান আই চ্যাট উইথ ইউ?
– নো, সরি, অ্যাট ফার্স্ট আই মাস্ট নো হু ইউ আর।
– আ নিউ ফ্রেন্ড।
– ফ্রেন্ডস নো ইচ আদার।
– ওকে, মে বি সাম আদার ডে। বাই।
রিমি বিরক্ত হয়ে ফোনটা টেবিলের ওপর রাখল। সে আজ কাজে বেরোয়নি ঠিকই, ভেবেছিল বিশ্রাম নেবে। কিন্তু তার মাথা গজগজ করছে চিন্তায়। তার কাজ আর অভিকে নিয়ে একটা টানাপোড়েন শুরু হয়েছে বেশ কয়েকদিন হল। সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। যে-প্রোজেক্টটা নিয়ে সে এখানে এসেছে, সেটা তার কাছে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। তার আগাগোড়া মেধাবী কেরিয়ার এতে উজ্জ্বলতর হবে। অভি কেন বুঝতে চাইছে না? যদিও সে জানে, এই দীর্ঘদিনের অসাক্ষাৎ তাদের দু’জনের পক্ষেই বেদনাদায়ক। দু’মাস হয়ে গেল দু’জনের দেখা নেই। যদিও ওয়েব ক্যাম-এ পরস্পরকে দেখতে দেখতেই তারা চ্যাট করে। কিন্তু অভির মুখে বিরহের পরিবর্তে বিরক্তিই বেশি।
রিমির মাঝে মাঝে মনে হয়, ভৌগোলিক দূরত্ব কি তাদের মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি করছে। এরকমটা হয় সে জানে। কিন্তু… না না না… তাদের ক্ষেত্রে অন্তত এটা সত্যি না। এই তো ক’দিন আগে এক বছরের ডেপুটেশনে অভিকে অফিস থেকে দিল্লি পাঠাল, তখনও তারা চ্যাট করত, ফোনে কথা বলত, রিমি যথেষ্ট ‘ভাল্লাগে না ভাল্লাগে না’-ও করত। কিন্তু এত চাপ সৃষ্টি করত না। হঠাৎ করে সে জার্মানিতে আসার পর থেকেই বিয়ের ছটফটানি শুরু হল কেন? তার ছাব্বিশ চলছে, অভির তিরিশ। এতে কি বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে!
কাপুচিনোটা শেষ হয়ে গেছে। রিমি রুমে এসে ওভারকোটটা গা’য় চাপিয়ে মাথার হুডটা তুলে নিল। মাফলার, দস্তানা, ওয়াটারপ্রুফ জুতো জোড়া। তারপর রুমের ল্যাচটা টেনে লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তুষারপাতটা বেড়েছে। তবু সে রাইন নদীর ধার ধরে হাঁটতে লাগল। মুখে শানানো ছুরির মতো কনকনে ঠান্ডার আঘাত। সে হাঁটছে হাঁটছে হাঁটছে। কোথা থেকে? কোথায়? সে জানে না। মনে হয় সে সত্যিই অভির থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আর এটা হয়েছে জার্মানিতে আসার আগেই। শুধু বোঝা গেছে আসার পর।
এই শহরের বাকি যা কাজ, কালকের মধ্যে সেরে ফেলতে হবে। ব্যাপারটা চাপের হয়ে গেল, শুধু শুধু একটা দিন নষ্ট করল সে। পরশু সে কোলোন চলে যাবে। তবু, আজ যদি দিনটা সে রাইনের হাত ধরে অনেক দূর চলে যেতে পারে, সেও তো কম পাওয়া নয়।
ফোনটা কাঁপছে। সে পকেটের মধ্যে থেকে ফোন বার করল। অভি। অনলাইন।
– ওখানকার কাজ শেষ হল?
– নাহ্, আজ কোনও কাজ হল না, জানো! কালকে সব সারতে হবে, হয়ে যাবে। চিন্তার কিছু নেই।
– রুমে পেলাম না, কোথায় বেরিয়েছ?
– এই হাঁটছি, রাইনের ধার ধরে। বরফ পড়ছে, জানো! আর কী ঠান্ডা হাওয়া।
– শুধু শুধু ঠান্ডা লাগাচ্ছ কেন, হোটেলে ফিরে যাও।
রিমির মনে হল, অভি যদি তার সঙ্গে থাকত, সে বোধ হয় এভাবে এই কথাগুলো বলত না। বরং বলত – চলো আরও হাঁটি।সেই একসঙ্গে হাঁটার দিন কি তাদের ফুরিয়ে এল!
সারাদিন এদিক ওদিক উলটোপালটা ঘুরল সে। ভাগ্যিস তার কাছে দু’টো দরকারি জিনিস ছিল। এক – শহরের একটা ম্যাপ, দুই – হোটেলের ফোন নাম্বার। সন্ধে নাগাদ বরফ আর হাওয়ার দাপট বাড়ল। এবার হোটেলে ফিরতে হবে। বিরাট বিরাট শপিং প্লাজাগুলি আলো-ঝলমল, কিন্তু রাস্তায় কোনও লোক নেই, গাড়িও হাতেগোনা। রিমি হোটেলে ফিরে এল।
রুমে ফিরে বাঁ হাতের দস্তানাটা টেনে খুলবার জন্য ডান হাত বার করল। আশ্চর্য, ডানহাতের দস্তানাটা কোথায়! অভিকে মেসেজ করার সময় সে ডানহাতের দস্তানাটা খুলেছিল। তারপর নির্ঘাত পকেটে ঢোকাতে গিয়ে পড়ে গেছে। রিমির কান্না পায়। এই এক জোড়া গ্লাভ্স তাকে জ্বালিয়ে মারল। সে নীচে নেমে এল। রিসেপশনে একটি মেয়ে। তাকে এগিয়ে যেতে দেখে গম্ভীর মুখে বলল – ইয়েস ম্যাম?
– আই লস্ট মাই… এই অবধি বলেই রিমির মনে হল সেই ছেলেটি, যে তাকে গ্লাভ্সের দোকানে নিয়ে গিয়েছিল, সেরকম কাউকে তো মেয়েটি ঠিক করে দেবে না, আর সে নিজেও রাস্তা চিনে চিনে এই অন্ধকারে যেতে পারবে না। সে বাকি কথাটা গিলে নিল, বলল – আই থিংক আই লস্ট মাই রুম কি।
মেয়েটি চাবি ঝোলানো বোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল – ইয়োর রুম নাম্বার?
রিমি বলল। মেয়েটি গম্ভীর মুখেই বলল – নো, ইট্স দেয়ার। ইউ সাবমিটেড বিফোর গোইং আউট।
– ওঃহো, থ্যাংক্স আ লট।
কেন কে জানে মেয়েটিকে তার ডাঙ্কে শ্যুন বলতে ইচ্ছে করল না।
পরের দিন কাজে কাজেই সময় কেটে গেল। দস্তানা আর কেনা হল না। রাত্রিবেলা ঘরে ফিরে সে রিসেপশনের দিকে একবার তাকাল। না, পরিচিত ছেলেটি নেই। থাকলে সে একটু বিদায় নিত। কাল ভোর ভোর বেরিয়ে পড়তে হবে।
ভোরে বেরোনোর সময় লাগেজ নিয়ে নীচে নেমে রিমি রিসেপশনে চাবি জমা দিতে গেল। গিয়ে দেখল ছেলেটি আছে। রিমি খুশি হল। চেনা মানুষ দেখলে যেমন আনন্দ হয়। সে বলল – ইউ নো হোয়াট, আই লস্ট আ গ্ল্যাভ্স এগেন।
– ও মাই গড! হাউ?
– ডোন্ট রিমেমবার, মে বি আই ড্রপড ইট ফ্রম মাই পকেট। অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ মেসেজিং মাই বয়ফ্রেন্ড, মাই উড-বি।
– ওহ, ওয়াও! ছেলেটি হঠাৎ আরও ভদ্র হয়ে গেল। – কনগ্র্যাটস অ্যান্ড গ্রিটিংস টু বোথ অফ ইউ।
– ডাঙ্কে, ডাঙ্কে শ্যুন।
– মোস্ট ওয়েলকাম!
রিমি হাত বাড়াল, তার দস্তানাবিহীন নগ্ন ডানহাত।
ছেলেটি হাতটা ধরল। উষ্ণ স্পর্শ। বলল – হ্যাভ আ ওয়ানডারফুল লাইফ। ফাইনালি, বিফোর উই পার্ট, মে উই ইনট্রোডিউস আওয়ারসেলভ্স আ বিট মোর পার্সোনালি?
– ও শিওর শিওর, ইউ আর সো হেল্পফুল, আই উইল রিমেমবার ইউ। প্লিজ টেল মি ইয়োর নেম।
– হ্যালো, দিস ইজ অরূপ মহাজন।
দু’মুহূর্ত দু’জনেই চুপ, তারপর দু’জনেই একসাথে হেসে উঠল। রিমি বলল
– বাট ফ্রম হোয়্যার দা হেল ইউ গট দ্যাট ইন্ডিয়ান নেম!
– উই হ্যাড আ বোর্ডার ফ্রম ইন্ডিয়া আ ফিউ ডেজ এগো।
– হা হা হা, হাউ ফানি। নাউ ইউ মাস্ট টেল মি ইয়োর রিয়েল নেম।
– অলিভার, অলিভার ম্যাথাউজ।
– হাই, আয়্যাম রিমি, রিমি বোস।
– হ্যালো রিমি, ইট ওয়াজ আওয়ার প্লেজার টু হ্যাভ ইউ হিয়ার ইন আওয়ার হোটেল।
– ওকে, নো ফর্মালিটিজ, বি জাস্ট দ্য ওয়ে ইউ আর, অ্যান্ড সেন্ড মি ইওর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট, আই উইল অ্যাকসেপ্ট। বাই।
রিমি খেয়াল করেনি তার ডান হাতটা তখনও ছেলেটির মুঠোতে ধরা।
তার দস্তানার অভাব এভাবে পূরণ হলে মন্দ কী?