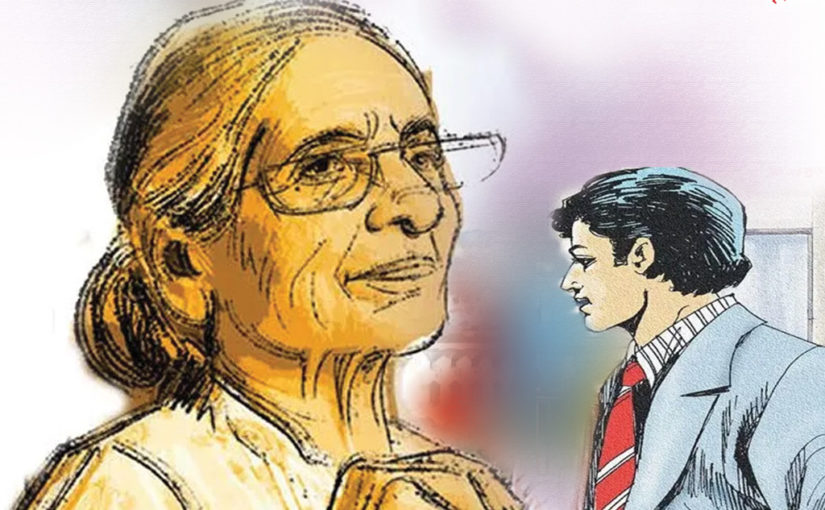সৌমিত্র ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন ধরে দিল্লিতে আছেন। তাই পরিচিতিও হয়েছে। এক রবিবার সৌমিত্র-র মোবাইলটা সকাল সকাল বেজে ওঠাতে সে একটু অবাকও হল। এত সকালে কে ফোন করল। কারণ দিল্লিতে রবিবার প্রায় অনেকেই একটু দেরিতে বিছানা ছাড়েন! এমনকী কেউ সকাল এগারোটার আগে কাউকে ফোনও করেন না।
সবাই জানেন, শনিবার হয়তো কোনও না কোনও কাজে লোকেরা শুতে দেরি করেছেন। তাই রবিবার এত সকালে ঘুমের ব্যাঘাত করাটা ঠিক নয়। এই অলিখিত নিয়মটা চলে আসছে অনেকদিন থেকেই। তাই বিরক্তি সহকারে ফোনটা তুলতেই দেখতে পেল তাতে নাম লেখা আসছে বিনোদ আহুজা, রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (আরডব্লিউএ)। ভাবল এত সকাল সকাল কী এমন দরকার পড়ল।
ফোনটা তুলে হ্যালো বলতেই, অন্যদিক থেকে বিনোদ আহুজার কণ্ঠস্বর ভেসে এল— দাদা, একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আমাদের আবাসনের ১০৭ নম্বর ফ্ল্যাটের একজন বাঙালি মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে। দরজা খুলছেন না। পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা জানিয়েছেন। একটু তাড়াতাড়ি আসুন দাদা। দেখুন তো আপনি চিনতে পারেন কিনা। আমি পুলিশে খবর দিয়েছি। দরজা ভাঙতে হতে পারে বা অন্য কোনও উপায়ে ওনাকে উদ্ধার করতে হবে।
একথা শুনেই সৌমিত্র যেন কেমন হয়ে গেল। মনে মনে ভেবে দেখল ওখানে বাঙালি কেউ থাকেন বলে তো তার জানা ছিল না। হতে পারে এমন কেউ যাকে দেখলে চিনতে পারবে। ভাবল এই অসময়ে অবশ্যই তার যাওয়া দরকার। তড়িঘড়ি করে মোবাইলটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আজকাল মোবাইল ছাড়া কোনও কাজই হয় না।
গন্তব্যে পৌঁছে গিয়ে শুনল, পাশের বাড়ির প্রতিবেশীরা বলছেন— গতকাল থেকে ১০৭ নম্বরের বয়স্কা মহিলা অনিতা সরকার দরজা খুলছেন না। উনি কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। ওনার স্বামী ভারত সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারি পদে ছিলেন এবং গত হয়েছেন অনেক বছর হল। এক ছেলে, সেও চাকরির খাতিরে আমেরিকাতে থাকেন। এর বেশি ওনারা কিছুই জানেন না। ভদ্রমহিলা খুবই অসামাজিক মানে যাকে বলে আনসোশ্যাল ছিলেন! কারও সঙ্গে মিশতেন না। এমনকী তাদের সঙ্গেও না।
সৌমিত্রবাবু বললেন আর দেরি না করে দরজা ভাঙা হোক। তবে অবশ্যই পুলিশকে ডেকে। বিনোদ বললেন— দাদা আমি আমাদের বিট কনেস্টবলকে ফোন করে দিয়েছি। এলেন বলে। ইতিমধ্যেই পুলিশও এসে হাজির হল। পিছনের ব্যালকনির দিকের দরজা ভেঙে দেখা গেল, অনিতা সরকার খাট থেকে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। তবে তখনও প্রাণবায়ু বেরোয়নি। পালস চলছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল। ঘরে তালা লাগিয়ে দেওয়া হল। সৌমিত্র ভদ্রমহিলাকে চেনেন না। তবে কয়েকবার বাজারে ও দোকানে দেখেছেন জিনিসপত্র কিনতে। কাঁধে একটি সাইডব্যাগ থাকত। দেখলে মনে হবে যেন লেখক-কবি-সাহিত্যিক।
এরপর পাঁচদিন বাদে অনিতা সরকারকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল। তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে তার ফ্ল্যাটে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল। ইতিমধ্যেই সৌমিত্রবাবু এই অনিতা সরকারের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে শুরু করেছিলেন। পাড়াতে পুজো কমিটিকে জানানো হল। তারা এই নামে কাউকে চেনেন না বলে দায়সারা গোছের উত্তর দিয়ে এড়িয়ে গেলেন। আসলে কেউ এর মধ্যে ঢুকতে চাইছেন না এটা বুঝতে সৌমিত্রবাবুর আর বাকি রইল না।
সৌমিত্রবাবু পাড়ার আরডব্লিউএ-কে অনুরোধ করলেন যে, চব্বিশ ঘণ্টা থাকা ও ওনাকে দেখাশোনা করার জন্য যেন একজন নার্স-কাম পরিচারিকা রাখা হয়।
আরডব্লিউএ-এর সেক্রেটারি বললেন— দাদা, নার্স তো রেখে দেব কিন্তু এর খরচা কে দেবে? কারণ প্রতিমাসে চব্বিশ ঘণ্টা থাকার জন্য এজেন্সিগুলো ২৫ হাজার টাকা নেয়। টাকা কে দেবে বলুন? আমাদের ফান্ডেও অত টাকা নেই। আপনি বরং অন্য কিছু ভাবুন।
—আমি দেখছি কী করা যায়। কিন্তু এখন প্রথম কাজ হল ওনার দেখাশোনা করার জন্য কাউকে সবসময়ের জন্য রাখা।
—ঠিক আছে আমি ব্যবস্থা করছি। তবে আপনি টাকার কথা ভাবুন। নয়তো পুরো টাকাটা আপনার পকেট থেকে দিতে হবে। বলল বিনোদ আহুজা।
সৌমিত্রবাবুর কথায় একজন নার্স-কাম পরিচারিকার ব্যবস্থা করা হল। অনিতা সরকারের ছোটো একটা ফোন আছে দেখে সেই ফোন ঘেঁটে আমেরিকার একটি ফোন নম্বর পাওয়া গেল। সৌমিত্রবাবু ভাবলেন প্রথম কর্তব্য হল ওনার ছেলেকে জানানো। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাকে ফোনে পাওয়া গেল না !
এরপর অন্য একটি ফোন নম্বর পাওয়া গেল যেটি এসেছিল অন্য কোথাও থেকে। সেই নম্বরে ডায়াল করতেই অন্যপ্রান্ত থেকে এক মহিলার কণ্ঠ ভেসে এল। সৌমিত্রবাবু বললেন –আপনি কি অনিতা সরকারকে চেনেন?
—হ্যাঁ চিনি। উনি আমার বড়ো বউদি হন। কিন্তু আপনি কে? আর কেনই বা আমাকে ফোন করছেন?
—দেখুন আমি অনিতাদেবীর প্রতিবেশী। উনি খুবই অসুস্থ। আপনারা একবার ওনার ছেলেকে ফোন করে খবরটা জানালে খুব ভালো হয়। ফোন করে বলুন যে, মা খুব অসুস্থ, তাই এ সময় তার আসাটা খুব জরুরি। আর হ্যাঁ, আপনি কোথায় থাকেন? আপনারা কেউ এসে ওনার দ্বায়িত্ব নিলে খুব ভালো হয়, কারণ ওনাকে দেখার জন্য এখানে কেউ নেই। এই অসময়ে ওনার কাছে কারও থাকা খুবই জরুরি।
(ক্রমশ…)