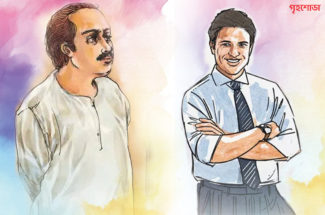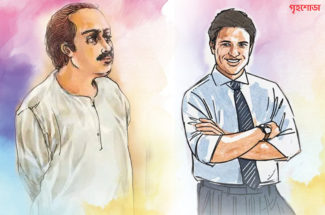গ্রন্থসাহেবে উল্লেখ আছে দশম গুরু গোবিন্দ সিংজি পূর্বজন্মে মেধস মুনি নামে এক সরোবরের তীরে তপস্যা করেন এবং দৈবাদেশ পান খালিসা ধর্ম প্রচারের। গাড়োয়াল হিমালয়ের বরফাবৃত সপ্তশৃঙ্গে ঘেরা নীল-সবুজ জলের সেই সরোবরই নাকি হেমকুণ্ড। হেমকুণ্ডসাহিব তাই শিখ ধর্মাবলম্বীদের কাছে পবিত্র তীর্থস্থান। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে শিখ পুণ্যার্থীরা এখানে আসেন, পুণ্যস্নান করেন। আর আসেন উৎসাহী ট্রেকার্স। যদিও তাদের সংখ্যা হাতেগোনা। পাশেই বদ্রিনারায়ণ বা বদ্রিনাথে, বছরে যে-পরিমাণ পর্যটক আসেন, তার এক শতাংশ পর্যটকও এখানে আসেন না। এর অন্যতম কারণ হয়তো যাতায়াতের দুর্গমতা। প্রায় ৪০ কিলোমিটার পথ যেতে হবে পায়ে হেঁটে কিংবা ঘোড়ায় চেপে। তবু গরমের ছুটিটাকে আমরা বেছে নিয়েছিলাম হেমকুণ্ড ভ্রমণের জন্য।
হাওড়া থেকে উপাসনা এক্সপ্রেসে চেপে পরদিন সাড়ে চারটে নাগাদ হরিদ্বার পৌঁছই। সেদিনই সন্ধ্যার আগে ২৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে হূষীকেশ পৌঁছে যাই রাত্রিবাসের জন্যে। কারণ হূষীকেশ থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো। হরিদ্বারের তুলনায় অনেক বেশি বাস ছাড়ে বদ্রিনাথগামী। যদিও বাস নয়, আমরা একটা সুমো জাতীয় গাড়ি রিজার্ভ করি। নিজেদের গাড়ি থাকলে সুবিধা বেশি পাওয়া যাবে। পথে পড়বে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান, বিশেষ করে পঞ্চপ্রয়াগের পাঁচটি প্রয়াগ, সেগুলিও দেখে নিতে চাই এই যাত্রায়।
পরদিন সকাল আটটা নাগাদ গাড়ি ছাড়ল হৃষীকেশ থেকে। যাব গোবিন্দঘাট, ২৭১ কিলোমিটার রাস্তা। একটানা ৬৯ কিলোমিটার চলার পর প্রথম গাড়ি থামল দেবপ্রয়াগে। এলাহাবাদের সঙ্গমের পরেই দেবপ্রয়াগের স্থান। মন্দাকিনী ও অলকানন্দার মিলিত সলিলে গোমুখ থেকে আসা ভাগীরথীর মিলন ঘটেছে এখানে। দুটি নদীর ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই রঙের, একটি সাদা অন্যটি পান্নাসবুজ। গঙ্গা নামের উৎপত্তি এই দেবপ্রয়াগ থেকেই। কথিত আছে, রাজা দশরথ দেবপ্রয়াগেই অজক মুনির পুত্রকে শব্দভেদী বাণে বিদ্ধ করেছিলেন। রাবণ বধের পরে শ্রীরামচন্দ্র পাপস্খালনের জন্য তপস্যা করেন এখানে, এমনকী দেবপ্রয়াগেই আছে ভগবান বিষ্ণুর নাভি। দেবপ্রয়াগ দর্শন শেষ করে আবার গাড়িতে চাপি। পরবর্তী গন্তব্য রুদ্রপ্রয়াগ।
হৃষীকেশ থেকে রুদ্রপ্রয়াগের দূরত্ব ১৪১ কিমি অর্থাৎ দেবপ্রয়াগ থেকে ৭২ কিমি। প্রয়াগ দর্শনের পাশাপাশি দুপুরের আহারপর্বটিও এখানে সেরে নিই। অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল রুদ্রপ্রয়াগ। কথিত আছে, দেবর্ষি নারদ এই রুদ্রপ্রয়াগে বসেই সংগীত সাধনা করতেন, রুদ্রনাথ (শিব) এখানে বসেই রাগরাগিণীর জন্ম দেন– নাম তাই রুদ্রপ্রয়াগ।
রুদ্রপ্রয়াগের পর কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ থেকে দূরত্ব ৩২ কিমি। অলকানন্দা আর কর্ণগঙ্গার সঙ্গম। মহাভারতের বীর যোদ্ধা কর্ণের তপস্যাস্থল। সূর্যদেব এখানেই তার পুত্রকে কবচ ও কুণ্ডল দান করেন। কর্ণের মন্দির ছাড়াও আরও অনেক দেব-দেবীর মন্দির রয়েছে কর্ণপ্রয়াগে। মহাকবি কালিদাসের কাব্যে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের মিলন ঘটেছিল এই কর্ণপ্রয়াগেই।

কর্ণপ্রয়াগ থেকে ২১ কিমি দূরে অলকানন্দা ও নন্দাকিনীর সঙ্গম– নন্দপ্রয়াগ। নন্দপ্রয়াগ থেকে ৬৮ কিমি দূরে অলকানন্দা এবং ধৌলিগঙ্গার সঙ্গম বিষ্ণুপ্রয়াগ দর্শন করে সারাদিনের জার্নি শেষ হয় গোবিন্দঘাট পৌঁছে, ঘড়িতে তখন ঠিক সন্ধ্যা ছ’টা।
অলকানন্দা ও ভুইন্দর গঙ্গার সঙ্গমে পাইন দেওদার গাছে ঘেরা ছবির মতো সুন্দর গোবিন্দঘাট হেমকুণ্ডসাহিবের গেটওয়ে। গোবিন্দঘাট থেকে বদ্রিনাথের দূরত্ব আর মাত্র ২৩ কিমি। হাতে সময় থাকলে গোবিন্দঘাটের জন্যে একটা দিন বরাদ্দ করতে পারেন। তাতে যেমন ঘুরে দেখে নেওয়া যাবে জায়গাটা, উচ্চতা জনিত সমস্যার সঙ্গে মানিয়ে নিতেও সুবিধা হবে, সর্বোপরি ট্রেকিং শুরুর আগে একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে পথে নামা হবে। এখানে থাকার জন্যে অসংখ্য হোটেল এবং গুরুদোয়ারা আছে। গুরুদোয়ারায় থাকা-খাওয়া ফ্রি, ব্যবস্থা উত্তম, তবে ধূমপান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আসক্তি প্রবল হলে গাঁটের পয়সা খরচ করে আমাদের মতো হোটেলে উঠতে হবে।
পরদিন রোদ ঝলমল সকাল। সকাল সাতটার মধ্যে প্রয়োজনীয় মালপত্র রুকস্যাকে ভরে বেরিয়ে পড়লাম। অতিরিক্ত মালপত্র রাখা থাকল গুরুদোয়ারার স্টোর রুমে। না, এজন্য কোনও দক্ষিণা দিতে হয় না। আজ যাব ঘাংঘারিয়া পর্যন্ত, দূরত্ব ১৩ কিমি। পথ গিয়েছে অলকানন্দার উপনদী লক্ষ্মণ (ভুইন্দর) গঙ্গার পাড় ধরে। পাইন, দেবদারু, ভুজ আর রডোডেনড্রনের ছায়ায় ঢাকা অসাধারণ মোহময় এই পথশোভা আগাগোড়া চড়াই এ পথের পথকষ্ট অনেকটাই ভুলিয়ে দেয়। পথে অসংখ্য চা আর ফাস্টফুডের দোকান, ক্ষণিক বিশ্রাম আর তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে পকেট পারমিট করলেই হল। অধিকাংশ ট্রেকিং রুটে যে সুবিধা পাওয়া যায় না বললেই চলে।
ঘাংঘারিয়া পৌঁছোতে বিকাল হয়ে গেল। প্রকৃতি ততক্ষণে বিমুখ হয়েছে। টিপটিপ বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। উচ্চতার কারণে এমনটা এখানকার স্বাভাবিক ব্যাপার, দুপুরের পর থেকেই আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করে। ঘাংঘারিয়াতেও থাকার জন্যে আছে অসংখ্য হোটেল এবং গুরুদোয়ারা। গুরুদোয়ারার ব্যবস্থা গোবিন্দঘাটের মতোই, থাকা-খাওয়া ফ্রি তবে ধুমপান নিষেধ। এখানেও আমরা হোটেল নিলাম। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, হেমকুণ্ডের সিজন শুরু হয় জুন মাস থেকে, আমরা এসেছি মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। হোটেল ভাড়া তাই সস্তাই। সারাদিনের পথশ্রমে শরীর ক্লান্ত ছিল, ন’টার মধ্যে খেয়েদেয়ে কম্বলের তলায় ঢুকলাম। কাল পৌঁছব কাঙ্খিত লক্ষ্যে, অর্থাৎ হেমকুণ্ডে। যত সকাল সকাল সম্ভব বেরিয়ে পড়ব। এ পথেও দুপুরের পর আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। তুষারপাত নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ফিরতেও হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।
পরদিন ঘুম ভাঙতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। কতক্ষণ চলবে কে জানে। ভয় পাচ্ছি, দিনটা পাছে নষ্ট না হয়। ভাগ্য প্রসন্ন ছিল বোধহয়, ঘণ্টাখানিকের ব্যবধানে বৃষ্টি কমে এল। থেমেও গেল একসময়। আমাদের চমকে দিয়ে ঝলমলে রোদ উঠল। অনেকদূর পর্যন্ত এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দূরের পাহাড়গুলোর মাথা সাদা বরফের চাদরে ঢেকে গেছে। ঘর ছেড়ে বাইরে আসি আমরা। সুযোগ পেতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরাও বেরিয়ে পড়েছে। অসংখ্য প্রজাতির রংবেরঙের পাখি কিচিরমিচির করছে চারপাশে। শুরু হয়েছে স্থানীয় মানুষের দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা। বেশ কিছু ট্রেকার্সকে দেখলাম হেমকুণ্ডের উদ্দেশে রওনা দিতে। তৈরি হয়েই ছিল তারা। আমাদের একটু সময় লাগল, আটটা নাগাদ বেরোলাম। দূরত্ব ৬ কিমি। অসম্ভব চড়াই এ রাস্তা, প্রায় ৭০ ডিগ্রি খাড়া। তেমন দুর্গম। একটুতেই হাঁফ ধরে আসে। একটানা বেশিদূর হাঁটতে পারি না। বিশ্রাম নিতে নিতে এগোই। দূরে দেখা যাচ্ছে পুরু বরফের চাদরে মোড়া সব গিরিশীর্ষ। এখনও জানি না, ওইসব গিরিশৃঙ্গের কোনটা আমাদের গন্তব্য। এ পথেও বেশ কিছু দোকানপাট আছে। গরম চায়ে গলা ভিজিয়ে নেওয়া যায়, প্রয়োজনে হালকা টিফিনও করতে পারেন।
৩ কিমি যাওয়ার পর প্রথম বরফের দেখা পেলাম। আরও কিছুদূর এগোলে গ্লেসিয়ার। গ্লেসিয়ার কেটে পায়ে চলার রাস্তা। এপথের শেষ দোকান এখানেই। দোকানে চা-পানের জন্যে বসেছিলাম, শুরু হল আবার বৃষ্টি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম। অযথা সময় নষ্ট না করাই ভালো। তাছাড়া এতদূর এসে যদি ফিরে যেতে হয়, তার মতো দুঃখের আর কিছু নেই।
দু’পাশে পুরু বরফের চাদর, মাঝখানে পিচ্ছিল পথ, সন্তর্পণে পথ হাঁটি আমরা। একটু অসাবধান হলেই বড়ো ধরনের বিপদ ঘটবে। ভাগ্যিস ঘাংঘারিয়া থেকে বেরোনোর সময় প্রত্যেকে একটি করে লাঠি নিয়েছিলাম সঙ্গে। এখন সুফল পাচ্ছি। লাঠি ঠুকে ঠুকে আরও এক কিমি অতিক্রম করে ফেলি। শেষ দু’কিমি অসম্ভব চড়াই। এটুকু পেরোতেই প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লেগে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে যখন সরোবরের সামনে পৌঁছলাম, শরীরে এক তিলও শক্তি অবশিষ্ট নেই। কুণ্ডের পাশে নির্দিষ্ট লোহার বেঞ্চগুলোর একটায় শরীর এলিয়ে বসলেও, চোখ বন্ধ করতে মন চাইল না। এ কোথায় পৌঁছেছি? ভারত না সুইজারল্যান্ড? যেদিকে তাকাই সব সাদা। বরফের চাদরে ঢেকে আছে চরাচর। সরোবরের চারপাশ-বেষ্টিত পাহাড়গুলোও সাদা হয়ে আছে। ইতিমধ্যে রোদ ওঠে এক ঝলক। রুপোর পাতের মতো ঝলমল করে ওঠে চারপাশ। হেমকুণ্ডের স্বচ্ছ জলে সেইসব তুষারাবৃত সপ্তশৃঙ্গের উজ্জ্বল প্রতিবিম্বের শ্বাসরোধকারী সৌন্দর্য। সারাবছরই বরফ ভাসে সরোবরের জলে।

নয়নাভিরাম এই সরোবরের (৪৩২৯ মিটার) পাড়ে ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠা পায় গ্রন্থসাহেব, গড়ে ওঠে কুঠি। ১৯৩০ সালে এ জায়গা আবিষ্কার করেন হাবিলদার মোহন সিং। পরবর্তীকালে সরোবরের পাড়েই তৈরি হয় দ্বিতল গুরুদোয়ারা। মর্মর পাথরে তৈরি এই গুরুদোয়ারার আকৃতি অনেকটা নক্ষত্রাকার। লক্ষণ-গঙ্গার উৎসও এই হেমকুণ্ড। জুলাই থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি হেমকুণ্ডের পথে দেখা মেলে অসংখ্য ব্রহ্মকমলের। যেহেতু আমরা এসেছি স্কুলের গরমের ছুটিতে, মে মাসে, তাই বঞ্চিত হই সেই বিরল দৃশ্য থেকে। হেমকুণ্ডের পাশেই আছে হিন্দু তীর্থ লক্ষ্মণমন্দির। ত্রেতাযুগে ইন্দ্রজিৎ বধের পাপস্খালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের ভাই লক্ষ্মণ তপস্যা করেন এখানে। স্মারক হিসাবে তৈরি হয়েছে মন্দির। মন্দিরে কালো পাথরের লক্ষ্মণমূর্তি ছাড়াও আছে লোকপাল, গণেশ আর মহাদেবের মূর্তি।
হেমকুণ্ড যেন একটুকরো স্বর্গ। এমন শ্বাসরোধকারী সৌন্দর্য… যদিও সে সৌন্দর্য খুব বেশিক্ষণ উপভোগ করতে পারিনি। শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। গুরুদোয়ারার লঙ্গরখানার এক কোণায় বসে পড়ি। হেমকুণ্ড দর্শনার্থীদের জন্য এখানে প্রসাদ হিসাবে সবসময় গরম গরম খিচুড়ি আর চায়ের ব্যবস্থা, যার যত ইচ্ছা খেতে পারেন। তবে নষ্ট না করাই শ্রেয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, হেমকুণ্ডে দোকানপাট কিছু নেই।
শ্বাসকষ্টে কষ্ট পেতে দেখে গুরুদোয়ারা কর্তৃপক্ষের একজন এগিয়ে আসেন উপযাচক হয়ে। সমস্যার কথা জেনে নিয়ে আমাকে বিশেষ একটি ঘরে পাঠান। সেখানে টেবিলের উপর বিভিন্নরকম ওষুধ সাজিয়ে একজন বসে আছেন। সমস্যার কথা জেনে নিয়ে দু’রকম ট্যাবলেট দিলেন। ওষুধ দুটো খেয়ে ফিরে গিয়ে আগের জায়গায় বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুম এসে গেল। ঘুম ভাঙল ঘণ্টাখানেক বাদে। তখন পুরোপুরি সুস্থ। কিন্তু বদলে গেছে বাইরের প্রকৃতি। ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে গেছে চরাচর। মাত্র দশ হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হল তুষারপাত। প্রথমে সামান্য মাত্রায় হলেও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। পেঁজা তুলোর মতো সাদা বরফ হালকা পালকের মতো অনবরত নেমে আসছে। বিদেশি সিনেমায় এধরনের দৃশ্য দেখলেও, নিজের চোখে কখনও দেখার সৌভাগ্য হয়নি। বন্ধুরা আনন্দে মেতে ওঠে। সারা গায়ে বরফ মেখে হইচই করে। ছবি তোলে। গড়াগড়ি খায়। ইচ্ছা হলেও তাদের সঙ্গে সঙ্গ দেওয়ার সাহস হয় না আমার। একটু আগের স্মৃতি এখনও আমার মধ্যে। সাধ করে আর বিপদ বাড়াতে চাই না। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছবি তুলি। গুরুদোয়ারার বাইরে বেরোই ছাতা মাথায় দিয়ে। তাতে আমার শরীর যেমন বাঁচে, ক্যামেরাটাও বাঁচে। প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে যায় এভাবে। তখনও তুষারপাত কমার কোনও লক্ষণ নেই। বরং বাড়ছে, যত সময় যাচ্ছে। আমাদের উচ্ছ্বাসও আস্তে আস্তে কমতে থাকে। বাড়ে দুশ্চিন্তা। এভাবে চলতে থাকলে ফিরব কী করে? ফেরার সময় ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত। তুষারপাত মাথায় নিয়েই ফেরার পথ ধরছে অনেকে। আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছি, এমন সময় উপযাচক হয়েই গুরুদোয়ারার এক সাধু এগিয়ে আসেন। বলেন, ফিরতে হলে এখনই বেরিয়ে পড়া উচিত। বেলা যত বাড়বে, আবহাওয়া তত খারাপ হবে। বাড়বে তুষারপাত। এটা এখানকার স্বাভাবিক চরিত্র। কখন থামবে বলা সম্ভব নয়। সারারাতও চলতে পারে। কখনও সখনও দিনের পর দিন এরকমটা চলে। এখানে আর একমুহূর্তও থাকা উচিত হবে না। গুরুদোয়ারায় থাকার ব্যবস্থা থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্যই। তাছাড়া রাতের দিকে তাপমাত্রা এমন জায়গায় পৌঁছোয় যে, যারা এখানকার কর্মী বা আবাসিক, তারাও মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্টে ভোগেন। এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।
অগত্যা পথে নামলাম। গায়ে বর্ষাতি। মাথায়, ঘাড়ে বরফ জমছে, মাঝে মাঝে সরিয়ে দিচ্ছি হাত দিয়ে। ক্যামেরা ব্যাগবন্দি করে ভরে নিয়েছি বর্ষাতির ভেতরে। ছবি তোলার মতো অবস্থা বা মানসিকতা কোনওটাই নেই। লাঠি ভর দিয়ে খুব সন্তর্পণে পা ফেলে নামতে হচ্ছে। মাত্র পাঁচ হাত দূরের মানুষও অস্পষ্ট। যাওয়ার সময় রাস্তার যেসব জায়গায় বরফ ছিল না, এখন সেখানেও গোড়ালি অবধি ডুবে যাচ্ছে। কোথাও বিশ্রাম নেওয়ার কথা মনে হয়নি প্রাণের ভয়ে, একটানা ৩ কিলোমিটার নামার পর সেই চায়ের দোকানে পৌঁছে প্রথম থামি। যাওয়ার সময় এখানে হালকা বরফ দেখেছিলাম, এখন পুরু বরফের চাদরে মোড়া। পাশের সেতুটিও সাদা। সাদা দোকানের মাথায় কালো ত্রিপলটিও। নীচেও যতদূর দেখতে পাচ্ছি সব সাদা। কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম নিয়ে, গরম চায়ে গলা ভিজিয়ে কিছুটা উষ্ণতা সঞ্চয় করার পর আবার হাঁটতে শুরু করি। টানা তিনঘণ্টা তুষারপাতের পর এবার কমতে শুরু করে, অথবা আমরা তুষারকার অধ্যুষিত অঞ্চলের বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকি। আরও ১ কিলোমিটার হাঁটার পর পুরোপুরি স্বাভাবিক এলাকায় প্রবেশ করি। ঘাংঘারিয়া এখনও দু’কিমি। রোদ উঠেছে ঝলমলে। পেছন ফিরে দেখি দূরের হেমকুণ্ড পাহাড়, সপ্তশৃঙ্গ। বিস্ময় লাগে আমাদের। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাই ঘাংঘারিয়া।
পরদিন ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হল। আসলে তেমন তাড়া ছিল না। পথ অল্প, ধীরে সুস্থে গেলেই হল। গুছিয়ে বেরোতে বেরোতে সকাল ন’টা বেজে গেল। আমাদের আজকের গন্তব্য ‘ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস্’। দূরত্ব মাত্র ৩ কিমি। এপথে ঘোড়া বা ডান্ডির চল নেই। এমনকী খাবার বা প্লাস্টিক নিয়েও প্রবেশ নিষেধ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্যেই নিয়মের এত কড়াকড়ি।
হোটেল ছেড়ে কিছুদূর এগোতেই দু’ভাগ হয়েছে– ডাইনে হেমকুণ্ডসাহিব তার বাঁয়ে ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস্। বাঁদিকে টার্ন নিতেই সামনে পড়ল জাতীয় উদ্যানের তোরণদ্বার এবং অফিস। এখান থেকে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হল মাথাপিছু ৪০ টাকার বিনিময়ে। ভিডিও ক্যামেরার ক্ষেত্রে ১০০ টাকা, স্টিল ক্যামেরার জন্যে কোনও চার্জ লাগল না।

তোরণ পেরোতেই আমরা অফিসিয়ালি ফুলের উপত্যকায় প্রবেশ করলাম। ফুলের উপত্যকা ভুইন্দর, যার পোশাকি নাম ‘নন্দাদেবী জাতীয় উদ্যান’। লোকমুখে জনপ্রিয় ‘ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস্’ নামে। ৩৫২৫ মিটার উঁচুতে ৫*২ কিমি প্রশস্ত ‘U’ শেপের এই উপত্যকার উত্তরে নীলগিরি, দক্ষিণে সপ্তশৃঙ্গ আর পশ্চিমে রতাবন– তিনদিকে বরফে মোড়া পাহাড়শ্রেণি প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে। মাঝখানে বয়ে চলেছে ঘোড়ি পর্বতের গ্লেসিয়ার থেকে জাত পুষ্পবতী নদী। সিজনে, অর্থাৎ ১৫ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রায় ৩০০ প্রজাতির অ্যালপাইনস্ ফুলের সমারোহে সত্যিই যেন স্বর্গের পুষ্পোদ্যান এই মর্তধামে নেমে আসে। ১৯৩১ সালে কামেট অভিযান করে ফেরার পথে পথ হারিয়ে ফেলেন ফ্র্যাঙ্ক স্মিথ নামে একজন বিদেশি পর্যটক। পরিত্রাণের আশায় ঘুরতে ঘুরতে একসময় তিনি এসে পড়েন এই অনিন্দ্যসুন্দর ফুলের উপত্যকায়। আবিষ্কার করেন এই ‘ফুলোঁ কি ঘাটি’। ১৯৮১ সালে এটি জাতীয় উদ্যানের শিরোপা পায়। নামকরণ হয় ‘নন্দাদেবী জাতীয় উদ্যান’।
উদ্যানের তোরণ পেরিয়ে কিছুদূর এগোলেই ইতস্তত ফুলের দেখা মিলবে। উল্লেখযোগ্য পটেনটিলা, অ্যাস্টার, জোরোলিয়াম, জুনিপার, প্রাইমুলা, বিরল প্রজাতির নীল পপি ছাড়াও অসংখ্য অ্যালপাইন। ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ। পাইন-দেওদার-ভুজ ছাড়াও আছে অসংখ্য প্রজাতির বৃক্ষ। আছে অসংখ্য প্রজাতির পাখি। আরও কিছুদূর এগোলে চোখে পড়ে একটি সমাধি ফলক। ফলকে মৃতের নাম-পরিচয় লেখা। ১৯৩৯ সালের ৪ জুলাই পা পিছলে পড়ে মারা যান লন্ডন থেকে আসা পুষ্পপ্রেমিকা তরুণী জোয়ান মার্গারেট লেগি। এখানেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়।
আরও কিছুদূর এগোলে দেখা হয় এক নদীর সাথে, নাম তার পুষ্পবতী। বোল্ডারে বাড়ি খেতে খেতে কলতান তুলে এগিয়ে চলেছে। নদীর উপরে পুল। পুল পেরিয়ে বুগিয়াল থেকে বামহাতি পথ গিয়েছে নন্দনকানন। ডানদিকে তাকালে চোখে পড়ে হেমকুণ্ড পাহাড় সহ সপ্তশৃঙ্গ। উপত্যকার কেন্দ্রবিন্দু বা ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সের প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছে কিছুটা হলেও হতাশ হলাম। এখনও সেভাবে ফুল ফুটতে শুরু করেনি, সবে কুঁড়ি আসতে শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই বিকশিত হয়ে আলো করে তুলবে এই উপত্যকা। পা ফেলার জায়গা থাকবে না। নির্দিষ্ট সময়ের ১৫-২০ দিন আগে আসাতেই বঞ্চিত হতে হল। তবে যা দেখলাম তাই বা কম কী? সামনেই রতাবন গ্লেসিয়ার, গ্লেসিয়ারের শিরে টোপর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিবলিঙ্গের মতো সুমেরু শৃঙ্গ। শিখরে রোদ পড়ে ঝলমল করছে রুপোর পাতের মতো। এলোমেলো ঘুরতে থাকি আমরা। প্রাণভরে ছবি তুলি। সারাদিন পুষ্পবতী নদীর তীরে পুষ্পোদ্যানে কাটিয়ে সন্ধ্যার আগেই ঘাংঘারিয়া ফিরে আসি।
কাল সকালেই নেমে যাব গোবিন্দঘাট। সেখান থেকে নতুন গন্তব্যে। সে গল্প অন্য কোনও সময়, হয়তো বা অন্য কোনও খানে…।
কীভাবে যাবেন –
হাওড়া থেকে উপাসনা এক্সপ্রেস বা দুন এক্সপ্রেসে হরিদ্বার পৌঁছে, পারলে সে দিনই হূষীকেশ চলে যান। হূষীকেশ থেকে বাস পেতে সুবিধা। বদ্রিনাথগামী বাসে চেপে সারাদিনের জার্নিতে বদ্রিনাথ থেকে ২৩ কিমি আগে গোবিন্দঘাটে নামুন। পরদিন গোবিন্দঘাট থেকে ঘাংঘারিয়া পর্যন্ত ১৩ কিমি ট্রেকিং। তৃতীয় দিন ঘাংঘারিয়া থেকে ৬ কিমি দূরে হেমকুণ্ডসাহিব দর্শন করে আবার
ঘাংঘারিয়া ফিরে আসা। চতুর্থ দিন সাড়ে তিন কিমি দূরে ভ্যালি অফ ফ্ল্যাওয়ার্স দর্শন করে আবার ঘাংঘারিয়া ফিরে আসা। পঞ্চমদিন নেমে আসুন গোবিন্দঘাট। পারলে সে দিনই চলে যান যোশিমঠ পর্যন্ত। আর যদি হাতে একটি দিন অতিরিক্ত সময় থাকে, বদ্রিনাথ থেকে ঘুরে আসুন।
কখন যাবেন –
১৫ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ভরা মরশুম। তবে দিন পনেরো আগে বা পরে গেলেও বিশেষ অসুবিধা নেই।
কোথায় থাকবেন –
ঘাংঘারিয়া এবং গোবিন্দঘাট– দুই জায়গাতেই থাকার জন্য পর্যাপ্ত হোটেল ও গুরুদোয়ারা আছে। গুরুদোয়ারায় থাকা-খাওয়া ফ্রি। আগে থেকে হোটেল বুক না করে গেলেও চলবে।
সতর্কতা –
সঙ্গে পর্যাপ্ত শীত পোশাক, টর্চ লাইট, বর্ষাতি, ছাতা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ নিতে ভুলবেন না। উচ্চতাজনিত শ্বাসকষ্ট থাকলে সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ওষুধ ‘কোকা-৬’ রাখতে হবে।