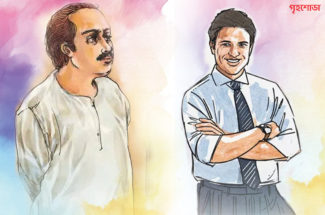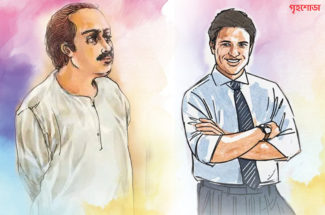গাড়িটার দুরন্ত গতি হঠাৎই শ্লথ হল। রাস্তাজুড়ে তা-ধিন-ধিনা বেতাল নৃত্য। খেয়াল করলাম, গাড়ির ভিতর আমার শরীরখানা আমার বশে নেই। নৃত্যরত পথের নেশায় সেও বেয়াড়া নাচের তালবেতালে টালমাটাল। সামনের নদী টপকানো সেতুর বুকে চাকা গড়াতেই খানিক স্বস্তি। তখন মেঘের কপাট হাট করে প্রকৃতির আঙিনা ভরে উঠেছে কনে দেখা গোধূলির লাজুক-রাঙা আলোয়। সেই আলোতেই ওকে প্রথম দেখা। ‘নরম দদাতি ইতি’ নর্মদা। মজা-নদীর অল্প জলে বিকেল-আলোর কল্পমায়া। পুরাণকথায়, শিবের মানসপুত্রী নর্মদার জন্ম এই শিবভূমি অমরকণ্টকেই। মেখল পাহাড়ের কোলে নিসর্গ আর ধর্মের সমাহারে অমরকণ্টক হিন্দুদের কাছে এক পুণ্যতীর্থও বটে।
হোটেল আগে থেকেই বুক করা ছিল। ক্লান্তিহরণ বিছানাটাও তৈরি ছিল আমার জন্য। আজ আর বেরব না। কেবল হোটেল মালিকের সাহায্যে কালকের ভ্রমণের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা পাকা করে নিলাম।

প্রকৃতি তখনও অন্ধকারের ওড়নায় ঘুমাচ্ছন্ন। আমার গাড়ি ছুটল সোনমুড়ার দিকে। অমরকণ্টক থেকে দেড় কিলোমিটার। মধ্যপ্রদেশের আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন। তাই রাতে আর ভোরে বেশ ঠান্ডা লাগে। গাড়ি-জানলার বন্ধ কাচে চোখ পেতে দেখি অল্প অল্প করে ঊষার গল্প শুরু। অজস্র বীরপুংগবদের উৎপাত উপেক্ষা করে গাড়ি থামল সোনমুড়ায়। সূর্যোদয় দেখার আদর্শ স্থান। পুবের আকাশ ফরসা হল কিছুটা। পিচরাস্তা ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম সানরাইজ পয়েন্টে। দূরের দিগন্তে তখনও পৌঁছোয়নি পাখির ডাক। গাছের পাতাগুলো সদ্য জন্ম নেওয়া শিশু-আলো গায়ে মেখে সবেমাত্র হাই তুলছে। একটি-দুটি লোক সমাগমে ভরে উঠছে সানরাইজ গ্যালারি। সময় এল। জবাপুষ্পের মতো লোহিতবর্ণে সেজে সূর্য উঠল। নীল কপালের মাঝখানটিতে মঙ্গলটিপ এঁকে যেন ভৈরব-যোগী ভোর সামনে এসে দাঁড়াল।
সানরাইজ পয়েন্টটা অতল খাদের বুকে ঝুলন্ত বারান্দার মতো। বাটির মতো পৃথিবীটার বুক সেজেছে সবুজ-ঘন সবুজের রং-বিসারী খেলায়। যত দূরে গেছে, সবুজ ততই নীলচে হয়ে কুয়াশায় মিলিয়েছে। সোনমুড়ায় শুধু সূর্যোদয় নয়, গল্প আছে আরও। সানরাইজ গ্যালারি যাবার পথে ডানহাতে বজরংবলীর বিরাট মূর্তি। তাকে ফেলে এক কুণ্ড। অবিরত জল এসে জমা হচ্ছে সেখানে। অদ্ভুত ব্যাপার! কেউ জানে না সেই জলের উৎস কোথায়? এটাই সোন নদের উৎস। জনশ্রুতি, ব্রহ্মার চোখের জল থেকে এর উৎপত্তি। এখানকার শিবলিঙ্গটিও স্বয়ম্ভু অর্থাৎ আপনা-আপনিই মাটি ফুঁড়ে আবির্ভাব হয়েছে। পাশেই উঠে যাওয়া সিঁড়ি টপকে দুর্গামাতার মন্দির। সাজগোজ-অলংকারে বৈষ্ণোদেবীর মতো। সকালের আরতি সমাপন। চোখ জুড়োল। মন্দিরের পাশে পর্ণকুটিরে এক সাধু ও তার সাধনসঙ্গিনী আপন মনে গান গেয়ে চলে দিবানিশি। ওদের, সংগীতেই মুক্তি ও সংগীতেই শান্তি।
সোন নদ আর নদী নর্মদা। যোগসূত্র খুঁজতে গেলে ডুব দিতেই হবে গপ্পো-কথায়। সোনভদ্র ছিলেন একজন সন্ন্যাসী-রাজপুত্র। আর নর্মদা ছিলেন শিবপুত্রী মতান্তরে মেখলরাজার মেয়ে। বিবাহ স্থির হয় দুজনের। বরযাত্রীরা এসে বিশ্রাম নেন অমরকণ্টক থেকে কিছুদূরে বরাতি ধাম বা বরাতি গ্রামের অক্ষয় বটের নীচে। যে-গাছটি আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। কিন্তু নর্মদারই এক সহচরী সুযোগ বুঝে নিজের মোহিনী রূপে সোনভদ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সোনভদ্র ভাবেন ইনিই বুঝি নর্মদা। সবকিছু জানাজানি হতে নর্মদা ক্ষুব্ধ হন। উন্মত্ত উন্মাদিনী হয়ে ছুটতে থাকেন। কপিলমুনি প্রবোধ দেন। কিন্তু নর্মদা সে বাধা অগ্রাহ্য করে পশ্চিমে ছোটেন। শোকে-দুঃখে সোনও চলতে থাকেন উত্তরে। পরস্পরের অভিশাপে দুজনেই জলরাশি হয়ে আজও ছুটে চলেছে পাগলপারা। এরও দ্বিমত আছে। সোনমুড়াতেই ধাবা আছে প্রচুর। পোহা (এক ধরনের চিঁড়ের পোলাও)-র স্বাদে সাতসকালের জলযোগ সেখানেই।
দেখা-না দেখার ভাব-ভালোবাসায় আবার আমি পথের সাথি। ছায়া সুনিবিড় বনপাহাড়ি পাকদণ্ডি পেরিয়ে মাই-কি-বাগিয়া। বাংলায় অর্থ মায়ের বাগান। শান্ত, সবুজ, শীতল পরিবেশ। কথিত আছে, নর্মদা এখানে তার বাল্যসহচরীদের সঙ্গে খেলতেন। স্থানীয় মানুষ এখানে শিব আর নর্মদার পুজো করে যান।
বেলা বাড়ছে। রোদের তাতে আগুনের ইশারা। এবার অমরকণ্টকের খ্যাতির কেন্দ্রবিন্দু দর্শন। সাতাশ মন্দির কমপ্লেক্স। প্রবেশতোরণই চোখ টেনে নেবে। ১৯৩৯ সালে রেওয়ারাজের তৈরি কারুকলা বিন্যস্ত প্রবেশতোরণটি বর্তমানের মতোই ঝকঝকে। জুতো খুলে খালি পায়ে দেবদেউলের বুকে। পায়ের তলায় যেন উত্তপ্ত কয়লার চুম্বন। খানিক চকিত হরিণের মতোই লাফাতে লাফাতে মূল মন্দিরের অন্দরে।
১৯২৯-এ ইন্দোররাজের উদ্যোগে এই মন্দিরটির সংস্কার হয়। গর্ভগৃহে তিন ফুট উঁচু কষ্টিপাথরের মূর্তি রয়েছে নর্মদা মায়ের। এটাই মূল নর্মদা মন্দির। নবম শতকের রেওয়ারাজা গুলাব সিং এই মন্দিরের নির্মাতা। দেবীর ঘরে ক্যামেরার প্রবেশ নিষেধ। মন্দিরের পাশেই ভক্ত-মানুষের আজব কাণ্ড। একটা পাথরের হাতির তলা দিয়ে সাষ্টাঙ্গে গলে যাবার কী সাংঘাতিক প্রচেষ্টা। একবারে গলে যেতে পারলে পাপক্ষয় হয়, এমনই বিশ্বাস। স্থূলকায় মহিলাটির কপালটাই খারাপ। মাথা, বুক, পেট কোনওরকমে গলে গেলেও বেঢপ কোমরখানা নিয়ে তার বিপত্তির অন্ত নেই। দুজন মহিলা পিছন থেকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও তেনাকে গলাতে পারছেন না। তারা যত ঠেলে হাতিও তত পাথুরে গতরের ফাঁকে চেপে ধরে। ‘তুইও নাছোড় মুইও নাছোড়’ গোছের অবস্থা। ঠিক এরই পাশে স্বচ্ছ জলের কুণ্ডে কিছু মানুষের শান্তির অবগাহন। কেউ আবার পুণ্যবারি ঠাসা বোতলের ছিপিটাতে বেশ কষে মোচড় দিচ্ছেন। হাতে-পায়ে-মাথায় পবিত্র বারি বর্ষণেই কারও শান্তি। যার যেখানে মনের তৃপ্তি। মূল মন্দিরকে বেষ্টন করে আছে কার্তিকেয়, অন্নপূর্ণা, শিব, সূর্যনারায়ণ, ভাঙেশ্বর, রাম-জানকী এমনই কত মন্দিরগুচ্ছ। সঙ্গে আরও একটি ছোট্ট কুণ্ড– নর্মদা মাই কি উদগম। নদী নর্মদার সৃষ্টি এখানেই। কিন্তু কীভাবে? কেউ জানে না। সোনের মতো এর উৎসও অজানার অন্তরালে। পুরাণে ব্যাখ্যা আছে, প্রমাণ নেই। প্রতি সন্ধেয় আলোর সাজ পরে মোহিনী হয়ে ওঠে এই মন্দির। নর্মদার পুজো হয় এই কুণ্ডে। সমবেত মন্ত্রসংগীত আর পুণ্য করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে রাতের অমরকণ্টক।
পিচরাস্তার যে পাশে সাতাশ মন্দির কমপ্লেক্স, ঠিক তার উলটোদিকেই শ্যামল শোভায় কালচুরিদের কাল আজও জীবন্ত। মহারাজা কর্ণদেবের হাতে তৈরি পাতালেশ্বর শিবমন্দির। সাধুসন্তের পীঠভূমি এই স্থানে মৃত্তিকাগর্ভে জলের তলায় দেবাদিদেব স্বমহিমায় বিরাজমান। হারিয়ে যাওয়া অতীতের পাতা উলটোলে দেখা যাবে একসময় এখানকার পুরো অঞ্চলটা জুড়েই বেণুবন অর্থাৎ বাঁশবন ছিল। তাই এখানকার শিবকে বেণেশ্বর শিবও বলা হয়। মন্দিররাজির বেশ কিছু ভগ্নপ্রায়। তবু সবুজ গালিচার বুক ছাপানো মেটেরঙা পাথরের বর্ণবৈপরিত্য দেখার মতো। হাতের স্পর্শে কথা বলে ওঠে অনুপম ভাস্কর্যেরা।
উদরপুরে হাঁক উঠতেই রিস্ট ওয়াচে চোখ। দেড়টা বাজতে যায়। ড্রাইভার নিয়ে গেল ভাত-রুটির হোটেলে। ধর্মের আঁতুড় ঘরে মাছ-মাংস নিষিদ্ধ। তাই নিরামিষ আহারেই ক্ষুধানিবৃত্তির তোড়জোড়। তারপরেই চলে যাওয়া পথের পাশের পঞ্চমুখী গায়ত্রী বা মার্কণ্ডেয়াশ্রম। মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টক যতই রুখাশুখা হোক, এর শিল্পকলা ভ্রামণিকদের মনে রসসঞ্চার করবেই। মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্যাস্থলও এর ব্যতিক্রম নয়।
তীর্থরাজ অমরকণ্টকে দেখার শেষ নেই। বেলা দ্বিপ্রহরের বেশকিছু পর গাড়ি ছুটল কপিলধারার দিকে। সেখানে নর্মদার উচ্ছল রূপ! সময়টা যদিও গ্রীষ্ম ছুঁইছুঁই। জলের ধারা কেমন থাকবে জানা নেই। অমরকণ্টক থেকে ছ’কিলোমিটার দূরত্বে গাড়ি থামল। দু’পাশ জোড়া প্রকৃতির খোলা খাতা। সারে সারে টুকিটাকির অস্থায়ী দোকান। মাঝখানের রাস্তাটা ঢালু হয়ে সোজা নেমে গেছে। মাথার উপর নীল চাঁদোয়ায় বেলা শেষের চড়া তাত। জায়গা কপিলবন। হাঁটাপথে পৌঁছোতে হবে কপিলধারার কাছে। সোজা নেমে ডানহাতে সেতু পেরিয়ে মেঠো-রাস্তার বাঁক। একপাশে গভীর খাদ, অন্যপাশে গাঢ় সবুজের নিগূঢ় আলিঙ্গন। দুর্গম পথ, অন্তত আমার চোখে। বড়ো বড়ো পাথর, হঠাৎ হঠাৎ ক্ষয়ে যাওয়া মেঠো-ধুলোর গহ্বর। কখনও খাড়া হয়ে নেমেছে কখনও বা আঁকাবাঁকা। আগাছার জঙ্গল মাড়িয়ে প্রায় শতখানেক সিঁড়ি। বক্ষপিঞ্জরে প্রবল শ্বাসটান। তবু রোমাঞ্চের বিরাম নেই। দারুণ লাগছে। অবশেষে পৌঁছোলাম। মাথার উপর খোলা আকাশ বটে, তবু এখানে রোদের খুব একটা ছাড়পত্র মেলেনি। চোখ তুলে গোল করে নিজের চারপাশটাকে দেখলে পৌরাণিক পুঁথির অনুভূতিগুলো ঘিরে ধরে। পাহাড়-প্রাচীর, ঘন সবুজের গহিন মিছিল, নিভৃত গুহা, ভস্মমাখা সাধুর সাধন, বাঁপাশে লাফিয়ে নামছে কপিলধারা, ডান-হাতে কিছুটা নেমে তারই জলের আর এক অংশ নামছে দুগ্ধধারা বা দুধধারা নামে। কপিলমুনির সাধনক্ষেত্র ছিল এই স্থান, তাই এখানে গড়ে উঠেছে কপিলাশ্রম। ঝরনাটারও তাঁর নামে নিত্যি ঝরে পড়া। বোল্ডার টপকে কাছে গেলাম। নিষেধ আছে, তবুও। জলকুচিতে একটু ছোঁয়া, না ভিজেও ভেজা ভেজা আভাস, অনেকটা ভালোলাগা আর বিপুল রোমাঞ্চ। খাড়া পাহাড়ের গায়েই ঝরনার উচ্ছলতাকে তোয়াক্বা না করেই অজস্র চাকে ঘর বেঁধেছে মউপিয়াসীদের দল। এই কারণেই ঝরনার কাছে আসা মানা। পঞ্চাশ ফুট উপর থেকে ঝরনা ঝরছে পাথরের ওপর। কতক্ষণ যে চুপ করে দাঁড়িয়ে ওই বৃহতের সামনে নিজের ক্ষুদ্রতাকে অনুভব করেছি খেয়াল নেই। ফিরলাম দুগ্ধধারার কাছে। এক নদী নর্মদা, তবু রূপ তার ভিন্ন। দুগ্ধধারা তাঁর ক্ষুদ্র শরীরটাকে অনুচ্চ পাথরের উপর থেকে ঝরিয়ে দিয়ে অন্য অন্য পাথরের আড়াল খুঁজে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। পুরো রাস্তাজুড়ে এমনই লুকোচুরি খেলছে নর্মদা। এই আছে এই নেই। আসছে বা কোত্থেকে? যাচ্ছেই বা কোথায়?
আজ শেষবারের মতো শান্ত নর্মদার বুকে মুখ রেখেছে অস্তগামী সূর্য। নদীর জল অবেলার আলোটাকে বুকে আগলে তিরতিরিয়ে মিলিয়ে গেল। ছায়া নামল পাহাড়ে-অরণ্যে-গুহায়। ফিরতি পথে দুর্গম চড়াই চড়তে চড়তে কানে এল বুনো গন্ধের মজলিসে ছমছমে ঝিল্লি-ঝনক। সন্ধের কূলে যখন আমার গাড়ি ভিড়ল, অমরকণ্টক তখন আলোয় আলোকময়। নর্মদার পুজোয় মন্ত্রোচ্চারণের দেহাতি সুর, আমায় ঘিরে ছুটে বেড়াল অমরকণ্টকের বাতাসে।
পরদিন সন্ধেবেলায় পেন্ড্রা স্টেশন থেকে জব্বলপুরের ট্রেন। তাই সেদিন সকাল-সকাল ভৃগু কমণ্ডলুর কাছে যাওয়া। আকাশখোলা প্রান্তরে একটিমাত্র গাছ। তার ছায়াতেই গাড়িটাকে বিশ্রাম দিয়ে গাইডকে সঙ্গে নিয়ে এগোলাম। এ’পথে গাইড নিতেই হয়। তবে আমার গাইডবাবাজির মতো বেআক্বেলে আর দুটি নেই। কোথায় আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবে তা না, নিজেই তরতরিয়ে বিরাট বনভূমির মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। আমিও খানিক হাঁটি তো খানিক দৌড়োই, থেকে থেকে জিভ ঝুলিয়ে হাঁপিয়ে মরি। ঘন শালের বন। তার বুক ফুঁড়েই চলা। পায়ের নীচে শুকনো পাতার মর্মরধবনি। কানের কাছে অচিন পাখির সুর। পাতার ফাঁকে সোনার আলোর ঝিকমিক লুকোচুরি। জঙ্গল ট্রেলে গাড়ি চেপে ঘোরার চেয়ে এ ঢের বেশি ভালো। উঁচু-নীচু, ঢাল-সমান কতরকম পথের বাহার! অবশেষে ছোট্ট এক আশ্রম, ধুনিবাবার আখড়া। একটিমাত্র অর্ধ উলঙ্গ সাধুবাবার সামনে ধুনির অনির্বাণ প্রজ্জ্বলন। ভীষণ শান্ত, নিস্তব্ধ। পরিবেশটাই একটা ইলিউশন সৃষ্টি করেছে। ওঁর কাছ থেকেই শুনলাম চণ্ডীরূপা দেবীর কথা। সে পথে সাধুসন্ত ছাড়া আর কেউ না কি যেতেই পারে না। মনে জেদ চেপে গেল। কী এমন পথ যে, তারা যেতে পারে আর সাধারণ মানুষ যেতে পারে না! পৌরাণিক কালের মতো ফুসমন্তর হয়ে তো আর তাঁরা সে পথে চলে যান না। দেখাই যাক। গাইড কিছুতেই যাবে না। ‘হাম উধার নেহি যা সকতে’। আমিও পণ করেছি, যাবই।
যেতে যেতেই বনের গহিনে দেখা ভৃগুমুনির তপস্যাস্থল। একটা বিরাট পাথর। আকৃতিটা কমণ্ডলুর মতো। গায়ের গর্ত দিয়ে হাত গলিয়ে জল ছুঁতে পারলে তাঁর মতো ভাগ্যবান আর হয় না। দিলাম গলিয়ে হাতখানাকে। অমনি কপালজোড়া ভাগ্য আমায় ভেংচি কেটে বলল, ‘এ মা! আমায় ধরতে পারে না!’ না পারি তো বয়েই গেল। চললাম চণ্ডীরূপার দর্শনে। চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অনেকটা গিয়ে পথের শেষ খাদের ধারে। যাঃ! রাস্তা কই? গাইড দেখাল, ‘উও দেখিয়ে রাস্তা’। চোখ মেলেই দেখি সামনে অনন্ত অতল গিরিখাদ। তারই পাশে পাহাড়ের গায়ে সরু ফিতের মতো একটা রাস্তা যেন চলে গেছে। তাও আবার বাঁক নিয়েই মিলিয়ে গেছে। একবার পা হড়কালে চণ্ডী থেকে চণ্ডমুণ্ড কারও সাধ্য নেই আমায় বাঁচায়। সুতরাং বিফল মনোরথে ফেরা।
মাই-কি-মাড়োয়া– তেমন একটা যায় না কেউ। রুখা প্রান্তর, শুখা অরণ্য ফেলে অনেকটা পথ। পৌঁছোলে আবার অন্য ছবি। বিশ্বপ্রকৃতির নিবিড় চুম্বনে শ্যামল আলিঙ্গন। চড়ুইভাতির আদর্শ জায়গা। বিশাল বিশাল পাথরের মাথা ডিঙিয়ে নর্মদার পাড়, সেখান থেকে গুহাগহ্বরে পা ফেললেই নির্জন ছায়ায় মহাদেবের একান্ত যাপন। কবীর চবুতরাতে তেমন কিছু নেই। বিকেলে পেন্ড্রা যাবার পথে আরও এক অচেনা ঠিকানা। একজায়গায় গাড়়ি থামিয়ে আমি আর ড্রাইভারভাই পায়ে পায়ে এগোচ্ছিলাম জনশূন্য অরণ্যের বিজন প্রান্তরেখা ধরে। কী যেন একটা লুকিয়ে আছে। প্রথমে গম্ভীর শব্দ কানে এল। তারপর রূপের উজানে মনচুরি পালা। জংলাপাতার ফাঁকফোকরে আদিম কন্যের ঢালা লাবণ্য। শম্ভোধারা। পায়ের নীচের ঘাস জমিনটা হঠাৎই ফুরিয়ে যাবে। পাহাড়ের ঢালু শরীর ঘেঁষে সরু ধাপ কাটা রাস্তা। সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়েই পাতাবিহীন গাছের শক্ত ডালটাকে ধরে নেওয়া। তারপরেই তরলিত চন্দ্রিকা চন্দনবর্ণা ঝরনা।ঞ্জঅনাঘ্রাত শম্ভোধারার সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন প্রথম বুঝেছি ‘আদিম’ শব্দের প্রকৃত অর্থ।
জব্বলপুর পৌঁছোতে রাত তিনটে। সকালের আলো ফুটতেই অটো নিয়ে রেস্ত বুঝে হোটেল নিলাম। পোহা জলযোগে পেটপূর্তি সেরেই বেরিয়ে পড়া। কাছেই রানি দুর্গাবতীর মিউজিয়াম। অন্দরে চকচকে কাচ-আলো আর রকমারি সৃজনবাহারে ইতিহাসও যেন জেগে উঠেছে। পাথরমূর্তি, অস্ত্রশস্ত্র, পুতুলছবিতে তৎকালীন জনজীবন, রানি দুর্গাবতীর মূর্তি সবকিছুই চমৎকার সযত্নে সজ্জিত। ভারতীয় পর্যটকদের জন্য দশ টাকায় ফেলে আসা অদেখা দিনগুলোয় ফিরে যাওয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য।
জব্বলপুর মানে পাথরের শহর। ভাড়া করা অটোটা যখন রাস্তা মাতিয়ে ছুটছে, তখন চারপাশে শুধু প্রস্তর স্বাক্ষর। চলে আসা ব্যালেন্সিং রকে। এক পাথরের বুকে অন্য পাথরের চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকা। মাত্র একটি বিন্দুতে ভর করে। এ এক আশ্চর্য প্রাকৃতিক সার্কাস। পাশেই রানি দুর্গাবতীর স্মৃতি আঁকড়ে মদনমহল দুর্গ। গোন্ড রাজাদের স্মৃতিকথার ফলক ফেলে চড়াই সিঁড়ি টপকে মহলের চৌহদ্দি। চত্বরের একপাশে ভাঙা ঘরের সারি। অন্যপাশে সদম্ভে রাজৈতিহাসিক ধবজা হয়ে দাঁড়িয়ে খাঁখাঁ মদনমহল দুর্গটা। ছাদের ওপর থেকে শহরের পুরো ছবিটাই দেখা দেয় পাখির চোখে। অটোয় চেপেই হুকুম ছুড়লাম, ‘ভাইসাব, ত্রিপুরী গাঁও চলিয়ে।’
‘ত্রিপুরী? অ্যায়সা তো কোই ভি গাঁও নেহি হ্যায় ইঁহাপর।’
অ্যাঁ! ব্যাটা বলে কী? স্পষ্ট বইতে পড়ে এলাম ত্রিপুরী গ্রামের কথা। সেখানে না কি সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। কুষাণকালেরও কত কী ইতিহাস রয়েছে শুনেছি। অবিশ্যি এইসব ইতিবৃত্তান্ত অটোভাইকে বলা বৃথা। সে পথ-অপথের হদিশ ছাড়া কিছুই বোঝে না। ত্রিপুরী গ্রাম খুঁজে পাওয়া গেল না। কিন্তু পেলাম যা তাতেই মন ভরে গেল। শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে এক অখ্যাত গ্রাম। নাম তেওয়ার। আগের নাম হাতিয়াড়া। এখানেই রয়েছে বিশাল ত্রিপুরসুন্দরী মন্দির। হয়তো এটাই অপভ্রংশে ত্রিপুরী। নাটমন্দিরটাই দেখার মতো। ঘটা করে পুজো হয়। স্বর্ণালংকারে শোভিতা দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর মূর্তিটি সপ্তম শতাব্দীর। ঘণ্টাধবনি আর কীর্তনের সুরে দেবদেউল পরিপূর্ণ। মন্দিরজুড়ে রং-আলাপী কারুকাজ।
ভরদুপুরের ভরাপেটে থামলাম গিয়ে গোলকি মঠে। চত্বরটা গোলাকার তাই এমন নাম। এটাই চৌষটযোগিনীর মন্দির। মধ্যপ্রদেশ জুড়ে কেবল সিঁড়ি আর সিঁড়ি। মালাইচাকিটা খুলে এবার হাতে আসার জোগাড়। তার ওপর চাঁদি ফাটা রোদ্দুর। মাঝখানের মূল মন্দিরকে ঘিরে চৌষট্টিজন যোগিনীর অধিষ্ঠান। অনেক মূর্তিই সময়ের ভারে ন্যুব্জ হয়ে ক্ষয়ে গেছে। মাঝের গর্ভমন্দিরে কষ্টি পাথরের মূর্তিতে স্বয়ং শিব বিয়ে করে দেবী পার্বতীকে নিজ আলয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ঐশ্বরীয় বন্ধনের ঊধের্ব উঠে ভাবনার অভিনবত্বই অজানা শিল্পীর উন্নত শিল্পচিন্তাকে চিনিয়ে দেয়।

এবার দুই পাহাড়ের মিলে নর্মদার জলে ভাসানিয়া গান। দুটো পাহাড়ের মিলন তাই নাম ভেরাঘাট। শহর থেকে তেইশ কিলোমিটার। ঘাট ছোঁয়ার সিঁড়িপথে পাথরকাটা শৌখিন দ্রব্যসম্ভারের ঢালাও পসরা। ভেরাঘাট-ই মার্বেল রকস। চাঁদনি রাতের রুপোলি আলোয় জলছোঁয়া উত্তুঙ্গ পাহাড়-প্রাচীরগুলোর গায়ে চলে মায়াবী বায়োস্কোপ। ঘাট থেকেই পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় নৌকো ভাসে নর্মদার টলটলে শরীরে। দাঁড়ে জল কাটে ছলাৎছল। মাঝির মুখে কাব্য ফেনিয়ে ওঠে অনর্গল। কবিতার সুরে চিনে নেওয়া যায় এই জল-দুনিয়ার পাহাড়-প্রকৃতিকে। ম্যাগনেসিয়াম আর চুনাপাথর-পাহাড়ের গলতা বেয়ে নৌকো চলে একের পর এক। সাদা-কালো-সোনালি রং বদলায় পাথরের। এক জায়গায় উত্তাল নর্মদা প্রবল উল্লাসে লাফিয়ে নামছে মার্বেল রকসের জলে। নামতেই উধাও তার উচ্ছলতা। তখন শান্ত বুকের অতল, সেজে ওঠে পান্না-সবুজ গভীরতায়। কেবল নৌকোর চলায় চঞ্চল হয় সে।
ভেরাঘাটের কিনারায় অস্তরাগের চুম্বন। ভক্তমনের ইচ্ছেপ্রদীপ ভেসে যায় অলক্ষে। দিন ফুরোয়। সোনায় সাজে নর্মদা।
সকাল ফুটেছে অনেকক্ষণ। আনকোরা নতুনের অভিষেকে আজকের দিন শুরু। শহর থেকে খানিকটা পথ। কচনর সিটি। ছাইরঙা প্রবেশতোরণে হলদে তুলির চোখটানা কাজ। ভিতরে ঝিরিঝিরি পাতার সবুজ গন্ডি-টানা দারুণ একটা জায়গা। চারপাশের পাথরমূর্তিতে সাধু, ঋষিবরগন, দেবতাকূল শিববন্দনায় রত। মাঝখানে কোনও এক বাঙালি স্থপতির তৈরি বিশাল ধ্যানমৌন মহাদেবের মূর্তি। শান্ত, সৌম্য পরিবেশটাই মুগ্ধতা বয়ে আনে মনগহনে।
এরপরেই রাস্তা মেশে পিসান হরিজৈন টেম্পল-এ। দীর্ঘ স্থান জুড়ে জৈনমন্দিরের অভাবনীয় বৈভব। বাহুবলীর আকাশছোঁয়া প্রস্তরমূর্তি, অন্দরে কাচের আলংকারিক বাহার, আলো প্রতিবিম্বিত চকচকে জৈনদেবতার আবক্ষ মূর্তি, স্থাপত্য-ভাস্কর্য সবখানেতেই শিল্পের অনন্য প্রকাশ। দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে যায়। জব্বলপুরের শেষ গন্তব্য ধুঁয়াধার জলপ্রপাত।
‘শিল্পী, তোমার ঠিকানা কোথায়? কত দুর্গের উঠোন আর রাজমহলের অন্দর পেরিয়ে এলাম। কই, স্বচক্ষে তোমাকে তো দেখলাম না।’
নম্রকণ্ঠে উত্তর আসে, ‘কোনও বৈভব-তো আমার ঠিকানা নয় বন্ধু। আমি থাকি আকাশনীল খোলা ছাদের তলায়, একখণ্ড মাটির ওপর’– কাল্পনিক সংলাপটা আমার আর ওই মানুষগুলোর মনে মনেই রইল। ওরা রোজ ধুঁয়াধারে যাবার পথের একধারে বসে নরম সাদা পাথর কেটে বানিয়ে চলে রকমারি শৌখিন জিনিস। কেউ কেনে, কেউ কেনে না। কেবল চোখের দেখা দেখে আমারই মতো হেঁটে চলে যায় ঝরনার দিকে। প্রথমেই রোপওয়ে চেপে ধুঁয়াধারকে পেরিয়ে ওই পারে। রোপওয়ের মাথার ওপরের চাকাটা ঘুরে যেতেই আমি যেন দুটো ডানা পেলাম। পায়ের নীচে সগর্জনে নর্মদারূপী মহাকালের পতন। মাথার ওপর হাত বাড়ালেই আগুনতাতা নীল আকাশ। ওপারে পৌঁছে খানিক বিরতি। এবারে এক্বেবারে কাছ থেকে উত্তাল নর্মদার যৌবনগম্ভীর ধুঁয়াধার রূপ। পাথর ছাপিয়ে উদ্দাম ফল্গুধারায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে ১২০ ফুট উঁচু থেকে। যেন এক জলীয় তাণ্ডব। ঝরনার গা ছুঁয়ে উড়ছে ধোঁয়া ধোঁয়া জলের কুচি। তারই মাঝে রঙিন পথরেখায় রামধনুর উঁকিঝুঁকি। জলের তোড়ে পাথর ক্ষয়ে নদীবুকে এক নন্দিমূর্তি। রোপওয়ে চড়ে আবার ফিরে আসা এ’পাশে। হঠাৎই চোখের পাতায় ধাক্বা লাগল যেন। খানিক্ষণ ধরেই একটি পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে ঝরনাপাহাড়ের গায়ের রেলিং ধরে ঘুরঘুর করছিল। আচমকাই ওই বিপুল জলের বুকে ঝাঁপ দিল। মুহূর্তে হূদপিণ্ডে এক দমকা বাতাস স্তব্ধ করে দিল আমায়। কী হল? কোথায় গেল ছেলেটা? পুরোপুরি বোঝার আগেই মাকড়সামানুষের মতো পাহাড় বেয়ে সপসপে ভিজে শরীরে আমাদের সামনে উঠে এল ছেলেটি। তারপরেই দাঁড়িয়ে থাকা প্রকৃতিমগ্ন পর্যটকদের কাছ থেকে কুড়ি টাকা আদায় করল। এটাই ওদের পেট চালানোর নিত্য খেলা। কেউ দিল, কেউ দিল না। বয়েই গেল তার। আবারও ঝাঁপ, আবার সাঁতার, আবারও উঠে এসে রিক্ত-সিক্ত হাতটাকে মেলে ধরা সকলের সামনে, ‘বাবু, বিশ রুপিয়া দে দিজিয়ে না’। ওরা রুদ্র নর্মদাকে বন্ধু করেছে, দুর্গম পাহাড়কে সোপান করেছে আর জীবন ওদের নির্লজ্জ করেছে…
তাই-তো ওরা নর্মদার মতো বারবার হারিয়েও বেঁচে ওঠে প্রতিবার।
কীভাবে যাবেন – প্রথমে হাওড়া থেকে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস, হাওড়া-মুম্বই মেল, আজাদ-হিন্দ এক্সপ্রেসে চেপে বিলাসপুর। তারপর সেখান থেকে অমরকণ্টকগামী বাস বা গাড়ি ভাড়া করে অমরকণ্টক। অমরকণ্টক থেকে গাড়ি ভাড়া করে ৪৩ কিলোমিটার দূরের পেন্ড্রা স্টেশন। সেখান থেকে জব্বলপুরগামী ট্রেনে জব্বলপুর পৌঁছোন।
কোথায় থাকবেন – অমরকন্টকে থাকতে পারেন মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের হোটেল হলিডে হোমস। এছাড়া আরও হেটেল আছে।
জব্বলপুরে থাকতে পারেন মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের হোটেল কালচুরি রেসিডেন্সি। বেসরকারি হোটেল আছে সারা শহর জুড়ে। যাবার আগে অবশ্যই ফোন নম্বর ও ঘরভাড়া চেক করে নেবেন। কারণ দুটোই পরিবর্তনশীল।