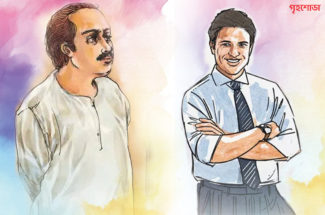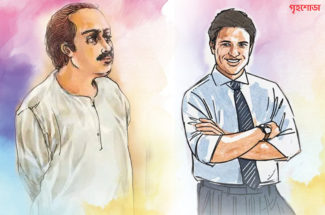একটা ‘হ-য-ব-র-ল’ পাকিয়ে দিনটা শুরু। আপ মজফ্ফরপুর ফার্স্ট প্যাসেঞ্জারে টিকিট। উঠব ব্যান্ডেল জংশন থেকে। অনেক আগে থেকেই অপেক্ষা করছি। লেট না খাইয়ে ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ইন করল। কিন্তু এমাথা-ওমাথা ছুটোছুটি করেও, সংরক্ষিত কামরার অস্তিত্বই পেলাম না। পিছোতে বলে কেউ, তো অন্যরা সামনে। যাক, সামনে চলে এসে পিছোতে যাব, ট্রেন ছেড়ে দিল। নিখুদাকে বললাম, বুদ্ধি খাটাও এতগুলো লোক ছুটোছুটি করব যশিডি পর্যন্ত। আউট না দেওয়া আম্পায়ারের মতো নিখুদা দাঁড়িয়ে রইল। কী মনে হল আমার, রুকস্যাকের সাইড পকেট থেকে টিকিটটা বার করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ওই কামরাতেই সিট মিলিয়ে-মিলিয়ে জায়গা করে নিলাম। কোনও ক্ষেত্রে লোকজনদের তুলে আবার কোনও-কোনও ক্ষেত্রে সাইড করে। তারা তো বুঝতেই পারছে না, কোথা থেকে এই কামরা রিজার্ভ হল? খুব খারাপ লাগছিল ছলনার আশ্রয় নিয়ে এভাবে জায়গা দখল। এই হয়রানির জন্য কি অভিযোগের আঙুল তোলা যায় না, ভারতীয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতার প্রতি?

যশিডিতে ট্রেন থেকে নেমে মনের খচখচানিটা দূর হল। বারবেলা পার না করে ফুড প্লাজায় ঢুকে পড়লাম। তারপর নিখুদা’র সঙ্গে দুটো অটোওয়ালার কি অর্থচুক্তি স্বাক্ষরিত হল বলতে পারব না, তবে কালকের লোকাল সাইট সিয়িং-এর ব্যাপারটা নিশ্চিত হল।
দেওঘরের ল্যান্ডমার্ক ক্লকটাওয়ার। হোটেলের অবস্থান তার আশেপাশেই। আমরা বাজারের হৈ-হট্টগোল এড়াতে টাওয়ার চকের আগেই হোটেল নিলাম। একটু ফ্রেশ হয়েই চক্বর কাটলাম প্যাঁড়া গলি দিয়ে। ধাক্বাধাক্বি হয়েও গেল কলকাতা বাবু-বিবিদের সঙ্গে।
আলো ফুটতেই হাজির মন্দিরে। যাঁর নামে খ্যাত এই শহর সেই বৈদ্যনাথ শিবের মন্দির ও সংলগ্ন চত্বরটি বিশাল। এই সাত-সকালেই পুণ্যার্থীদের ভিড় উপচে পড়ছে। পান্ডার সাহায্য ছাড়া এখানে পুজো দেওয়া অসম্ভব। তুলনামূলক বয়স্ক এবং অর্থের চাহিদা কম এমন একজন পান্ডাকে সন্ধান করে বার করা হল। কিন্তু মন্দির চত্বরে বসে পুজোপর্ব ও মন্দির অভ্যন্তরে বিগ্রহ দর্শন সব মিলিয়ে– তিনি যা দাবি করলেন, তা শুনে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। ধর্মের নামে এই অর্থদণ্ড দিতে আমরা নারাজ। তবে তিরুপতি মন্দিরের কথা ভাবলে, এই অর্থদণ্ড যৎসামান্যই বলা যায়।
শ্রাবণ মাসে এই শহর হয়ে ওঠে গেরুয়া শহর। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর চাপে মন্দির চত্বরে প্রবেশ অসম্ভব হয়ে ওঠে। পুণ্যার্থীরা সুলতানগঞ্জের গঙ্গা থেকে জল নিয়ে ১০৫ কিমি রাস্তা অতিক্রম করে এখানে হাজির হন। মনস্কামনা পূরণের আশায় তাঁরা বাবার মাথায় জল ঢালেন। পুরাণে আছে রাক্ষসরাজ রাবণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে, মহেশ্বর তাকে শর্ত সাপেক্ষে বর দেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাবণ শিবলিঙ্গ-সহ লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু শর্তের মারপ্যাঁচে বাধ্য হন দেওঘরে এই শিবলিঙ্গ ফেলে যেতে। পরে বৈজু নামক এক ভিলের হাত ধরে জনসম্মুখে আসে এই শিবলিঙ্গ। তাই বৈজনাথ শিব। শ্রাবণের গেরুয়ার গুঁতো এখন নেই। কিন্তু ভিড়ের মাঝেও চোখে পড়ছে বাঁকবাহিত বহু গেরুয়া ভক্তদের।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বৈদ্যনাথ বাবার পুণ্যভূমি শক্তিপীঠ হিসাবেও খ্যাত। এখানে সতীর হৃদয় পড়েছিল। অতএব টানাপোড়েন, রাজনীতি আর প্রধান মন্দির ছাড়াও একই চত্বরে অন্নপূর্ণা, পার্বতী, গণেশ, সরস্বতী, হনুুমান, মনসা প্রভৃতি কুড়িটি মন্দির বিরাজমান। মন্দিরের উত্তরে আছে ১৫০ টি সিঁড়ি বিশিষ্ট রাবণতাল বা ক্ষীরগঙ্গা পুকুর। এই পুকুরে স্নান করে পুজো দেওয়ার নিয়ম। নিয়ম আরও আছে। পুণ্যার্থীরা দেওঘরের সাথে সাথে বাসুকিনাথেও জল নিয়ে যান। যার দূরত্ব দেওঘর থেকে ১৮ কিমি। উভয়স্থানে পুজো দিলেই টোটাল পুজোর সার্কিট কমপ্লিট হয়।
ফুরফুরে সকাল। কালকের অটো দুটো নির্ধারিত সময়ের আগেই এসে হাজির। কচুরি, জিলিপি আর চা-পর্ব মিটতেই যাত্রা শুরু। প্রথমেই সকালের শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশের সঙ্গে সাযুজ্য রাখতে রামকৃষ্ণ মিশন। উইলিয়ামস্ টাউনের অবস্থান। অন্যান্য শাখার মতো এখানেও বিশাল কমপাউন্ড। গেট পেরিয়ে ঢুকতেই রাস্তার দু’দিকে কেয়ারি করা বাগান। তাতে মরসুমি ফুল আর বাহারি গাছের সারি। অনতিদূরে মিশনের প্রতীক নিয়ে দাঁড়িয়ে শ্বেতশুভ্র মন্দির ও প্রার্থনাগৃহ। লাগোয়া স্কুল, হোস্টেল, অফিসরুম। জুতো খুলে প্রবেশ করলাম ভিতরে। ভাবগম্ভীর স্নিগ্ধ মিষ্টি বাতাবরণের মাঝে রামকৃষ্ণ, সারদামণি ও বিবেকানন্দের বহুদর্শিত মূর্তি। ধ্যানে মগ্ন বেশ কিছু মানুষজন। আমরাও বসে পড়লাম। ছড়িয়ে যাওয়া মনকে একবিন্দুতে এনে যখন চোখ বুজতে যাচ্ছি, নিখুদা তাগাদা লাগায়। বাধ্য হই উঠতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকালের মনটা পরিপূর্ণতায় ভরে গেল এই মধুর পরিবেশে। স্বাস্থ্য, চরিত্র ও শিক্ষার ব্রতে গড়ে ওঠা এই আশ্রমিক পরিবেশ ছেড়ে যেতেই মন চাইছিল না। এখানে ছবি তোলা মানা। অতএব ক্যামেরা বার করেও, ব্যাগে ঢুকিয়ে দিলাম।
পশ্চিমের হাওয়া বদলের এখন আমরা চলেছি দেওঘরের পশ্চিমে। এখানে আছে নন্দনপাহাড়। শহর থেকে মাত্র চার কিমি দূরে এর অবস্থান। ছায়াঘেরা তরুবৃক্ষের মাঝে অটো এসে দাঁড়াল। উপরে ওঠার সিঁড়িপথ অনতিদূরে। একেবারেই নীচু পাহাড়। ধাপ সিঁড়ির মুখে টিকিটঘর। পার্কের প্রবেশমূল্য ব্যক্তিপ্রতি পাঁচ টাকা। সোজা সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে, তারপরই আকাশকে মাথায় রেখে একটা বড়ো প্রাঙ্গণ। তাকে বেষ্টন করে রামসীতা-সহ কয়েকটি ছোটো ছোটো মন্দির। কিছু স্থানীয় মানুষজন ভক্তিভরে পুজো দিচ্ছে। সিঁড়ির কয়েকধাপ নীচে ডানদিকের সিঁড়ি পথটাই ঢুকেছে পার্কে। এই অ্যামিউজমেন্ট পার্কে সব ধরনের রাইডই চোখে পড়ছে। উলটোদিকের ধাপ পাহাড়ের শেষে এক বড়ো জলাশয়। সেখানে জলবিহারের ব্যবস্থা আছে। পাহাড়ের এই প্রান্তে দেখি এক ভোজপুরি সিনেমার শুটিং চলছে। একটা গানের সিচুয়েশনে নায়ক-নায়িকা ও সহশিল্পীরা নেচে চলেছেন। খুব চটকদার সে গান ও গানের দৃশ্য। নৃত্যের সাথে গান চলতেই থাকল। চলতে থাকল ক্যামেরা। আমরা ফিরে চললাম। কানে তখনও আসছে কোরিওগ্রাফারের প্যারেড ভঙ্গিতে টেকনিক্যালি নির্দেশ– এক-দুই-স্টার্ট। নীচে নেমে অটোওয়ালাদের এই সিচুয়েশন ব্যক্ত করতেই ছেলেদুটো ছুটল শুটিং দেখতে। সেই ফাঁকে গাছপালার মাঝে এক চায়ের দোকানে চা খেতে বসে গেলাম।
‘লেটস্ গো’ বলে এবার ত্রিকূটের পথে। প্রায় ১২ কিমি দূরে এই পাহাড়। চলার রাস্তাটা এক কথায় ফাটাফাটি। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। প্রবল হাওয়ায় ‘ধানের ক্ষেতের রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা’। দূরে দূরে গাছপালা জড়ানো গ্রামের বাড়িঘর। ল্যান্ডস্কেপে রকমারি পাথুরে কোলাজ। পথপার্শ্বে বৃক্ষও অজস্র। চেনার তালিকায় শাল, মহুয়া, পলাশ ও ইউক্যালিপ্টাস। হুসহাস ছুটে যাচ্ছে দুমকাগামী বাস। বাসুকিনাথে যাত্রীদেরও পথে দেখা যাচ্ছে। দল বেঁধে ক্লান্ত, অবসন্ন শরীরে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। দিগন্তরেখায় এবার পাহাড়ের উঁকিঝুঁকি। দূরে দৃশ্যমান তিনটে মাথাওয়ালা পাহাড়ই ত্রিকূট। ক্রমেই তার ব্যাপ্তি ফুটে উঠছে। যত এগোচ্ছি মনে হচ্ছে আর বুঝি বেশি দেরি নেই পৌঁছোতে। কিন্তু বাস্তবিক তখনও তাকে ছুঁতে পথ ভাঙতে হবে অনেকটা।
অটো যেখানে আপাত বিরতি টানল, দেখি সেখানে বসেছে বিরাট বাজার। খাবারের দোকানই বেশি। খাবার চোখের সামনে দেখলেই পেট সাধারণত কান্নাকাটি শুরু করে। তবে বেলা তো অনেকটাই গড়াল। তাই ওর দোষ দিয়ে লাভ নেই। মশলামুড়ি কেনা হল প্রত্যেকের জন্য। এখানে হনুমান ও বাঁদরদের উৎপাতের গল্পও শোনা ছিল। দেখি আমাদের পূর্বপুরুষরা খাদ্য সংগ্রাহকের জীবিকা ছেড়ে এতটুকু বার হতে পারেনি। আমাদের হাত থেকে মুড়ি মশলার প্যাকেট খোয়া গেল। তাদের বেঁচে থাকার তাগিদে এইটুকু ত্যাগ তো আমাদের করতেই হবে। এখানে এখন আর ট্রেক পথ ধরে হাঁটাহাঁটি নয়। হয়েছে রোপ-ওয়ে রুট। টিকিট কেটে চড়ে বসলাম তাতে। রাজগিরের চেয়েও ভয়ঙ্কর লাগল শেষ চড়াইটা অতিক্রম করতে।

উপরে উঠে দেখি চওড়া পাথুরে জমিতে চা, চিপস্ কোল্ড-ড্রিংকসের বেশ কয়েকটা দোকান। পাহাড় কিনারায় দাঁড়িয়ে শহরটাকে লাগছে অসাধারণ। চোখের সামনে প্রকৃতির ক্যানভাস জুড়ে অসাধারণ রঙের কারিকুরি। ইচ্ছা করলেই যেন ছোঁয়া যাবে নীলরঙ করা আকাশটা। ঘোর কাটিয়ে এবার চা-পর্ব। দল বেঁধে এবার চললাম জঙ্গলের ফালি রাস্তায়। এই পথের ধারেও দোকানের সারি। তবে খাবার বা পোশাকের নয়, বিকিকিনির অধিকাংশ পসরাই জড়িবুটির। কত ধরনের গাছগাছড়া যে বিক্রি হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিনছেও বহু লোকজন। স্থানীয়দের বিশ্বাস, রামায়ণে বর্ণিত গন্ধমাদন পর্বত প্রকৃতপক্ষে এইটাই। এখান থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল বিশল্যকরণী। যদিও এই মতের সপক্ষে-বিপক্ষে আছে হাজার যুক্তি।
জঙ্গলঘেরা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি সকলে। রাস্তাটা যেখানে আপাত সমাপ্ত হয়েছে, সেখানেই দেখলাম রাবণগুহা। দুটো নাতিদীর্ঘ পাহাড়ের মাঝখানে এই গুহার অবস্থান। এক শিবলিঙ্গ দেখি গুহা প্রাঙ্গণে। কয়েকজন জটাধারী সাধুও গুহাকন্দরে। গুহা এলাকায় এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে ফিরে চলি। ফেরার পথে চললাম জঙ্গলের বেপথে। এক চটান পাথরে উঠে প্রকৃতির পাগল করা রূপ দেখে মুগ্ধ হলাম। কিছুক্ষণ এইভাবেই কাটল– প্রকৃতির রূপের হাটে। আবার ভয়ঙ্কর সেই রোপওয়ে পথে নীচে অবতরণ।
খিদের চোটে কথা বলাই বন্ধ হয়ে গেছে সকলের। একবার প্রস্তাব হয়েছিল ছোলা, ছাতু আর মুড়ি-সহ লাঞ্চের। কিন্তু বাঙালির দুপুরে ভাত না হলে চলে? অতএব ভরদুপুরে ভাতের খোঁজে ছুটল গাড়ি। কিন্তু মিলল না কোনও হোটেল। অগত্যা ধাবা। কিন্তু এত লোকের খাবার রেডি করতে, সেই ধাবার ম্যানেজার সময় চেয়ে নিল কিছুটা। তাই সই। এই সময় কেবল বসে বসে প্রকৃতির জাবরকাটা। ধাবাটার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অসাধারণ। দু’পাশে সবুজের আঁচল ছড়ানো ধানখেত। ডানদিকে পাহারারত তালগাছের হাতধরাধরি বৃক্ষশৃঙ্খল। অনতিদূরে ত্রিকূটের মনোমুগ্ধকর হাতছানি। খাওয়াদাওয়ার পরও গালে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। প্রকৃতির রূপে বিভোর হলে এইরকমই হয়।
চলে এসেছি সৎসঙ্গনগর। ক্লকটাওয়ার থেকে রেলস্টেশনমুখী রাস্তায় কিমি তিনেক গেলেই মিলবে এই নগর। দেওঘরের এক উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান। এখানে আছে অনুকূল ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম। যে-আশ্রমের শাখা ছড়িয়ে আছে সারা ভারতজুড়ে। বিশাল এলাকা জুড়ে এই আশ্রমের ব্যাপ্তি। ভিতরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে স্কুল, হাসপাতাল, পাওয়ার স্টেশন, প্রার্থনাগৃহ, সমাধিক্ষেত্র, চিড়িয়াখানা, অফিসঘর ইত্যাদি। যা ভালোভাবে দেখতে একটা গোটা দিন ব্যয় করতে হবে। সব মিলিয়ে দেখার মতো এক বিরাট কর্মকাণ্ড। যদিও আশ্রমের চিড়িয়াখানার অবস্থা সংকীর্ণ। উল্লেখযোগ্য পশুপাখি নিয়ে গিয়েছে বন দফতর। পড়ে রয়েছে শূন্য সব খাঁচা। এই আশ্রমের এক প্রান্তে ঠাকুর শ্রীশ্রী অনুকূল চন্দ্রের বড়দা’র বাড়ি। ঠাকুরের সমাধি দেখতে কেয়ারি করা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে হল কিছুটা। অতি যত্নে পালিত হাজার-হাজার গাছপালা দিয়ে ঘেরা এই আশ্রম যেন মর্ত্যের নন্দনকানন।
ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি প্রার্থনাকক্ষের সামনে। প্রেয়ার হল অবশ্য একাধিক। নীচে কার্পেট বিছোনো। শূণ্য হল জুড়ে পাতা বিছানায় সাদা কাপড়ের আধিক্য। এখানেই একটা ঘরে অনুকূল ঠাকুর ও তাঁর স্ত্রীর পূর্ণাবয়ব মূর্তি। পাশেই ঠাকুরের ব্যবহৃৎ নানান জিনিসপত্র। ঠাকুরের বাণী আশ্রমের ঘরে-বাইরে, রাস্তার ধারে, প্রার্থনাকক্ষে, অফিসঘরে সর্বত্র। শ্বেতশুভ্র পোশাকে ভক্তদের আশ্রমজুড়ে উপস্থিতি একটা শুদ্ধ, সরল, রুচিশীল মানসিকতার পরিচয় বহন করে।
পরবর্তী ডেস্টিনেশন তপোবন। নানা মুনিঋষিদের তপস্যাস্থল হিসাবে খ্যাত এই তপোবন। আটো যেখানে এসে স্ট্যান্ড করল, তার কাছেই এক জমজমাট বাজার। বাজারকে লম্বোচ্ছেদ করে পাহাড়ের ওপরে উঠে গেছে এক রাস্তা। যদিও এই পাহাড়ের পরিধিকে পরখ করতে কোনও বাধাই সম্মুখে উপস্থিত নেই। তবে উৎরাই-এর সিঁড়ি জুড়ে হনুমানের উৎপাত মাত্রাতিরিক্ত। এখানে স্থানীয় কিছু যুবক ‘হনুমানের খাবার’ বিক্রি করছে দেখলাম। সে খাবার আসলে, আটা বা ময়দার ছোটো ছোটো পাকানো মণ্ড। তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে হনুমানদের প্রলোভিত করে বাধ্য করাচ্ছে ওই প্যাকেট ভ্রমণার্থীদের কেনাতে। এভাবে জবরদস্তি ভাবে হনুমানের খাবার কিনতে অনেকেই বিরক্ত হচ্ছেন। অরিন্দমের সাথে এইরকম এক বাঁদর ছেলের বাঁদরামিটা মাত্রাতিরিক্ত জায়গায় উপস্থিত হয়। শেষমেশ সিঁড়ি ভেঙে যেখানে হাজির হলাম, দেখি ছোটো-বড়ো অজস্র পাথরের কোলাজ। পরিবেশ দেখে ছবি তোলার হিড়িক পড়ে গেল। নীচে বিকালের নরম আলোতে ল্যাণ্ডস্কেপ অসাধারণ। এখানে আছে ছোটো-বড়ো অনেক গুহা। যেখানে প্রাচীনকাল থেকেই বহু সন্ন্যাসী ডেরা করে থাকতেন। তপস্যা করার আদর্শ ঠিকানা যে এটাই, তা বোধহয় কাউকে বলে দিতে হবে না। জানলাম বালানন্দ ব্রহ্মচারী এরকমই কোনও গুহায় তপস্যা করেছিলেন। এখান থেকে আরও ওপরে উঠলে মিলবে তপোবন শিবের মন্দির। কিন্তু সময়াভাবে আর উপরে ওঠা হয়নি। ফেরার পথে একটা ব্রেক নেওয়া হল চায়ের দোকানে। যে দোকানে জুতো জোড়া জমা রেখে হাঁটতে শুরু করেছিলাম আমরা। একটা কানা হনুমানের সঙ্গে আলাপ হল। মানুষঘেঁষা হনুমানটা নিখুদার কাছে হাত পেতে চেয়ে নিল খানকতক বিস্কুট। আমিও চা খাইয়ে আলাপটা গাঢ় করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মুখপোড়ার চায়ে মুখ পুড়লে, আমার যে কি হাল হবে এই ভেবে আর এগোনোর সাহস পায় নি।
এখন বিকাল ফুরোচ্ছে। চোখধাঁধানো রঙের খেলায় মেতে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। খুশির রঙ আমাদের মনেও। শেষ আলোটুকু সঙ্গে নিয়েই হাজির হলাম নওলক্ষা মন্দিরে। রানি চারুশিলা তাঁর গুরু বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আদেশে এই অনুপম মন্দিরটি নির্মাণ করেন। তৎকালীন দিনে এর নির্মাণ খরচ নয় লক্ষ টাকা হলেও, বর্তমান অর্থমূল্য দিয়ে বিচার করা যাবে না। মন্দিরের মূল বিগ্রহ শ্বেতপাথরের বালানন্দ ব্রহ্মচারী। উচ্চচূড়া ও বারান্দা বিশিষ্ট মিশ্র স্থাপত্যের নিদর্শন মেলে এই মন্দিরে।
ফিরে এলাম হোটেলে। সারাদিনের ক্লান্তি মেটাতে চায়ের অর্ডার দিলাম। সারাদিনের দেখা-না-দেখা দ্রষ্টব্যগুলিই ঘুরে-ফিরে এল নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনায়। ক্লক টাওয়ারের কাছে এক হোটেলে গেলাম রাত-আহার সারতে। নিখুদা দেখি তখনও কেনাকাটা করছেন। অন্য সদস্যরাও গৃহস্থালির টুকিটাকি জিনিসে ভর্তি করছে ব্যাগ। আমিও ব্যতিক্রম নয়। কিনলাম দেওঘরের বিখ্যাত প্যাঁড়া। ঠিক আছে কাল সকালের জনশতাব্দীতে ফিরব কলকাতায়।