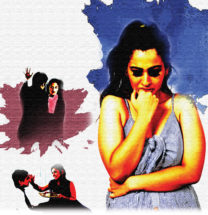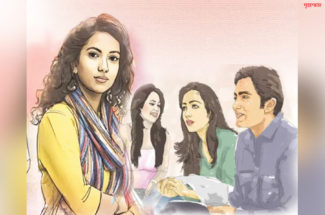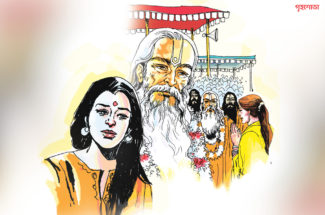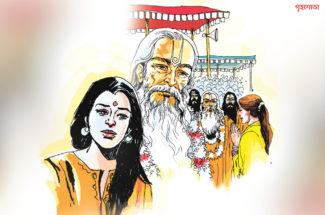দিদি থাকত মা-বাপির কাছে, আর ও মামাবাড়িতে। ওর মনের এক কোণে যেমন ধুলোটে বিষাদ জমে আছে বাপি-মায়ের ভালোবাসার জন্য, দিম্মা পায়েলের থেকে ওকে বেশি ভালোবাসায় দিদির মনেও কী কোথাও হিংসের বীজ রয়ে গেছে? দিদির গায়ে রংটা ওর তুলনায় একটু চাপা। দিম্মামা মাঝে মাঝে মজা করে সেকথা দিদিকে বলত। কস্তুরী শুনেছে। সেটাই কি দিদির মনে গভীর জাল বুনে মনে মনে এতটা পাঁকের আকার নিয়েছে? উফঃ মাথার রগদুটো দপদপ করছে। ভাবতে পারছে না আর।
দিদির জীবনে এত বড়ো একটা খুশির সময় কিন্তু কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না কস্তুরী। কেউ কেন বুঝতে পারছিল না এই চরিত্রহীন লম্পট মানুষটার সঙ্গে বিয়ে হলে দিদি ঘর বাঁধতে পারবে না; অঘটন ঘটবে আরও বেশি। কী করে বিশ্বাস করাবে সবাইকে যে, ও দিদির ভালো চায়।
দেখতে দেখতে সেই সর্বনাশের দিনটা এসেই পড়েছিল। বিয়ে নয়, আশীর্বাদ। ইচ্ছে না থাকলেও বাপি-মায়ের সঙ্গে ওকে যেতে হয়েছিল দিদির শ্বশুরবাড়ি। অনেক লোকজন, হই-হল্লা, খাওয়াদাওয়ায় বেলা গড়িয়ে যাচ্ছিল। খোলামেলা পরিবেশে ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাঝে আলাপ হয়েছিল ওর বয়সি দুএকজন ছেলেমেয়ে সাথে। দিদি আসেনি, তবুও হবু শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেকেই পায়েলের কথা আলোচনায় মশগুল ছিল। কস্তুরী অবাক হয়ে দেখছিল কীভাবে ওর জামাইবাবু শুধুমাত্র অভিনয় করে একটা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখল। সবার মাঝে থাকলেও ওর সঙ্গে এসে মাঝে মধ্যে ফর্মালি ইয়ার্কি ঠাট্টা করে যাচ্ছিল। বোঝাতে চাইছিল ওদের সম্পর্কটা নেহাতই আর পাঁচটা শালি-জামাইবাবুর মতো মজার।
হঠাৎ বাড়ি চলে আসার সময়ই একটা ঘটনা ঘটে। বিয়ে পরে দিদি যে-ঘরে থাকবে জামাইবাবুর মা ওকে ডেকে নিয়ে যায় সে ঘরে। ঘরের রং, নতুন পর্দা, এসি মেশিনের প্রপার অ্যাডজাস্টমেন্ট দেখাতে দেখাতে কিছুটা কাছে সরে এসে ভদ্রমহিলা বলেন, তোমাদের বাড়ির অবস্থা তো বিশেষ ভালো নয়। তোমার দিদিকে যেমন সবকিছু আমরাই দিচ্ছি, তোমাকেও দেবো, চিন্তা কোরো না। ঋজু যদি কিছু করে থাকে তাহলে সেটা তোমার মধ্যেই রেখো। পাঁচকান কোরো না। কী লাভ বলো? তোমার দিদি খামোকা কষ্ট পাবে। আর তাছাড়া এসব জানাজানি হলে পরে যদি তোমারও বিয়েটা আটকে যায়?
ঘিনঘিনে অস্বস্তিটা পিছু ছাড়ছিল না। তাহলে বাড়িশুদ্ধু সবাই জানে। এদের বাড়ির সবাই জানে কস্তুরীর কথাটা? কিন্তু তাই বা কী করে হয়? দিদি এসে এখানে বলেছে? আর দোষটা? দোষীর কথা? মাথার মধ্যেটা জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে কী করা উচিত কস্তুরীর মাথায় আসছিল না।
বাপি-মাকে ডাকবে? উনি কী বললেন তা জানাবে? ওরা যদি আবারও অবিশ্বাস করে? আবারও ওকে দোষ দেয় সমস্ত নিমন্ত্রিত অতিথির কাছে?
কস্তুরী ঘর থেকে বেরোনোর জন্য ছটফট করছিল। পা তুলে চৌকাঠ ডিঙোতে গিয়ে বুঝেছিল ওর একেকটা পায়ে ওজন যেন দশমন ভারী হয়ে গেছে। মেঝের কোনও আকর্ষণ ওর গোটা শরীরটাকে মাটিতে গেঁথে দিচ্ছিল একটু একটু করে। জিভ বুলিয়ে ঠোঁটের শুকনো চামড়া ভিজিয়ে কস্তুরী একটা যথায়থ উত্তর খুঁজছিল। একটা সত্যি উত্তর।
( ৬ )
লক্ষ্মীকাকিমা উত্তরে কী বলেছিল ঠিক শুনতে না পেলেও ঠাকুমা, মানে তমালের ঠাকুমার কথাটা পরিষ্কার শুনেছিল কস্তুরী।
জানো আমাগো বড়ো বৌমার নাড়ি তো শুকায়ে গেছে। না হলি আজও একখান বাচ্চা হলনি?
হ্যাঁ ঠিক এই কথাটাই শুনেছিল ও। ঠাকুমাশাশুড়ির কথায় যে রসালো আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল বুঝতে পারছিল সেটাও। বাড়ির ঠিকে কাজের বউ থেকে তমালের মা পর্যন্ত সেই আলোচনায় অংশ নিয়েছিল। গোটা ব্যাপারটা এতটাই যন্ত্রণার বলে বোঝানো যাবে না।
তমাল আর কস্তুরীর বিয়েটা হয়েছে অনেকটা শিখণ্ডীর মতো। বাড়ির বড়ো ছেলে হওয়া সত্ত্বেও তেমন কোনও দাগ কেটে যাওয়া অস্তিত্ব তমালের কথায় কিংবা কাজে কোনওদিনই ছিল না। তমালের বাবা ছেলেকে অ্যানিমেশন শেখানোয় উত্সাহী হলেও মা যে একেবারেই রাজি ছিলেন না, তা বোঝাই যায়। আসলে মা চাইতেন ছেলে সরকারি চাকরি করুক। মাস গেলে নিশ্চিন্ত একটা মাইনে ঢুকুক ঘরে। কিন্তু তমাল সরকারি চাকরির পরীক্ষা দেওয়া তো দুরস্ত উলটে প্রাইভেটে অ্যানিমেশনের দিকে ঝুঁকল। ওর জন্য লাখখানেক টাকা ইনভেস্টও করতে হল। কিন্তু হরেদরে দেখা গেল শুরু শুরুতে তমালের মাস গেলে মাইনে ঢুকছে পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার। বছরে ইনক্রিমেন্ট এক হাজার মতো।