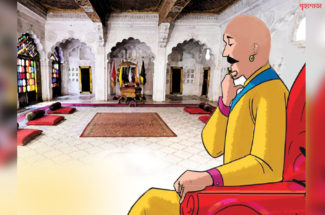মেঘালয়ের রাজধানী শিলং এসেছি গতকাল। মেঘমুলুকে এসে মেঘ-বৃষ্টির লুকোচুরি খেলা নতুন কথা নয়। বৃষ্টির অনুষঙ্গ পেয়ে মনও বিন্দাস। কাল রাত-ভোর শুনেছি বৃষ্টির আওয়াজ। সকালে অবশ্য ধারাবাহিক ধারাপাতের বিন্দুবিসর্গ নেই। তবে মেঘের গতিবিধি দেখে, মেঘালয়ের জলহাওয়ার চটজলদি ভবিষ্যদ্বাণী করা খুবই কঠিন। গতকাল শিলং সাইটটা সারাদিন দেখে, আজ চলেছি বৃষ্টিভেজা চিরসবুজের দেশে। এক কথায় বললে, চেরাপুঞ্জি সাইট সিয়িং।
চেরাপুঞ্জি খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে একটা ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ১,৪৮৪ মিটার। চেরাপুঞ্জির স্থানীয় নাম ‘সোহরা’ বা সোরা। স্থানীয় খাসিয়া ভাষায় যার অর্থ কয়লা। ব্রিটিশদের উচ্চারণে সোরা হয়ে যায় চেরা। ছেলেবেলায় পড়া চেরাপুঞ্জির নাম আজও মনের কোণে অনুরণন তোলে। এখন আমরা সেই মেঘপুঞ্জের দেশে। সোহরা বাজার ও সংলগ্ন জনপদ বেশ বড়োসড়োই মনে হল। এখানকার কমলালেবু, দারুচিনি, চেরি, ব্রান্ডি আর কমলালেবুর ফুলের মধু বিখ্যাত। ছুটে চলা গাড়ি জানলা দিয়ে সোহরা বাজারের দিকে তাকালাম। কর্মচঞ্চল মানুষজন, স্কুল ফেরত কচিকাঁচা, পথিক– সব মিলিয়ে মেঘালয়ের জন জাতিগোষ্ঠীর একখন্ড চিত্র।
শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি ৫৬ কিমির মতো পথ। ব্রেকফাস্টের পর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কাল রাতের বৃষ্টিতে ভিজে পথপার্শ্বস্থ গাছপালাগুলো হয়ে উঠেছে আরও সজীব, সবুজ, প্রাণবন্ত। শিলং-সোহারা হাইওয়ে ধরে ছুটে চলেছে গাড়ি। বায়ুসেনা ব্যারাকের পরই কংক্রিটের জঙ্গল থেকে সবুজের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করি। পথ যথেষ্ট প্রশস্ত ও মসৃণ। পাকদণ্ডি হলেও, গাড়োয়ালের মতো তেমন দুর্গম বলা চলে না। পথ ছবিতে মাঝে-মাঝেই চোখ আটকায়। বিশেষত ঢেউ খেলানো পাহাড়ি ল্যান্ডস্কেপ আর মাখামাখি সবুজের বৈচিত্র্যে।
পাইন জঙ্গলের উৎরাই ছেড়ে গাড়ি এখন উপত্যকার মাঝে। দেখি চেরি, পিচ, আর নাসপাতির বাগানে কাজ করছে খাসি নারী-পুরুষরা। জানা ছিল, পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলের শিরোপো আর চেরাপুঞ্জির দখলে নেই। তার গড় বৃষ্টিপাত কমে হয়েছে ১২,০২৯ মিলিমিটার। কিন্তু ছোটোবেলার ভূগোল বই-এর স্মৃতি কি অত সহজে ভোলা যায়! মূলত গাছপালার অপ্রতুলতায় কম বৃষ্টির একটা বড়ো-সড়ো কারণ। এই পাহাড়ি পথে তাই এখন আর তেমন বড়ো-সড়ো গাছপালার অস্তিত্ব মেলে না। ফলে সামনে শুধুই সবুজ গাছের ঘোমটা পড়া নাতিদীর্ঘ পাহাড় সারি। এই পাহাড়ের উপরে সামান্য মাটির আস্তরণ থাকলেও, পাহাড়ের নীচে সবটাই পাথুরে জমি।
সরকারি তরফে এই সমস্ত জমিতে নিবিড় বনসৃজনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও সে ভাবে সাফল্য আসেনি। অনুকূল আবহাওয়া থাকলে দিব্যি হতে পারত দিগন্ত বিস্তৃত চা-বাগান অথবা বৃষ্টিকে ধরে রেখে ধানের মতো প্রধান ফসল। কিন্তু যে পাহাড়ের নীচে খনিজ সম্পদ অঢেল, সেখানে কোনওটাই উৎপাদন করা সম্ভব নয়। কেবল উপত্যকা জুড়ে মানুষজনের অক্লান্ত চেষ্টায় গড়ে উঠেছে নিবিড় সবজি চাষ।
চলতি পথে চোখে পড়ল, বেশ কয়েকটা পাথরকুচির কারখানা। চোখ এড়ালো না পরিত্যক্ত কয়েকটা কয়লা খাদানও। শুনলাম মেঘালয় সরকার কয়লা তোলার উপর বর্তমানে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। খাদানের কাজ বন্ধ হওয়ায় স্থানীয় মানুষজনের রুজি-রুটিতে টান পড়েছে।
সবুজ উপত্যকা ছুঁয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি। ‘আমার পথ চলাতেই আনন্দ’ গানের মতো পথের সৌন্দর্যই যেন বিমোহিত করে তোলে। চেরা বাজারের আগেই গাড়ি দাঁড়ায় এক ভিউ পয়েন্টে। নাম দুয়ান-সিং-সিয়েম। রাস্তার ধারে গাড়ি থেকে নামতেই অবাক হয়ে গেলাম। এই সাত সকালেই পর্যটক ও স্থানীয় মানুষজনে ভর্তি জায়গাটা। সামনের ল্যান্ডস্কেপ জুড়ে পাহাড়ের প্যানরামিক ভিউ।
দুরে পাহাড়ি খাদ থেকে উঠে আসা ঘন সবুজ পাহাড় পরিবারদের দেখে মনে হচ্ছিল সাজানো পাপড়ি মেলা বড়োসড়ো এক পদ্মফুল, ধূপছায়ার কারসাজিতে হয়ে উঠেছে অসাধারণ। পাথুরে ধাপ সিঁড়ি ধরে গেলাম অনেকটা নীচে। সিড়ির বাঁকে উঁকি দিল এক তন্বী ঝরনা। ঝোপ জঙ্গলের মাঝে সে নিজেকে রেখেছে অবগুণ্ঠিত। ভিউ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে বিন্যস্ত গিরিবর্গের ছবি তুললাম বেশ কয়েকটা। উপরে উঠে দেখি পথপার্শে চা, ম্যাগি, চিপস-এর অস্থায়ী সব দোকান। আছে চাদর, টুপি, স্কার্ফ, জ্যাকেটের মতো প্রয়োজনীয় সামগ্রীও।

একটা ঝোরার টানে ছুটে চলার পর এক উপত্যকার মাঝে হঠাৎ গাড়ি দাঁড়ায়। কিন্তু মজার ব্যাপার, গাড়ি থেকে নেমে কোনও ঝরনার অস্থিত্বই মেলে না। শুধু খাড়াই পাহাড়ি এক ঢাল নেমে গেছে অনেকটা নীচে। সামনের দিগন্তরেখা জুড়ে শুধু ছোটো-বড়ো কয়েকটা পাহারের সমন্বয়। ড্রাইভার বলল, ‘পাথুরে উৎরাই পথে নীচে নেমে যান। পাবেন তিন-তিনটে সুন্দরী ঝরনা। তাদের দেখে ফিরে আসুন। আমি অপেক্ষায় থাকছি।’
শব্দ সন্ধান করে গড়ানে বেপথে নামতে থাকি। এলোমেলো পাথুরে পথ। কিছুটা নামার পরেই চক্ষুস্থির। সামনে রাস্তা শেষ। আর তারপরই অতলস্পর্শী খাদের শুরু। আর খাদের ও প্রান্তে পলকহীন সবুজ পাহাড়শ্রেণির রূপমাধুর্য। যেন প্রকৃতির ক্যানভাসে জলরং তুলির সার্থক রূপটান। হঠাৎ উড়ে আসা জলকণাকে বৃষ্টি ভেবে ছাতাই বার করে ফেললাম। পরে বুঝলাম, উড়ে আসা জলকণা আসলে এক ঝরণা। যার মাথাতেই দাঁড়িয়ে আছি। তাই উপলব্ধি হচ্ছে না কিছুই। উলটো দিকের পাহাড়ি বাঁক থেকে সেই ঝরনার পূর্ণাবয়ব রূপ দেখলাম। শুনলাম এর নাম ডানথিয়েন ফলস্। ছোটো হলেও এই ফলস্ সেভেন সিস্টার ফলস্ দেখার আগে পর্যটকদের অনেকটাই মুগ্ধ করবে।
গাড়ি এবার ছুটে চলেছে নাহোকালিকাই ফলসের দিকে। এই পথেই পড়ল রামকৃষ্ণ মিশন। নির্জন পাহাড়ের কোলে অনেকটা জায়গা জুড়ে এই মিশন। মিশনের শান্ত পরিবেশ মনে এনে দিল এক প্রশান্তি। শুনলাম ১৯৫২ সালে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এই মিশনের উদ্বোধন করেন। নাহোকালিকাই ফলস্ অবশ্য বিনি পয়সায় দেখা গেল না। ব্যক্তি প্রতি টিকিট এখানে দশ টাকা। এছাড়াও ক্যামেরা ও গাড়ি পার্কিং এর জন্য গুনতে হল বাড়তি আরও কিছু অর্থ। বিশ্বের চতুর্থ ও এশিয়ার দ্বিতীয় উচ্চতম জলপ্রপাত এই নাহোকোলিকাই ফলস্ । ফলসের সম্মুখের রেলিং দিয়ে ঘেরা পাহাড়ি খাদের প্রান্তে এখন আমি দাঁড়িয়ে। আমার পায়ের নীচে অতলস্পর্শী খাদ। যার অপর পাড়ের পাহাড়ি শীর্ষদেশ থেকে ঝরে পড়ছে একটি শীর্ণকায় জলধারা। ঘন জঙ্গলের ফাঁকফোকড় গলে, কঠিন পাথুরে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে সশব্দে।
প্রায় ২০০০ ফুট উচ্চতা থেকে এই দুধসাদা জলধারার ঝরে পড়া অসাধারণ লাগছে। সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে এখানে রামধনুর সৃষ্টি হয়েছে। তার পতনস্থলে সৃষ্টি হয়েছে এক কুন্ড। বিচ্ছুরিত জলকণায় সে কুন্ড এখন কুহকিনী। লোকপ্রবাদ অনুসারে বলা হয় দ্বিতীয় স্বামীর হাতে প্রথম পক্ষের কন্যার মৃত্যুর পর দুঃখে-শোকে মা লিকাই ঝাঁপ দেন এই পাহড়ি খাদে। বিশ্বাসী মানুষজন মনে করে, তারই রূপান্তরিত রূপ এই জলপ্রপাত।
একে সুইসাইডাল ফলস্ও বলা হয়। ফলস্কে ছুঁয়ে দেখতে হলে নামতে হবে নীচে, কুন্ডের কাছে। আছে পাথুরে ধাপসিড়ি। দূরে প্রতিবেশী বাংলাদেশের জলমগ্ন ল্যান্ডস্কেপের অমোঘ হাতছানি। ফলস-কে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছে জমজমাট বাজার। আছে টয়লেটের সুব্যবস্থাও। রাস্তার ধারেও পসরা সাজিয়ে বসেছে স্থানীয় মানুষজন। বিক্রি হচ্ছে দারুচিনি, মধু, গোলমরিচ ইত্যাদি। ওদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা মধু কিনলাম। দাম তুলনামূলক অনেক কম।
গাড়ি এবার চলে আসে সীমান্তবর্তী এলাকায় এক ইকো পার্কে। সামনেই সাজানো-গোছানো এক শিশুউদ্যান। আছে বাচ্চাদের একাধিক রাইড। এর বাইরে এটাকে অ্যাকোয়াটিকার কাছাকাছি পার্ক বললে হয়তো ভুল বলা হবে না। কারণ ঝরনার জলকে ঘুরপথে পাহাড়ের গা বেয়ে যেভাবে একাধিক ওয়াটার রাইড তৈরি করা হয়েছে তা বেশ অভিনব। অনেকেই এই কৃত্রিম ফলসে স্নান করছেন। কেউ কেউ আবার স্রেফ পা ডুবিয়ে বসে আছেন। এই স্থানের আর এক বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের ঝলক দর্শন। এই সব সীমান্তে অবশ্য কাঁটা তারের বেড়া নেই। দুর্গম পাহাড়ি খাদই এখানে আন্তর্জাতিক সীমানা। ঘুর পথে আসা কৃত্রিম জলধারার জলই পাহাড়ি খাদে পড়ে এক অপরূপ ঝরনার রূপ নিয়েছে। সীমান্ত পেরিয়ে এই জলই পৌঁছোচ্ছে বাংলাদেশের নাবাল জমিতে।

এবার চলেছি সেভেন সিস্টার ফলস্ দেখতে। মেইন রাস্তা ছেড়ে শাখাপথে সামান্য এগোতেই সামনাসামনি দেখা সেভেন সিস্টারের সঙ্গে। গাড়ি থেকে নামতেই দেখি সারিবদ্ধ বৃত্তাকার পাহাড়ের মাঝে অতলস্পর্শী এক গিরিখাদ। তার বামদিকের পাহাড়েই ঝোলানো ওড়নার মতো সাত সাতটি ছোটো-বড়ো ঝরনা, যা সেভেন সিস্টার ফলস্ নামে পরিচিত। সাতবোনের মধ্যে এ বলে আমায় দেখ, তো ও বলে আমায়। গুনতে গিয়ে মনে হলো সংখ্যাটা যেন আরও বেশি। তাই নামটা ইলেভেন সিস্টার ফলস্ হলেও মন্দ হতো না। মোসমাই গ্রামের সন্নিকটে বলে অনেকে একে মোসমাই ফলস্ও বলে থাকেন। সবুজের প্রেক্ষাপটে ঝরে পড়া শ্বেতশুভ্র একাধিক জলধারার মিলিত ঐক্যতান অনবদ্য। আশ মিটিয়ে দেখেও যেন আবার দেখার খিদেটা রয়ে যায়। এখানে বাইনোকুলারের সাহায্যে ফলস্ দেখানোর ব্যবস্থা আছে। এক মিনিটের জন্য দশ টাকা। ভালো লাগার আবেশ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসেই রইলাম। একসাথে সাত সাতটা সুন্দরীকে ছেড়ে আসতে ইচ্ছা করছিল না একটুও। কিন্তু না ফিরে তো উপায়ও নেই।
আজকের শেষ দ্রষ্টব্য মোসমাই কেভস্। সেভেন সিস্টার ফলস্ থেকে সামান্য দূরেই মোসমাই গুহা। পার্কিং জোন থেকে এগিয়ে যেতেই গুহা প্রবেশের টিকিট কাউন্টার। টিকিট সংগ্রহ করে পর্যটকরা অতি আগ্রহসহ এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু গুহামুখ থেকে সাহস হারিয়ে অনেকে ফিরে আসছেন। প্রবেশ ও প্রস্থানপথে রয়েছে চমৎকার পাথর বাঁধানো প্রশস্ত পথ। প্যান্ট গুটিয়ে খালি পায়ে বুকে সাহস নিয়ে এগিয়ে যাই। গুহা অভ্যন্তরে আলোর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে এ আলো নিতান্তই টিমটিমে। গুহার দেয়াল জুড়ে দেখছি অজস্র বাদুড় ঝুলছে। চলার পথে তাই দু’একটা ঝাপটাও মারছে মুখে। মনে পড়ে যাচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশের বোরাকেভ, ছত্তিশগড়ের কুটুমসোর অথবা কুমায়ুনের পাতাল ভুবনেশ্বর গুহার কথা।
ক্রমান্বয়ে পড়তে থাকা টুপটাপ জলে অসমান পাথুরে পথ হয়েছে পিচ্ছিল। স্যাঁতসেতে পরিবেশের মধ্যে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাই। মাথার উপর কিম্ভূত আকারের সব স্ট্যালাকটাইট পাথরের অবয়ব। একটু এগিয়ে যেতেই পায়ের নীচে এসে যায় শীতল জলধারা। গা-টা শিরশির করে ওঠে। ভাবছি কোনও সাপ-খোপ এসে পা-টা জড়িয়ে ধরবে না তো! আলো আঁধারি পথে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগিয়ে চলেছি। কোথাও ভাঙতে হচ্ছে হাঁটুজল। অবস্থা বিশেষে কোথাও বা হামাগুড়ি দিতে হচ্ছে। চুঁইয়ে পড়া জলধারায় গা-মাথা ভিজে একসা। সব মিলিয়ে এই ১৫০ মিটার গুহাট্রেকের যে অসাধারণ অনুভূতি তা বোধ হয় ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।
বাইরে বেরিয়ে ধাতস্থ হতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। মোসমাই গুহাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক ছোট্ট বাজার। হাতে গোনা কয়েকটা ভাতের হোটেল চোখে পড়ল। মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য এর মধ্যে একটি হোটেলে ঢুকলাম। ফেরার পথে শুরু হল অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। সেই মেঘ কুয়াশাকে উপেক্ষা করেই ছুটে চলে গাড়ি শিলং শহরের দিকে৷
কীভাবে যাবেন – কলকাতা থেকে প্রথমে পৌঁছোতে হবে গুয়াহাটি। বিমান অথবা ট্রেন পথে চলুন। ট্রেন পাবেন সরাইঘাট এক্সপ্রেস, কামরূপ এক্সপ্রেস, কাঞ্চনজঙঘা এক্সপ্রেস অথবা দ্বি-সাপ্তাহিক কলকাতা-গুয়াহাটি গরিবরথ এক্সপ্রেস। গুয়াহাটি স্টেশনের বিপরীত দিকেই পল্টন বাজার। এখান থেকে মিলবে শেয়ার সুমো। নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় গাড়ি ভাড়া করেও ১৫০ কিমি দূরের শিলং শহরে পৌঁছোতে পারেন। চেরাপুঞ্জি ঘোরার জন্য মেঘালয় টুরিজমের তত্বাবধানে চেরাপুঞ্জি টুরের টিকিট কাটুন। ভাড়া জন প্রতি ২৫০ টাকা। সকাল ৮ টায় শুরু হয়ে শেষ হয় বিকাল ৫ টায়। শিলং-এর মেঘালয় ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বিপরীতে অবস্থিত এদের অফিস। নিজেদের উদ্যোগে গাড়ি বুকিং করে চেরাপুঞ্জি ঘুরতে চাইলে, খরচ পড়বে ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা।
কোথায় থাকবেন – শিলং থেকে দিনে-দিনেই ঘুরে আসা যায় চেরাপুঞ্জি। শিলং শহরে থাকার জন্য আছে অসংখ্য হোটেল। এখানে সিংহভাগ হোটেলের অবস্থানই পুলিশ বাজার ও জি এস রোডের আশেপাশে। হোটেল ভাড়া এখানে যথেষ্ট বেশি।