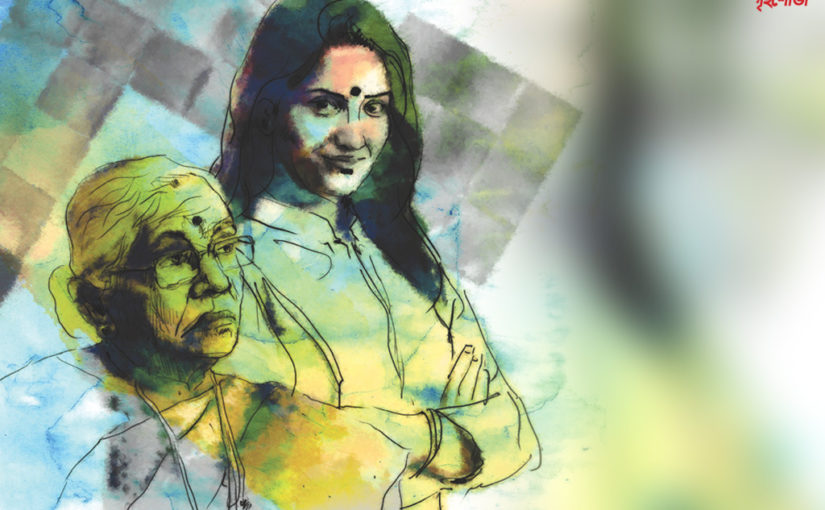ঘটকপুকুরে যেতে চাইলে দুটো স্টপেজে নামা যায়। এক, ডাক্তারখানা স্টপেজ। এক কামরার একটা মাটির চালা, সামনে ছোট্ট বারান্দা। একসময় রুগির ভিড় উপচে পড়ত সেই বারান্দায়, ভেতরঘরে নড়বড়ে চেয়ার-টেবিল পেতে বসে থাকত প্রতাপ ডাক্তার। প্রতাপ কাঁড়ার, হোমিওপ্যাথ। এক শিশি সুগার অব মিল্কে এক ফোঁটা ওষুধ ফেলে সাত গাঁয়ের লোককে খাওয়াত, লোকে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলত, ‘সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি’। সেই ধন্বন্তরি প্রতাপ ডাক্তারকে হঠাৎ একদিন সকালে কেউ দেখতে পেল না। চেয়ার, টেবিল আছে, খোপ-খোপ ওষুধের বাক্স আছে, তক্তাপোশে তেলচিটে বিছানা, নীচে স্টোভ. কালি-লাগা হাঁড়িকুড়ি, দড়িতে ধুতি-গামছা, সব যেমনকার তেমন আছে। শুধু মানুষটা নেই। কেউ বলল, স্বপ্নে আদেশ পেয়ে হিমালয়ে চলে গেছে ডাক্তার, কেউ বলে বাড়ি থেকে খারাপ খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়েছে। প্রতাপ ডাক্তার চলে যেতে সাত গাঁয়ের লোক কিছুদিন হা-হুতাশ করল, তারপর নতুন ডাক্তার খুঁজে নিল। কিন্তু ডাক্তারের ঘরটা তেমনই পড়ে রইল, থাকতে থাকতে জরাজীর্ণ হয়ে গেলেও ঠিক দাঁড়িয়ে রইল মাটির ওপর। আর বাস স্টপেজের নাম হয়ে গেল ডাক্তারখানা।
দ্বিতীয় স্টপেজের নাম ঘটকপুকুর স্ট্যান্ড। এখান থেকে রাস্তা একদিকে রায়দিঘি অন্যদিকে কাকদ্বীপের দিকে চলে গেছে। জায়গাটা সবসময়ই সরগরম। তিন-চারটে মিষ্টির দোকান, চপ-ফুলুরিও বেশ কয়েকটা, সারের দোকান, টেলারিং, ইদানীং একটা টিভি মেরামতের দোকানও খুলেছে পঞ্চায়েত প্রধানের ভাইপো নাড়ু। বিকেলে একটা রোল-চাওমিনের চলমান দোকানও বসে। তার গায়ে বড়ো বড়ো করে লেখা ‘ঘটকপুকুর রোল কর্নার’।
ঘটকপুকুর গ্রামে যেতে গেলে এই স্ট্যান্ড থেকে একটু পিছিয়ে আসতে হয়। ডাক্তারখানা স্টপেজে নেমে অবশ্য সোজা ঢুকে গেলেই হল। গাছগাছালির ছায়ায় ছায়ায়, পুকুরে হাঁসের সাঁতার দেখতে দেখতে গ্রামীণ ব্যাংকের পাশ দিয়ে সোজা ঘটকপুকুর হাটতলায় ঢুকে পড়া যাবে। এই হাটতলাটাই গ্রামের প্রাণকেন্দ্র। গ্রামটা তাকে ঘিরে পদ্মের পাপড়ির মতো ফুটে আছে।
ডাক্তারখানা আর স্ট্যান্ড– এই দুই স্টপেজের মাঝে গ্রামে ঢোকার আর একটা তৃতীয় রাস্তা আছে। বাস ওখানে দাঁড়ায় না। যদি দাঁড়ায়, তবে হয়তো স্টপেজটার নাম হতো, কাওরাপাড়া স্টপেজ। ঘটকপুকুরের কোনও মান্যগণ্য লোককে প্রকাশ্যে এ রাস্তায় যাতায়াত করতে দেখা যায় না। আগেকার দিনে বাড়িতে যেমন মেথর ঢোকার আলাদা পথ থাকত, এই রাস্তাটাও তেমনি। ভদ্রসমাজের অস্পৃশ্য, অব্যবহূত। আসলে এই পাড়ার বাসিন্দারাও তাই। পন্ডিতেরা বলেন এরা আগে ছিল জমিদারের পালকিবাহক, কাহার সম্প্রদায়। কাহার থেকে কাওরা। যারা পালকি না বইলে ভদ্রলোকের সভ্যতার গতিরুদ্ধ হয়ে যেত, অফিস-কাছারি, পালা-পার্বণে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যেত, এমনকী পালকি শুদ্ধু গঙ্গায় ডুবিয়ে পুণ্যের থলিটা বোঝাই করা যাদের দাক্ষিণ্যে, তারা নাকি এত নীচু জাত যে গ্রামের ভেতরে তাদের বাস চলে না, তাদের রাস্তাটাও বিপদে না পড়লে কেউ ব্যবহার করে না। তো সেই কাওরাপাড়ায় লকলক করে লাউডগার মতো বেড়ে উঠছে ফুল্লরা কাওরা। তাকে নিয়েই এই গল্প।
ফুল্লরা একরাশ গোবর কুড়িয়ে ঘরে ফিরে দেখল তার মা সনকা দাওয়ায় বসে চুল খুলছে। সে প্রায়ই দড়ি দিয়ে চুল বাঁধতে গিয়ে গিঁট ফেলে দেয়, তাই দড়ির বদলে অনেকসময় শাড়ির পাড় ছিঁড়ে নেয়। আজ মার কাঁচাপাকা চুলে লালরঙের শাড়ির পাড় কেমন বেখাপ্পা লাগল ফুল্লরার। মার সিঁথির জায়গাটা ফটফটে ফাঁকা। তার বাপ দুখে মারা গেছে দু-মাসও হয়নি। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, দুখেকে খুন করা হয়েছে।
দুখে কাওরার স্থায়ী কোনও পেশা ছিল না। মাঝে মাঝে সে নিত্য শাহ-র সিমেন্টের দোকানে মাল বওয়ার কাজ করত বটে, কিন্তু বেশিরভাগ দিনই তাকে কাজ করবার মতো সুস্থ অবস্থায় পাওয়া যেত না। সে পড়ে থাকত পঞ্চার তাড়ির ঠেকে কিংবা মণিকা-কণিকার বাড়ি। সেখানে মদের আসর বসত, তবে সেটা মুখ্য নয়। দুখে খুব ভালো গান গাইত। তার গলায় গোষ্ঠগোপাল দাসের ‘গুরু না ভজি মুই সন্ধ্যা সকালে মন প্রাণ দিয়া’ শুনে মহাপাতকের চোখেও জল আসত। তার গানের সঙ্গে নাল বাজাত সাগর। আর মণিকা-কণিকা, যাদের নামে গ্রামের সবাই বলে, তারা গ্রামের বুকেই, ভদ্রপাড়ায় লাইন খুলে বসেছে, তারা গানের মাঝে মাঝে মদ, চাট এবং হাসি পরিবেশন করত আর পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে তাদের আঁচল বার-বার খসে পড়ত।
এরকম অবস্থায় তাবড়-তাবড় ঋষিদেরই ধ্যানভঙ্গ হয়, দুখে তো কোন ছার! সে শুধু মনস্থির করতে পারছিল না, মণিকা না কণিকা– কে তার মন বেশি টেনেছে। নিজের এই সংশয়ে সে এতই নিবিষ্ট ছিল যে খেয়ালই করেনি, যে তার বাজনদার সাগর, তাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করেছে। এ বাড়িতে সাগরের যাতায়াত দুখের অনেক আগে থেকে, দুটি বোনকেই সে তার হাতের বাজনার মতোই ভালো বাজাতে পারে। তারাই যখন, দুখের গানে মজে, নতুন হাতে বাজতে চাইল, সে মেনে নিল না।
দুখে আর সাগর মাঝে মাঝেই দূর দূর গ্রামে মাচা প্রোগ্রাম করতে যেত। সেবার তারা গেল কাঁটাগাছি, কাঁটাগাছি ব্যবসায়ী সমিতির ডাক পেয়ে। ফেরার সময় সাগর একাই ফিরল, দুখে নাকি ওখান থেকে কোথায় চলে গেছে, কাউকে কিছু না বলে। কয়েকদিন পর দুখের বডি ভেসে উঠল খালের জলে। সনকা থানায় রিপোর্ট লেখাতে গিয়ে ফিরে এল। একে তো সাগর উঁচুজাত, তার ওপর সে পঞ্চায়েত প্রধানের লতায়পাতায় আত্মীয় হয়। সনকা চোখের জল মুছে বাড়ি ফিরে এল।
সনকার ফটফটে সাদা সিঁথিটা দেখে ফুল্লরার মনে আবার সেই ভয়ংকর দিনগুলো ফিরে আসে। সেই জল থেকে তোলা ফুলে ঢোল বডি, বাবা বলে চেনাই যায় না। পোস্টমর্টেম রিপোর্টও হাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু ফুল্লরা জানে তার বাবাকে ছুরি মেরে খুন করেছে সাগর। পুলিশের মুখ বন্ধ করলেও লোকের মুখ অত সহজে বন্ধ করা যায় না। ইস্কুলের টিউকলে জল নিতে গিয়ে শুনে এসেছে সে, গাঁয়ের বউ-ঝিরা সেখানে খাবার জল নিতে ভিড় করে সকালে-বিকেলে।
যত আগে গিয়েই লাইন দিক, ফুল্লরা জানে যে, সে জল পাবে সবার পরে। ছোটোবেলা থেকেই এমন দেখে আসছে। তখন বুঝত না। জেদ করে ওদের লাইনে দাঁড়াতে গিয়েছিল একবার। ওরা ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। খোয়ার ওপর পড়ে কপাল একটুর জন্যে ফাটেনি, কিন্তু মাটির কলসি ভেঙে গিয়েছিল। ছোট্ট ফুল্লরার কপালে গাঁদা পাতার রস লাগাতে লাগাতে তার মা বুঝিয়েছিল উঁচুজাতের জলের লাইন আলাদা, ওদের ছোঁয়া লাগলে যে জল ওরা খেতে পারবে না। ফুল্লরা বুঝতে পারেনি, সরকারি কলের জল ওদের ছোঁয়ায় কী করে অশুদ্ধ হতে পারে। তখনও ইস্কুল ছাড়েনি। খিচুড়ি ইস্কুল। সেখানে খুব করে প্রার্থনা গাইতে হতো, ‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।’ গাইতে গাইতে ওর বুকে কীরকম একটা কষ্ট হতো। ওর মনে হতো, এখানে যে আগুনের কথা বলা হয়েছে, সেই আগুন তো বইয়ের অক্ষরের মধ্যে লুকোনো আছে। সেই আগুন যে ছুঁয়েছে, সে-ই শুদ্ধ। তার আবার জল-অচল কী? ইস্কুলে বেশিদিন যেতে পারেনি ফুল্লরা, কিন্তু গানটা ভোলেনি।
সবার পরে জল নিতে এখন আর কষ্ট হয় না। ও জেনে গেছে এটাই নিয়ম। কাওরাপাড়ায় দুখে কাওরার ঘরে জন্মালে এরকমই হয়। সেই জন্মদাতা বাবাও যদি ওরকম বেঘোরে চলে যায়। শ্যাওলা-জড়ানো, ফুলে ঢোল দুখের লাশ মনে পড়ে যায় বারবার ফুল্লরার।
সনকার চুল খোলা হয়ে গেছিল। সে কেমন চোখে ফুল্লরাকে দেখতে দেখতে বলল, ‘ঘরে শ্যাম্পুর পাতা আছে, মাথা ঘষে চান কর। বিকেলে, তোর মামি গেলবার যে শাড়িটা দিয়েছিল, নীল করে, ওটা পরবি।’
ফুল্লরা অবাক হয়ে গেল। মার ভালো শাড়ি বলতে ওই একটাই। কোনওদিন চাইলেও পরতে দেয় না। বলে ছিঁড়ে যাবে। হরিসভায় মোচ্ছবের সময় তাদের পাড়ার মেয়েরা কত সেজেগুজে যায়। সেসময় কতবার শাড়িটা পরতে চেয়েছে ফুল্লরা, মা দেয়নি। আজ কী হল তার! সে তবু কিছু জিজ্ঞেস করে না মাকে। বাবা চলে যাবার পর মা কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে। দশবাড়ি খেটে খেটে সারাক্ষণ তেতেপুড়ে থাকে, কিছু জিজ্ঞেস করলেই ঝাঁঝিয়ে ওঠে।
সে গোবরটা উঠোনে রেখে হাত ধুয়ে কোমরে বাঁধা ওড়নায় মুছে নিল। তারপর ঘরে এল। শ্যাম্পুর পাতাটা নেবে। নীচু ঘর, দিনের বেলাতেও আলো ঢোকে না। দেয়ালে একটা আয়না ঝোলানো আছে। তার ঘষা কাচে ফুল্লরা নিজেকে দেখার চেষ্টা করে।
এ গাঁয়ের অনেক মেয়েরই সকাল সকাল বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের সরকারি বয়সে পৌছনোর অনেক আগেই। শুধু গরিব ঘরে বা নীচু জাতের মধ্যে নয়, বড়ো বড়ো ঘরেও এটাই স্বাভাবিক। ভালো ছেলে পেয়ে গেলে সবাই হাঁকপাঁক করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়। সে সামনে মাধ্যমিক থাকলেও। আর ফুল্লরা তো স্কুলেই যায় না। তারওপর বাবাও নেই। তাই তার এই বয়সে বিয়ে ঠিক হওয়ায় কেউ অবাক হল না। কিন্তু ছেলের বাড়ি কোথায় জেনে সবার চোখ কপালে উঠে গেল। কথায় বলে, ‘কোনও কালে নেই ষষ্ঠীপুজো। একেবারে দশভুজো।’ একেবারে বম্বে। বম্বে তো একেবারে কল্পলোক। সেখানে ক্যাটরিনা কইফ, সলমন খান, শাহরুখ খান রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়। ভোরে সমুদ্র ধরে হাঁটলে বিগ বি-র সঙ্গে ধাক্বা লাগতে পারে। সেখানে শ্বশুরঘর করতে যাবে কাওরাপাড়ার ফুল্লরা কাওরা!
ফুল্লরার বন্ধুরা শুনে বলল, ‘তোর নাকি শাহরুখ খানের সঙ্গে বিয়ে!’
যদিও ঠাট্টা, তবু ফুল্লরার বুক তিরতির করে কেঁপে উঠল। সত্যি তার বিয়ে, তাও আবার বম্বেতে! মাঠে গোবর কুড়োনো, সেফটিপিন দিয়ে ফ্রক আঁটা, সবার শেষে জল নেওয়া– এই ছেঁড়াফাটা, তালিমারা জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে তার? শাহরুখ খান না হোক, তার বরের নাকি মেলা জমি-জিরেত, এখনকার মতো ভাতের ভাবনা থাকবে না বিয়ের পর। কিন্তু তাদের গাঁয়ের লোকগুলো কি হিংসুটে, কেউ একবেলা ভাত দেবে না, কিন্তু কু গাইতে ওস্তাদ। তাদের কাওরা পাড়ার বউ-ঝি থেকে শুরু করে, যে-বাবুদের বাড়ি মা কাজ করে, তারাও বলছে, ‘হুট করে কোথায় বিদেশ বিভুঁইয়ে বিয়ে ঠিক করে ফেললে, জানো তো, বিয়ের নাম করে মেয়ে পাচার চক্র চলছে রমরমিয়ে, মেয়েগুলোকে দিয়ে কী যে করাবে–’
তার ধলাদাদু তাকে পাচার করে দেবে! ভাবলেও হাসি পায়। বাবা মারা যাবার পর এই দাদুই তো তাদের টেনেছে সাধ্যমতো। ধলাদাদু, মার কীরকম কাকা হয়, বম্বের একটা ফ্ল্যাটে পাহারাদারের কাজ করে। সেই এনেছে সম্বন্ধটা। ছেলের বাড়ি বম্বে শহর থেকে একটু দূরে। বিট্টলপুরা বলে একটা গাঁয়ে। ছেলের বয়স নাকি একটু বেশি। ছেলের এক মেসো কলকাতায় থাকে, সেই এসে দেখে গেছে ফুল্লরাকে। মা যেদিন তাকে নীল শাড়ি পরে সেজেগুজে থাকতে বলেছিল, সেইদিনই। মেসোর নাম ভগবান দাস। পাকানো গোঁফে মোচড় দিতে দিতে সেই ভগবান দাস ফুল্লরাকে একটা প্রশ্নই করেছিল–
‘পিনে কা পানি আনতে কতদূর যেতে হয় বেটি?’
প্রশ্ন শুনে অবাক হয়েছিল, কিন্তু ঠিকঠাক উত্তরই দিয়েছিল। খুশি হয়েছিল ভগবান দাস। কে জানে, এক ঘণ্টা-দু ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ানোর কথা তাকে এত মুগ্ধ করেছিল কেন। হয়তো সে পরখ করে দেখতে চাইছিল ফুল্লরার ধৈর্য, সহ্যক্ষমতা। তারপর ফুল্লরাকে সুপুরি, রুপোর টাকা ও জরিন শাড়ি দিয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেছিল ভগবান দাস।
কয়েকদিনের মধ্যেই নিত্য শাহ-র বাড়ি কাজ করতে করতে ফোনে শুভ খবর পেয়েছিল সনকা। ফুল্লরাকে ওদের পছন্দ হয়েছে। কিন্তু জমি-জিরেত ছেড়ে ছেলে বিয়ে করতে আসতে পারবে না। ফুল্লরাকেই যেতে হবে। তাকে নিয়ে যাবে ভগবান দাস।
এতদিন গাঁয়ের লোকের নানান কথাতেও সনকার মন টলেনি। কিন্তু এখন বিয়ে হবে শুনে সে কেমন কেঁপে উঠল। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, ভাষাও অন্য, মেয়েটাকে সে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিচ্ছে, সব সে জানে, আর কী-ই বা করার আছে তার? কিন্তু সাতপাকটা অন্তত যদি তার সামনে হয়ে যেত, বুকটা আঁটা থাকত। এই ভগবান দাস, যাকে সে একদিন মাত্র দেখেছে, তার হাতে একটা উঠতি বয়সের মেয়েকে সঁপে দেবে? ফোনের মধ্যে তার আশঙ্কা টের পেয়েছিল ভগবান দাস, সে আশ্বস্ত করেছিল সনকাকে। ‘আরে বেটি, ঘাবড়াও মৎ। তোর মেয়েকে আমি কোনও কোঠিতে বেচতে যাচ্ছি না। সোজা শাদির মন্ডপে নিয়ে গিয়ে তুলব। আর তোর চাচা তো আছেই ওখানে।’
নির্দিষ্ট দিনে ভগবান দাস তাকে নিতে এসেছিল। নিত্য শাহ-র বউয়ের দেওয়া একটা পুরোনো কাপড়ের ব্যাগে টুকিটাকি জিনিস গুছিয়ে নিতে নিতে ফুল্লরা আবিষ্কার করেছিল মা কখন যেন নীল শাড়িটা তার ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এতদিন ঘোরের মধ্যে থেকে সে ভাবেইনি বিয়ে মানে মাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাওয়া। নীল শাড়িটা তার সেই ভুলে থাকা ব্যথাটা খুঁচিয়ে দিয়েছিল। বিছানায় উপুড় হয়ে কেঁদেছিল ফুল্লরা।
নতুন জায়গায় ঘুম আসতে দেরি হয়। কিন্তু বিট্টলপুরায় এসে বিছানায় পিঠ ঠেকাতেই ঘুম এসে গেল ফুল্লরার। কারণ দুদিনের ট্রেন জার্নিতে সে প্রায় ঘুমোয়নি বললেই চলে। মাকে ছেড়ে এতদূর চলে আসার কষ্ট একটা ফোড়ার মতো টাটিয়ে ছিল বুকের মধ্যে, তার ওপর অচেনা একটা লোকের সঙ্গে আসা, প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল হিংস্র নেকড়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।
স্টেশনে নেমে ধলাদাদুকে দেখে ওর মন অনেক হালকা হয়ে গেল। ধলাদাদু আজ যেতে পারছে না, তবে বিয়ের দিন অবশ্যই যাবে। তারপর দুবার বাস পালটে সন্ধে নাগাদ বিট্টলপুরায় এসে পৌঁছলো।
বাস থেকে নেমে সে দেখল পুরো গ্রামটা অন্ধকারে ডুবে আছে। মাঝে মাঝে টিমটিমে লণ্ঠনের আলো। গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ আসেনি। বাস থেকে নেমে কাঁচা সড়ক দিয়ে অল্প একটু হেঁটে ওর শ্বশুরবাড়ি। একটা লোক আলো নিয়ে এগোতে গেছিল। উঠোন ঘিরে ছড়ানো ছিটোনো ঘর। লণ্ঠনের আলোয় ও বুঝতে পারল না ভালো। ওরা ঢুকতেই একদল বাচ্চা ছুটে এল। ওদের চিৎকার থেকে একটাই শব্দ বুঝতে পারল ফুল্লরা।
‘পানিবাই! পানিবাই!’
কাকে বলছে কথাটা? নতুন বউকে এরা পানিবাই বলে নাকি? ওকে হাত-পা ধোবার জায়গা দেখিয়ে দিতে গেল এক মহিলা। খুব শক্ত, হাড়-হাড় চেহারা, রাগি মুখ। সে দাঁতে দাঁত চেপে যা বলল, তা থেকে মোদ্দা কথা বুঝে নিল ফুল্লরা। মহিলা ওকে বলছে, এটা শুখা দেশ, বাংলার মতো হরা-ভরা নয়, তাই পানি কম খরচ করতে হবে।
তাদের ঘটকপুকুরে তাকে খাবার জল পাবার জন্যে সবার পেছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াতে হয়েছে সত্যি, কিন্তু সে তো অন্য কারণে। সেখানে জলের ছড়াছড়ি। বাড়ির পেছনে হাঁসপুকুরে তারা ঝাঁপাঝাঁপি করে চান করত। আর এখানে দু-এক ঘটিতে তো পুরো গা-ও ভিজবে না। রাতের খাবারে মোটা মোটা রুটি আর বিচ্ছিরি স্বাদের একটা সবজি খেতেও ওর তত কষ্ট হচ্ছিল না, যতটা জলের জন্য হচ্ছিল।
রাতে ওকে শুতে দেওয়া হল একটা বুড়ির সঙ্গে। তাদের দেশে বয়স হলে সাদা বা হালকা খোলের শাড়ি পরে, এ বুড়ি পরে আছে ক্যাটকেটে সবুজ রঙের শাড়ি। তবে মানুষটা এমনি খারাপ না। শুয়ে শুয়ে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল আর বিড়বিড় করে কীসব বলছিল। একসময় বুড়ির হাত ওর কোমরে এসে থামল। কোমর টিপে টিপে বুড়ি যেন কী পরখ করার চেষ্টা করছে। হাতটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে ফুল্লরা কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সে নিজেও জানে না। মাঝরাতে হঠাৎ কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙল। বিছানা হাতড়ে দেখল বুড়িটা নেই। ঘরের বাইরে থেকে মেয়েগুলোর কান্না আর পুরুষের চিৎকার ভেসে আসছে। শুনতে শুনতে ফুল্লরা আবার ঘুমিয়ে গেল।
পরদিন ঘুম ভাঙল শক্ত এক হাতের ধাক্বায়। সেই রাগি রাগি বউটা ওকে ঠেলা দিচ্ছে।
‘এত বেলা অবদি ঘুমোলে পানি মিলবে?’
কে যেন পাশ থেকে বলল, ‘আহা, সে তো আজই নয়, আগে তো শাদি হোক।’
‘আরে রাখো তোমার শাদি, আজ যদি ঝুঁটি ধরে না তুলি, তবে আদত পড়ে যাবে বিছানায় শুয়ে থাকার।’
আরেকটি বউ অমনি ঝনঝন করে হেসে উঠল, ‘আহা কোন সুখে বিছানা আঁকড়ে থাকবে বলো, সে তো তুমিই দখল করে আছ!’
এই কথা শুনে রাগি বউটি দপদপ করে চলে গেল। অন্য বউগুলো, যারা ফুল্লরার বিছানার চারদিক ঘিরে ছিল, তারা বলল, ‘জলদি জলদি উঠে পড়, আজ না তোর শাদি?’
তাদের গাঁয়ে ‘ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে’ বলে একটা কথা আছে। কিন্তু ফুল্লরার বুক কেমন ধক্ করে উঠল শুনে। ‘আজই শাদি! ধলাদাদু যে বলল তিনদিন পরে?’
‘আহা, এই তিনদিন পানি আনার জন্য অন্য বাই রাখবে নাকি?’
আসা থেকেই ‘পানি’ শব্দটা কতবার শুনেছে ফুল্লরা। মাথায় এখন যেন সেই জল টলটল করে উঠল। বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল ও। বউগুলো চেঁচিয়ে উঠে বলল, ‘হায় হায়! এই দুবলি পাতলি লেড়কি কী করে পানিবাই হবে? ভগবানচাচা কেমন মেয়ে ঢুঁড়ে আনল!’
পাশ থেকে কে যেন বলল, ‘আশপাশের গাঁয়ে তো কেউ রাজি হল না। ভগবানচাচা তাই বলল, বাঙালি লেড়কিরা কথা শোনে, তার ওপর বাপও নেই।’
বিয়ের মন্ডপে বসেও ফুল্লরার মাথায় টলমলানি যাচ্ছিল না। পানিবাই! পানিবাই মানে কী! নতুন বউকে এদেশে পানিবাই বলে নাকি? ভগবানচাচাকে ও কোথাও দেখতে পাচ্ছিল না। পেলে বলত মাকে ফোনে ধরে দিতে। মা এখন নিত্য শাহ-র বাড়ি ঘর মুছতে মুছতে জানতেও পারছে না তার মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।
নিজের চিন্তায় এতখানি ডুবে ছিল ফুল্লরা, যে সে বুঝতেও পারেনি বিবাহমন্ডপে কখন বর এসে হাজির হয়েছে। বাচ্চাদের ‘দুলহা আ গয়া, দুলহা আ গয়া’ চিৎকারে সে সচকিত হয়ে দেখল তার সামনে এক দীর্ঘদেহ, প্রশস্ত বক্ষ মানুষ, এদেশের রীতি অনুযায়ী মুখ ঢেকে এসে দাঁড়িয়েছে। ফুল্লরার বুক দুরদুর করে উঠল, সমস্ত ভয়, সন্দেহ, অপমান, ক্ষুধা দূর হয়ে যাবে এইবার। তার কল্পলোকের শাহরুখ খান এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে বরমাল্য হাতে। কে যেন চেঁচিয়ে বলল, ‘মুখ খোলো কিষণলাল।’ দুলহা মুখের ওপর থেকে চাঁদমালার মতো ঢাকা সরিয়ে নিল। অমনি ফুল্লরার নাকে এসে লাগল একটা পচা গন্ধ। বাবাকে জল থেকে তোলার পর যেমন গন্ধ বেরোচ্ছিল। কিন্তু সত্যি সত্যি তো এমন গন্ধ কোথাও নেই। চারদিকে ঘিরে থাকা বউ-মেয়েরা সুগন্ধি ফুল ছুঁড়ছিল, কিষণলাল কড়া সেন্ট মেখে আছে, তবে? আসলে বুড়ো মানুষদের শরীর থেকে একধরনের পচা গন্ধ বেরোয়, শিথিল চামড়া, নড়া দাঁতের গন্ধ, বহু বছর দুনিয়া দেখে ভেতরটা পচে যাবার গন্ধ। সামনে দুলহা সেজে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, তার বয়স সত্তরের কম নয়। লোকটা ভাবলেশহীন চোখে ফুল্লরাকে দেখছিল, আর ফুল্লরার ষোলো বছরের সবুজ লাউডগা শরীর গুলিয়ে উঠছিল। এই তার শাহরুখ খান! সে মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল।
জ্ঞান ফিরতে দেখল, সেই বুড়ি মহিলা তার চোখমুখে অল্প অল্প জলের ছিটে দিচ্ছে। জলের স্পর্শে আরাম হচ্ছিল ফুল্লরার। আবার মায়ের কথাও মনে পড়ছিল। সে ডুকরে কেঁদে উঠতেই বুড়ি তাকে প্রবোধ দিয়ে বলল, ‘দুলহার বয়স আর রূপ দেখে ফালতু কষ্ট পাচ্ছিস। যেমন নাম-কা-ওয়াস্তে শাদি, তেমনি নাম-কা-ওয়াস্তে পতি। তোর আসলি মরদ তো ওইটা।’ বলে কী যেন একটা আঙুল দিয়ে দেখায় বুড়িটা। তার আঙুল অনুসরণ করে ফুল্লরা দেখে ঘরের কোণে একটা পিতলের বিশাল কলশি। গড়নটা তাদের দেশের তুলনায় খানিকটা আলাদা, কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেক বেশি ভারী। এতে করে জল আনতে গেলে মোষের শক্তি দরকার। আচমকা তার মাথায় পর-পর কিছু দৃশ্য-শব্দ খেলে যায়, গত রাতে বুড়ির তার কোমর পরখ করা, দুবলি-পাতলি বাঙালি, পানিবাই! সে-ই পানিবাই নয়তো?
কান্নায় তার শরীর ফুলে ফুলে ওঠে। বুড়ি তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, ‘পাগলি কাঁহিকা! এখনও বরের বয়স ভাবছিস বসে বসে। আরে, ও তোকে কোনওদিনই বিছানায় নেবে না। সে তো আছেই আশাবাই। ধরমপত্নী। তবে কি না, পুরুষের কাম, কখন কাকে দেখে জেগে ওঠে। কুছ সাল পহলে, এক বরসাতের রাতে, আশাবাই বাচ্চা বিয়োতে মাইকে গেছে, আমাকে ডাকল। তা কী করে না বলি বল, পানিবাই হলেও বউ তো বটে। শরীরের স্বাদ পেয়েছিল তো, তাই আমায় তাড়ায়নি। এখন তো আর পানি আনতে পারি না, তাও রেখে দিয়েছে। অথচ কত পানিবাই এল আর গেল।’
কান্না থামিয়ে বিষ্ময়ে হতবাক ফুল্লরা বুড়ির দিকে তাকায়। এই বুড়ি কিষণলালের বউ!
বুড়ি বলে চলে, ‘আসলি বাত কী জানিস? এ হল শুখা দেশ। সহজে পানি মেলে না। পানি দু-তিন গাঁও ভেঙে আনতে যেতে হয়। সকালে গেলে ফিরতে ফিরতে বিকেল তিনটে-চারটে। তা ঘরের বউ যদি পানি আনতে যায়, তবে ঘরের কাম-কাজ কী করে চলবে, খানাপাকানো, বালবাচ্চাদের পালপোষ কে করবে? তাই পানিবাইদের দরকার। শাদি তো একটা হচ্ছে, তাই মাইনে দিতে হয় না, ডাল-রুটি তো মিলবে দুবেলা। তা, কিষণলালের খুব বদনাম, বউটাও রাগি, তাই এখানকার কেউ আর পানিবাই হয়ে আসতে চায় না। একজনকে তো পিটিয়েই…’ বুড়ি কী যেন বলতে গিয়ে চুপ করে যায়। ফুল্লরা হাঁটুর ওপর মুখ রেখে সেই নৈঃশব্দ্য থেকে কিছু খুঁড়ে বার করার চেষ্টা করে, জলের মতো। শুখা দেশে চোখের জলও যে শুকিয়ে যায়, কে জানত!
দূরে দূরে ছোটো কয়েকটা টিলা। পশ্চিমের টিলার পেছন থেকে কমলা আলোর বলটাকে আস্তে আস্তে নেমে যেতে দেখল ফুল্লরা। সূর্য ডুবছে। আজ তার বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এখানকার বউরা মাথায় কলশি নিয়ে চলতে পারে। সেটা তার এখনও অভ্যাস হয়নি। সে কলশি নেয় কাঁখে। প্রথম প্রথম এত ভারী কলশি বইতে পারত না, একবার তো জলভরা কলশি দরজার কাছে পর্যন্ত এনে ফেলে দিয়েছিল। সেজন্য আশাবাই খুব মেরেছিল তাকে। রাতে খেতেও দেয়নি। গায়ের ব্যথায় সে পরেরদিন উঠতে পারেনি, জল আনাও হয়নি। সেই থেকে আশাবাই তাকে মারে না, কিন্তু বোলি বড়ো তীক্ষ্ণ তার। চাবুকের মতো সপাং করে গায়ে বেঁধে।
কিষণলাল বলে যে-লোকটা তার স্বামী, সে অবশ্য কিছু বলে না। উঠোনে পাতা চৌপাইতে বসে শুধু চোখ দিয়ে অনুসরণ করে তাকে। সে দৃষ্টি দেখলেই গা ছমছম করে ফুল্লরার। কারণ কিষণলাল তাকে যে দেখছে, সেটা আবার আশাবাই-এর নজর এড়ায় না। একসঙ্গে দুজোড়া চোখের ভার বহন করা কঠিন।
অন্যদিন ঠাঁ ঠাঁ দুপুর রোদে সে ফেরে। আজ রোদ পড়ে গেছে। অত কষ্ট হচ্ছে না তার। কিন্তু মাসিক শুরু হওয়ায় কোমরে সে আর কলশি রাখত পারছে না। এবার থেকে এদেশের বউ-ঝিদের মতো মাথায় কলশি বওয়া অভ্যাস করতে হবে তাকে।
রোদ নেই। তবু কলশি নামিয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্য একটা গাছের ছায়া খুঁজল ফুল্লরা। গাছ, গাছের ছায়া তাকে বাংলার কথা, নদীর কথা, মায়ের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সেই বিয়ের দিন মাকে একবার ফোন করেছিল ভগবান চাচাকে ধরে করে। তারপর কত দিন, কত মাস হয়ে গেল কোনও খোঁজ খবর নেই। কিষণলালের একটা মোবাইল আছে, সারাক্ষণ সে সেটা গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কোনও বরসাতের রাতে সে যদি ফুল্লরার শরীর চায়, তাহলে, কিষণলালের মোবাইল নাগালে পেয়েও, মাকে ফোন করা হবে না ফুল্লরার। মার তো ফোন নেই। মাকে ফোন করতে হবে দিনের বেলা, মা যখন কারও বাড়ি কাজ করে। জল আনতে আসা-যাওয়ার পথে কোনও বাজার পড়ে না, যে সেখানে একটা ফোনের বুথ খুঁজে ফোন করতে পারে। তার কাছে অবশ্য পয়সা নেই, পানিবাইরা তো পেটখোরাকি, হাতে পয়সা পায় না। কিন্তু তার নাকে এককুচি রুপোর নাকফুল আছে, বাবার শেষ স্মৃতি। ফোনের বুথ পেলে ওই ফুল দিয়ে সে মাকে ফোন করবে। মা যেন ধলাদাদুকে পাঠিয়ে তাকে এখান থেকে নিয়ে যায়।
খুঁজতে খুঁজতে ফুল্লরা দেখল দূরে একটা শিমুল গাছ। মাংসল লাল ফুলে ছেয়ে আছে। শিমুল ফুল ফুটেছে! তার মানে এটা বসন্তকাল! আর কদিন পরেই বৈশাখ মাস পড়বে, তাদের হরিসভায় মোচ্ছব হবে, তাদের পাড়ার মেয়েরা সেজেগুজে গিয়ে কত মজা করবে, শুধু সে-ই থাকবে না। সবাই জানবে যে শাহরুখ খানের…
হঠাৎ শিমুলফুলের রং দেখে বুক ধক্ করে ওঠে ফুল্লরার। বসন্ত এসে গেছে! তার মানে একদিন বর্ষাও আসবে। আশাবাই-এর আবার গর্ভ হয়েছে, বুড়ি, যার নাম যশোমতী জানিয়েছে তাকে। বর্ষাকালেই হয়তো সে মাইকে যাবে। সেইসময়, অন্ধকার রাতে, কিষণলালের বুকে তৃষ্ণা জেগে ওঠে যদি? বাংলার শ্যামল-সবুজ জল-ছলছল শরীর পান করার সাধ জাগে তার? যশোমতী বলেছে তাতে অন্যায় কিছু নেই । কিষণলাল তো তার শাদি করা মরদ, সে তার শরীর নিতেই পারে। কিন্তু আশাবাই-এর মতো ঘর বা বিছানা সে পাবে না কোনওদিন। কিন্তু কিষণলালের ইচ্ছেয় সায় দিলে আখেরে তারই ভালো। যখন ফুল্লরা একদিন বুড়ি হয়ে যাবে যশোমতীর মতো, আর পানি আনতে পারবে না দূর গাঁও থেকে, তখন, কিষণলালের মনে জাগরুক থাকতে পারে তার শরীরের স্মৃতি, সে হয়তো তাড়াবে না ফুল্লরাকে। তা না হলে রাস্তায় রাস্তায় ভিখ মেগে বেড়াতে হবে তাকে।
ফুল্লরা কি তাহলে সারাজীবন জল বয়ে আনবে একটা সংসারের জন্য, যে-সংসারটা তার নয়। তার নিজের আনা জলে দু-ঢোঁকের বেশি অধিকার থাকবে না তার? জল আনতে আনতে যশোমতীর মতো বুড়ি হয়ে যাবে সে? তখন তাকে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে, যদি না কোনও বরসাতের রাতে কিষণলালের ইচ্ছেয় সে সাড়া দেয়?
ভাবতেই ভেতরটা কেঁপে ওঠে। শিমুল ফুলের টকটকে লাল রং যেন বিপদ সংকেতের মতো তার চোখের সামনে নাচতে থাকে। বসন্ত থেকে বর্ষা আর কতই বা দূর। তাকে পালাতে হবে। তাকে এখনি পালাতে হবে। দৌড় শুরু করার আগে সে নিজের আনা জল, কলশি কাত করে আঁজলা ভরে আশ মিটিয়ে খেয়ে নেয়। তারপর ধাক্বা মেরে উলটে দেয় কলশিটা। জল মাটিতে গড়িয়ে যায়, শুখা মাটি তা শুষে নেয় মুহূর্তে।
অনেকক্ষণ থেকে মেয়েটাকে লক্ষ্য করছিলেন ইনস্পেকটর ঘোসলে। মেয়েটার সাজপোশাক মারাঠি গাঁয়ের বউয়ের মতো, কিন্তু ওর সবুজ পানপাতার মতো মুখ, নরম চাউনি বলে দিচ্ছে ও বাঙালি। কিছুক্ষণ আগে তিনি এক দল বাঙালি মেয়েকে উদ্ধার করেছেন মুম্বইয়ের এক কুখ্যাত কোঠি থেকে। এদের কলকাতা নিয়ে যাওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের দুজন প্রতিনিধি এসেছে কলকাতা থেকে। তিনি নীচুগলায় তাদের সঙ্গে কীসব বলেন…
হাওড়া স্টেশনে ট্রেনটা থামার পর টিভি ক্যামেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েগুলোর ওপর। সবাই ওড়না বা শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে ফেলল অমনি। শুধু একটা মেয়ে উদাসীন মুখে বসেছিল। সাংবাদিকদের হাজার প্রশ্নের উত্তরে যে শুধু একটাই কথা বলল, ‘পানিবাই’।
আবার ইস্কুলের সামনের টিউকল থেকে জল নিতে এসেছে ফুল্লরা। আগে যেমন আসত। কিন্তু ঠিক আগের মতো যে আর সবকিছু নেই তা সে বুঝতে পারছে। আগের মতো জলের জন্য সবার পেছনে দাঁড়াতে হচ্ছে বটে, কিন্তু আগে তাকে দেখে বউদের এরকম কানাকানি, গা-টেপাটেপি ছিল না। সেদিন হাওড়া স্টেশনের ছবি অনেকেই দেখেছে টিভিতে। ওকে মুম্বইয়ের কোঠি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, এরকম একটা খবর রটে গেছে চারদিকে। তাতে নতুন করে কিছু ক্ষতি হয়নি, আগেও ওরা একটেরে কাওরাপাড়ায় আধপেটা খেয়ে থাকত, এখনও তাই। মায়ের কাজগুলোও যায়নি, বরঞ্চ তার মেয়ের মুখ টিভিতে দেখা গেছে বলে খানিকটা সমীহ তৈরি হয়েছে। তবে সবাই সনকাকে বলছে, ‘আগেই তোমাকে বলেছিলাম, শুনলে না।’
তবে লাভ একটা হয়েছে, কলকাতা থেকে ভালো শাড়ি-জামা পরা, চশমা চোখে একদল মহিলা দামি গাড়ি চেপে এসেছিল শুধু ওর সঙ্গে কথা বলতে। তারা ওকে শহরের মহিলা স্বনির্ভর কেন্দ্রে ভর্তির ব্যবস্থা করেছে। কাজ শেখার পাশাপাশি কিছু রোজগারও হবে।
সবার জল নেওয়া হয়ে গেছে ভেবে ফুল্লরা তাড়াতাড়ি তার প্লাস্টিকের বোতল কলের মুখে বসাতে গেল। ঘোষেদের মেজোবউয়ের যে আর একটা বোতল বাকি আছে সে দেখতে পায়নি। মেজোবউ অমনি খরখরে গলায় বলে ওঠে, ‘আরে ছুঁড়ি, মর মর। তোকে ছুঁয়ে আবার অবেলায় চান করব নাকি? একে কাওরা-হাঁড়ি, তারওপর দিল্লি বোম্বে সৃষ্টি জজিয়ে এসেছিস!’
শুনে শুনে অভ্যস্ত, তবু খামোখা চোখে জল এল ফুল্লরার। কয়েক মাস আগেও তার আনা জলের জন্য হাঁ করে থাকত আশাবাই আর তার ছেলেমেয়েরা। কিষণলাল লোটা ভরে পানি খেয়ে তৃপ্তিতে বলত ‘আঃ’। ফুল্লরা বাড়ির জন্য কান্নাকাটি করলে যশোমতী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলত, ‘লোককে পানি পিলানা বড়ো পুণ্যের কাজ রে। পানিবাই কি যে সে হতে পারে?’ কয়েক মাসের তফাতে, সেই একই জল, তার ছোঁয়ায় অশুদ্ধ হয়ে গেল!