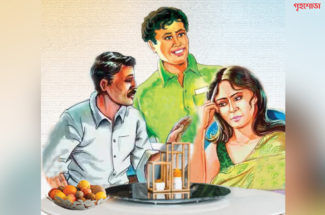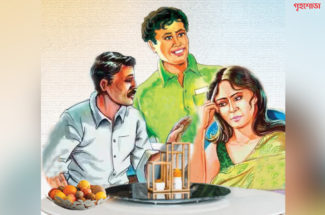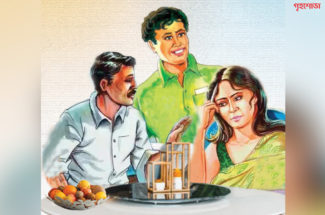‘আমিই সেই মেয়েটি–
আমিই সেই মেয়ে যার জন্মের
সময় কোনও শাঁখ বাজেনি
জন্ম থেকেই যে জ্যোতিষীর ছকে বন্দি।
যার লগ্ন রাশি রাহু কেতুর দিশা খোঁজা হয়েছে
না– তার নিজের জন্য নয়…’
যতবার শুনেছি শব্দগুলো বারবার মনে হয়েছে যে বংশপ্রদীপ বা কূলতিলক, এই আখ্যা শুধু ছেলেদের জন্যই বরাদ্দ থাকে কেন? শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের দ্বারা বংশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াতেই কি সন্তানের যাবতীয় সার্থকতা? কিন্তু তার বাইরেও তো অনেক কিছু থাকে নাড়ির বন্ধনে। ভক্তি, ভালোবাসা, দায়িত্ব, কর্তব্য– যা দিয়ে অটুট থাকে সম্পর্কের টান। মেয়েরা অর্থাৎ কন্যা সন্তানরা কি বাবা-মাকে এর কোনওটা দিতে অপারগ?
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার ছোটো হয়েছে। বেশিরভাগ বাড়িতেই একটি বা দুটি সন্তান। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার একটি বা দুটিই কন্যা। সময়ে তাদের পাত্রস্থ করে কর্তব্য পালন করেন পিতা-মাতা। ‘কন্যা-দায় শব্দটা বড়ো করুণ ভাবে বাজে প্রত্যেকটি মেয়ের বুকে কিন্তু প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রেখে তাকে গাঁটছড়া বাঁধতে হয় অন্য একটি পুরুষের সঙ্গে, বাবা-মাকে কর্তব্য বা দায় থেকে মুক্তি দিয়ে।
তাই বলে একটা মেয়ের তার মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব বা কর্তব্য সেখানেই ফুরিয়ে যায় না। এটা মেয়েরাও যেমন উপলব্ধি করেছে, তেমনই একক কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়া দম্পতিরাও। পুরোনো ধারণা বদলে তারাও বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, বিয়ে হয়ে অন্য পরিবারে চলে যাওয়ার পরও মেয়েরা তাদের মা-বাবার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে না, বিপদে আপদে পাশে দাঁড়ায়। ততটাই নির্ভর করা যায় সন্ততির উপর, যতটা তারা তাদের পুত্রের উপর নির্ভর করতে পারতেন।
এই রৌদ্রোজ্জ্বল ছবিটার অন্যপিঠেই কিন্তু মেঘলা দিনের বিষণ্ণতা। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। এখনও বেশিরভাগ পরিবারেই মেয়ে জন্মালে তাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানানো হয় না। নাগরিক জীবনের বাইরে মেয়ে হওয়ার আনন্দে কেউ মিষ্টিমুখ করায় না, তার জন্মদিন পালনেও কেউ তেমন উৎসাহী নয়। শুরু থেকেই ধরে নেওয়া হয় মেয়ে জন্মেছেই পরের ঘরে যাবে বলে, সে গলগ্রহ বই তো নয়। অথচ একসময় ‘মেঘে ঢাকা তারা’র নীতারা, ‘অন্য না’ ছবির অনন্যার মতো নিজের সব সুখ বিসর্জন দিয়ে কাঁধে তুলে নেয় মা-বাবার সংসারের দায়ভার।
আসলে বিয়ের সময় বা বলা ভালো কন্যা বিদায়ের সময়, কনকাঞ্জলির মধ্যে দিয়ে মায়ের সব ঋণ শোধ করে চলে যাওয়ার প্রতীকী আচার আজও পালন করা হয়। কিন্তু সত্যিই কি সব দায়-দায়িত্ব, ঋণ থেকে এভাবে বেরিয়ে আসতে পারে মেয়েরা? প্রকৃতিগত ভাবেই তাদের ইমোশনাল বন্ডিং অনেক বেশি থাকে জন্মদাতা বা জন্মদাত্রীর সঙ্গে। সুতরাং নিজের কাঁধে তাদের দায়িত্ব নিতে বিমুখ হয় না কন্যাসন্তানটি।
অনেকক্ষেত্রেই স্বামীর সহযোগিতা প্রার্থী হয় তারা, বিশেষ করে যখন তার মা-বাবার একটি মাত্র সন্তান সেই মেয়েটি। আজকাল স্বামীরাও যথেষ্ট সহযোগিতার মনোভাব সম্পন্ন। তারাও সেই দায়িত্ব ভাগ করে নিতে প্রস্তুত থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে তো মেয়ে নিজের কাছাকাছি কোনও ফ্ল্যাটে বা বাড়িতে বাবা-মাকে নিয়ে চলে আসে দেখাশোনার সুবিধা হবে ভেবে। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির যুগে এমন দৃষ্টান্তও কম নেই।
পরিচিত একটি মেয়ে, তার উপার্জনের একটি অংশ প্রতিমাসে তার মা-বাবার হাতে তুলে দিয়ে আসে বলে জানি। এতে তার স্বামীরও কখনও আপত্তি হয়নি। সুতরাং দিনকাল বদলের সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতাতে পরিবর্তন আসছে মানুষের– এটা সত্যিই সদর্থক ভাবনারই প্রকাশ।
আলো আছে তাই পাশাপাশি কালোও আছে। সাম্প্রতিক একটা রিপোর্টে বেশ চমকে দেওয়ার মতো খবর হল, সন্তান দ্বারা নির্যাতিত বয়স্ক মা-বাবার সংখ্যাটা দিনে দিনে বাড়ছে। ছেলের কাছে মা-বাবা বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তারা দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করছে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে কেন এই সামাজিক অবক্ষয়? তাহলে কি মানুষ সহানুভূতি, ভালোবাসার মতো সুকোমল বৃত্তিগুলো হারিয়ে ফেলছে?
বড়ো শহরগুলিতে করা সার্ভে থেকে এর কিছু কারণ অবশ্য মূল্যায়ন করা হয়েছে। উচ্চাকাঙ্খী পুরুষরা কর্মসূত্রে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন বা অন্য কোনও শহরে। কাজের ব্যস্ততা, ছোটো পরিবার নিয়ে সুখী থাকার অভিপ্রায়, ছোটো ফ্ল্যাটের অপরিসরতা, বারবার চাকরিসূত্রে ট্রান্সফার নেওয়া, সন্তানের পড়াশোনার খরচ– এমন নানা কারণ এখন গুরুত্ব পায়।
এই জীবনশৈলীর কোথাও স্থান হয় না প্রান্ত বয়সে এসে পড়া মানুষদুটোর। বিজ্ঞাপনের দম্পতি ও একটি সন্তানের সুখী ছবিতে বয়স্ক মা-বাবা নেহাতই বেমানান। বাড়িতে বন্ধুবান্ধব বা বসকে খুশি করতে পানভোজন, পার্টি এসব লেগেই থাকে। সেখানে বাবা-মায়ের উপস্থিতি বড়োসড়ো অন্তরায়। ফলে নিঃসঙ্গ বাবা-মার, ছেলের ঝকঝকে আধুনিক ফ্ল্যাটে নয়, স্থান হয় ভিটেবাড়ির স্যাঁতসেঁতে ঘরে। কখনও দু-একটা ফোনে পোশাকি খোঁজ নেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে সন্তানের কর্তব্য।
প্রশ্ন আরও একটা আছে। এই সময়ের সন্তানরা যেমন শিক্ষিত, তাদের মা-বাবাদের শিক্ষার মান তার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। তাহলে কি এটা নিতান্তই বাবা-মায়ের ব্যর্থতা? তারাই কি পারেননি সন্তানকে সুশিক্ষা দিয়ে বড়ো করতে?
মনোবিদরা বলছেন সমস্যার বীজ অন্য জায়গায়। আধুনিক সমাজে পুত্র-কন্যার সমানাধিকার, এমনকী সম্পত্তির ক্ষেত্রেও, একধরনের কর্তব্য বিমুখতার জন্ম দিচ্ছে পুত্রসন্তানটির মনে। তারা ভাবতে শুরু করেছে মা-বাবার দায়িত্ব মেয়েরও তাহলে গ্রহণ করা উচিত। সেই জায়গা থেকেই সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখিয়ে থাকে কিছু কিছু সন্তান।
বস্তুত মেয়েরা আবেগপ্রবণ, তাদের মা-বাবার সঙ্গে অ্যাটচমেন্টও বেশি। দায়টা অস্বীকার করা ছেলেদের পক্ষে যতটা সহজ, মেয়েদের পক্ষে প্রায়শই তা হয় না।
তাই আধুনিক সময়ের বৃদ্ধ মা-বাবা আজ নতুন করে ভাবছেন। তারাও অনেক বেশি নিশ্চিত হতে পারছেন যে মেয়েটি তার কর্তব্য থেকে পিছু হঠবে না। আর-পাঁচটা কাজের মতোই মেয়েরাও দায়িত্ব নিতে সক্ষম মা-বাবার, এটা বোঝার সময় এসেছে। তাই ভুলবেন না, আপনার কন্যা সন্তানটির কাঁধটা নরম হতে পারে, দুর্বল নয়।