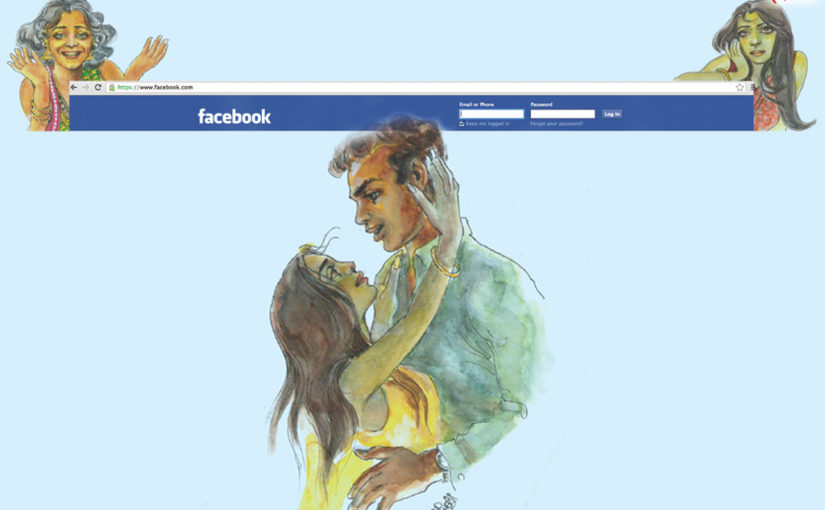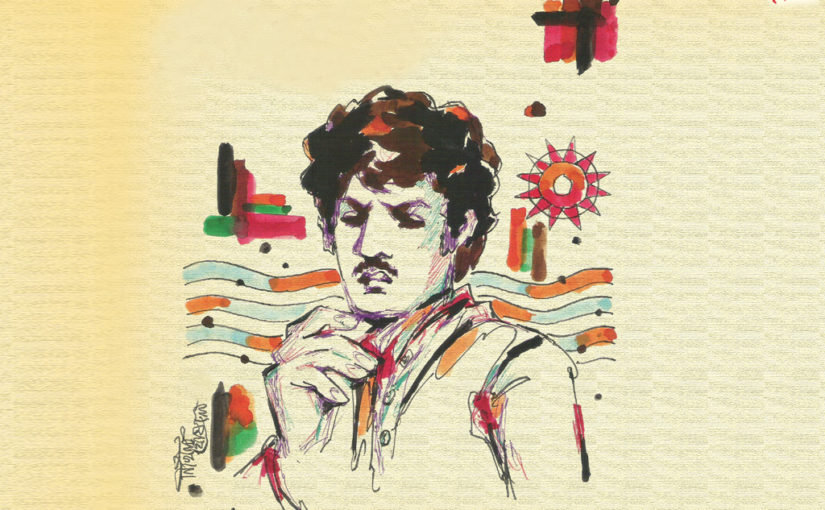অন্ধকারের মধ্যে দ্রুত গতিতে পিছিয়ে যাচ্ছে কিছু আলো। গ্রাম অথবা শহরের। এছাড়া দেখার মতো কিছু নেই। ট্রেনটার ডিপারচারই ছিল হাওড়া থেকে রাত আটটায়। কিছু দেখা যাবে না, জেনেও জানলার পাশের সিটটা দখল নিয়েছে ইমন। বাকি তিনবন্ধু ওকে আটকায়নি। কোনও এক আশ্চর্য কারণে ওরা ইমনকে বাড়তি অ্যাডভান্টেজটুকু দেয়। অন্তত হাওয়া খাওয়ার লোভে ওদের কেউ একজন ইমনকে জানলার সিটে বসতে বাধা দিতে পারত, দেওয়ার কথা ভাবেইনি। চারজনের মধ্যে ইমনের অধিকার যেন সবচেয়ে আগে। যদিও শুধু হাওয়ার কারণে ইমন এখানে বসেনি, হাওয়ার চরিত্র বুঝতে বসেছে। সে জানত এই টুরে হাওয়ার ধরনটা আলাদা হবে।
তাই হয়েছে, অন্য টুরের তুলনায় হাওয়ার ওজন প্রায় অর্ধেক। বাইরের অন্ধকারটাও তত নিরেট নয়, গাছপালা, পুকুর ঘাট, খেত-জমি, কুঁড়েঘর, পাকাবাড়ি সবই দিব্যি আন্দাজ করা যাচ্ছে। এমনকী মনোনিবেশ একটু গভীর করলেই কুঁড়েঘরে দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করা কিশোরীটিকেও যেন পাচ্ছে দেখতে। ফ্ল্যাটবাড়ির ইন্টারনেটে বুঁদ তরুণও নজর এড়াতে পারছে না। এসব দেখার চোখ বা আগ্রহ কোনওটাই নেই ইমনের তিনবন্ধুর, পার্থ, জয়দীপ, কৌশিকের। না থাকাটা অপরাধের নয় মোটেই। ওদেরও যে যার মতো নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তবে চারবন্ধুর বন্ধুত্ব কিন্তু খুব নিবিড়।
কলেজে এই চারজন একটা কোর গ্রুপ। এরা কেউই একে অপরের স্কুলের বন্ধু নয়। আলাপ হয়েছে কলেজে এসে। সম্পর্ক গাঢ় হয়েছে গত তিনবছর ধরে। ঘটনাচক্রে ইমনের স্কুলের কোনও বন্ধুই এই কমার্সখ্যাত কলেজটায় ভর্তি হয়নি। স্কুলেও ইমনদের একটা কোর গ্রুপ ছিল, সেটা কলেজের থেকে অনেক বড়ো। সেখানেও ইমনকে অজানা কারণে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। উদাহরণ হিসেবে যেমন বলা যায়, ইন্টার-স্কুল ফুটবল ম্যাচে কোনও বন্ধু চার পাঁচজন প্লেয়ারকে কাটিয়ে গোল করার সময় ইমনের উদ্দেশে বলটা বাড়িয়ে দিত। অন্যদের তুলনায় দুর্বল প্লেয়ার হওয়া সত্ত্বেও ম্যাচের পর ম্যাচ গোল পেয়ে টিমে টিঁকে যেত ইমন। এই ফেভার করাটা সোজাসাপটা ভালোবাসা নয়, ইমনকে সাফল্য এনে দিতে পেরে খুশি হয় বন্ধুরা।
স্কুল পেরিয়ে কলেজ শেষেও এই ধারা অব্যাহত রয়ে গেছে। অথচ বন্ধুরা গেছে পালটে। এমন নয় যে ইমনের মধ্যে লিডারশিপ কোয়ালিটি আছে, আবার ইমনকে দেখে মায়া বা করুণা জাগারও কোনও সম্ভাবনা নেই। সেরকম ঢিলে ব্যক্তিত্ব তার নয়। তবুও বন্ধুরা কেন যে এই ট্রিটমেন্টটা করে, আজও আবিষ্কার করতে পারল না। এর ফলস্বরূপ বন্ধুত্ব যতই নিবিড় হোক না কেন, বন্ধুদের সঙ্গে নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব রয়েই যায় ইমনের। যেমন ট্রেনের জানলার পাশে বসে সে উপলব্ধি করছে, এ টুরের বাতাস ওজনে হালকা, অন্ধকার তত নিরেট নয়, এটা তিন বন্ধুকে বলতে পারবে না। বললেও বুঝবে না তারা। না বুঝে ইমনের কথায় সায় দিয়ে দেবে। আঁতেল বলে ইমনের লেগ পুলও করবে না।
এবারের বেড়াতে যাওয়াতে তিন বন্ধুর আচরণেও অনেক বদল দেখা দিয়েছে। সেটা আদৌ তারা টের পাচ্ছে কিনা, কে জানে! একটু বেশিই হুল্লোড় করছে। সমগ্র এ বদলের মূল উৎস হচ্ছে, চারজন বন্ধু জীবনে প্রথমবার কোনও গার্জেন ছাড়া বেড়াতে যাচ্ছে বেশ কয়েক দিনের জন্য। পুরী যাচ্ছে। বাড়িতে বলেই রেখেছিল, ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষার পর আমরা চারজন কোথাও একটা বেড়াতে যাব। ‘না’ করতে পারবে না। এদের বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা চার বাড়িতেই অজানা নয়। পরস্পরের গার্জেনদের মধ্যেও আলাপ আছে। সেই বিশ্বস্ততা থেকে ছাড়া হয়েছে চার মূর্তিকে। জয়দীপ, পার্থর বাবা এসেছিল সি-অফ করতে। দুজনেই নিজের নিজের বাবাকে ফেরত পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বলছিল, আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে! ট্রেন ছাড়তে দেরি আছে। ছাড়লে ফোন করে দেব। আসলে ‘বাবা ছাড়তে এসেছে’ ব্যাপারটা ট্রেনের অন্য প্যাসেঞ্জারদের কাছে লুকোতে চাইছিল। নিজেদের অ্যাডাল্টহুড খাটো হয়ে যাচ্ছিল যে এখন অবশ্য বড়ো হয়ে যাওয়াটা সদম্ভে প্রকাশ করছে।
ইমন কৌশিককে জিজ্ঞেস করেছিল, তোর বাড়ি থেকে কেউ এল না! নাকি আড়াল থেকে লক্ষ্য রাখছে?
– না। যখন মানা করে দিয়েছি আসতে, কেউ আসবে না। বেশ কনফিডেন্স নিয়ে বলেছিল কৌশিক।
ইমন বলে, তোর কথার তার মানে একটা ওয়েট আছে বাড়িতে।
– তা আছে তেমনি আমিও বাড়ির কথা সব মেনে চলি। এই টুরে যেমন যা যা করতে আমায় বারণ করা হয়েছে কোনওটাই করব না।
কৌশিকের বলা শেষ হতেই ইমন জানতে চেয়েছিল, কী কী বারণ আছে?
– মদ খাওয়া আর সমুদ্রে চান করা। মাকে প্রণাম করে যখন বেরিয়ে আসছি, এই দুটো কথা বলে দিয়েছে।
ইমন অবাক গলায় বলেছিল, মদ না হয় নাই খেলি। সমুদ্রে যদি চান না করিস, তাহলে পুরী আসার মজাটাই তো পাবি না।
– কিছু করার নেইরে ভাই। চোখের আড়ালে থাকছি, তবু মা যখন আমায় বিশ্বাস করছে, তার মর্যাদা আমাকে দিতেই হবে। শুকনো মুখে বলেছিল কৌশিক। ওর মাতৃভক্তি যে এতটা গভীর, জানত না ইমন, দেখা যাক গোটা টুরে সেটা কতটা অটুট থাকে।
ইমনের মা-বাবাকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। রাতে খাওয়ার টেবিলে কথাটা যখন পেড়েছিল ইমন, মা সামান্য আঁতকে বলে উঠেছিল, তোরা একা একা যাবি! সঙ্গে কোনও বড়ো কেউ থাকবে না?
ইমনের হয়ে উত্তর দিয়েছিল বাবা। খেতে খেতে বলেছিল, ‘তোরা’ আবার ‘একা একা’ কী করে হল! যথেষ্ট বড়ো হয়েছে ওরা। তোমার ভাগ্য ভালো যে, ছেলে বাড়ির খাবার খেয়ে কলেজ করেছে। আজকাল তো বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে হিল্লিদিল্লির কলেজে চলে যাচ্ছে পড়তে।
মা আর কিছু বলতে পারেনি। আকাঙক্ষাও পুরোপুরি মোছেনি মুখ থেকে। এরপর বাবা ইমনের উদ্দেশ্যে বলেছিল, কলেজের পর থেকে চাকরিতে ঢোকার আগে পর্যন্ত বেড়াতে যাওয়াগুলো খুব ইন্টারেস্টিং হয়। জীবনে ভুলতে পারবি না এর স্বাদ। আমিও ভুলিনি। কোনও খারাপ অভিজ্ঞতা, বাজে স্মৃতি, বদ অভ্যাস নিয়ে ফিরবি না। যা সংগ্রহ করে আনবি, সব যেন ভালো হয়। সকলের জন্য গিফ্ট কিনবি, আলাদা করে টাকা দিয়ে দেব।
– নুলিয়া নিয়ে যেন সমুদ্রে চান করে, সেটা বলে দাও। বলেছিল মা।
বাবা বলল, ওর বয়সে নুলিয়ার হাত ধরে চান করা প্রেস্টিজের ব্যাপার। নেবে না জানি। তবে একটা কথা বলে দিই, সামনের দুসারি সাহসী লোকের পরে স্নান করবি। জানবি, সমুদ্রস্নানে সাহস দেখানোটা বোকামি, একই সঙ্গে সাহসের অপচয়ও বটে। ওই এনার্জিটা সমাজের কাজে খরচ করা উচিত।
বাবার কথাবার্তার ধরন কলেজের প্রফেসারদের মতো। আসলে কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানির অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক। মা মেয়েদের স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। বাবার কথাগুলোর মধ্যে আপাত ভাবে প্রশ্রয় থাকলেও, ছোট্ট একটা নিষেধও ছিল, ‘বদ অভ্যাস নিয়ে ফিরবি না’ মানে হার্ড ড্রিংক-এর কথা বলেছে বাবা। ইমন যে মাঝে মাঝে সিগারেট খায়, টের পেয়েছে আগে। দেয়ালকে শোনানোর মতো করে একদিন বলল, স্ট্রেসের কারণে মানুষ নেশার কবলে পড়ে। একসময় স্ট্রেস ঠিক মরে যায়। নেশা মানুষকে ছেড়ে যেতে চায় না। যেমন আমার ক্ষেত্রে যায়নি। পড়াশোনার চাপে কলেজ লাইফে ধরেছিলাম। ভালো কোনও এফেক্ট পড়েনি রেজাল্টে।
বাবা যতই বলুক, এই টুরে মদ খাবেই ইমন। কৌশিকের মতো অত সতী সে নয়, মাকে কথা দিয়েছে সমুদ্রে চান করবে না তো, করবেই না। ভাগ্যিস ওর মা মদ খেতে বারণ করেনি। ইতিমধ্যেই চারবন্ধু একসঙ্গে কয়েকবার মদ খেয়েছে। দারুণ মস্তি হয়। তবে রোজ খাওয়ার ইচ্ছে জাগেনি। পার্থ, জয়দীপ অবশ্য সিগারেটে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। স্মোকিংটা এই টুরে রেস্ট্রিক্ট করে চলবে ইমন, কোনও বদঅভ্যাস নিয়ে বাড়ি ফিরবে না। বাবার সিগারেট খাওয়া নিয়ে মা দিনরাত খিটখিট করে। অপরাধবোধের চিলতে সংকোচ লেগে থাকে বাবার মুখে।
– নাও, শান্ত ছেলে, চা-টা ধরো।
উলটোদিকের বার্থে বসে থাকা বউদির ডাকে চিন্তা ছেঁড়ে ইমনের। কাগজের কাপ বাড়িয়ে ধরেছে ট্রেনে সদ্য আলাপ হওয়া বউদি। লাজুক হেসে কাপটা নেয় ইমন। চাওয়ালাকে দাম মেটাচ্ছে বউদির হাজব্যান্ড। লোকটার মধ্যে বউ-গদগদ ভাব। উনি রীতিমতো বাচাল। এই কুপের ছটা বার্থে বউদিরা দুজন, বাকি চারটেতে ইমনরা। ছাব্বিশ, সাতাশের সুশ্রী বউদিকে নিজেদের কুপে দেখে খুবই উৎসাহিত হয়েছিল ইমনের তিনবন্ধু। ভেবেছিল, জমিয়ে বউদিবাজি করবে। সেই স্কোপ ওরা পায়নি। বউদি আগ বাড়িয়ে আলাপ করে নিল সবার সঙ্গে। তারপর থেকে চুটিয়ে চ্যাংড়ামি করে যাচ্ছে। তবে শ্লীলতার মাত্রা রেখে। ইমনদের গ্রুপও ওপেনলি
নোংরা ঠাট্টাইয়ার্কি করতে পছন্দ করে না। এই কম্পার্টমেন্টে আরও একটি আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য আবিস্কার করেছে ইমনের তিন সাগরেদ, একদম লাস্ট কুপে নাকি দারুণ এক সুন্দরী ট্র্যাভেল করছে তার ফ্যামিলির সঙ্গে। পর্যায়ক্রমে তিনবন্ধু মেয়েটাকে দেখে আসছে, চেষ্টা করছে নজর কাড়ার। এখনও পর্যন্ত পাত্তা পায়নি। এখন যেমন কৌশিক এই কুপে নেই। মেয়েটার কুপের কাছে গেছে। এটা নিয়ে তিনবার ট্রাই মারতে গেল। কে বলবে কৌশিকের স্টেডি গার্লফ্রেন্ড আছে! সুছন্দা, ওর পাড়াতেই থাকে। ছোটোবেলার প্রেম। জানলার পাশে বসে বন্ধুদের সমস্ত গতিবিধি টের পাচ্ছে ইমন, মেয়েটাকে দেখতে যাওয়ার কৌতূহল হয়নি। সুন্দর মেয়ে দেখার আগ্রহ ইমনেরও আছে, এই মুহূর্তে তার চেয়েও বেশি উপভোগ করছে জানলার পাশে বসে প্রথম স্বাধীনভাবে বেড়াতে যাওয়ার আনন্দ।
চা শেষ করে কাপ জানলার বাইরে ফেলে ইমন। ফের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। কৌশিক ফিরে এসেছে, এমন ভাবে হাঁপাচ্ছে, যেন একশো মিটার দৌড়ে এল। বলছে, নাঃ, কোনও চান্স নেই। হেভি ঘ্যাম। প্রথমবার তো তাকায়নি। এখন এমন ভাবে দেখছে, আমি বুঝি জেল পালানো আসামি। গতকালই ছবি বেরিয়েছে কাগজে।
বাকিরা তো সবাই হাসছেই, ইমনও হেসে ফেলে। কৌশিক এসে বসে তার পাশে, বউদি সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে বলে, দেখতে ভালো মেয়েরা ঘ্যাম একটু নিয়েই থাকে। এর জন্য ধৈর্য দেখাতে হয়।
দাদা বলে ওঠে, আরে, আমারও কি টাইম কম লেগেছে তোমাদের বউদিকে পটাতে! পাক্বা একবছর পিছন পিছন ঘুরেছি। তবে গিয়ে…
ইমন ভেবেছিল, বউদি বুঝি লজ্জা পাবে এই কথায়। তার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। কমপ্লিমেন্টটা নির্দ্বিধায় গিলে নিয়ে জয়দীপকে বলল, তোমাদের শান্ত বন্ধুটি তো একবারও মেয়েটাকে দেখতে গেল না। ওকে পাঠাও।
জয়দীপ ইমনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বউদিকে বলল, ও ভীষণ মুডি। জোর করে কিছু করানো যাবে না। যদি ইচ্ছে হয় নিজেই যাবে।
– নাকি রিফিউজ্যালের ভয়। কথাটা বলে বাঁকা হাসি সমেত ইমনের মুখের ওপর চোখ রাখল বউদি।
উত্তর দিল পার্থ। বলল, বার খাইয়ে লাভ নেই। এসব ওর গায়ে লাগে না। ও চিজই আলাদা।
জয়দীপ গা ঝাড়া দিয়ে সিট থেকে উঠল। বলল, দেখি, আর একবার ট্রাই মারি। এত কীসের অহংকার রে বাবা!
পার্থ আর দাদা সমস্বরে বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার। একেবারে ফিট করে ফিরতে হবে।
কুপ ছেড়ে বেরিয়ে গেল জয়দীপ। ওরও বোধহয় তিনবার হল। ইমন কিন্তু একটু অবাকই হচ্ছে। জয়দীপ তাদের মধ্যে সবচেয়ে ম্যানলি দেখতে। ছ’ফুটের ওপর হাইট। নিয়মিত জিমে যায়। চারবন্ধু হেঁটে যায় রাস্তায়, মেয়েরা জয়দীপের দিকে তাকায় প্রথমে। তবে জয় কথাবার্তায় তেমন চৌকশ নয়। কিন্তু মেয়েটা যে তাকাচ্ছেই না, কথা তো অনেক পরের ব্যাপার। মেয়েটাকে কি একবার দেখে আসবে ইমন? মনে হচ্ছে একটু অন্যরকম মেয়ে। একই সঙ্গে ভীষণ আলস্য লাগছে দেখতে যেতে। কী হবে দেখে? তিনটে ছেলেকে পাত্তা না দিয়ে মেয়েটা যে বিরাট কিছু করে ফেলেছে, তা তো নয়। এত গুরুত্ব দেওয়ার কোনও মানে হয় না।
একটু আগে ট্রেনটা বেশ স্লো চলছিল। ফের স্পিড নিয়েছে। আবার ছিটকে ছিটকে সরে যাচ্ছে গ্রাম, শহরের আলো। মেয়েদের ব্যাপারে ইমনের আলস্যটা বরাবরের। এই কারণেই দু’চারটে প্রেম জমে ওঠার আগেই কেটে গেছে। আসলে চেতনায় নাড়া দেওয়ার মতো সর্বক্ষণ আকর্ষণ জাগিয়ে রাখার মতো মেয়ের দেখা পায়নি সে।
– এই যে হ্যালো! কার কথা ভাবছ এত মন দিয়ে?
আবার বউদির ডাক। শান্তিতে চিন্তা-ভাবনা করতে দেবে না। ঘাড় ফেরায় ইমন। বলতে ইচ্ছে করছে, ক্যাটরিনা কইফের কথা ভাবছি। আপনার জায়গায় সে বসে থাকলে ভালোলাগত।
ইংরেজি, হিন্দি দুটোই ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারি না। বেশি বকতে হতো না। কথাগুলো না বলে ইমন আপন-হাসি হাসে। বউদির ভ্রূদুটো কাছাকাছি চলে এসেছে। বলে, ওরকমভাবে হাসছ যে বড়ো! কী বোঝাতে চাইছ, কেউ নেই?
– ওর কাছে অনেক আসে। টেঁকে না। ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বলল পার্থ।
– কে ছাড়ে? ঠোঁটের কোলে হাসি সমেত জানতে চাইল পলা বউদি। নাম-ঠিকানা আদানপ্রদান হয়ে গেছে অনেক আগে।
নির্বিকার ভঙ্গিতে ইমন উত্তর দিল, মেয়েরা। মাথা নাড়িয়ে প্রতিবাদের ঢঙে বউদি বলতে লাগল, হতেই পারে না। তোমার মতো লাভার বয় মার্কা দেখতে ছেলেদের ছেড়ে যেতেই চাইবে না মেয়েরা। ভালো চাকরিবাকরি যদি না পাও, তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। এব্যাপারে বেশির ভাগ মেয়েই ভীষণ প্র্যাকটিকাল।
– ‘লাভার বয় মার্কা দেখতে’ ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না! বলল ইমন।
পলা বউদি বলে, মানে, ‘প্রেমিক প্রেমিক’ দেখতে। যাদের সঙ্গে হাঁটলে, সিনেমায় গেলে অন্য মেয়েরা হিংসের চোখে দেখবে।
এবারও ব্যাপারটা ঠিক ক্লিয়ার হল না ইমনের কাছে। বউদি যেন তাকে নতুন
রং করা ম্যাটাডোরের সঙ্গে তুলনা করছে। যে-গাড়ির পিছনে লেখা আছে, দেখবি আর জ্বলবি লুচির মতো ফুলবি।
ফিরে এল জয়দীপ। চেহারায় হতাশা। দু’বাংক-এ দু’হাত রেখে, ঘাড় ঝুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে বলল, হল না। করিডোরে অনেক ঘুরঘুর করলাম, মাঝে মাঝে তাকিয়ে রইলাম ঠায়, একবারই তাকাল এমন বিরক্তির চোখে, আমার শার্টে যেন নর্দমার কাদা লেগে আছে।
কৌশিক জয়দীপের টি-শার্ট ধরে টেনে পাশে বসাতে বসাতে বলল, জানে দে ইয়ার, মেয়েটার বোধহয় কোনও প্রবলেম আছে।
– কী প্রবলেম? অবাক গলায় জিজ্ঞেস করে রঞ্জনদা।
কৌশিক বলল, কত কিছু হতে পারে। মেয়েটা হয়তো লেসবি।
‘লেসবি’ শব্দটায় সিঁটিয়ে গেল মন। পলা বউদির সামনে এই প্রথম ‘নীল’ মার্কা কথা বলে ফেলল তারা।
বউদির কোনও হেলদোল দেখা গেল না। রীতিমতো তর্ক জুড়ে দিল। বলতে লাগল, মেয়েটা যেহেতু তোমাদের পাত্তা দেয়নি অমনি সমকামী হয়ে গেল! নিজেদের ফেলিওর মানতে পারছ না।
হতাশ জয়দীপ ইমনের দিকে তাকিয়ে মিনতির সুরে বলল, বস্, তুই একবার যা। আমাদের মানটা রাখ।
– কোনও ইন্টারেস্ট নেই আমার বলে ইমন মুখ ফেরায় চলন্ত ট্রেনের জানলার বাইরে। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ফের বলতে থাকে, এ অপমানটা তোদের প্রাপ্য। মেয়ে দেখলেই খালি ছোঁকছোঁকানি। অথচ তোদের তিনজনের মধ্যে দু’জনের গার্ল ফ্রেন্ড আছে। তাদের প্রতি কমিটেড তোরা।
জয়দীপ আর রা কাড়ে না। শ্রেয়ার সঙ্গে ওর পাঁচবছর ধরে প্রেম। প্রায় রোজই দেখা করে। শ্রেয়ার স্কুল ছুটির সময় দাঁড়িয়ে থাকে চৌমাথায়। দু’দিন যদি না দাঁড়ায়, শ্রেয়া ফোন না করে সোজা চলে আসে কলেজে। সারপ্রাইজ ভিজিট, নিজেদের রিলেশনটা জয়দীপের কলেজ বান্ধবীদের কাছে এস্ট্যাবলিশ করে দিয়ে যায়।
– প্রেম করি বলে কি অন্য মেয়ে দেখব না? ওই মেয়েটারও বয়ফ্রেন্ড থাকতে পারে। তাতে আমাদের দিকে তাকালে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে। এটুকু ঝাড়ি সকলেই মেরে থাকে। বলল কৌশিক। সমর্থনে পলা বউদি বলে ওঠে, এটা একেবারে ঠিক বলেছে কৌশিক। তোমাদের রঞ্জনদাও এ ব্যাপারে কিছু কম যায় না।
বলার পর নিজের বরের দিকে কপট শাসনের দৃষ্টিতে তাকাল বউদি। চোখ নামিয়ে লজ্জা পাওয়া হাসি হাসছে রঞ্জনদা।
পার্থ বলে ওঠে, এই ইমন, আমার তো কোনও প্রেম নেই। তুই আমার হয়ে যা না।
ইমন বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে পার্থর দিকে তাকায়। বলে তাতে তোর কী সুবিধে হবে?
কথাটা ভেবে বলেনি পার্থ, ফলে চুপ করে যায়। ওর হয়ে পলা বউদি বলতে থাকে, আসলে তোমরা হলে একটা ইউনিট। তোমাদের কারুর জিত হলে সকলের জয়।
– আমি ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম। বলার পর পার্থ বলে। যা না ইমন। তুই পারবি। একটু আগে বউদি ঠিকই বলছিল, তুই ‘লাভার বয়’ মার্কা আছিস। আমরা দেখেছি মেয়েরা সবসময়ই দামি চকোলেট দেখার মতো তোর দিকে একবার আড়েঠাড়ে দেখে নেয়। তুই এমন বেভুল হয়ে থাকিস, মেয়েরা ভাবে তোর হেভি পার্সোনালিটি। ঘাঁটাতে ভয় পায় তোকে।
বার খায় না জেনেও পার্থ কথাগুলো কেন যে বলছে! ইমন ফের মুখ ঘুরিয়ে নেয় জানলার বাইরে। এখন শুধু ট্রেনের ঘটা ঘং, ঘটা ঘং শব্দ। দুপাশে বোধহয় ধু ধু প্রান্তর, আলোটালো কিছু দেখা যাচেচ্ছ না।
কুপের সবাই খানিকক্ষণ চুপ করে ছিল। কৌশিক শুরু করল কথা। বলল, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে মেয়েটা খোঁড়া। বহুদিন আগে একটা গল্পে পড়েছিলাম, অনুবাদ না
বাংলার কোনও লেখকের মনে পড়ছে না। একটা ছেলে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়ের প্রেমে পড়ল। রোজ দেখত তাকে। ঘটনাচক্রে একদিন তাকে দেখল রাস্তায়। মেয়েটার একটা পা নেই। প্রচন্ড মানসিক ধাক্বা খেয়েছিল প্রেমিক। প্রেমের শেষ পরিণতি কী হয়েছিল এখন আর মনে নেই।
কৌশিক থামার পর কেউ কিছু বলল না। ট্রেনের স্পিড বুঝি একটু কমল। হুইসেল দিচ্ছে। এক্সপ্রেস ট্রেন এমনিতে মিতভাষী, হুইসেল টুইসেল বড়ো একটা দেয় না। অন্ধকারে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে কাউকে যেন ডাকছে ট্রেনটা।
নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ে ইমন। বলে, যাই, দেখে আসি। কার জন্য তোরা এত লাফাচ্ছিস।
ইমনের ডিসিশনে তিনবন্ধু এতটাই চমকেছে, একজন বাক্যহারা হলেও, দু’জন একসঙ্গে সবিস্ময়ে বলে ওঠে, সত্যিই যাবি!
করিডোরে পা দিয়ে লাস্ট কুপের দিকে তাকাতেই মেজাজ খিঁচড়ে যায় ইমনের। পরিস্থিতি মোটেই অনুকূল নয়। টিটি চেক করছে টিকিট। চেকারের গায়ে সেঁটে আছে দুটো প্যাসেঞ্জার। এরা নিশ্চয়ই আরএসি অথবা ওয়েটিং লিস্ট। বার্থ কনফার্ম করতে চাইছে। টিটি লাস্ট কুপের টিকিট চেক করতে ব্যস্ত। কোনও একটা ব্যাপারে টিটির সঙ্গে লাস্ট কুপের বচসা চলছে। ইমন পায়ে পায়ে পৌঁছে যায় কুপটার সামনে। প্রথমেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে মেয়েটাকে, সবে হয়তো মাধ্যমিক দিয়েছে। বাস্তবিকই পরীক্ষাটা শেষ হয়েছে দু’দিন আগে। তবে সৌন্দর্যকে যেন ডমিনেট করছে ওর আভিজাত্য। খাড়াই নাক, চওড়া কপাল, পাতলা ঠোঁট, না ফোলানো সিল্কি কালো লম্বা চুল, গায়ের রং গোলাপি ফরসা। মেয়েটার এই মুহূর্তের মুখের অভিব্যক্তি চেহারার সঙ্গে মানানসই নয়। কিছুটা বিরক্ত আর হেল্পলেস ভাব। ইমনের উপস্থিতিটাও সে এখনও লক্ষ্য করেনি। কারণ, তার সমস্ত মনোযোগ টিটির ওপর। ইমনও বুঝে নিয়েছে টিকিট চেকার এখন যে-ক্যাচালটা করছে মেয়েটার ফ্যামিলির সঙ্গে, স্রেফ পয়সা খাওয়ার ধান্দা।
মেয়েটার বাবার সঙ্গে চেকারের তর্ক চলছে, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ওর বাবা, মুখের অনেক মিল। কেসটা হচ্ছে এই, মেয়েটার ফ্যামিলির দু’জন সিনিয়র সিটিজেন, একজন মহিলা অন্যজন পুরুষ। খুব বুড়ো না হলেও, দু’জনেই ষাট ক্রস করেছেন, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ থাকার কথা নয়। টিকিটের দামে ছাড় পেয়েছেন তাঁরা। নিয়ম অনুযায়ী টিটি ওই দু’জনের বয়সের প্রমাণপত্র দেখতে চাইছে। সেরকম কোনও আইকার্ড তাঁদের কাছে নেই। নিয়মটা তাঁরাও জানেন, বাড়ি থেকে বেরোনোর শেষ মুহূর্তে বার করে রাখা ভোটার কার্ডটা লাগেজে রাখতে ভুলে গেছেন। এ সমস্ত কিছুই কনফেস করা হয়েছে টিটিকে। কোনও কথা শুনবে না টিটি। বিশাল অঙ্কের ফাইন আর নানান নিয়মকানুন শোনাচ্ছে। টিটির গায়ে সেঁটে থাকা বার্থ কনফার্ম না হওয়া দুই প্যাসেঞ্জার নিজেদের সমস্যার কথা তুলতেই পারছে না এই তর্কবিতর্কের মাঝে।
ঝামেলাটা দেখতে আরও দু’চারজন প্যাসেঞ্জার ইমনের পাশে, ঘাড়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সিনে এবার এন্ট্রি নেয় ইমন। বলে, একটা কথা বলি?
চশমার ওপর দিয়ে ইমনকে একবার মেপে নিল চেকার। বলল, বলো।
কুপে বসা বৃদ্ধ, বৃদ্ধার দিকে একবার চোখ-নির্দেশ করে নিয়ে ইমন চেকারকে বলল, ওঁদের দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে ষাট পেরিয়েছেন, আর ভুলে যাওয়া একটা স্বাভাবিক ঘটনা। আপনি ইচ্ছে করলেই আইকার্ডের ব্যাপারটা ইগনোর করতে পারেন।
– আমি চাকরির রুল অনুযায়ী কাজ করছি। তুমি কে এ ব্যাপারে বলার? বলল টিটি।
ইমন চটজলদি জবাব দেয়, আমি এ দেশের একজন নাগরিক। আমার কর্তব্য সিনিয়র সিটিজেনকে হেল্প করা। আমি সেটাই করছি।
টিকিট চেকার একটু ধস খেল মনে হচ্ছে। চোখ নামিয়েছে নিজের হাতে ধরা লিস্টে, পেন ঠেকিয়ে পড়ার ভান করছে। প্রতিপক্ষ দুর্বল হয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটাকে যেতে হয়। ইমন বলে ওঠে, যদি ওঁদের বয়স আন্দাজ করতে আপনার অসুবিধে হয়, আমাদের গ্রুপ তো আছেই, কম্পার্টমেন্টের আরও অনেক প্যাসেঞ্জারকে ডেকে ওঁদের দু’জকে দেখাতে পারি। দেখুন তারা কী বলে। মেজরিটি তো মানবেন?
চেকারের দম শেষ। হেরে যাওয়া দৃষ্টি নিয়ে তাকায় ইমনের দিকে। হাসি পেয়ে যাচ্ছে ইমনের, সে যে যুক্তিটা দিয়েছে, এগেনস্টে আরও অনেক পয়েন্ট তোলা যায়। বোঝা যাচ্ছে টিটির স্টকে সে সব নেই। মাথা নিচু করে লোকটা গজগজ করতে থাকে, আইন ইজ আইন। যখন একবার পাস হয়ে গেছে মেনে চলতে হবে আমাদের। আমরা তো চাকরি করি…
কথাগুলো বলছে বটে টিটি, গ্রুপ টিকিটটা ফেরত দিয়ে দিয়েছে মেয়েটির বাবার হাতে। ইমন ক্রেডিট নেওয়ার জন্য মেয়েটির দিকে একবার তাকায়, ভীষণ বিস্মিত হয়, মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে হাসছে! ঠোঁটে নয়, চোখে জ্বলজ্বল করছে হাসির আভা। লজ্জায় চোখ সরিয়ে নেয় ইমন, এগিয়ে যায় সামনে। এখানে ট্রেনের দরজা। দুটোই বন্ধ। বাঁদিকের দরজাটা খুলে দাঁড়়ায় ইমন। হাওয়ার ঝাপট এসে লাগছে গায়ে, উড়ছে চুল। সামনে অন্ধকার প্রান্তর।
মেয়েটার হাসি ভেঙে দিল ওর নিজেরই আভিজাত্যের মোড়ক, সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়ল শরীরের কানায় কানায়। সম্পূর্ণ সাদা ড্রেস পরেছে মেয়েটা, আপারটা কুর্তি, নীচেরটা ফুল লেংথ কিছু একটা হবে। বাবু হয়ে বসেছিল বলে বোঝা যায়নি। সব মিলিয়ে মেয়েটার মধ্যে একটা ইতিহাসের রাজকন্যা টাইপ ভাব এসেছে। চোখের হাসি দিয়ে ইমনকে ভালোলাগাটা সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতে পেরেছে। ইমনের দারুণ ভালো লেগেছে মেয়েটাকে। বুকটা কেমন যেন জ্বালা জ্বালা করছে, সেইজন্যই দাঁড়িয়েছে হাওয়ায়। কারওকে ভালো লাগলে বুক জ্বালা করে, এই প্রথম জানল ইমন। আসলে এত ভালো আগে তো কোনও মেয়েকে দেখেনি সে।
ঘাড় তোলা উটের নাকের ডগায় ডুবন্ত সূর্য। ডিজিটাল ক্যামেরার সি্্ক্রনে ফোটোটা ফ্রেম করেও শাটার টিপল না ইমন। ফোটোটার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। পুরী ফেরত চেনা-পরিচিতদের কাছে এই ছবি হামেশাই দেখা যায়। তালুর সাইজের ক্যামেরাটা প্যান্টের পকেটে পুরে ইমন ফের হাঁটতে থাকে স্বর্গদ্বারের রাস্তা ধরে। বিকেল থেকে এই রাস্তায় পায়চারি করে চলেছে। একবার মেরিন ড্রাইভ রোডের দিকে চলে গিয়েছিল, ফিরে এসেছে তড়িঘড়ি। ওদিকে বড়োলোক টুরিস্টদের বিচরণক্ষেত্র। দামি ঝকঝকে সব হোটেল।ঞ্জট্রেনের মেয়েটার ফ্যামিলি ওদিকের হোটেলে উঠবে না। মেয়েটার চেহারায় যে-আভিজাত্য দেখা গিয়েছিল, সেটা জিনগত। ওই গ্রুপের হাবেভাবে, পোশাকেআশাকে টাকাপয়সার উদাসীন ঔদ্ধত্য ছিল না। নেহাতই মিডলক্লাস ফ্যামিলি। খানিকটা ভীরুও বটে, টিটির সঙ্গে গুছিয়ে ঝগড়াও করে উঠতে পারছিল না। ট্রাভেল করছিল স্লিপার ক্লাসে, এসিতে নয়। ওরা স্বর্গদ্বারের আশপাশের কোনও হোটেল বা হলিডে হোমেই উঠেছে। হলিডে হোমের সম্ভাবনাই বেশি। মেয়েটি ছাড়া বাকিদের বয়স এবং বডিল্যাঙ্গোয়েজ দেখে বোঝা যায়, এরা হলিডে হোমেই স্বচ্ছন্দ।
ইমনরাও হলিডে হোমে উঠেছে। পার্থর বাবার ব্যাংক-এর হলিডে হোম। উনিই অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছেন। বাজেটের কারণেই ব্যাংকটা বেছে নেওয়া। ইমনরা কেউ তো রোজগার করে না। তবে পার্থ যেমনটা বলেছিল, হলিডে হোমের ঘর থেকেই সমুদ্র দেখা যায়, মোটেই তা নয়। ছাদে বা ব্যালকনিতে যেতে হচ্ছে। সমুদ্র আড়াল করে আছে হলিডে হোমের সামনে বিশাল এক হোটেল। পার্থ বলছে, বছর চারেক আগে ও যখন বাবা, মা-র সঙ্গে হলিডে হোমটায় এসে উঠেছিল হোটেলটা ছিল না। কথাটা কোনও বন্ধুই বিশ্বাস করেনি। চার বছর বয়স হতেই পারে না হোটেলটার। হয় পার্থ মিথ্যে বলছে অথবা কোথাও একটা ভুল করছে। চারবছর আগে অন্য কোনও জায়গায় উঠেছিল হয়তো। হলিডে হোমের রুম অবশ্য বেশ ভালো। স্পেসিয়াস, মোজাইক ফ্লোর। চারতলা বাড়ি পুরোটই হলিডে হোমের।
ইমনরা আছে দোতলায়। সেখানে তিনটে রুম, অ্যাটাচড বাথ। তিনটে ইউনিট থাকতে পারে। ঘরগুলোর ডবল সাইজের এরিয়ায় কমন কিচেন কাম ডাইনিং। ইমনদের নিয়ে দোতলায় এখন দুটো ইউনিট। একটা ঘরে বুকিং নেই, তালা দেওয়া। অন্য যে-ইউনিট আছে দোতলায়, তিনজন মেম্বার, বৃদ্ধ বৃদ্ধা আর কাজের মেয়ে নমিতা। মেয়েটার নামটা জেনে যাওয়ার কারণ, বুড়োবুড়ি কিছুক্ষণ অন্তর ওই নাম ধরে ডাকছে, কিছু না কিছু ফরমাশ করতে ডাকা। ইমন বুড়োবুড়িকে এখনও চাক্ষুস করেনি, মেয়েটাকে দেখেছে। খানিকটা কৌতুহল বশেই দেখা।
ট্রেন কাকভোরে পৌঁছে গিয়েছিল পুরী স্টেশনে। অটোরিক্সায় হলিডে হোমে পৌঁছে একঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল ভিতরে ঢুকতে। গেটে তালা। হাঁকডাক করে কারওর সাড়া পাওয়া গেল না। ভোরের দিকে ঘুম গাঢ় হয়, কেয়ারটেকার তেড়ে ঘুম লাগিয়েছে। কাঁধে লাগেজ নিয়ে ইমনরা চারবন্ধু গিয়েছিল গলির মুখে চায়ের দোকানে। অত ভোরে চায়ের দোকান কিন্তু খুলে গেছে। হয়তো বুঝেশুনে খুলে রেখেছে। ভ্যানে, অত ভোরে হোটেল, হলিডে হোমে ঢুকতে পারবে না টুরিস্টরা।
হলিডে হোমের গেট খুলেছিল ভোর ছটায়। মুশকো চেহারার নিদ্রালু চোখের কেয়ারটেকারকে কৌশিক ঝাঁঝিয়ে বলে উঠেছিল, ভোরের দিকে যখন এরকম একটা ইম্পর্ট্যান্ট ট্রেন আছে, কত টুরিস্ট আসে, গেট খোলা রাখেন না কেন? লাগেজ নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি একঘণ্টার ওপর।
পোড় খাওয়া মস্তানের মতো কৌশিকের দিকে তাকিয়ে ছিল লোকটা। যেন বলতে চাইল, সস্তায় থাকতে এসেছ, কাঁচাঘুম থেকে উঠে গেট খুলে দিচ্ছি এই ঢের। বাড়াবাড়ি করলে ঘাড় ধরে বার করে দেব।
ওই তাকনোতেই ধস খেয়ে গিয়েছিল চারবন্ধু। কেয়ারটেকারের থেকে চাবি নিয়ে গুটিগুটি পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নিজেদের রুমের তালা খোলে। তখনই কানে এসেছিল ‘নমিতা’ নামটা। বৃদ্ধ অশক্ত গলায় মেয়েটার নাম ধরে ডেকে কিছু একটা দিতেটিতে বলছিলেন।
ইমনরা ঘরে ঢুকে প্রথমেই দুটো ডবলবেড এক জায়গায় করে নিল। চারজন একসঙ্গে শোবে। টয়লেটের কাজ সেরে ওরা তৈরি হচ্ছিল সমুদ্রে স্নান করতে যাবে বলে, সকলেরই মধ্যেই বেশ তাড়া। হলিডে হোমে আসার পথে সমুদ্রকে দেখেছিল প্রায় অন্ধকারের মধ্যে। ফসফরাসের মুকুট মাথায় দিয়ে ধেয়ে আসছিল ঢেউগুলো। ধীরে ধীরে ফরসা হয়েছে চারপাশ, সমুদ্র তাদের যেন ডাকছিল। ঢেউয়ের গর্জন আবছা হয়ে এসে পৌঁছোচ্ছিল কানে। সেইসময় কৌশিক এসে খবর দিল, পাশের মেয়েটা একেবারে ঝক্বাস জিনিস! ডাইনিং-এ চা বানাচ্ছে, একবার দেখে আয়।
পার্থ, জয়দীপ লাফিয়ে চলে গিয়েছিল দেখতে। ফিরে এসে বলেছিল, নাঃ, সত্যিই হেভি জিনিস!
ওদের কথা শুনে কৌতূহলী হয়েছিল ইমন, গরিব পরিবার থেকে আসা কাজের মেয়ে কত ভালো দেখতে হতে পারে! ইমন গিয়েছিল যাচাই করতে। ডাইনিং কাম কিচেনে পা রাখতেই ঘুরে তাকিয়েছিল বছর তেরো চোদ্দোর মেয়েটা। শ্যামলা রং, একমাথা কোঁকড়া চুল, চোখে কোনও ভাষা নেই। পরনে জংলা ছাপ ফ্রিল দেওয়া ফ্রক। শরীরে সদ্য যৌবনের অবশ্যম্ভাবী লাবণ্য। হবেইবা না কেন? অবস্থাপন্নের বাড়িতে কাজ করার সুবাদে খেতে পরতে পায় ভালো। মোদ্দা কথা মেয়েটার মধ্যে অসাধারণ কিছু দেখেনি ইমন। হতাশ লেগেছিল বন্ধুদের রুচির কথা ভেবে। ট্রেনের মেয়েটিকে দেখেও বলেছিল, দারুণ দেখতে! এই মেয়েটার ক্ষেত্রেও তাই। দু’মেয়ের চেহারায় আভিজাত্যের বিশাল ফারাকটা চোখেই পড়ছে না!
হলিডে হোম থেকে বেরোনোর আগে জয়দীপ আলাপ সেরে এল বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সঙ্গে। ওঁরা একমাসের জন্য বুক করেছেন ঘর। অবসর জীবনের ছুটি কাটাচ্ছেন। নিজেদের দেখভালের জন্য বাড়ির কাজের মেয়েটিকে নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে। ইতিমধ্যে পুরীতে সাতদিন কাটিয়ে ফেলেছেন ওঁরা। বৃদ্ধ বাজার করে আনছেন, নমিতা রান্না করে খাওয়াচ্ছে। ইমনরা রান্না করতে জানে না, লোকাল কারওকে দিয়ে করানোর কথাও ভাবেনি। বাইরে খেয়ে নেবে ঠিক করেছে।
আজ সমুদ্রে নামার আগে খাবার দোকানে ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছিল ইমনরা। সি-বিচের বালিতে পা দিয়েই চারবন্ধু ভুলে গিয়েছিল অনেক কিছুই, রুদ্ধশ্বাসে দৌড়েছিল জলের দিকে। মা সমুদ্রে নামতে বারণ করেছে, ভুলে গিয়েছিল কৌশিক। ইমন ভুলে মেরে দিয়েছিল বাবার কথা, সামনে দু’সারি সাহসী মানুষের পরের সারিতে স্নান করতে বলেছিল বাবা। ইমনরা যেখানে ঢেউয়ের সঙ্গে ওস্তাদি করছিল, সামনে কোনও সারি ছিল না, সাহসী দু’চারটে মানুষ আরও দুটো ব্রেকের পর গিয়ে স্নান করছিল। সি বিচে এসে ট্রেনের দাদা-বউদিকে খুঁজে নেওয়ার কথা ছিল চরবন্ধুর। স্নানের মজায় সেসব ভাবনা উড়ে গিয়েছিল মাথা থেকে।
ইমন বাদে ট্রেনের সেই মেয়েটার কথাও ভুলে গিয়েছিল তিনজন। জলের সঙ্গে হুটোপাটির মধ্যেও ইমন এপাশ ওপাশ তাকাচ্ছিল, যদি দেখা যায় তাকে। জলে দাপাদাপি করা ভেজা পোশাকের টুরিস্টদের মধ্যে যদি বিদ্যুতের মতো ঝলকে ওঠে সাদা ড্রেসের সেই মেয়ে! পরক্ষণেই মনে হয়েছিল, কী বোকা আমি! ট্রেনের ড্রেসটা পরেই স্নান করতে আসবে তার কী মানে আছে! নানান পোশাকের ভিড়ে মেয়েটাকে চিনে নিতে হবে। তার মুখোমুখি আর একবার অন্তত হবেই ইমন। দেখে নেবে মেয়েটি বিশেষ পছন্দের যে-দৃষ্টিতে ইমনের দিকে তাকিয়ে ছিল, তা কতটা গভীর? টুরে কিংবা কোনও অনুষ্ঠানে টাইম পাসের জন্য আলগা ভালো লাগা ছিল না তো সেটা? এখানে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে সে যদি না চেনার ভান করে, ইমন মোটেই ধাওয়া করবে না। রিলেশন একতরফা হয় না কখনও। সাদা ড্রেসের রাজকুমারী লুকের মেয়েটা স্মৃতিতে থেকে যাবে সারাজীবন। কেননা এতদিন পর্যন্ত সত্যিকারের ভালোলাগা বলতে এই মেয়েটাকেই লেগেছে ইমনের। মেয়েটা তার দিকে হাসির আভা সমেত তাকানোর পর ইমন নিজেকে সামলাতে গিয়ে দাঁড়়িয়েছিল ট্রেনের দরজায়। অদ্ভুত একটা রি-অ্যাকশন হচ্ছিল বুক জুড়ে। হয়তো একেই বলে প্রথম প্রেমে পড়ার অনুভূতি!
সুখের মুহূর্তটা খানিকবাদেই হোঁচট খেয়েছিল। ইমনের সন্দেহ হচ্ছিল নিজেকে, আমি ঠিক দেখলাম তো? মেয়েটার এক্সপ্রেশন রিড করতে ভুল হয়নি কোনও? নাকি নিজের বাসনাটা মেয়েটির মুখে বসিয়ে দিয়েছি? যেহেতু ওকে খুব পছন্দ হয়েছে আমার। ব্যাপারটা নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য দরজা থেকে সরে এসে করিডোর ধরে ফিরছিল ইমন, মেয়েটির কুপের সামনে এসে হাঁটা স্লো করে নিয়েছিল। দৃষ্টি কেড়ে নিল যেন মেয়েটিই, তখন আর চোখের ভাষায় হাসছিল না, হাসি চলকে এসেছিল ঠোঁটেও। দু’টো বিট মিস করেছিল ইমনের হার্ট। হাসি বিনিময়ের চেষ্টা না করে বাড়িয়ে দিয়েছিল হাঁটার স্পিড। জানত, হাসতে গেলেই ভীষণ ক্যাবলা দেখাত তাকে।
অতিরিক্ত আনন্দে কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল ইমন। এমনটাই হয়, অপ্রত্যাশিত সুসংবাদে যেমন কেঁদে ফেলে মানুষ। ইমন গম্ভীরমুখে ফিরেছিল নিজেদের কুপে। বন্ধুরা সোৎসাহে জানতে চেয়েছিল, কী হল রে? দেখলাম, টিটির সঙ্গে আর্গুমেন্ট করে ওদের ফ্যামিলিতে এন্ট্রি নিচ্ছিস। জানলার ধারে ইমনের ছেড়ে যাওয়া জায়গাটা ফাঁকাই ছিল। সেখানে গিয়ে বসতে বসতে ইমন বলেছিল, তাকিয়েছে, হেসেছেও।
‘সে-এ-এ-এ কী-ই-ই-ই রে-এ-এ-এ’ বলে এত জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিল তিনবন্ধু, কম্পার্টমেন্টের সব প্যাসেঞ্জার নিশ্চয়ই একবার চমকে উঠেছিল। লাস্ট কুপে ওই মেয়েটার কানেও অবশ্যই আওয়াজটা গেছে। কেমন জানি অস্বস্তি হচ্ছিল ইমনের। পলা বউদি বলেছিল, তা এত বড়ো একটা অ্যাচিভমেন্টের পর মুখটা ওরকম গোমড়াথেরিয়াম করে বসে আছো কেন?
– এত এক্সাইটেড হওয়ারইবা কী আছে! দুনিয়ায় প্রতি মিনিটে কোটিকোটি ইয়ং ছেলেমেয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে প্রথমবার হাসছে!
ইমনের কথায় উৎসাহে ভাঁটা পড়েছিল পলা বউদির। জয়দীপ ছোট্ট করে ফুট কেটেছিল, ম্যাথে ওর মাথা চিরকালই ভালো।
পলা বউদি হেসে জানতে চেয়েছিল, কী গো, সত্যিই হেসেছে তো। নাকি পাত্তা দেয়নি বলে রেগে আছো?
– ক্যালি নেওয়ার জন্য ঢপ মারার ছেলে ও নয়। তবে মালটা একটু বেরসিক। বলেছিল পার্থ। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে গিয়েছিল অন্য প্রসঙ্গে। ইমনের দায় থেকে গেল ঘটনা সত্যি প্রমাণ করার। বন্ধুরা তাকে বহুদিন ধরে চেনে, মেয়েটা যে তার প্রতি ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে বিশ্বাস করেছে সহজেই। চ্যালেঞ্জটা রয়ে গেল রঞ্জনদা, পলা বউদির কাছে।
রাত গড়াতে বাড়ি থেকে আনা খাবার খেয়ে যে যার বাংকে শুয়ে পড়ল। ঘুম আসতে দেরি হয়েছিল ইমনের, মনের চোখে ভাসছিল মেয়েটার হাসিমুখের ছবি। শেষ রাতে গাঢ় হয়েছিল ঘুম। ধাক্বা মেরে তুলে দিল পার্থ, এরে ওঠ ওঠ, প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে গাড়ি।
ধড়মড় করে উঠে বসে লাগেজ প্যাক করতে শুরু করেছিল ইমন। কামরার অনেকেরই ইমনের মতো অবস্থা, হুড়োহুড়ি করে ব্যাগ গোছাচ্ছে। রাত থাকতে গন্তব্যে পৌঁছে গেলে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। ইমনের তাড়া একটু বেশি, মেয়েটা না চোখের আড়ালে চলে যায়। আর হয়তো দেখা হবে না। পুরীতে যা ভিড় থাকে টুরিস্টের! দেখা হওয়াটা কো-ইন্সিডেন্স নির্ভর। প্ল্যাটফর্মেই চোখাচোখি হওয়াটা দরকার। পলা বউদি, রঞ্জনদা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি, মেয়েটা ইমনের ব্যাপারে ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে।
দেখা হল। দাদা, বউদি সমেত ইমনরা যখন ব্যাগ কাঁধে ট্রেন থেকে নামল, দেখেছিল প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় মেয়েটা ফ্যামিলির সঙ্গে এক্সিট-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পরনে সেই সাদা ড্রেস। বারবার পিছন ফিরছে মেয়েটা।
ইমনের পাশে হাঁটতে থাকা কৌশিক বলেছিল, তোকে খুঁজছে। হাত নাড়, হাত নাড়…
হাত তুলতে হয়নি। মেয়েটা খুঁজে নিয়েছিল ইমনকে। ফ্যামিলি মেম্বারদের থেকে ইচ্ছাকৃত পিছিয়ে পড়ে হাত নেড়েছিল ইমনকে লক্ষ্য করে। তারপর লজ্জা পেয়ে হারিয়ে গেল ভিড়ে।
‘জিও ওস্তাদ!’ বলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছিল ইমনের বন্ধুরা। পার্থ একটা ডিগবাজি মারার প্রয়াস নিয়েছিল, ইমন তাকে আটকায়। ডিগবাজি মারার প্রবণতা পার্থর বরাবরের। আনন্দ-স্ফূর্তির ঘটনা ঘটলেই যেখানে সেখানে ডিগবাজি খেয়ে নেয়।
প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই বন্ধুরা শপথ নিল, এই ট্রিপেই মেয়েটার সঙ্গে ইমনের প্রেমের পাকা একটা সম্পর্ক করিয়ে ছাড়বে। চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে খুঁজে বার করবে মেয়েটার ফ্যামিলি পুরীতে কোথায় উঠেছে।
সকালে সমুদ্রস্নানে গিয়ে সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে গেল ওরা। রঞ্জনদা, পলা বউদির খোঁজও করেনি। দাদা-বউদি বলে দিয়েছিল তারা স্বর্গদ্বারের কাছেই থাকবে, কোনও এক কোম্পানির গেস্ট হাউসে। কোম্পানির নামটা ভুলে গেছে ইমন। বাকি তিনবন্ধু দাদা-বউদির নামই নিচ্ছে না। সমুদ্রে ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে ইমনরা হা-ক্লান্ত হয়ে ফিরেছিল হলিডে হোমে। সমুদ্রের নোনাজল, বালি ধুতে ফের আর-এক প্রস্থ স্নান করল বাথরুমে গিয়ে। হলিডে হোম থেকে বেরিয়ে ভাতের হোটেলে লাঞ্চ সারল। ফিরে এসে টানা ঘুম। যখন উঠল, বেলা গড়িয়ে গেছে অনেক। জানলার বাইরে হলুদ আলো দেখে ইমন বন্ধুদের তাড়া দিয়েছিল, চ চ, বেরোবি তো!
ওদের মধ্যে কোনও উৎসাহ দেখা গেল না।ঞ্জজয়দীপ বলেছিল, তুই ঘুরে আয়। সকাল থেকে যা গেল, হেভি টায়ার্ড লাগছে, এই বেলাটা রেস্ট নেওয়া ভালো।
পার্থ, কৌশিকেরও দেখা গেল একই মত। বিছানা ছেড়ে উঠতে চাইছে না। ড্রেস চেঞ্জ করে পকেটে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল ইমন। তারও টায়ার্ড থাকার কথা, কোন এনার্জিতে বেরিয়ে পড়ল, বন্ধুরা বোধহয় খেয়াল করেনি। বিচ-এর দিকে তাকিয়ে পাকারাস্তা ধরে সেই কখন থেকে হাঁটাচলা করল ইমন, ট্রেনের মেয়েটা চোখে পড়ল না। ওরাও কি রেস্ট নিচ্ছে? নেওয়ার কথা কিন্তু নয়। ইমনদের মতো সকালে নিশ্চয়ই সমুদ্রে দু’ঘণ্টা দাপাদাপি করেনি। তাছাড়া ইমনের তিনবন্ধু যতটা না ক্লান্তির কারণে বিশ্রাম করছে, তার চেয়ে বেশি আলস্য উপভোগ করছে। যতদূর মনে হচ্ছে মেয়েটার ফ্যামিলি উঠেছে চক্রতীর্থ রোডের দিকে। ওই রাস্তায় যায়নি ইমন, এখান থেকে অনকটাই দূর। কাল একবার ট্রাই নেবে।
সানসেট দেখতে বিচ-এ প্রচুর ভিড় হয়েছিল। সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। টুরিস্টরা সিলুয়েট হয়ে গেছে। সি-বিচের স্থায়ী মেলায় জ্বলে উঠছে লম্প, হ্যাজ্যাক, রঙিন টুনিবাল্বের মালা। সমুদ্রের এলোপাথারি বাতাস কিছু যেন বলতে চাইছে ইমনকে! মেয়েটা এখন কোথায়, বলছে হয়তো সেটাই। বাতাসের গতিবিধি যেহেতু অবাধ, জানে মেয়েটার হদিশ। ইমন অনুবাদ করতে পারছে না বাতাসের ভাষা। নিজের আস্তানায় ফিরতে থাকে ইমন।
সিঁড়ি ভেঙে হলিডে হোমের দোতলায় এসে ইমন থমকে দাঁড়াল। তাদের রুমের দরজা আর তালাবন্ধ রুমটা মুখোমুখি। তারপরই করিডোরের টিমটিমে আলোয় দাঁড়িয়ে গল্প করছে কৌশিক আর বুড়োবুড়ির কাজের মেয়ে নমিতা। কৌশিক কথা বলছে বেশি, দেয়ালে ঠেসান দেওয়া নমিতা সলজ্জ হাসি ধরে রেখেছে মুখে। কৌশিক একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ইমনের দিকে। ফের মেয়েটার সঙ্গে কথায় মেতে গেল।
ইমন বড়োবড়ো পায়ে ঢুকল নিজেদের রুমে। কৌশিকের কান্ড দেখে মাথা গরম হয়ে গেছে তার। জয়দীপ, পার্থ বিছানায় ড্রিংক্স সাজিয়ে বসেছে। ওদের উদ্দেশ্যে ইমন রাগের সঙ্গে বলে ওঠে, কৌশিক এটা কী করছে!
পার্থ গ্লাসে এক সিপ মেরে বলল, কী আবার করবে! ওর যা স্বভাব, মেয়ে দেখলেই লাইন মারার ধান্দা…
– তোদের বারণ করা উচিত ছিল। গরিব ঘরের মেয়ে, লেখাপড়া জানে না, কৌশিককে তো বিশ্বাস করে বসবে।
ইমনের কথা গ্রাহ্যে না এনে জয়দীপ বলে, ওইসব মেয়ে লেখাপড়া না জানলেও কাকে কতটা বিশ্বাস করবে, তার হিসেব ভালোই করতে পারে। তুই চাপ নিস না। মাল খাবি আয়।
– আমার ইচ্ছে করছে না। বলে নিজের লাগেজ ব্যাগের দিকে এগিয়ে যায় ইমন, একটা গল্পের বই এনেছে পড়ার জন্য। পিছন থেকে ফের জয়দীপ বলে উঠল, দেখা পেলি ট্রেনের মেয়েটার। মেজাজ দেখে মনে হচ্ছে তো পাসনি।
ঘুরে দাঁড়ায় ইমন। সন্ধানী দৃষ্টি রাখে জয়দীপের ওপর। কী বলতে চাইল জয়? মেয়েটার সঙ্গে দেখা না হওয়ার কারণেই ইমনের ঈর্ষা হচ্ছে কৌশিককে। ও যেহেতু একটা মেয়ে পেয়ে গেছে! ইমনকে বুঝতে এত ভুল করছে বন্ধুরা! এদের সঙ্গে বেড়াতে না এলেই ভালো হতো। কাল যদি পুরী ছেড়ে চলে যায় ইমন, কোনও আপশোশ হবে না।… এতদূর ভেবে হোঁচট খায় ইমন, না, এই ট্রিপে না এলে রাজকন্যা টাইপের মেয়েটার সঙ্গে তার দেখাই হতো না। মেয়েটাকে যে করে হোক খুঁজে বার করবে কাল।
এবারটা নিয়ে চারবার পুরী আসা হল ইমনের। প্রথমবার খুবই ছোটো ছিল, যাকে বলে জ্ঞান হয়নি। বাবা, মায়ের থেকে গল্প শুনেছে। দ্বিতীয়বার এসেছিল ক্লাস সিক্সে। লাস্ট মাধ্যমিক দেওয়ার পর। তার মানে বছর পাঁচেক আগে। সেই স্মৃতির সঙ্গে এখনকার পুরীর পরিবেশের কোনও মিল নেই। তখনও ভিড় ছিল আবার প্রতিটি মানুষের গা-লাগোয়া নির্জনতাকেও লক্ষ্য করা যেত। সকলের হাঁটাচলার মধ্যে ঢিলেঢালা আয়েসি ভাব। এখন ছবিটা উলটো, ভিড় তো বেড়েইছে, সবার মধ্যে কেমন একটা হুড়োহুড়ি ভাব। যেন অফিসের বাস ধরার তাড়া। সমুদ্রে স্নান করতেও দৌড়োচ্ছে সেইভাবেই।
ইমনরাও স্নান করতে এসেছে বিচে। কালকের মতো এসেই জলে নেমে পড়েনি। হলিডে হোম থেকে বেরিয়ে দোকানে ব্রেকফাস্ট করতে করতে ঠিক করে নিয়েছে স্নানের আগে বিচের এদিক ওদিক ঘুরে ট্রেনের মেয়েটা এবং পলা বউদি-রঞ্জনদার খোঁজ করবে তারা। বিচে এসে একটা জায়গা মিটিং পয়েন্ট হিসেবে নির্দিষ্ট করল চারবন্ধু। সেখানে একহাত মতো বালি খুঁড়ে দু’জন করে বিপরীত দিকে হাঁটা শুরু করেছে। ইমনের সঙ্গে ছিল কৌশিক, কখন যে সে সরে পড়েছে টের পাওয়া যায়নি। ইমন এখন একাই বিচ ধরে হেঁটে চলেছে, দৃষ্টি স্নানরত টুরিস্টদের ওপর। কথা হয়েছে দশমিনিট হাঁটার পর বালি খুঁড়ে রাখা জায়গায় দু’দল মিট করবে। তার মধ্যে যদি যাদের খোঁজা হচ্ছে, পাওয়া যায় ভালো, না পেলে ফের বিকেলে চেষ্টা করা হবে।
দশ মিনিটের অনেক বেশিই হেঁটে ফেলেছে ইমন। আশা করে বসে আছে দেখা পাবে ট্রেনের মেয়েটার। এমনটা নাও হতে পারে, ইমন যেদিকে চলেছে হয়তো দেখা হয়ে গেল রঞ্জনদা-পলা বউদির সঙ্গে। জয়দীপ, পার্থ যে-ডিরেকশন-এ গেছে সেখানেই পাওয়া গেল ট্রেনের মেয়েটাকে। সেই হিসেবে ইমন মেয়েটার থেকে অনেকটাই দূরে চলে এসেছে। এবার বোধহয় ফেরা উচিত। হাঁটা থামিয়ে দেয় ইমন। বিচ-এ দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে প্যানারমিক ভিউ দেয় সমুদ্রে স্নানরতদের ওপর। মেয়েটার আভাসমাত্র নেই, ফ্যামিলিরও কারওকে চোখে পড়ছে না। দেখা নেই রঞ্জনদা-পলা বউদিরও। থিকথিকে ভিড়ের ভিতর থেকে ওদের শনাক্ত করাটাও দুঃসাধ্য কাজ। কৌশিক যদি ছেড়ে না পালাত ইমনকে, দু’জনে মিলে খোঁজাটা আরও জোরালো হতো। কৌশিকের সরে পড়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কাল সন্ধেবেলা কৌশিককে প্রচুর কথা শুনিয়েছে ইমন। বুড়োবুড়ির কাজের মেয়েটার সঙ্গে যখন গল্প করে ফিরল কৌশিক, ইমন চার্জ করেছিল, ওর সঙ্গে কী কথা হল তোর এতক্ষণ?
কৌশিক দাঁত বার করে বলেছিল, কিছুই না। ওই কোথায় থাকেটাকে জিজ্ঞেস করলাম। সিনেমার কোন হিরোর ফ্যান? এইসব আটভাট।
– আটভাটগুলোও একটু শুনি। এতটা সময় কাটালি কী কী কথায়? বলে কৌশিককে চেপে ধরেছিল ইমন।
তখনও আহ্লাদ কাটেনি কৌশিকের, ইমনকে আগ্রাহ্য করে বোকাবোকা হেসে জয়দীপকে বলেছিল, কীরে, আমার জন্য বানা ড্রিংক্স!
জয়দীপ গ্লাসে ওর জন্য মদ, জল মিশিয়ে এগিয়ে দিয়েছিল। ইমন কৌশিককে ছাড়েনি, ফের জিজ্ঞেস করেছিল, কী হল, বল। আর কী কথা হল?
গ্লাসে চুমুক মেরে কৌশিক বলেছিল, বললাম, তোমাকে অনেকটা শুভশ্রীর মতো লাগে দেখতে। নায়িকার সঙ্গে তুলনা করাতে খুব খুশি হল।
কৌশিককে কোণঠাসা করার জন্য ইমন জানতে চেয়েছিল, মেয়েটা কোথায় থাকে বলল?
– কোথায় আবার, বুড়োবুড়ির কাছে, টালিগঞ্জে।
– ওর নিজের বাড়ি কোথায়?
– ক্যানিং-এর দিকে। গ্রামের নাম কী বলল, এখন আর মনে নেই।
– ক্যানিং-এর গন্ডগ্রামের মেয়েটা পরিবারের অভাবের তাড়নায় এই অল্পবয়সে শহরে লোকের বাড়ি এসে কাজ করছে। তোর কথায় বিশ্বাস করে ও যদি নিজেকে শুভশ্রী ভাবতে শুরু করে এবং তোর মতো ভদ্রবাড়ির ছেলের পিছনে ঘুরতে থাকে, বারংবার ঠকবে। তুইও ওকে নিজের বাড়িতে কাজের মেয়ের চেয়ে বেশি মর্যাদ দিবি না। এইভাবে মেয়েটার মনে মিথ্যে আশা জুগিয়ে দেওয়া কি ঠিক? ইমনের কথা আর ওড়াতে পারেনি কৌশিক, থতমত খেয়ে গিয়েছিল। বাকি দুই বন্ধুও ছিল চুপ করে। ইমন কথা শেষ করেছিল এই বলে, তোর কাছে অবশ্য এসব কথার কোনও মূল্য নেই। মায়ের পা ছুঁয়ে করা প্রমিস তুই রাখতে পারিস না, মদও খেলি, চানও করলি সমুদ্রে। একটা কোথাকার কোন মেয়ের জন্য তুই ভাবতে যাবি কেন! তোর যে একটা প্রেম আছে সেটাও হয়তো ভুলে গেছিস!
ডোজটা একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। গুম মেরে যায় তিনবন্ধু। মদের গ্লাস ধরে রেখেছিল হাতে, মুখে তুলছিল না। ওদের রিলিফ দিতে ইমন উঠে গিয়েছিল হলিডে হোমের ছাদে। তারা জ্বলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রের সাদা ঢেউ দেখছিল। একা লাগছিল বড্ড। মনে পড়ছিল বাড়ির কথা। মোবাইল থেকে ফোন করে কথা বলল মায়ের সঙ্গে। মাকে অবশ্য বুঝতে দেয়নি মনের অবস্থা, ‘বেড়াতে দারুণ লাগছে’ এমনটাই বলেছিল। পুরী এসেই পৌঁছোন
সংবাদ দিয়েছিল ফোনে, সেদিনই আবার ফোন করাতে মায়ের খটকা লাগে। জিজ্ঞেস করেছিল, সত্যিই ভালো আছিস তো? থাকার জায়গাটায়গা মনের মতো হয়েছে?
– হ্যাঁরে বাবা, হ্যাঁ। দারুণ আছি। এইমাত্র ছাদে এলাম। কী হাওয়া! সমুদ্রও দেখা যাচ্ছে। বাড়তি উচ্ছ্বাস দেখিয়ে মাকে আশ্বস্ত করেছিল ইমন।
রাতে যখন বাইরে খেতে যাওয়া হল, তিনবন্ধু সহজ হওয়ার চেষ্টা করছিল ইমনের সঙ্গে। জয়দীপ, পার্থর সঙ্গে কথা বললেও, কৌশিককে এড়িয়ে থেকেছে ইমন। দূরত্বটা বজায় ছিল সি-বিচে স্নান করতে আসা অবধি। জয়দীপ ব্যাপারটা নোটিশঞ্জকরেই ইমন-কৌশিক জুটি বানিয়ে এদিকে পাঠাল। কিন্তু কিন্তু করছিল কৌশিক। জয়দীপ কোনও কথা শোনেনি।
ইমন, কৌশিক একসঙ্গে হাঁটা শুরু করলেও, ইমন কথা বলা তো দূরে থাক, ঘুরেও দেখছে না দেখে কৌশিক চুপচাপ কেটে পড়েছে। অপরাধ বোধে ভুগছে বলে যেচে কথাও বলতে পারেনি।
– এই যে, তোমাকেই খুঁজছিলাম।
কাঁধে হাত রেখে কে যেন বলে উঠল কথাটা। চমকে ঘাড় ফেরায় ইমন। আবারও চমকায়, এবার ভিতরে। কাঁধে হাত রেখেছেন ট্রেনের সেই ভদ্রলোক, মেয়েটার বাবা। গায়ে গামছা, ফোল্ড করা লুঙ্গি পরনে। মেয়েটা পরিবারের সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে খানিক দূরে। রোদের চোটে কপাল কুঁচকে থাকলেও ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি। পরনে ট্রেনের পোশাকটাই, সাদা পাতিয়ালা-কামিজ।
কাঁধ থেকে হাত ফিরিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ট্রেনে তোমায় থ্যাংক্স জানানো হয়নি। গিন্নি খুব রাগ করছিল। এখানে এসে থেকে তোমায় খুঁজছি। জোর বাঁচিয়েছ টিটির হাত থেকে।
ইমন কথাগুলো শুনছে ঠিকই, দৃষ্টি চলে যাচ্ছে মেয়েটার দিকে। পায়ের তলার বালি ক্রমশ নরম হয়ে যাচ্ছে যেন। মেয়েটিও চোখ সরাচ্ছে না। ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, কোথায় উঠেছ? বন্ধুদের সঙ্গে এসেছ দেখলাম মনে হল ট্রেনে।
ইমন ঘাড় হেলিয়ে নিজেদের হলিডে হোমের নামটা বলে। তারপর জানতে চাইল, আপনারা কোথায় উঠেছেন?
মেয়েটার বাবা পিছন ঘুরে আঙুল তুলে বলল, ওই হোটেলটার পাশের গলিতে একটা হলিডে হোমেই উঠেছি আমরা।
‘কোন হলিডে হোম’ জিজ্ঞেস করতে
সংকোচ হচ্ছে ইমনের। সেই ফাঁকে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, চলি। আমরা স্নান করতে এসেছি। পরে আবার দেখা হয়ে যাবে।
ভদ্রলোক এগিয়ে যাচ্ছেন জলের দিকে। পরিবারের বাকিরাও এগোল। সকলের অলক্ষে মেয়েটা এবার ইমনের দিকে তাকিয়ে হাসল, যেন একরাশ মুক্তো ঝিকিয়ে উঠল সমুদ্রতটের রোদে। তারপর সাদা রাজহংসীর মতো সে ভেসে পড়ল জলে।
মেয়েটার দেখা পাওয়াতে বন্ধুদের প্রতি সমস্ত বিরূপতা কেটে গেছে ইমনের। মনে মনে কৌশিককেও ক্ষমা করে দিয়েছে। সুখবরটা বন্ধুদের দিতে সে এখন দৌড়োচ্ছে সিবিচ ধরে। মিটিং পয়েন্টে পৌঁছোনোর আগে দৌড় থেমে যায়। মজার একটা ব্যাপার দেখে দাঁড়িয়ে গিয়ে ফের হাঁটতে থাকে ইমন। মিটিং স্পটের যে-গর্তটা খোঁড়া হয়েছিল সেখানে এখন পোঁতা হয়েছে পলা বউদিকে। মানে বালি চাপা দেওয়া হয়েছে। শুধু মুণ্ডুটা উপরে। কাজটাকে নিখুঁত করতে এখনও লাস্ট মিনিট টাচ দিচ্ছে জয়দীপ, পার্থ। কৌশিককে আশপাশে দেখা যাচ্ছে না। রঞ্জনদাকেও না। দাদা-বউদির খোঁজ তার মানে এরা অনেক আগেই পেয়েছে। পলা বউদির গোটা বডিটা বালিতে চাপা দেওয়া যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।
ঘটনাটা দূর থেকে যতটা মজার মনে হয়েছিল, কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই আশাভঙ্গ হল ইমনের। কপালে ভাঁজ নিয়ে সে দেখল, পলা বউদির বুকের অংশের বালির ওপর আঙুল মাপের অনেকটা ফুটো। বদমাইশিটা করছে পার্থ। দু’হাতের লম্বা আঙুলটা বুকের দিকে রেখে বালি চাপা দিচ্ছে। পলা বউদির বুক ছোঁওয়ার ফিকির। এখনও ছুঁতে পেরেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। পলা বউদি খুশির হাসি হাসছে। সেটা খেলার আনন্দে না যৌন সুড়সুড়িতে, আন্দাজ করা কঠিন! ইমনের টেনশন হচ্ছে রঞ্জনদার কথা ভেবে। এসে যদি দেখে বউয়ের বুকের ওপর বালিতে ভীমরুলের চাকের মতো ফুটো, মধুলোভীদের অভিপ্রায় টের পেয়ে যাবে। ইমনদের গ্রুপটাকে চিনবে ছোটোলোকের দল হিসেবে।
হাঁটু মুড়ে বালিতে বসে পড়ে ইমন, হাতের ঝটকায় সরিয়ে দেয় পার্থর হাত। জয়দীপ পলা বউদির পেটের দিকে বালির ফিনিশিং টাচ দিচ্ছে। ইমনের চোখ চলে যায় জলের দিকে, স্নান সেরে উঠে আসছে রঞ্জনদা। তড়িঘড়ি বউদির বুকের ওপর বালির গর্তগুলো চাপা দিতে থাকে ইমন।
রঞ্জনদা চলে এসেছে কাছে। বলে উঠল, আরেঃ, তোমরা তো দেখছি আমার বউটাকে ভ্যানিশ করে দিয়েছ।
জয়দীপ, পার্থ বোকাবোকা হাসছে। ইমন চেষ্টা করেও হাসতে পারছে না। বন্ধুর অপকর্মের চিহ্ন অবশ্য মুছে ফেলতে পেরেছে। পলা বউদি বলে ওঠে, ভিতরটা কী ঠান্ডা গো! পুরো এসিতে আছি মনে হচ্ছে।
রঞ্জনদা সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল। বলল, বউয়ের পাশটিতে আমাকেও সমাধি দিয়ে দাও।
পূর্ণ উদ্যোমে রঞ্জনদার জন্য বালি খুঁড়তে লাগল জয়দীপ, পার্থ। রঞ্জনদাও খুঁড়ছে, ইমন হঠাৎ দেখতে পায় কৌশিককে। তডিঘড়ি পায়ে এগিয়ে আসছে, চেহারায় কেমন যেন ভয় আতঙ্কের ভাব!
ইমন উঠে দাঁড়ায়। কী হয়েছে কৌশিকের? উৎকণ্ঠিত ইমনের দিকে না তাকিয়ে কৌশিক, দাদা-বউদির মাথার কাছে গিয়ে জয়দীপকে ডাকে। বালি লাগা হাত ঝেড়ে উঠে যায় জয়দীপ। ইমন শুনতে পায় কৌশিক বলছে, মেয়েটা মাইরি সিবিচে চলে এসেছে। পিছন ছাড়ছে না। আমি শালা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। কী করি বল তো?
– খেয়েছে রে। কেসটা এতটা পাকিয়ে ফেলেছিস! না বুঝেশুনে কেন যে লাইন মারতে যাস। উদ্বেগ, বিরক্তি একসঙ্গে জানায় জয়দীপ। তারপর হাঁক দেয়, ইমন একবার এদিকে শুনে যা প্লিজ। কঠিন প্যাঁচে পড়লে এই বন্ধুরা বরাবরই ইমনের শরণাপন্ন হয়।ঞ্জবিবেচনাবোধ ইমনের বেশি। বন্ধুরা খানিকটা সমীহ করে চলে সেই কারণেই। ইমন পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ায় জয়দীপ, কৌশিকের কাছে। কৌশিক সমস্যাটা আবার করে বলতে যাচ্ছিল, ইমন বলল শুনেছি। তোর কাছে কী আশা করছে মেয়েটা?
– আশা করলে তবু হতো। পূরণের জন্য টাইম দেয় মানুষ। এ তো সময়ই দিচ্ছে না। সারাক্ষণ সেঁটে থাকতে চাইছে। তুই ঠিকই বলেছিলি, বার খাওয়ানো ভুল হয়ে গেছে মেয়েটাকে। ও সত্যিই ধরে নিয়েছে, আমি ওকে লাইক করেছি।
কৌশিকের কথা শুনতে শুনতে চারপাশে চোখ বোলাচ্ছিল ইমন, খানিক দূরে ভিড়ের মধ্যে দেখতে পায় শ্যামলা, ঝাঁকড়়া চুলের নমিতাকে। মেলায় হারিয়ে যাওয়ার মতো মেয়েটা এলোমেলো ঘুরে খুঁজছে অবশ্যই কৌশিককেই। ইমন এগিয়ে যায় নমিতাকে লক্ষ্য করে। কৌশিককে আড়াল করার জন্য কিছু একটা করতে হবে।ঞ্জনিজের ভুল বুঝতে পেরেছে কৌশিক।
যেন হঠাৎ দেখতে পেয়েছে, এইভাবে নমিতার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ইমন। বলল, আরেঃ, তুমি একা! বড়োরা কোথায়?
– দাদু, দিদা আসেনি। হোটেলেই আছে।
মেয়েটার গলা প্রথম শুনল ইমন। কণ্ঠস্বরে ‘বালিকা’ভাব এখনও কাটেনি। হলিডে হোম যে হোটেল নয়, শেখায়নি মালিক, মালকিন। অথচ নিজেদের দাদু-দিদা বলে ডাকতে শিখিয়েছে। যাতে কাজ আদায় করতে সুবিধে হয়। ইমন বলে, একা একা সি-বিচে ঘোরা তোমার ঠিক হচ্ছে না। এখানে অনেক খারাপ লোকজন ঘুরঘুর করে।
– আমি চান করতে এসেছিলাম। কৌশিকদা বলেছিল করিয়ে দেবে। এখানে এসে একবার দেখলাম কৌশিকদাকে। তারপর কোথায় যে চলে গেল! আপনি দেখেছেন আপনার বন্ধুকে?
যেন ভীষণ মজার কোনও জোক শুনল ইমন, সেরকমই হেসে বলল, কৌশিক তোমাকে চান করাবে! ও ব্যাটা নিজেই ভীতুর ডিম। ইয়ার্কি মেরেছে তোমার সঙ্গে।
এত রোদ সত্ত্বেও ছায়া নেমে এল নমিতার মুখে। বলল, এখানে এসে থেকে একদিনও সমুদ্রে চান করিনি। দাদু-দিদা করবে না বলে দিয়েছে। আপনি একটু জলে গিয়ে আমাকে ধরবেন? দু’তিনটে ডুব দিয়েই চলে আসব।
– আমি কৌশিকের চেয়েও বেশি ভয় পাই সমুদ্রে নামতে। নুলিয়া খুঁজতে বেরিয়েছি। দেখাও পাচ্ছি না তাদের।
ইমনের সাহায্য পাবে না বুঝে নিয়ে ফের ঘাড় ঘুরিয়ে কৌশিককে খুঁজতে থাকে নমিতা। ইমন বোঝানোর সুরে বলে, দাদু-দিদাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন এসো। নুলিয়ার হেল্প নিয়ে তবেই চান কোরো। দুমদাম কারওর ওপর ভরসা করা উচিত হবে না।
ঘুরিয়ে কৌশিকের থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিল ইমন। ডবল মিনিং ধরার শিক্ষা মেয়েটার নেই। ইন্সটিঙ্কট্ থেকে যদি কিছু বুঝতে পারে ভালো। ইমনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফেরার পথে এগোল নমিতা। নিরাশ ভঙ্গিতে বালি ভেঙে হেঁটে যাচ্ছে মেয়েটা। মায়া লাগে ইমনের। বেচারিকে ধরে থেকে একবার চান করিয়ে দিলে হতো। ঝুঁকিটা নিতে পারল না ইমন। ঢেউয়ের ভয়ে নমিতা যদি জাপটে ধরত ইমনকে, তিনবন্ধু আওয়াজ দিতে ছাড়ত না। বলত, তোরও তো লোভ কম নয়!
সকাল থেকে সন্ধে কনডাক্টেড টুর করে কাটল আজ। কোনারক, চন্দ্রভাগা বিচ, নন্দনকানন, উদয়গিরি খণ্ডগিরিঃ সব ঘুরে বিকেল উতরে হলিডে হোমে ফিরেছে চারবন্ধু। প্রত্যেকেই অত্যন্ত ক্লান্ত, তাই বিচে না গিয়ে ঘরেই রেস্ট নিচ্ছে। ট্রেনের মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা বন্ধুদের বলেছে ইমন। আজ আর তাকে খোঁজা হল না। ইমনের ইচ্ছে থাকলেও, বাকিদের মতো তারও এনার্জি অবশিষ্ট নেই। কাল চেষ্টা করে দেখা যাবে। যদিও সেটাই হবে যোগাযোগের শেষ চেষ্টা।ঞ্জকাল রাত আটটার ট্রেনে ফিরে যাবে ইমনরা।
টুর করে যতই টায়ার্ড থাকুক, সন্ধের মুখে তো ঘুমিয়ে পড়া যায় না। ইমন তাই বিছানায় শুয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা গল্পের বইটা পড়ছে। বাকি তিনজনের বই পড়ার ঝোঁক প্রায় নেই বললেই চলে। ওরা তাস খেলছে বিছানাতেই। ব্রে খেলছে। পার্থ খেলতে খেলতে উঠে গেছে অনেকক্ষণ হল। এখন জয়দীপ আর কৌশিক খেলছে। পার্থর না-ফেরা নিয়ে দু’জনের কোনও হঁশ নেই। কোথায় গেল পার্থ? হলিডে হোমের বাইরে বেরিয়ে গেল কী? কিছু বলে গেল না তো! উপুড় হয়ে বই পড়া অবস্থা থেকে ঘাড় ফেরায় ইমন। দুই বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে, পার্থ কোথায় গেল রে? এখনও ফিরছে না!
দু’জনেই মন দিয়ে তাস খেলছে। পার্থর অ্যাবসেন্স নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। এক রাউন্ড শেষ হল। হাতের তাস ফেলে কৌশিক বলল, যাই, দেখে আসি। কোথায় গেল ব্যাটা।
কৌশিক বেরিয়ে যাওয়ার খানিক বাদেই ফিরে এল পার্থ। কোনও একটা কাজ সমাধা করে আসার ভঙ্গি। বসল কৌশিকের ছেড়ে যাওয়া জায়গায়। কোথায় গিয়েছিল, তা নিয়ে জয়দীপ ওকে কোনও প্রশ্নই করল না। দু’জনে মিলে তাস খেলতে লাগল। ইমনের খটকা লাগে, মনে হয় জয়দীপ জানে, পার্থ গিয়েছিল কোথায়। আন্দাজ খুব ভুল না হলে, কৌশিক গেছে সেখানেই। তিনজনের মধ্যে কোনও একটা গটআপ চলছে। ব্যাপারটা ইমনের কাছে গোপন করছে ওরা। ইমন পার্থকে জিজ্ঞেস করে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?
কথাটা যেন শুনতেই পেল না পার্থ, একমনে তাস খেলে যাচ্ছে। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে কোনও লাভ হবে না বুঝতে পারে ইমন। তিনজন মিলে গোলমাল পাকাচ্ছে কিছু। গ্রুপের মেম্বার হিসেবে যার দায়ভার ইমনের ওপরেও বর্তাবে। বিষয়টা সরেজমিনে দেখতে হবে। বই মাথার কাছে উলটে রেখে বিছানা থেকে নেমে আসে ইমন। পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।
চৌকাঠ ডিঙোনোর পর ইমন করিডোরের বাঁদিকটা দেখে, ওদিকে নীচে যাওয়ার সিঁড়ি। কৌশিক কি ওইদিকেই গেল? না কি বুড়ো-বুড়ির পোর্শনে? আগে ভিতরদিকটা দেখে নেওয়া যাক, ভেবে ইমন বুড়ো-বুড়ির রুমের উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। আলো-অন্ধকার কিচেন কাম ডাইনিং-এর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অন্যরকম একটা চাপা ঝটাপটির শব্দে ঘাড় ফেরায়, মুহূর্তের মধ্যে সারা শরীর যেন বরফের চাঁই হয়ে যায় ইমনের। কিচেন-ডাইনিং-এর ফ্লোরে প্রায় অনাবৃত দুটো শরীর দমচাপা ধস্তাধস্তি করে সেক্স-এ মেতেছে! একজন কৌশিক, অন্যজন নমিতা।…
আপ্রাণ প্রয়াসে নিজের জড়ত্ব কাটিয়ে ইমন দৌড়ে রুমে ফিরে আসে। নির্বিকার চিত্তে তাস খেলারও দুই বন্ধুর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে চায়, এ সব কী হচ্ছে! গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না। ভিতরটা রাগে উত্তেজনায় কাঁপছে। বিছানার কাছে এগিয়ে আসে ইমন। জয়দীপের কাঁধ ধরে নিজের দিকে ফেরানোর টান দেয়। গড়গড়ানির গলায় বলে, এগুলো নোংরামি, অন্যায়। তুই সব জেনেও কিছু বলছিস না!
জয়দীপকে একথা বলার কারণ আছে। বাকি দু’জনের মতো লাইট হার্টেড ও নয়। লম্বা চওড়া চেহারার মধ্যে একটা পার্সোনালিটি আছে। শ্রেয়ার সঙ্গে ওর রিলেশনটাও খুব স্টেডি। জয়দীপ কিন্তু প্রত্যাশা মতো উত্তর দিল না। ইমনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কীসের নোংরামি, কীসেরইবা অন্যায়? কোনারক মন্দিরের গায়ে যেগুলো দেখে এলি, সেসব তাহলে কী? মেয়েটা দিচ্ছে, তাই নিচ্ছে। জোর তো কিছু করছে না।
ইমনের বলতে ইচ্ছে করে, মেয়েটা কী খোয়াচ্ছে নিজেই জানে না। জানার বয়স বা বুদ্ধি কোনওটাই ওর হয়নি। ইমন জানে কথাগুলো স্বর হয়ে বেরোবে না গলা দিয়ে। গলা চোক্ড হয়ে গেছে তার। মাথাটাও ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। প্রায় টলতে টলতে ফিরে আসে, যেখানে শুয়েছিল। দু’হাতে মাথা রেখে বসে থাকে। চিন্তাশক্তি ক্রমশ লোপ পাচ্ছে ইমনের। কিছুই ভাবতে পারছে না।
এরই মাঝে কানে আসে এই ফ্লোরের বৃদ্ধের গলা। অসহায় গলায় ডাকছেন, নমিতা! নমিতা! কোথায় গেলি! নমিতা… টেনশন হতে থাকে ইমনের, বৃদ্ধ কি ঘর থেকে বেরিয়ে নমিতাকে খুঁজতে বেরোবেন? ধরা পড়ে যাবে কৌশিক? ফাঁস হয়ে যাবে ইমনদের গ্রুপটার কদর্য রূপ!
…থেমে গেছে বৃদ্ধের ডাক। আরও খানিকক্ষণ পর কৌশিকের গলা পাওয়া গেল। ফিরে এসেছে রুমে। বলল, জয়দীপ, যা এবার।
অবশ চেতনাতেও ধাক্বা লাগে ইমনের। বাকি দু’জনের চেয়ে একটু হলেও জয়দীপ বেশি ক্লোজ তার। জয়দীপের সঙ্গে শ্রেয়ার স্কুলে গেছে ইমন। জয়দীপই নিয়ে গেছে বেশ কয়েকবার। ইমনের মনের চোখে বারবার ভেসে উঠছে শ্রেয়ার সহজ সুন্দর হাসিহাসি মুখটা। জয়দীপকে কিছুতেই এই নোংরামির মধ্যে যেতে দেওয়া যাবে না। আটকাতেই হবে। ইমন ঘুরে গিয়ে জয়দীপের হাতটা ধরবে ভাবে, তার অনেক আগেই উঠে গেছে জয়দীপ। ঘরের চৌকাঠ ডিঙোচ্ছে।
ইমন আবার মাথা রাখে হাতের তালুতে। আরও ঘোলাটে হয়ে গেছে মাথা। অন্ধকার সমুদ্রের ঢেউ ধেয়ে আসছে চেতনায়। এই ঢেউ নিকষ কালো, ফসফরাসের আলো নেই এতে।
কতটা সময় কেটে গেল, কে জানে! রুমে ফিরে এল জয়দীপ। বলল, ইমন, যাবি তো যা। এক্সপিরিয়েন্স করে নে। এরকম হাতে-কলমে সুযোগ সহজে পাবি না।
কথাগুলো কোনও প্রভাব ফেলতে পারল না ইমনের মনে। যেন তার উদ্দেশ্যে বলা হয়নি। বন্ধুদের থেকে কেমন এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বোধ করছে সে। রুমটা যেন একটা ডরমেটরি, বাকি তিন আবাসিকের সঙ্গে কোনও পূর্ব পরিচয় নেই তার।
ইমন বিছানা ছেড়ে উঠে পাঞ্জাবির পকেটে পার্স, মোবাইল নেয়। এগিয়ে যায় দরজার দিকে। করিডোরে এসে সিঁড়ির দিকে ঘুরতে যাবে, স্লিপার ছেড়ে বাইরে বেরোনোর চটি পরে নিয়েছে, একবার বাঁদিকটা দেখে, ম্যাক্সি পরা নমিতা দাঁড়িয়ে আছে। চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি, আহ্বান নেই। আছে বোবা অপেক্ষার আকুলতা। আহ্বানের ছলনা জানার বয়স হয়নি মেয়েটার।
স্বর্গদ্বারের মোড়ে জমজম করছে মার্কেট। রাত বেশি হয়নি, সবে আটটা। রাস্তায় এত আলো, লোক, কেনাকাটা… এসব দেখে বিশ্বাসই হবে না, কিছু সময় আগে এখানকারই এক হলিডে হোমের আলো-অন্ধকার ঘরে কত বড়ো অন্যায় ঘটে গেছে।
মার্কেট ঘুরতে ঘুরতে ঘটনার অভিঘাত অনেকটাই কাটিয়ে ফেলেছে ইমন। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে এই তিনবন্ধুর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবে না। কাল সকালে যে-কোনও ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরে যাবে সে। উইদাউট রিজার্ভেশনে কষ্ট করেই যাবে। আজ রাতেই যেতে পারত। সাড়ে দশটায় এক্সপ্রেস আছে একটা। বাড়ির জন্য কিছুই কেনাকাটা হয়নি, এমনকী পুরীর বিখ্যাত খাজাও কেনেনি। বাবা বলেছিল ঘনিষ্ঠ পরিচিতজনদের জন্য কিছু না কিছু নিতে। তার জন্য আলাদা টাকাও দিয়েছে। সেই কারণেই সঙ্গে পার্স নিয়ে বেরিয়েছে ইমন। কিন্তু এতক্ষণ ঘোরাঘুরির পর এখনও ঠিক করতে পারছে না, কার জন্য কী কিনবে।
একা একা এধরনের শপিং আগে তো কখনও করেনি। বড়ো কারওর গাইডেন্স পেলে ভালো হতো। এখানে রঞ্জনদা-পলা বউদি হেল্পটা করতে পারে, দেখা হয়ে গেলে খুবই সুবিধে হয়। ভাবনা হোঁচট খায় খানিক দূরে একটা কাপড়-জামার দোকানের সামনে চোখ যেতে। ট্রেনের মেয়েটা না? হ্যাঁ, ট্রেনের মেয়েটাই। বেশি চেনা যাচ্ছে সাদা ড্রেসের জন্য। এখন চুড়িদার। মেয়েটা শুধু সাদা পোশাকই পছন্দ করে কেন?
কোনও জড়তা ছাড়াই ইমন মেয়েটাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যায়। যে করে হোক আলাপ করতে হবে। জেনে নিতে হবে ঠিকানা। পুরীতে এসে ওই মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা ইমনের একমাত্র প্রাপ্তি। ওর পাহাড়ি ঝরনার মতো হাসিটাই ভুলিয়ে দিতে পারবে পুরীর গ্লানিময় অভিজ্ঞতা।
পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই সামান্য চমকে ঘাড় ফেরায় মেয়েটা। ইমন বলে, বাড়ির আর সবাই কোথায়?
চোখের ইশারায় দোকানের ভিতরটা দেখায়। বলে, বড্ড গরম। বাইরে চলে এসেছি।
– নাম? জিজ্ঞেস করে ইমন।
দোকানের ভিতরে বাড়ির লোকের দিকে খেয়াল রেখে মেয়েটা বলে, নাম জেনে কী লাভ হবে? জপ করবে?
স্মার্ট আছে মেয়েটা। সত্যিই তো শুধু নাম জেনে তো আর যোগাযোগ রাখা যাবে না। নিজেকে শুধরে নিয়ে ইমন বলল, ফোন নাম্বার দাও।
– নিজের ফোন সেটটা বার করো তাড়াতাড়ি। দশটা ডিজিট বলার মতো টাইম পাব না, মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই রাখতে পারবে না মনে?
না, পারবে না ইমন। অন্য সময় হলে তবু চেষ্টা করা যেত। হঠাৎই এখন ভীষণ নার্ভাস ফিল করছে। কাঁপা হাতে পাঞ্জাবির পকেট থেকে ফোনসেট বার করে ইমন। মেয়েটা বলতে শুরু করেছে, নাইন এইট… দোকানের ভিতর থেকে মহিলা কণ্ঠ ডাকে, তুলতুল, এদিকে আয় একবার। কী হল আয়!
ইমনের দিকে না তাকিয়ে মেয়েটা বলল, মা ডাকছে। কাল রাতের ট্রেনে ফিরছি। আমাদের হলিডে হোমের দিকেও আসতে পারো দিনের বেলা।
দোকানে ঢুকে গেল তুলতুল। বাড়ির আদরের নাম নিশ্চয়ই এটা। আসল নামটা জনা হল না। কন্ট্যাক্ট রাখারও ব্যবস্থা করা গেল না কোনও। আবার কালকের দিনটার জন্য প্রতীক্ষা।
তুলতুল রাতের ট্রেনে ফিরবে বলে ইমন সকালের ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরে যায়নি। রয়ে গেছে পুরীতে। ওই ঘটনার পর তিনবন্ধুর সঙ্গে একটা কথাও বলেনি, নিজের মতো থেকেছে। বন্ধুরাও ওকে ঘাঁটায়নি। সকালে ওরা স্নান করতে বেরিয়ে যাওয়ার পর ইমন বেরিয়েছে। সি-বিচে একা ঘুরেঘুরে খুঁজেছে তুলতুলকে। পায়নি। স্নান করেছে একাই। বন্ধুদের সঙ্গে লাঞ্চও করেনি। বাইরে গিয়ে নিজের মতো খেয়ে নিয়েছে। দুপুরে ঘণ্টা তিনেক রেস্ট নিল। তারপর বেরিয়ে পড়েছে তুলতুলের খোঁজে। তিনবন্ধু অকাতরে ঘুমোচ্ছিল দুপুরে। নমিতার জন্য ছোঁকছোঁক করতে দেখা যায়নি। ইমনের অ্যাটিটিউড দেখেই ওরা একটু সমঝে গেছে। তবে ইমনের অবর্তমানে এখন কী করছে কে জানে। যাই করুক, ইমন এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে না। নিজের জীবন থেকে ওদের ছেঁটে ফেলেছে।
এদিকে ইমন যে-উদ্দেশ্যে বিকেলে বেরোল, তা সফল হয়নি। দেখা পাওয়া যায়নি তুলতুলের। মেয়েটার বাবা সি-বিচে দাঁড়িয়ে যেদিকে আঙুল তুলে বলেছিল, ওই হোটেলের পিছনে হলিডে হোমে আছিঃ সেখানে পরপর অনেকগুলো হলিডে হোম। ইমন ক্রমান্বয়ে পাক খেয়ে তুলতুলের হদিশ পায়নি। তারপর আন্দাজ করেছে, হয়তো মার্কেটে গেছে ওরা। ফ্যামিলি নিয়ে আসা বাঙালি টুরিস্টরা শেষবেলায় আরও একবার শপিং করবেই। প্রথমবার কিছু জিনিস কিনব ভেবেও কেনা হয়নি, মনে পড়েনি দু’একজন নিকটজনের কথা, সেই সব মিটিয়ে তবেই বাড়ি ফেরার জন্য প্যাকিং করবে।
মার্কেটেও ওদের দেখা পেল না ইমন। বাড়ি এবং আত্মীয়স্বজনের জন্য নিজেই কিছু কিনল। আগের সন্ধেতে কেনা হয়নি। দু’হাতে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ ঝুলিয়ে ইমন এখন হলিডে হোমে ফিরছে। ভীষণভাবে দমে আছে মনটা। এতটা হতাশ হওয়ার কারণ, তুলতুল জানিয়েছিল রাতের ট্রেনে ফিরবে। কোন ট্রেনে ফিরবে বলেনি। রাতের দিকে দুটো এক্সপ্রেস ট্রেন, একটা আটটায়, যেটাতে রিজার্ভেশন আছে ইমনদের। অন্যটা সাড়ে দশটায়। তুলতুলরা যদি পরের ট্রেনে ফেরে, ইমনের সঙ্গে কোনওদিন আর দেখাই হবে না। মেয়েটা ফেসবুকে আছে কিনা, কে জানে! থাকলেও কী নামে আছে, নিজের ছবি দেয়নি হয়তো, খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। মেয়েটাকে এভাবে হারিয়ে ফেলাটা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছে না ইমন। তুলতুল হল সেই মেয়ে, যাকে দেখে ইমনের প্রথমবার মনে হয়েছে, আমি তো এর অপেক্ষাতেই ছিলাম।
একটা কাজ করা যেতে পারে। ইমন লাগেজ নিয়ে নিজেদের ট্রেনের টাইমেই স্টেশনে পৌঁছোল, যদি দেখে তুলতুলরা উঠল না সেই ট্রেনে, ইমনও যাবে না। সাড়ে দশটার এক্সপ্রেসটা ধরবে। তুলতুলরা যাবে ওই ট্রেনেই। ইমন জেনারেল কম্পার্টমেন্টে উঠবে। হাওড়া স্টেশনে নেমে তুলতুলদের ফলো করে চিনে নেবে ওদের বাড়ি। মেয়েটা যেরকম রেসপন্স দিয়েছে, ইমনের প্রতি যে আগ্রহী, তাতে সন্দেহ থাকার কথা নয়… এত দূর ভাবতে পেরে নিশ্চিন্ত হয় ইমন। এই প্ল্যানটাই একেবারে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট।
হলিডে হোমে পৌঁছে গেছে ইমন। দু’হাতে প্যাকেট নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। লাগেজ মোটামুটি গুছিয়ে রেখেছে। এই গিফ্টগুলো ব্যাগে ঢুকিয়ে নেবে। এখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা, বন্ধুরা বলাবলি করছিল, ট্রেন ধরতে হলিডে হোম থেকে বেরোবে সাড়ে ছ’টা নাগাদ। ইমন ওদের সঙ্গে বেরোবে না। আগে পরে বেরিয়ে যাবে।
রুমে ঢুকে থমকে গেল ইমন। তিনবন্ধু ভীষণরকম গম্ভীরমুখে বিছানার তিনপ্রান্তে বসে আছে। পা মাটিতে নামানো। পরনে বাইরে বেরোনোর পোশাক। ওদের লাগেজগুলোও প্যাক করে রাখা চেন টানা অবস্থায়। ওরা ইমনের অপেক্ষা না করে ট্রেন ধরতে বেরিয়ে যাচ্ছিল, বোঝাই যাচ্ছে। কোনও একটা খবর শুনে মুলতুবি রেখেছে যাওয়া। সুখবর নয়, ওদের মুখ দেখেই আন্দাজ করা যায়। এত আগেই-বা স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছিল কেন? কিছুই মাথায় ঢুকছে না ইমনের। বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে, এনি থিং রং?
নার্ভাস গলায় জয়দীপ বলে ওঠে, হেভি ক্যাচাল হয়ে গেছে রে। মেয়েটা আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছে।
ইমন এক চান্স-এ বুঝতে পারে কোন মেয়েটার কথা বলা হচ্ছে। আর একটু ক্লিয়ার হয়ে নিতে জিজ্ঞেস করে, আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছে মানে?
– বুড়ো-বুড়িকে না জানিয়ে আমাদের সঙ্গে পালাবে। থাকবে আমাদের কাছেই। দুপুর থেকেই কথাটা বলছিল। আমরা ঘরে এনে অনেক বুঝিয়েছি। বোঝেনি। আমরা একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ার তাল করছিলাম। দেখি, সে-ও ব্যাগ গুছিয়ে রেডি। টানা কথা বলে থামল কৌশিক।
এবার খেই ধরল পার্থ। বলল, যতবার মাইরি ব্যাগ নিয়ে বাইরে বেরোতে যাচ্ছি, দরজা আগলে দাঁড়াচ্ছে। ওকে না নিলে যেতে দেবে না।
ইমন ঝাঁঝিয়ে ওঠে, ঠিক হয়েছে। মেয়েটার সঙ্গে যা করেছিস তোরা, এরকমটাই হওয়ার কথা ছিল। এখন ঠ্যালা সামলা।
জয়দীপ বলে, মাথা গরম করিস না ইমন। ব্যাপারটা ঠান্ডা মাথায় ভাব। মেয়েটাকে আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতেই পারি। পুরী স্টেশনে হয়তো সম্ভব হবে না, হাওড়া স্টেশনের ভিড়ে ওকে ফেলে পালাতেই পারি চারজনে। সমস্যা অন্য জায়গায়, মেয়েটা পালিয়েছে টের পেলেই বুড়ো-বুড়ি যাবে লোকাল থানায়। তারপর মেয়ে পাচারকারী হিসেবে পুলিশ আমাদের অ্যারেস্ট করবে, আজ না হয় কাল। চারজনের কারওকেই ছাড়বে না।
পিঠ বেয়ে হিমস্রোত নেমে যায় ইমনের। সে নোংরামির মধ্যে না থাকলেও, পুলিশ তাকে রেহাই দেবে না। যাত্রাপথে ধরতে না পারলে, বাড়িতে গিয়ে অ্যারেস্ট করবে। বাবা-মা দৌড়োদৌড়ি করবে উকিল, আদালতে, এসব সে ভাবতেই পারে না। যে করে হোক এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে তাকে।
গিফটের প্যাকেটগুলো ফ্লোরে নামিয়ে রেখে ইমন দরজার দিকে ঘুরে যায়। বাইরে বেরোতেই দেখে, করিডোরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নমিতা। পরনে স্কার্ট, টপ। পায়ের কাছে পুরোনো লাগেজ ব্যাগ। অভিমান আর জেদে থমথম করছে ওর মুখ। ইমনের দিকে তাকাল, চোখ দেখে বোঝাই যাচ্ছে, ও একেবারে মরিয়া।
ইমন নমিতার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। একটু সময় নিয়ে বলে, তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছ?
মাথা ওপর নীচ করে ‘হ্যাঁ’ জানায় নমিতা। ইমন বলে, তোমার সঙ্গে ওরা যা করেছে, তুমি যেতে চাইতেই পারো। কিন্তু কার বাড়িতে গিয়ে থাকবে? একসঙ্গে তিনজনের বাড়িতে তো থাকা যায় না।
কোনও উত্তর দেয় না নমিতা। মাথা নীচু করে আছে। ইমন ফের বলে, ওই তিনজনের মধ্যে কাকে তুমি বেশি ভালবাসো? তাহলে তাকে গিয়ে আমি বলতে পারি তোমার দায়িত্ব নিতে।
এখনও কোনও উত্তর নেই। প্রেমের কীই-বা বোঝে মেয়েটা। ভালোবাসা, কামকে আলাদা করতে শেখেনি। দুটোকে একই মনে করে। যাকে ভালোবাসবে, তাকেই যে নিজের সমস্ত কিছু দেওয়া উচিত, সেই জ্ঞানটুকু নেই। তথাকথিত তিন ভদ্রঘরের ছেলের আদর পেয়ে ভেবেছে, এটাই বুঝি ভালোবাসা। বড়োঘরের এমনটাই রেওয়াজ। ইমন আবার বলে, কী হল, বলো একজনের নাম। কাকে তুমি ভালোবাসো? সমাজ পরিবার তো একসঙ্গে তিনজনকে ভালোবাসাটা মেনে নেবে না। একজনকে বেছে নিতেই হবে তোমায়।
মুখ তোলে নমিতা। চোখ থেকে জল গড়িয়ে নেমেছে গালে। ইমনের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে। হতচকিত হয়ে পড়ে ইমন। ভীষণ রকম ফোঁপাচ্ছে নমিতা। ফুলে ফুলে কাঁদছে। এখন করণীয় কী, মেয়েটাকে কী বলে সান্ত্বনা দেবে কিছুই বুঝতে পারছে না ইমন। বুকে রাখা নমিতার মাথা আর পিঠে হাত রেখে ইমন ভাষাহীন সহমর্মিতা প্রকাশ করে।মেয়েটা কেঁদেই চলেছে। সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে গেছে ওর। এসবের মধ্যেই ইমন আড়চোখে দেখে নিয়েছে তিনবন্ধু একে একে কেটে পড়ল তার পিছন দিয়ে। ফাঁকিটা টের পেল না নমিতা। এবার বেশ শব্দ করেই কাঁদছে সে, ইমনের টেনশন হচ্ছে, কান্নার আওয়াজে বুড়ো-বুড়ি না চলে আসে।
ফোন বেজে ওঠে ইমনের। সেটা কানে নিতেই ওপ্রান্ত থেকে জয়দীপ বলে আমরা অটো নিয়ে ওয়েট করছি। তাড়াতাড়ি কেটে আয়। তোর লাগেজ নিয়ে এসেছি।
লাইনটা কেটে মোবাইলটা পকেটে রাখে ইমন। খানিকটা জোর খাটিয়ে নমিতাকে বুক থেকে সরিয়ে বলে, দেখেছ কান্ড! ওরা তো বেরিয়ে গেল। দাঁড়াও ধরে নিয়ে আসি। একটা বিহিত তো করতেই হবে।
ছিটকে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় ইমন। অসম্ভব দ্রুততায় নামতে থাকে নীচে। রাস্তায় এসে দেখে স্টার্ট নেওয়া অটোরিক্সা থেকে হাত বাড়িয়ে ডাকছে জয়দীপ। বলছে, কুইক, কুইক হারি আপ।
ট্রেন ছাড়ার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে প্ল্যাটফর্মে এল ইমনরা। এতটা সময় অটো করে পুরীর এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছে। নমিতাকে এড়ানোর জন্য এই সতর্কতা। চারজনকে ধরার জন্য প্ল্যাটফর্মে এসে বসে থাকে যদি ওই মেয়ে!
নিজেদের মধ্যে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে ভিড়ের মধ্যে মিশে ইমনরা এগোচ্ছে তাদের কামরার দিকে। সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে, মেয়েটা সত্যিই চলে এল কিনা?
নির্দিষ্ট কম্পার্টমেন্টের দরজায় পৌঁছে গেছে চারবন্ধু। জয়দীপ, পার্থ, কৌশিক সেঁদিয়ে গেল ভিতরে। সবশেষে ইমন, দরজার মুখে পা দিয়ে ট্রেনের পিছন দিকটা একবার দেখতে যেতেই বিদ্যুৎ খেলে গেল সারা শরীরে, নমিতা! উদভ্রান্তের মতো এপাশ ওপাশ তাকিয়ে খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে আসছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, ওর পরনে তুলতুলের সাদা ড্রেস!
ভিতরে ঢুকে এসেছে ইমন। থরথর করে কাঁপছে। বন্ধুদের বলে, মেয়েটা চলে এসেছে। খুঁজছে আমাদের।
– কী বলছিস তুই। বলে কৌতূহল সামলাতে না পেরে দরজার বাইরে মুখ বাড়ায় জয়দীপ, কারওকেই চোখে পড়ে না। ভিতরে ঢুকে এসে জয়দীপ বলল, কই, দেখলাম না তো!
– আছে, আছে। ড্রেস বদলে নিয়েছে। চিনতে পরিসনি। আমাদের বার্থে চল তাড়াতাড়ি। বলে ইমনই এগোতে থাকে প্রথমে।
পার্থ, কৌশিকের দিকে তাকায় জয়দীপ। তার মনে খটকা লেগেছে, মেয়েটা আসতেই পারে, ড্রেস চেঞ্জ করবে কেন? বাইরে বেরোনোর ড্রেস পরে সে তো রেডি হয়ে গিয়েছিল।
বার্থে পৌঁছে ইমন সেঁদিয়ে গেল একদম কোণায়। মাথা নীচু করে দু’হাতে মুখ আড়াল করেছে। গড়াতে শুরু করল ট্রেন। জয়দীপ বলল, অ্যাই ইমন, তুই কেন এমন করছিস! আমি তো দেখলাম না ওকে। ওটা তোর চোখের ভুল। ড্রেস চেঞ্জ করে সময় নষ্ট করতে যাবে কেন মেয়েটা!
ইমন কোনও উত্তর দেয় না। একই ভঙ্গিতে বসে থাকে। পোশাকটা হচ্ছে তুলতুলের সুখস্মৃতি, কঠিন বাস্তব হচ্ছে নমিতা। যে ধাওয়া করেছে ইমনকে। কিছুতেই ছাড়বে না। তিন ব্যভিচারীকে মেয়েটা পাহারায় রেখেছিল, ইমনের ওপর ভরসা করে আশ্রয়ের খোঁজ করেছিল সে। জানত না ইমনের সহমর্মীতা আসলে একটা চক্রান্ত। ফাঁকি দিয়ে চলে গেল তিন লম্পট। শর্ত, বিনিময়হীন যে বিশ্বাস ইমনের ওপর করেছিল নমিতা, তাতে আঘাত লাগলে সরাসরি আত্মা ক্ষতবিক্ষত হয়। ইমনকে সহজে ছাড়বে না নমিতা, জবাব চাইবে।
ট্রেন থামল পরবর্তী স্টেশনে। ফের চালু হয়েছে। ইমনের দেহভঙ্গিতে কোনও বদল নেই দেখে বন্ধুরা বলাবলি করছে, এরকম পাগলের মতো করছে কেন বল তো? কাকু-কাকিমাকে কী জবাব দেব?
মা-বাবাকে নিয়ে ইমনও ভাবছে। নমিতা তাকে ধাওয়া করে বাড়ি অবধি পৌঁছে যাবেই। বাবা বলেছিল, ‘কোনও বাজে স্মৃতি, খারাপ অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরবি না।’ শরীর জোড়া গ্লানি নিয়ে ফিরছে ইমন। নমিতা ট্রেনে উঠে পড়ছে, খুঁজছে ইমনকে। হাওড়া স্টেশনের ভিড়েও ওকে হারিয়ে ফেলা যাবে না। এতটাই একরোখা হয়ে উঠেছে সে। ইমনের তো এমনও মনে হচ্ছে, নমিতা যদি ট্রেনে উঠতে না-ও পারে, মুখ তুললেই ইমন দেখতে পাবে, জানলার বাইরে তুলতুলের সাদা পোশাক পরে ট্রেনের সঙ্গে দৌড়োচ্ছে মেয়েটা। তাকিয়ে আছে ইমনের দিকে। হাওড়া স্টেশনে নামাটা বোধহয় ঠিক হবে না ইমনের।
সাতদিন পর বেশ ক’টা খবরের কাগজে ‘নিরুদ্দেশের প্রতি’ বিজ্ঞাপনে ইমনের ছবি বেরোল। পুরী থেকে বাড়ি ফেরেনি ইমন। মাঝে কোনও স্টেশনে নেমে গেছে। বাড়ির লোক, আত্মীয়স্বজন সবাই ওকে খুঁজছে। ওই তিনবন্ধুও খুঁজছে, পুরীর ঘটনাটা চেপে গেছে সবার কাছে।
অনেক কাগজে বেরোনোর দরুন তুলতুল, নমিতার চোখেও নিশ্চয়ই পড়েছে বিজ্ঞাপনে ইমনের ছবিটা। দু’জনেই অস্থির হয়েছে খুব। দুই মেয়ে দু’রকম ভাবে বিশ্বাস করেছিল ইমনকে। আশপাশে ভরসা করার মতো যুবক দিনদিন দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে। ইমনের মতো ছেলের হারিয়ে যাওয়াটা দু’জনেই মানতে পারবে না। বিজ্ঞাপনে ইমনদের বাড়ির ফোন নম্বর দেওয়া আছে। অনেক ফোন আসার মাঝে হয়তো বা দুই কণ্ঠস্বরের ফোন আসবে। কখনও তুলতুল, কখনও নমিতার। ওরা জানতে চাইবে, ইমন ফিরেছে?