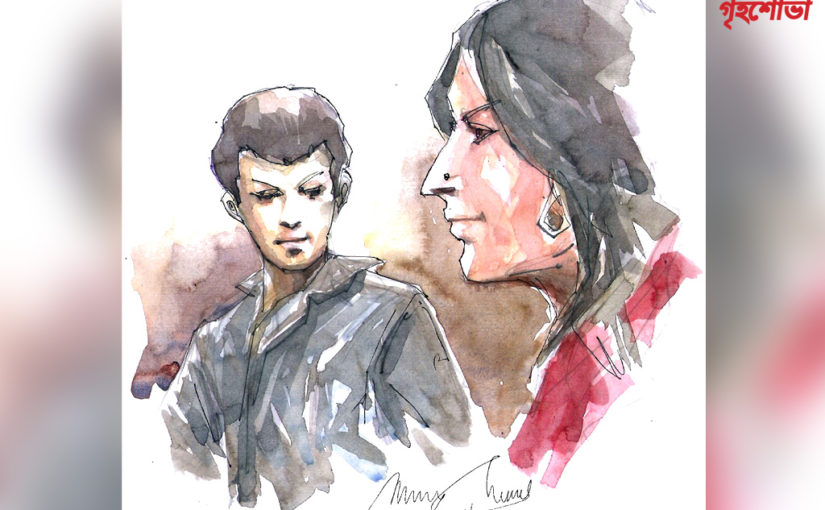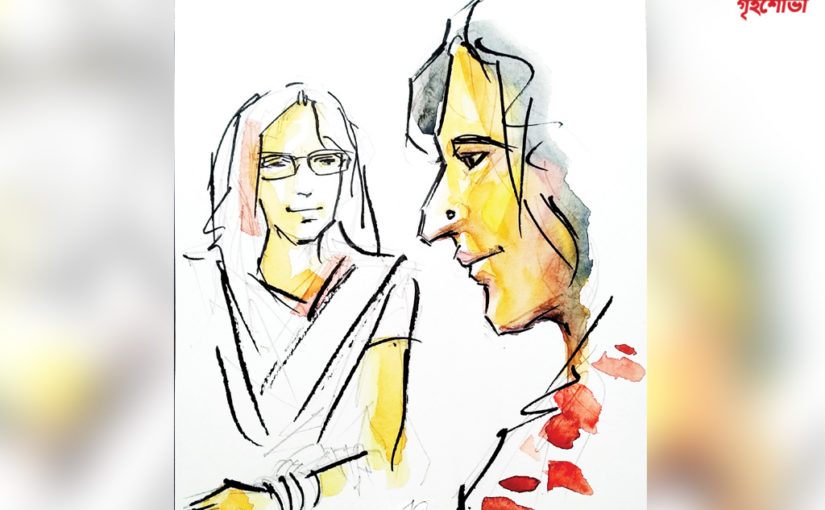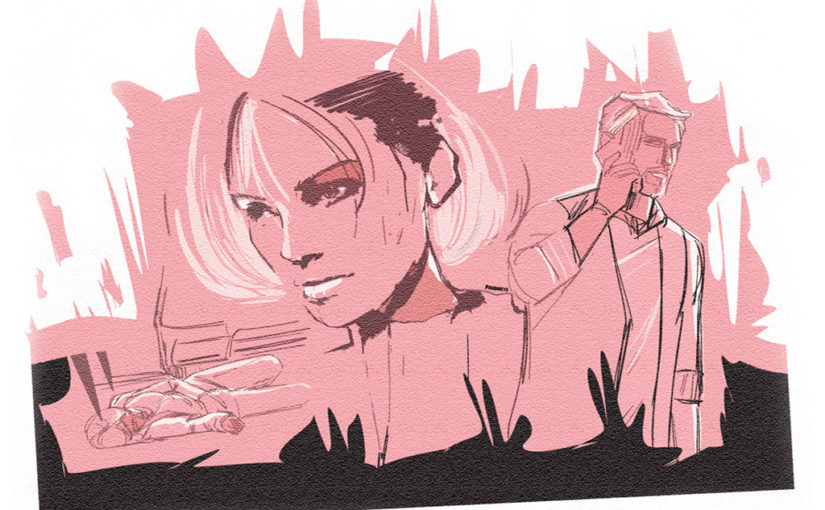অলকানন্দা,
প্রথম দর্শনে মানুষ প্রেমিকার প্রেমে পড়ে। আমি প্রথম দর্শনে তোমাকে চরিত্রহীন ভেবে বসি। তাছাড়া তোমার শরীরটাও বেশ পুরুষ্ট। সালোয়ারের ভেতর থেকে দুটো পুষি বিড়াল সবসময় উঁকি দেয়। প্রতি মুহূর্তে মনে হতো হাত লেগে গেলে ম্যাও করে ডেকে উঠবে। পরে বুঝেছি হুলোই। এসব অবশ্য শাহিনকে বলিনি। তোমার স্তন দুটোর দুটো নাম দিয়ে ছিলাম তুমি জানো? দোয়েল আর কোয়েল। মনে রাখার সুবিধার জন্য। আসলে আমি মনে মনে দুটোকেই হুলো বেড়াল বলতাম। অত সেজে বাড়িতে কেউ থাকে! থাকে হয়তো। আমার জানা ছিল না। তোমাকেই প্রথম দেখেছিলাম বাড়িতে অত সেজে থাকতে। অবশ্য তোমার থেকে প্রথম দেখা প্রথম শেখা জিনিস আমার জীবনে অনেক। অথচ তুমি আমি কেউ কারও প্রথম প্রেমিক বা প্রেমিকা ছিলাম না।
তোমার খিদিরপুরের যে-অঞ্চলে বাড়ি, সেটা মারদাঙ্গা, খুনখারাপি, রাহাজানির জন্য এক সময়ে কুখ্যাত ছিল। তখন থেমে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু বদনামটা এখনও রয়ে গেছে। বিশেষ করে আমার মতো মফস্সলের ছেলের কাছে তো বটেই। অবশ্য পৃথিবীর যে-কোনও বন্দর শহরের সে বদনাম একটু আধটু থাকেই। তাই বলে কি সেখানে সুন্দরী থাকে না! জলপরিদেরও তো জল থেকে উঠে আসতে বন্দর লাগে। লাগে না? না লাগলে তুমি ওখানে গেলে কী করে?
বদনামটার ভয়ে সেদিন শাহিনকে সঙ্গে নিয়েছিলাম। ও বেচে গাড়ি আর আমি গাড়ির ইনসিওরেন্স। সেদিন ওর ওদিকে কোনও দরকারই ছিল না। ওকে বলেছিলাম তোমরা একটা নতুন প্রাইভেট কার নেবে। আমরা দুজনেই গুড্স ভেহিকেলস মানে মালবাহী বড়ো বড়ো লরির এক্সপার্ট। কিন্তু তোমরা তখন সবে চবিবশটা লরির ফ্লিট্ নিচ্ছ। শাহিন আপশোশ করছিল, লিডটা আগে পেলে ও ডিলটা ডান করতে পারত। মার্কেটে চাপা খবর ছিল, তাই ওকে কারের টোপটা দিই। মার্কেটিং লাইনে এসব টুকটাক মিথ্যে কথা চলতেই থাকে। শাহিনও হয়তো মিথ্যেটা বুঝেছিল, কিন্তু ও একবার তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাইছিল যদি পরে কখনও গাড়ি কেনার সময় ওকে ডাকো।
খিদিরপুর অঞ্চলে তোমাদের অনেকগুলো বাড়ি। গলি, তার ভেতরে গলি, কখনও কখনও কানা গলিতে ধাক্বা মেরেছি বাইক নিয়ে। তোমাদের ব্যাবসার তখনও অফিস ছিল না। সবে সবে ব্যাবসায় নেমেছ। বাড়ির ঠিকানা একটা ছিল। কিন্তু ঠিকানা থাকলেও কলকাতাতে বাড়ি খুঁজে পাওয়া যে এত কঠিন, সেদিন প্রথম বুঝেছিলাম। গলিগুলোর কত বাহারি নাম। হরিমঞ্চলেন, রামবাবু গুপ্তা রোড, এডেন ভিলা রোড! বললাম না তোমার থেকে কত কী প্রথম শিখেছি। অথচ সেল্সে কয়েক বছর কাজ করার সুবাদে কলকাতায় এ-মাথা ও-মাথা করেছি, কখনও কখনও বাড়ির নাম্বার, রাস্তার নাম না জেনে কিছু ল্যান্ডমার্ক জেনে নিয়েই ঠিক পৌঁছে গেছি।
অনেকটা গলির ভেতর তোমাদের প্রথম বাড়িতে পৌঁছে শুনলাম ঋষি রাজা লেনের বাড়িতে গেলে মালিককে এখন পাওয়া যাবে। গলির ভেতরে গাড়ি ঘোরানো কী যে কষ্টের তোমাকে বোঝানো যাবে না। ওই রকম সরু গলির ভেতর অত লোক যাতায়াত করে সব সময়, বাইক ঘোরাতে গেলেই বোঝা যায়। দু-দিক দিয়ে হইহট্টগোল। জলদি কিজিয়ে, জলদি কিজিয়ে! আরে বাবা জলদিই তো করছি। জলদিরও তো একটা সময় লাগে নাকি!
তবে তোমাদের প্রথম বাড়িটা গলির অনেক ভেতরে হলে কী হবে, ঢুকেই বুঝেছিলাম অর্থের বৈভব। একটা ছাবিবশ-সাতাশ বছর বয়সি ছেলে, পরে তুমি বলেছিলে তোমার ভাই, হিন্দিতে খুব রোয়াবে ঠিকানাটা বলেছিল। অর্ধেক বুঝিনি। শাহিন চট করে ধরে নিয়েছিল ঠিকানাটা। ওর মামার বাড়ি ওই অঞ্চলেই। ছোটো বেলায় খুব থাকত। পার্ক সার্কাস লোহাপুলের বাড়ি থেকে খিদিরপুর কার্ল মার্ক্স সরণিতে সাইকেল নিয়েই যাতায়াত করত তখন। এখন রয়েল এন্ডফিল্ড। যাকে তুমি বুলেট বলো। তোমার বরের তো বুলেট ছিল, বলেছিলে।
দ্বিতীয় বাড়িটায় পৌঁছোলাম চট করে। রাস্তাটা শাহিন চিনত। ওর বাল্যবন্ধুর বাড়ি। আর বাড়িটাও চওড়া রাস্তার ধারে। অথচ দেখো চওড়া রাস্তার নামে লেনের পদবি আর গলিগুলোর রোড, স্ট্রিট। পরে এই নিয়ে দুজনে খুব হাসাহাসি করেছিলাম তোমার মনে আছে? কিন্তু দ্বিতীয় বাড়িতে গিয়ে শুনলাম মালিকের শরীর খারাপ, তাই জিতেন সিং স্ট্রিটের বাড়িতে রেস্ট নিচ্ছেন। এ লোকটা তোমাদের ভাড়াটে। খুব বাবু বাবু করছিল।
দুপুর ঢিঢি করছে চারিদিকে। গরমকাল ছিল মনে আছে। সেল্স-এর লোকেদের অবশ্য এসব অভ্যাস আছে। আমরা মনে মনে নাছোড়বান্দা যে-কোনও সেল্স কলেই। বিশেষ করে এক সাথে চবিবশটা গাড়ির ইনসিওরেন্স মানে আমার বাঁধা ইনসেন্টিভ সে মাসে! অনেকদিন ধরে বউ একটা বালা চাইছিল। সেটা মাথায় ছিল। ফিরে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না। তবু একটা তো মানসিক ক্লান্তি আসে। দুই বন্ধুতে রাস্তার পাশের গুমটি থেকে দুটো দামি ব্র্যান্ডের মেন্থল সিগারেট কিনে ধরাই। আমাদের টিফিন বলো, রেস্ট বলো সবই ওই সাদা কাঠির সুখ টান আর ধোঁয়া ভর্তি গালের জাবর কাটা। অবশেষে তৃতীয় বাড়িতে তোমাদের পেলাম। না তোমাকে তো খুঁজতে যাইনি। চবিবশটা ফ্লিটের মালিকের সন্ধান পেলাম।
খিদিরপুর অঞ্চলের গলির ভেতর গলি, তার ভেতরে বাড়ি যে এত বৈভবের হতে পারে ধারণা ছিল না। তৃতীয় বাড়িটা ফ্ল্যাট টাইপের। প্রথম বাড়িটার থেকেও বেশি সাজানো। বাড়িগুলো বাইরে থেকে ইট বালির কঙ্কাল লাগে কিন্তু ভেতরের আসবাব, মেঝে, দেয়ালের কারুকাজ সব অন্যরকম। ওই ঘিঞ্জির মাঝেও যে ইটালিয়ান মার্বেলের মেঝে দেখব ভাবিনি। পুরো ফ্ল্যাটটাই সেন্ট্রালি এসি। গরম থেকে বাড়িতে ঢুকতেই এক রাশ স্বস্তি। যতটা না এসির কৃত্রিম ঠান্ডার জন্য, তার থেকেও বেশি অবশেষে চবিবশটা ফ্লিটের মালিকের কাছে পৌঁছোতে পারার জন্য। দুজনের দুটো ভালো পদ-নাম ছিল। আমি সেল্স ম্যানেজারের তকমা নিয়ে ঘুরি আর শাহিন ব্রাঞ্চ ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার। আসলে আমরা বেচুবাবু। মাল বেচাই কাজ। আমরা যা পাই বেচে দেবার সুযাগ খুঁজি।
অনেক বার বলেছি, তোমাদের ফ্ল্যাটটার নকশা ভালো নয়। কোনও প্রাইভেসি নেই। অতবড়ো ফ্ল্যাট অথচ উদোম। প্রথমে তোমাকে দেখার কথাটা বলি। চবিবশটা ফ্লিটের মালিকের নাম সতীশবাবু, টাইটেল জানি না। আধজানা ঠিকানায় পৌঁছে দেখলাম বড়ো ফ্ল্যাট। নিঃশব্দ। বয়স্ক কাজের মহিলা দরজা খুলে ড্রইংরুমে বসতে দিয়েছে। সোফাটা দামি। বসতেই ডুবে গেলাম। বসেছি ভেতরের দিকে মুখ করে। অপেক্ষা করছি। বেশ অনেকক্ষণ। মনে মনে সাজিয়ে নিচ্ছি বিমাকথা। যে-কোনও ভাবে তুলতেই হবে চেকটা। বউ যে নতুন ডিজাইনের বালা দেখেছে, এক জোড়া না একটাই বানাবে বলেছে। ইনসিওরেন্স ইজ আ সাবজেক্ট ম্যাটার অফ সলিসিটেশন। গুলি মার সলিসিটেশনের। যে করে হোক চেকটা আমার চাই।
আমি বা শাহিন কেউ কথা বলছি না। কাস্টমারের বাড়িতে আমরা একদম শান্ত ভদ্র। চোখে চোখে কথা হচ্ছে। ঠোঁটের অল্প নড়াচড়াতে দুজনে দুজনের ভাষা বুঝতে পারি। দু-একবার পর্দার আড়ালে তোমাকে দেখলাম। নিঃশব্দে নড়াচড়া করছ। আমি আর শাহিন চোখাচোখি করলাম। আবছা অবয়ব। শরীরের বর্ণনা দেব না। প্রেমিকার শরীর নিয়ে কথা বলা নোংরামি। কিন্তু দুজনে তোমাদের সোফায় বসে চোখ দিয়ে নোংরামিই করছিলাম। ওসব ছেলে ছেলেতে হয়ে থাকে। রাগ কোরো না। আর তখন কি জানতাম যে তোমার সাথে ওরকম দুনিয়া ভোলানো প্রেম হবে। আমি দেখতে শুনতে ভালো, লোকে স্মার্ট বলে। বেশ লম্বা চওড়া। ফর্মাল ড্রেসে সবাইকেই ভালো লাগার কথা। তাই বলে তোমার মত মারকাটারি সুন্দরী, সেক্সি বলব না। প্রেমিকাকে সেক্সি বলতে নেই, আমার সাথে প্রেম করবে ভাবতেই পারিনি।
মিনিট কুড়ি মানে অনেকক্ষণ। নতুন জায়গায় এসে বসে আছি অথচ কেউ কোনও কথা বলছে না। কোনও শব্দ নেই। নিঝুম। শুধু তুমি হেঁটেছ কয়েক বার খসখস করে। ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ হওয়ার পরেই বাইরের রোদ, তাপ, কোলাহল থেকে বহুদূরে চলে এসেছি। অন্য একটা শহর মনে হতে শুরু করেছে। ঘরের আসবাব সব অন্যরকম। একবার সদর স্ট্রিটের একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ানের বাড়িতে ঢুকে এরকম মনে হয়েছিল। যেন অন্য শহরের বাড়ি। সে বাড়িটা অবশ্য কেমন পড়ো শহর মনে হয়েছিল। আর এ বাড়িটা খুব উজ্জ্বল। মনে হচ্ছে কোনও অন্তরীপ শহরের আসবাব।
সেল্সম্যানদের ধৈর্য অকল্পনীয়। তবু অস্বস্তি হতে শুরু করেছে। বাইরে বাইকটা পড়ে আছে। এ অঞ্চলের বদনাম ভয় ধরাচ্ছে। চুরি গেলে ইনসিওরেন্সের ফুল ক্লেম পেলেও নতুন বাইক হবে না। আর ক্লেম পেতেও বেশ সময় লাগবে। ততদিন চলবে কী করে! তখনই তুমি বাইরে এলে, এক বৃদ্ধকে প্রায় জাপটে ধরে বাথরুমে নিয়ে যাচ্ছ। একজন পুরুষ আর নারীর প্রকাশ্যে জাপটে থাকা সব সময়ই অশোভন। আর তোমার সেজে থাকা! নেল পালিশ, লিপস্টিক, টিপ। সব কিছু গুলিয়ে দিচ্ছিল তোমার ফেটে পড়া শরীর। অনেক সুন্দরী দেখেছি কিন্তু তোমার মতো যৌবনবতী সুন্দরী আর দেখা হয়নি। তাছাড়া সতীশবাবু বৃদ্ধ হলেও বৃষস্কন্ধ, বয়সের তুলনায় সুঠাম। আমার দোষ কী বলো!
শাহিনও তো তোমাকে ভুল বুঝেছিল। আমি ও শাহিন তোমাকে নিয়ে কত কী ভেবেছি। তৃতীয় পক্ষের বউ, বউমা, নাতনি এমনকী রক্ষিতাও। সেই জন্যই তোমাকে বললাম না, প্রথম দর্শনেই তোমাকে চরিত্রহীন ভাবি। তোমাকে নিয়ে কত গবেষণা করেছি দুজনে। তবু বাপ-মেয়ে একবারও ভাবতে পারিনি। ওরকম জাপটে থাকলে কেউ ভাবতে পারে না। তুমি পরে বলেছিলে বাবা অসুস্থ ছিল। সরি অলকা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে তুমি সতীশবাবুকে আমাদের কাছে সোফায় বসিয়ে দিয়ে গেলে। বসাতে গেলে ঝুঁকতেই হয়। আর ঝুঁকতেই তোমার সালোয়ারের ভেতর থেকে দুটো পুষি বিড়াল উঁকি দিয়ে গেল।
কাজের কথা বিশেষ কিছু হল না। তুমিও ওই যে সতীশবাবুকে বসিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকে গেলে আর বেরোলে না। সতীশবাবুর সামনে থেকে তো আর ঘরের পর্দার দিকে তাকিয়ে তোমাকে খোঁজা যায় না। তবু মনে মনে খুঁজছিলাম, যদি আর একবার দেখা যায় সুন্দরীকে। সতীশবাবু জাহাজে কাজ করতেন। আর জাহাজি মানুষের গল্পের শেষ নেই। সমুদ্র বৈচিত্র্যহীন কিন্তু বন্দরের তো গল্প অনেক। তখনই বুঝলাম তোমাদের বাড়ির অঙ্গসজ্জায় কেন বিদেশি সুবাস। বুঝলাম তোমার বাবা আর সমুদ্রে যেতে চায় না, এবার স্থলপথে আয় চায়। অনেক কষ্টে মুক্তি পেলাম। গল্প শুনতে ভালোই লাগছিল। কিন্তু কাজের তাড়া সেল্স-এর লোকেদের তাড়িয়ে বেড়ায়। এডেন বন্দর, তাহিতি, সুয়েজ ক্যানাল এসব গল্প কার না ভালো লাগে। আমার ভূগোলে জ্ঞান খারাপ, তবু ভালো লাগছিল। কানের মধ্যে একটা নতুন পৃথিবী তৈরি হয়ে পৌঁছে যাচ্ছিল হূদয়ে। শুধুমাত্র সতীশবাবুর মোবাইল নাম্বারটাই পেয়েছিলাম সেদিন। কবে আসব ইন্সিওরেন্সের জন্য জিজ্ঞাসা করতে নাম্বারটা দিয়ে বলেছিলেন, আসক্ মি ওভার টেলিফোন অ্যান্ড গিভ মি দ্য কোটেশন! তোমার বাবা ইংরেজি ছাড়া প্রায় কথাই বলতে পারে না।
চিঠিটা খুব বড়ো হয়ে যাচ্ছে জানি। আসলে আমারও তো বয়স বেড়েছে আরও দু-বছর, তোমারও। তোমার আমার গল্পও জমে গেছে অনেক। খুব স্মৃতি জমে গেলে রোমন্থন করেই আনন্দ। এসব কথা ফোনে হয় না। তুমি পড়লে আনন্দ পাবে ভেবেই লেখা। গতকাল আর আগামীকাল দুটোই আমাদের জীবনে দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিন। তাই লিখছি আনন্দে আর বিষাদে।
শাহিনের কাছে সতীশবাবু নেগেটিভ কাস্টমার। আমার কাছে ইনসেন্টিভ, বউ-এর গয়না গড়িয়ে দেওয়া প্রত্যাশা। আমি ফলো আপ করব ঠিক করেই সতীশবাবুর থেকে বিদায় নিলাম। তোমাকে নিয়ে বেশি কথা ভাবার ছিল না। শাহিনের সাথে দেখা হলেই ও তোমার রূপ, রূপসজ্জা অথবা রূপটান নিয়ে বলে। তার বেশি কিছু না। আমিই শরীরের বেশি বর্ণনা দিতাম। শাহিন শুনত। তবে তোমাকে নিয়ে আমরা অন্য কোনও লোকের কাছে কথা বলতাম না। যেন আমাদের গোপন অভিযানে পাওয়া সম্পত্তি। জানাজানি হলে অংশীদারের ভয়।
তিনদিন পরে সতীশবাবুকে ফোন করলাম। তোমার বাবা কোটেশন চাইল। কোটেশন তো তৈরিই ছিল। আমি বললাম এখুনি দিয়ে আসছি। এবার আর শাহিনকে নিলাম না। চেনা হয়ে গেছে। সোজা চলে গেলাম জিতেন সিং স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে। যে-ফ্ল্যাটে তোমাকে প্রথম তোমার বাবার সাথে দেখেছিলাম। একবারও ভাবিনি অন্য কোনও বাড়ির কথা।
তোমার একটা অমোঘ টান তো ছিলই। দরজা খুললে তুমি নিজেই। খুব অবাক হলাম তোমাকে দেখে। বিষণ্ণতার ঘন কুয়াশা তোমায় যেন মুড়ে রেখেছে। সেই প্রথম তোমার উপর মায়া হল। ধনীকে হঠাৎ গরিব দেখলে যেমন মায়া লাগে তার অস্বাচ্ছন্দ্যর কথা ভেবে, তেমনি। ভুল ভাঙল একটু পরেই। তুমি ভেতরে বসালে, যেন বাবাকে ডাকতে গেলে। বেশ কিছুক্ষণ আমি একাই সোফায়। খুব অস্বস্তিকর সময়। বাড়িতে একটাও বই নেই। টিভিও নেই যে চোখ মেলে সময় কাটাব। তোমার বাবা এল না। তুমিই এলে। আমার সামনের সোফায় বসলে। বসেই আমাকে সপাটে প্রশ্ন করলে, হ্যাংলার মতো আগের দিন তাকিয়ে ছিলেন কেন? আমি কী উত্তর দেব! লম্বায় ছয় ছুঁই ছুঁই কিন্তু লজ্জায় তখন জল ছুঁই ছুঁই। সেল্স লাইনে আমাকে সবাই ড্যাম স্মার্ট বলে। আমি বেচুবাবু হিসাবে যথেষ্ট কৃতি। গত তিনবছরে আমার মাইনে বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে, প্রোমোশন আর কোম্পানি পালটে। সেই আমি এসির ঠান্ডায় ঘামতে শুরু করি। এক গেলাস জল হলে ভালো হতো। ভাবি, একটা কমপ্লেন দিলেই চাকরিটা যাবে। আর এ-লাইনে চাকরি পাওয়া যাবে না। বউ বাচ্চা খাবে কী!
আমার অবস্থা দেখে তুমি নিজেই হেসে উঠলে। ছোটোবেলায় কুলগাছ নাড়িয়ে যেমন পাকা কুল পাড়তাম, কুল কুল করে তেমনি তুমি হেসে উঠলে। কোটেশন এনেছেন? দিন। বাবাকে দিয়ে দেব। এটা আমার বাড়ি। বাবার বাড়ি নয়। হাসতে হাসতে শুরু করে গম্ভীর হয়ে শেষ করলে কথাগুলো। পরে জেনেছি তুমি নাকি জানতে আমি আসব ওই ফ্ল্যাটেই। তুমি নাকি জানতে আমি ভালোবাসবই।
২৮ মার্চ, রবিবার ৮.১০ সকাল
জামদানীপুর।
রাজেন্দ্রনন্দিনী অলকানন্দা,
বাজার করতে গিয়েছিলাম। তুমি অবশ্য বাজার করা ব্যাপারটা বুঝবে না। নিজের হাতে বাজার করাটা খুব মজার ব্যাপার। টাটকা সবজি বেছে কেনা বা বড়ো হাঁসের ডিমটা খুঁজে নেওয়া। তোমরা ধনী। তোমাদের নিজস্ব বাজার সরকার আছে। সে-ই বাজার করে আনে। তিন বাড়িতে ভাগ করে দেয় বাজার। তুমি অবশ্য বেশির ভাগ দিন হোটেল থেকে খাবার কিনে আনাও বলেছ। তুমি ঝাল খেতে ভালোবাসো। লুকিয়ে দেখা করতে এসে দু-একবার তোমার বাড়িতে রান্না করা খাবার, টিফিন বাক্সে এনেছ। কী ঝাল, কী ঝাল! ঝালে আমি মরে যাই অবস্থা। আমি ভাবলাম তোমার জিভ থেকে ঠান্ডা নেব কিন্তু তোমার জিভও অত ঝাল কে জানত! তুমি ওই ঝাল চিলি চিকেন খেয়েই বেরিয়েছ বাড়ি থেকে। আমাকে বলোনি কেন? সেদিন তোমাকে বিষকন্যার মতো লাগছিল। সেদিন সেজেও ছিলে পাকা লংকা রঙের শাড়িতে।
প্রথম থেকেই তোমাদের ব্যাপারগুলো কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে ছিল। তোমার বাবার ইংরেজি আর ভাইয়ের হিন্দি শুনে ভেবেছিলাম তোমরা অবাঙালি হবে। ‘সতীশ সিং’ তোমার বাবার নাম লিখেছিলাম ইন্সিওরেন্স কভার নোটে মনে আছে। পরে তুমি বললে, তোমরা মুঙ্গেরের প্রবাসী বাঙালি। সিনহা, সিংহ হয়ে সিং-এ পৌঁছেছে। বারুইপুরে তোমাদের আদি শিকড়। বারুইপুর থেকে কয়েক পুরুষ আগে ভাগ্য অন্বেষণে মুঙ্গের। আবার ফেরা কলকাতায়। তোমার সাথে না আলাপ হলে জানতাম না, বারুইপুরে তোমার বাবার বিশাল অট্টালিকার কথা। অবশ্য তোমার সাথে আমার যেটা হয়েছে সেটা আলাপ নয়, দুকূল ছাপানো প্রেম। বারুইপুরের উঁচু পাঁচিল দেওয়া বাগানবাড়িতে একটা যৌবনবতী মহিলা কী করে বালিকাবেলায় ফিরে যেতে পারে সেদিন দেখেছিলাম। সেই প্রথম তোমাকে অযৌনতায় দেখি। খালি পায়ে মেক্সিকান ঘাসের উপর দৌড়োতে দৌড়োতে ক্লান্ত হয়ে আমার কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়েছিলে। আমি ঘাসে বসে তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম, যেমন বাড়িতে তিন বছরের মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।
আমার মেয়ে তিন্নি খুব আদর খেতে চায়। খুব বায়না। এটা আনবে ওটা আনবে। আজ ক্যাডবেরি তো কাল খেলনা গাড়ি। ওর বায়না মেটাই বলে আমার বউ খুব রাগ করে। মানসী স্কুল মাস্টারের মেয়ে। ওর কাছে আদর্শ ব্যাপারটা সহজাত। পয়সা একদমই নষ্ট করতে চায় না। নিজে দামি পরবে না, মেয়েকেও পরাতে দেবে না। আমার ওইটুকু মেয়ের সাজার খুব শখ। ঠিক তোমার মতো। মাঝে মাঝে মনে হয় তিন্নি তোমার মেয়ে। মানসীর সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র তোমার ও তিন্নির। মানসী অপ্রয়োজনে সাজে না। বাড়িতে টিপ পরতে বললেও লজ্জা অথচ মানসী দেখতে ভালোই। মুখশ্রী সুন্দর। তোমাকে তো আমাদের বিয়ের ফটো দেখিয়েছি। বাড়ি থেকে লুকিয়ে অ্যালবাম নিয়ে গেছি আমাদের বিয়ের। তুমি বহুবার আমাকে বলেছ তুমি মানসীকে খুব পছন্দ করো। আর তিন্নিকে তোমার খুব ভালো লাগে বলে সেই পছন্দটা এসেছে। তিন্নিকে তুমি বহুবার দেখতে চেয়েছ কিন্তু তিন বছরের মেয়েকে কী করে দেখাই বলো? আরও একটু বড়ো হোক কলকাতায় তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাব। এই মফস্সল থেকে এখনই নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মানসী এখন তিন্নিকে আমার সাথে একা ছাড়বেও না।
আমার মেয়ের কথা, বউয়ের কথা সব বলেছি। আমার বাড়ির সব কথাও। বাবা ঠাকুরদার গরিব জীবনের কথা। বিয়ে করার কথা। অথচ তুমি নিজের কথা ছাড়া বিশেষ কিছু বলতে চাও না। তোমার বাবার কথা মায়ের কথা প্রায় কিছুই বলোনি। যেটুকু জেনেছি তাও আমার অনন্ত প্রশ্নের আগ্রহে শোনা। তোমার মা দুটো বলেছিলে। তারা দুজনেই বেঁচে আছে না মরে গেছে কোনওদিন বলোনি। তোমার ভাই যাকে আমি প্রথমদিনই শাহিনের সাথে প্রথম বাড়িতে দেখি, সে কি তোমার সৎ ভাই? জিজ্ঞাসা করলে তুমি এড়িয়ে যাও। এই সব ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলেই তুমি শরীর দেখাও আর আমাকে জাগিয়ে দাও শরীরে। আমি রম্ভার শরীর দেখি, মাখি, ছানি, অসম্ভব সব বক্রতা থেকে আমার মনের মতো যৌনতা খুঁজি। আমাকে তুমি এত শরীরী-সুখ দিয়েছ মাঝে মাঝে মনে হয় তুমিই স্বর্গ অথবা চরম সত্য। অথচ তোমার সাথে যৌনসম্ভোগ তখনও হয়নি। চূড়ান্ত সম্ভোগের কোনও সম্ভাবনাও ছিল না। তুমি কিছুতেই রাজি ছিলে না। তুমি আমাকে শরীরে মাখতে কিন্তু শরীরে নিতে রাজি ছিলে না।
আজ রবিবার। বাজার করে এনে দিয়েছি। এখন খাবার সময় হয়ে এসেছে। মুড়িঘণ্ট ডাল আর খাসির মাংস। স্নান করতে হবে এবার। অথচ কিছুতেই স্নান করতে ইচ্ছা করছে না। গত দু-বছর আমাদের সম্পর্ক। দু-বছরে অনেক কথা হয়েছে। তুমি ভালোবাসবে না শুধু বন্ধুত্ব রাখতে চেয়েছ। সেখান থেকে অনেক কষ্টে তুমি স্বীকার করেছ ভালোবাসো। ভালোবাসা ছাড়া সম্পর্কটা টিকত না। ‘ভালোবাসি’ কথাটা তোমার মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলাম। একটা অন্য রকম স্বীকৃতি। তুমি বললে, সেই অমোঘ শব্দরাশি ভালোবাসি, ভালোবাসি। আমাকে বললে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে ভালোবাসো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম বরের থেকেও? তুমি থমকে গেলে। তারপর আবার সময় চাইলে। তোমার বর কী করে, কোথায় থাকে জানি না। পরে বলেছ সেও বাবার মতো জাহাজি। বাবার দেখে দেওয়া পাত্র। সেও নীল সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়। নীল আকাশে সমুদ্র-পাখি খোঁজে। আমি বলেছিলাম নাবিকের সংসার তো বন্দরে বন্দরে। তুমি কোনও উত্তর দাওনি। আমার মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়েছিলে অসম্ভব যৌনতা। আমি বাকরুদ্ধ হয়ে যাই তোমার কৌশলে। আমার সমস্ত প্রশ্ন হারিয়ে যায়। আমি তখন শিশুর মত পৃথিবী ভুলে মায়ের কোল খুঁজি নির্মল আনন্দে। আমার নিবাস, আবাস, পরবাস, সুবাস তখন তোমার মধ্যে। তুমি নিতেও পারো আমাকে অসম্ভব। যেন তুমিও আমার মধ্যে খুঁজতে অন্য পৃথিবী। একটা দুরন্ত বালকের মাতৃত্ব সামলানোর মতো আমায় তৃপ্ত করতে, দৃপ্ত করতে, দৃঢ় করতে।
আজ কিছুতেই স্নান করতে ইচ্ছা করছে না। গত দু-বছরে আমরা দুজনে দুজনকে কাল প্রথম সম্পূর্ণ পেলাম। তুমি স্বীকার করেছ আমাকেই সব থেকে বেশি ভালোবাসো। আমিই তোমাকে সব থেকে বেশি বুঝি অথবা তুমি আমার সঙ্গেই সময় কাটিয়ে সব থেকে বেশি সুখ পাও। তোমার কোনও সন্তান নেই। তবু তুমি আমার সাথে পালাতে পারবে না। আমার সংসার তুমি ভাঙতে চাও না। আর আমিও যতই তোমাকে ভালোবাসি, মানসীকে বা তিন্নিকে ছাড়তে চাই না। তোমার মতো উদ্ভিন্ন যৌবনা মেয়ে আমার মধ্যে কী দেখেছে জানি না কিন্তু কাল প্রথম যখন অনেক দূরের একটা হোটেলে আমাকে শরীরে নিলে, আমার মনে হয়েছিল তুমিও আমাতে তৃপ্ত। শুধু একবার চরম তৃপ্তির আগের মুহূর্তে দ্বিতীয় দিনে দেখা বিষণ্ণতা কয়েক পলের জন্য ফিরে এসেছিল। কাল আমাকে যেতেই হবে। কোম্পানি আমাকে সেল্স ম্যানেজার থেকে অসমের তিনসুকিয়ায় ব্রাঞ্চ ম্যানেজার করে পাঠাচ্ছে। এটাও সম্ভব হয়েছে তোমাদের চবিবশটা গাড়ির ইন্সিওরেন্স পাবার জন্য। তুমি আমার চলে যাওয়ার ব্যাপারে কোনও মতামত দাওনি। তুমি কি চাইছ আমি দূরে চলে যাই? না হলে একবারও কেন বললে না থেকে যেতে? কালই তোমাকে পুরোপুরি পেলাম আর আজ আমাকে চলে যেতে হবে ভাবলেই কষ্ট হচ্ছে। তুমি অবশ্য কথা দিয়েছ তিনসুকিয়ায় আসবে। থাকবে বেশ কিছুদিন। খুব মজা হবে পাহাড়ি ঝরনার নীচে জলপরিকে পেলে! এখন যাই। স্নান করি। না হলে মানসী রাগারাগি করবে। শরীরে তোমার সুবাস নিয়ে আবার আজ শাওয়ারের নীচে দাঁড়াব শুধু আজ পাশে তোমাকে, রতিক্লান্ত তোমাকে পাব না।
২৮ মার্চ, ১.৫৫ দুপুর,
জামদানীপুর।
অলকানন্দা,
চিঠিগুলো পোস্ট করা হয়নি। ভেবেছিলাম পরিষ্কার করে আবার লিখে তোমাকে তিনসুকিয়া থেকে পোস্ট করব। কিন্তু এখানে এসে চার্জ নিয়ে সব কাজকর্ম বুঝে নিতেই দিন দশেক হয়ে গেল। তোমাকে এখানের ফোন নাম্বার আগেই দিয়ে এসেছিলাম। আমি অফিসে এসেও তোমাকে ফোন করেছিলাম দু-দুবার। দুবারই তোমার মোবাইল বেজে বেজে বন্ধ হয়ে গেল। তুমি বলেছিলে কোনও বিপদ বা জানাজানি হয়ে গেলে চুপচাপ হয়ে যেতে। ছ-মাস পর সব ঠান্ডা হয়ে গেলে আবার যোগাযোগ করা হবে। আমি ভয় পেলাম বোধহয় জানাজানি হয়ে গেছে! তোমার কথা ভেবেই আমার কলকাতার মোবাইল নাম্বার চালু রেখেছি। কলকাতার কাস্টমাররা বিরক্ত করছে, ইনকামিং টাকা কাটছে, তবুও তোমার কথা ভেবে চালু আছে আজও। আমি ধীরে ধীরে কাজের মধ্যে ডুবে যাই। এখানে অনেক দায়িত্ব। তবু রোজ রাতে তোমাকে ফোন করতে চাইতাম। এখানে একা থাকি। ফোন করলে বউয়ের কাছে ধরা পড়ার ভয় নেই। ফোনটা বুকে চেপে ঘুমিয়ে পড়তাম। ভাবতাম এই বুঝি তুমি ফোন করবে। তবু তোমার বিপদের কথা ভেবে কোনও দিন ফোন করতাম না। তুমি বলেছিলে তোমার বাবা জানতে পারলে অনার কিলিং-এ তোমার নাম উঠবে। আমি স্রেফ ভয়ে ফোন করিনি। চিঠি পোস্ট করার প্রশ্নই ওঠে না।
গত কয়েকদিন থেকে মনে হচ্ছে ধনীর মেয়ে, বড়োলোকের বউ। বর বিদেশে থাকে! শরীরের চাহিদায় তুমি আমার কাছে এসেছিলে। শরীর যখন পেলে তখনই আমাকে বহুদূরে চলে আসতে হল। তাই আমার প্রতি আর কোনও টান নেই। হয়তো এরকমই করো তুমি। বা সব নাবিকের ঘরনিই এরকম ভাবে সময় কাটায়। আবার মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি সত্যিই ভালো। যেমন দেখেছি তেমনই ভালো। শরীর চাইলে পাঁচতারা হোটেলে শরীর খেলাতে পারতে। সব রকমই ভাবছি। সন্ধে থেকে একা এবং অফুরান সময়। ভাবনারাও খেলে বেড়ায় বামদিক ডানদিক, দুদিক। ভাবছি চূড়ান্ত তৃপ্তির আগের মুহূর্তের বিষাদ ব্যাধ কী তির মারল যে, তুমি এক পলকের জন্য উদাস হয়ে গেলে! বরের কথা মনে পড়েছিল? অথবা ব্যভিচারের সূক্ষ্ম পাপবোধ?
সব ভাবনাই শুধু ভাবার জন্য। উত্তর পাওয়ার কোনও উপায় নেই। কেউ জানে না আমাদের গোপন সম্পর্ক। কেউ না। শুধু শাহিন হয়তো কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। শাহিনকে জিজ্ঞাসা করব কিনা কয়েকদিন মরিয়া চিন্তায় আছি। হঠাৎ কাল অনেক রাতে শাহিন ফোন করে। আমি তোমার ব্যাপারে জানতে যাব, শাহিনই তুলল তোমার কথা। জানো বস্ খিদিরপুরের সতীশ সিং-এর বাড়ির সেই সুন্দরী মেয়েটা উত্তরাখণ্ডের একটা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সুইসাইড করেছে। নদীটার নাম নাকি মেয়েটার নামেই ছিল। মেয়েটাকে মনে পড়ে তোমার?
১২ এপ্রিল সকাল ৮টা
বক্স রোড তিনসুকিয়া, অসম।